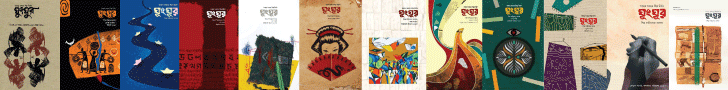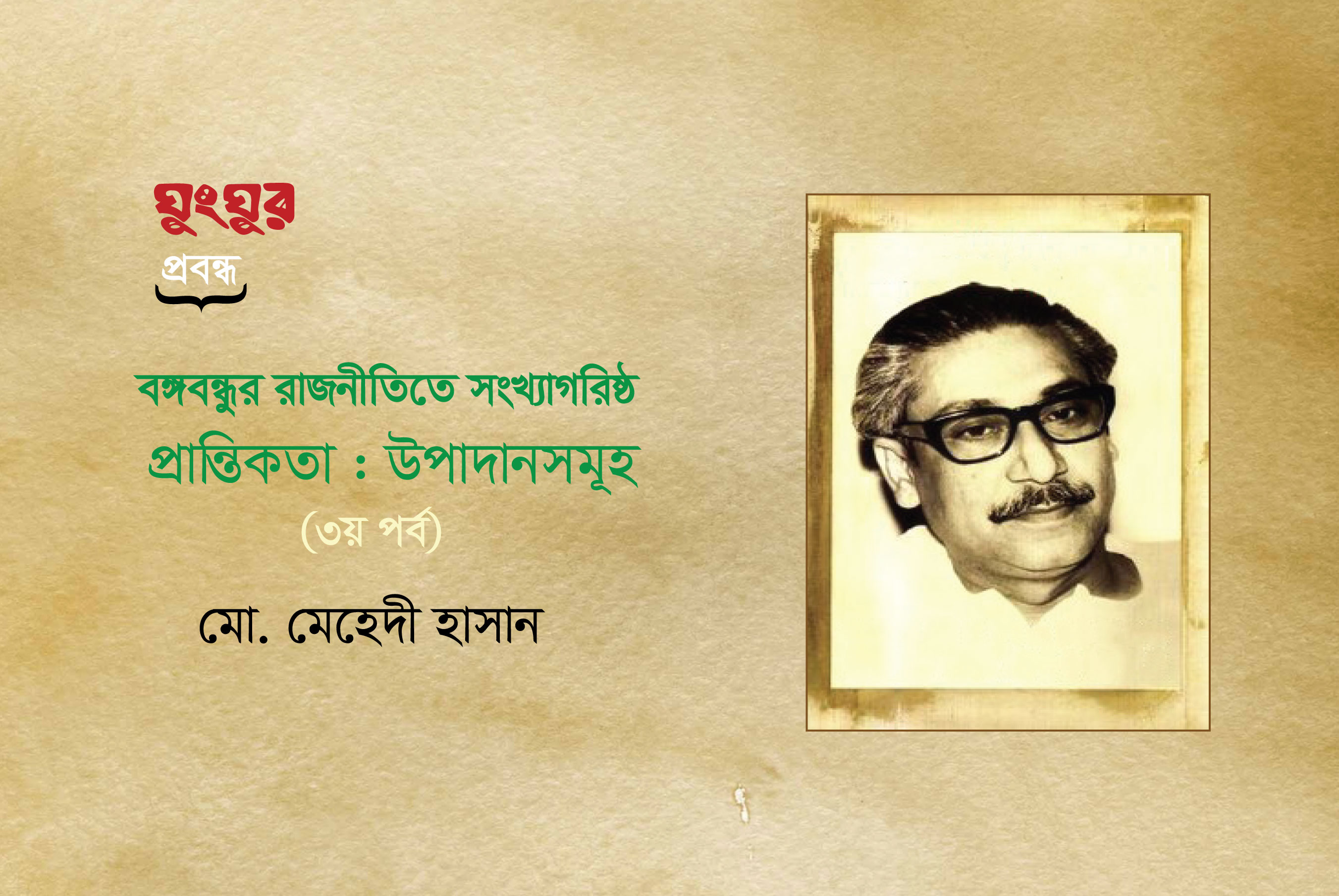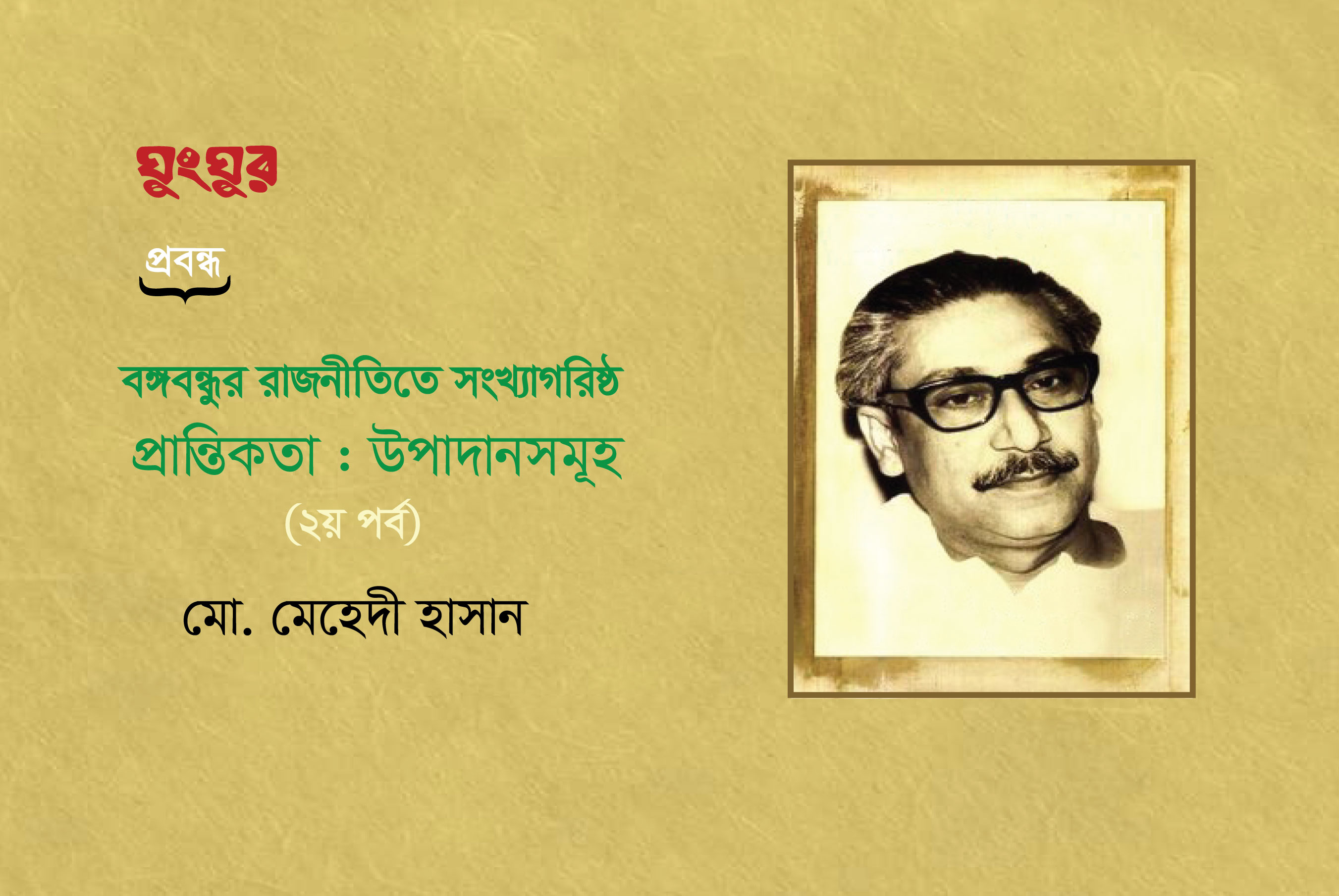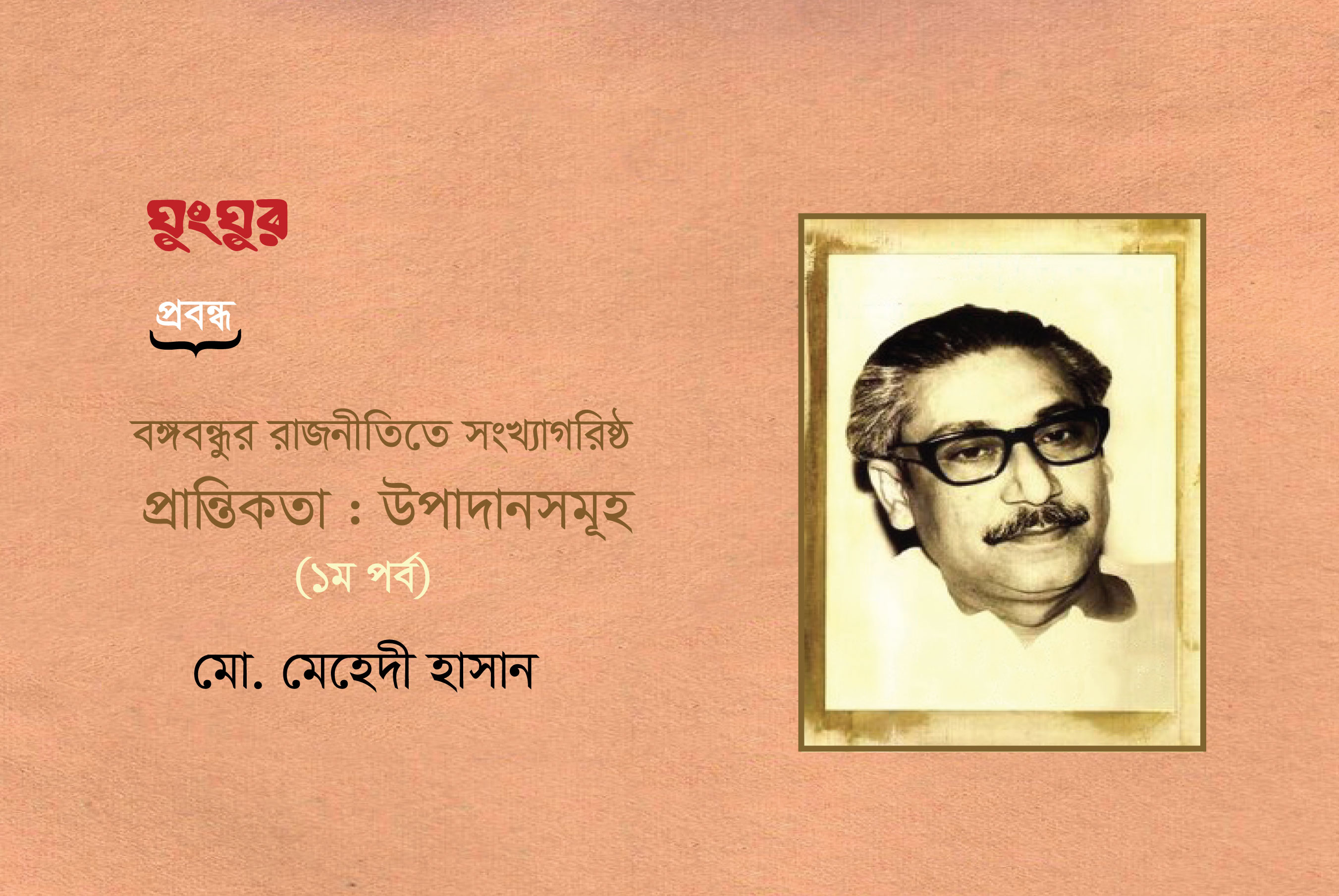তিনি গলায় বেঁধেছিলেন মুক্তির গান
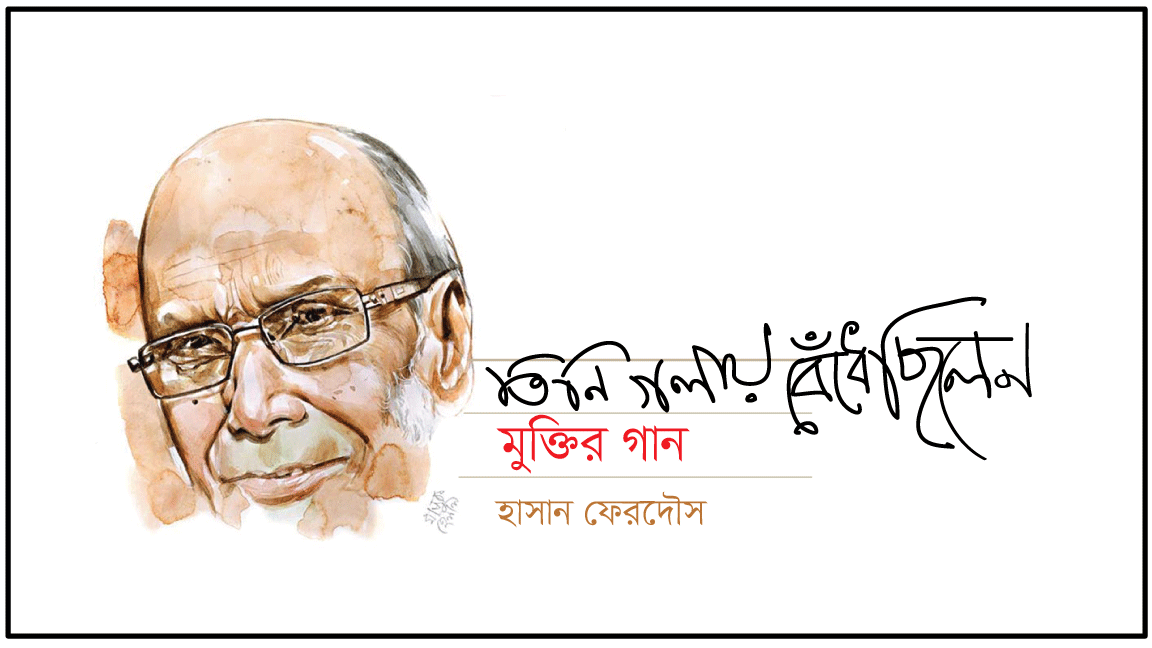
২০১৬ সালের মে মাসের কথা। লন্ডন যাবার আগের দিন খুব সকালে ফোন করেছিলেন সৈয়দ শামসুল হক। মে মাসের মাঝামাঝি তাঁর নিউইয়র্কে আসার কথা, মুক্তধারার বইমেলায়। সে বছর মেলার ২৫তম বার্ষিকী, তিনি থাকতে সম্মত হয়েছেন। কিছুটা নিম্নকণ্ঠ যেন, জানালেন তাঁকে চিকিৎসার জন্য লন্ডন যেতে হচ্ছে। ‘চিন্তা করো না, আমি নিউইয়র্কে আসছি।’ এবার যেন গলায় কিছুটা উত্তাপ নিয়ে বললেন, ‘শহীদের সাথে (কবি শহীদ কাদরী) আড্ডা হবে, তোমার সাথে মিউজিয়ামে যাব, ব্রডওয়েতে নাটক দেখব। আর হ্যাঁ, সেই যে গতবার জাপানি কাঁচা মাছ সুশি খেয়েছিলাম, সেটাও আরেকবার খেয়ে দেখব।’
অসুখ নিয়ে কোন উদ্বেগ আছে, গলায় তার আভাস পেলাম না। বিস্ময়ের কিছু নেই, বরাবরই তিনি আশাবাদী। দেশকে নিয়ে, বাংলা সাহিত্য নিয়ে, আগামী দিনের সম্ভাবনা নিয়ে, এমন আশাবাদী মানুষ বেশি চোখে পড়ে না। একাশি বছরের যুবক, পরনে ঝলসে যাওয়া জিন্স, পাট ভাঙা রঙিন জামা, সে জামার নীচে সুতোর মত সোনার চেইন। হাজার জনের মধ্যেও এমন একজন মানুষকে চিনে নেওয়া যায়। হাজার মাইল দূর থেকে ইথারে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরে তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পাই।
সৈয়দ শামসুল হককে আমরা সব্যসাচী লেখক বলি। কথাটার অর্থ দু’হাতে শর চালনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি। মহাভারতের নায়ক অর্জুনকে বলা হত সব্যসাচী, তিনি কেবল দু’হাতে শর নিক্ষেপেই পারদর্শী ছিলেন না, লক্ষ্যভেদেও তিনি ছিলেন অভ্রান্ত। সৈয়দ হক যথার্থই সব্যসাচী, শুধু এই কারণে নয় যে তিনি বহু বিচিত্র বিষয়ে দু’হাতে লিখতে পারেন। তিনি সব্যসাচী, কারণ তাঁর রচনা আমাদের স্মৃতি ও মেধায় অব্যর্থ শরের মত আঘাত করে, তা আমাদের বিচলিত করে, আমাদের ভাবতে বাধ্য করে।
বাংলাদেশের সাহিত্যে দেশ, ভাষা ও রাজনীতি বরাবরই একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। তাতে আবেগটাই মুখ্য, মেধা নয়, সেখানে পুনরাবৃত্তির একঘেয়েমি আমাদের ক্লান্ত করে। এই নিয়মের বড় ব্যতিক্রম হক ভাই, কোনো বিশেষ মোড়কে তিনি বাঁধা পড়তে চাননি কখনো। ষাট বছরের অধিক সাহিত্য জীবনে তিনি বারবার নিজেকে আবিষ্কার করেছেন, ভেঙেছেন গড়েছেন। ছাত্র বয়সে আমাদের অপুষ্ট যৌবনে হক ভাইয়ের লেখা আত্মজৈবনিক সেই দীর্ঘ কবিতা, বৈশাখে রচিত পঙ্ক্তিমালা, আমরা আনন্দিত আগ্রহে মালার মত বুকে জড়িয়ে নিয়েছিলাম। অপচয়িত যৌবনের আহত পঙ্ক্তিমালা, অথচ কী প্রবল প্রত্যয়ে সেখানে তিনি উচ্চারণ করেন,
বিপুল শহরে আমি হেঁটে হেঁটে যাব
শব্দের প্রদীপ হাতে অক্লান্ত, নিয়ত
আবার মৃত্যুক নেবো, আবার জীবন।
অনেক বছর আগে এই নিউইয়র্কেই হক ভাই এক বৈঠকে আমাদের সে কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন। ইংরেজিতে যাকে বলে ‘ট্রান্স’, পড়ার সময় কবি নিজে হারিয়ে গিয়েছিলেন সে রকম এক ঘোরের ভেতর। আমরাও তার সাথী হয়েছিলাম এক অভাবিত অভিযাত্রায়। ষাটের দশকে, কবি নিজে যখন আত্ম-আবিষ্কারের নেশায় এ দোর সে দোরে আঘাত হানছেন, ব্যক্তি-সময়-সমাজ যখন সামষ্টিক অর্থ নিয়ে তাঁর কাছে ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে, এই পঙ্ক্তিমালা সেই সময়ের সদ্য প্রকাশিত রক্তক্ষরণের মানচিত্র। এই কবিতার ভেতর দিয়ে যেমন কবি ও তাঁর সময়কে চিনেছি, তেমনি আয়নার মত তাতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। বুঝেছি একমাত্র কবিতাই পারে একজনের ব্যক্তিগত উচ্চারণকে বহুজনের আত্ম-আবিষ্কারের সূত্র হয়ে ওঠতে।
হক ভাই এক সময় ছিলেন প্রেমের ভাষ্যকার, তাঁর প্রথম দিককার ছোটগল্পে যার অনিবার্য প্রকাশ রয়েছে। একাত্তর এই মানুষটাকেই একদম বদলে দিল। সবাই যখন সে যুদ্ধে খোঁজার চেষ্টা করেছে বিজয়, তিনি সেখানে দেখলেন বাংলাদেশের নিজস্ব প্রাণশক্তি, মুক্তির জন্য তার ক্ষান্তিহীন অন্বেষণ, ভয়কে জয় করার অমোঘ মন্ত্র। একাত্তরের শুরু যে অনেক আগে, সিপাহী বিদ্রোহ কী তারও আগে, এই কথাটা আরো অনেকেই চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু হক ভাইয়ের মত ছবির মত তাকে এঁকে দেখাননি কেউ। ‘নূরলদিনের সারা জীবন’ এর কথা ভাবুন। একজন সাধারণ কৃষক, বাংলার বুকের ভেতর থেকে কুড়িয়ে আনলেন তাঁকে শুধু এই কথাটা আমাদের বোঝাতে যে মিছিলের সামনের সারিতে যারা দাঁড়ায় তারা আসলে আমার-আপনার মতই মানুষ। নায়ক হবার যোগ্যতা আমাদের সবারই আছে, কিন্তু তার জন্য চাই বৃহত্তর কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গের প্রস্তুতি ও অঙ্গীকার। আমাদের প্রত্যেকের ভেতরেই রয়েছে এক একজন নূরলদিন, শুধু প্রয়োজন তাকে চিনে নেওয়া।
হক ভাইয়ের একাত্তর-পরবর্তী অধিকাংশ রচনায় রয়েছে এই সাধারণ অথচ অসাধারণ নায়কের প্রতিরূপ। তিনি আমাদের প্রত্যেকের ভেতর সেই নায়কের আবির্ভাবের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করতেন। দু’বছর আগে নিউইয়র্কে এক সাহিত্য সম্মেলনে এসেছিলেন হক ভাই। সে সময় আমাদের শুনিয়েছিলেন তাঁর কবিতা, আকবর হোসেনের জন্য গান। একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা, আটাত্তরেই তার ট্রাইবুনালে বিচার হল। হক ভাই তাঁকে নিয়ে গান বাঁধলেন শুধু এই কথাটা বোঝাতে, যে স্বপ্ন নিয়ে আকবর যুদ্ধে গিয়েছিল, সে স্বপ্ন এখনো অপূর্ণ। যুদ্ধ শেষ কিন্তু মুক্তি আসেনি। এখন তাই প্রয়োজন আকবর হোসেনের, একজন নয় অনেক আকবর হোসেনের।
‘‘পুড়িয়ে খাচ্ছে ক্ষেতের আলু আকবর কব্বরে,
আমরা বাঁধি শোনাতে গান তাকেই সমস্বরে,
ও আকবর, হে আকবর, মৃত্যু এসে ছুঁলো,
পড়ছে কেন তবু তোমার চোখের অশ্রুগুলো?’’
২
সৈয়দ হক একাত্তরকে নিয়ে নাটক, কবিতা ও গল্প লিখেছেন অসংখ্য। কিন্তু যে রচনাটি বর্তমান লেখকের মনে এক আশ্চর্য বিস্ময় নিয়ে জেগে আছে সেটি তাঁর কাব্য নাটক, নূরলদিনের সারাজীবন। নিউইয়র্কে, হক ভাইকে পাশে নিয়ে ১৯৯৯ সালে সে নাটকের একটি প্রদর্শনী দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। আমি সেই অভিজ্ঞতার কথাটি বলতে চাই।
নূরলদীনের কাহিনি আঠারো শতকের শেষভাগে বাংলাদেশের রংপুরের এক কৃষক বিদ্রোহকে ঘিরে। একদিকে ইংরেজ প্রভু, অন্যদিকে তার বংশবদ স্থানীয় জমিদারের অত্যাচারে দীন থেকে দীনতর কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহের আকস্মিক ও আশ্চর্য এক মশাল জ্বেলে ধরে নূরলদীন। হিন্দু-মুসলমানে বিভক্ত বাংলা, ইংরেজদের পক্ষে-বিপক্ষে বিভক্ত বাঙালি এই প্রায় নিরক্ষর গ্রামীণ কৃষকের আহ্বানে সাড়া দেয়। গ্রামের পর গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে বিদ্রোহের আগুন। রংপুর থেকে দিনাজপুর, আরো দূরে কুচবিহার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে তার হলকা। সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে ইংরেজ। অতিরিক্ত ফৌজি এনে প্রবল রক্তপাতের ভেতর দিয়ে দাবিয়ে ফেলা হয় সেই বিদ্রোহ। নিহত হয় নূরলদীন।
এই-ই গল্প, অথচ মঞ্চে যখন তা প্রকাশিত হচ্ছে, ক্রমশ তার সম্পূর্ণ নতুন ও সাম্প্রতিক অর্থ ধরা পড়ছে দর্শকদের চোখে। নূরলদীন যে শুধু একটি ২০০ বছরের পুরনো ঐতিহাসিক চরিত্র, তা নয়। তার ভেতর খুঁজে পাই আজকের অসম ও বিভক্ত মানুষের অনিঃশেষ সংগ্রামের চিহ্ন, অনায়াসে দেখি বাংলার নিরন্ন কৃষকের কথার আয়নায় অভাবী নিকারাগুয়ান কৃষি শ্রমিকের বেদনা ও দীনতা, শুনি গুয়াতেমালার ইন্ডিয়ানদের ক্রদ্ধ প্রতিবাদ, পাই দক্ষিণ আফ্রিকার বৈষম্যপীড়িত কৃষ্ণকায়দের রক্ত ও ঘামের স্বাদ। নাটকটি প্রযোজনা করেছে নিউইয়র্কভিত্তিক সংগঠন এপিক অ্যাকটরস ওয়ার্কশপ অ্যান্ড ক্যয়ার। দুই বাংলার পেশাদার-অপেশাদার নাট্যামোদী নিয়ে গঠিত এই সংগঠন। তবে এ কথা বোধহয় অতিরিক্ত হবে না, যদি বলি, সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় এই সংগঠনের হৃদয়, মস্তিষ্ক ও পেশি। সেসময় টাফটস বিশ্ববিদ্যালয়ে পারফর্মিং আর্টসের নবীন অধ্যাপক তিনি, অভিনেতা হিসেবেও সুপরিচিত। নাটকটি অনুবাদ ও পরিচালনা ছাড়াও এর নাম চরিত্রেও অভিনয় করেছেন সুদীপ্ত।
একই নাটক আমি ঢাকায় দেখেছি।
নাগরিকের প্রযোজনায় দুর্দান্ত সে নাটক। অথচ তার বক্তব্যের এই দূরগামিতা, তার অর্গল খোলা এই আহ্বান এত স্পষ্ট ও তীব্রভাবে, এত ‘ইমেডিয়েটলি’, আর কখনো অনুভব করিনি। এর সম্ভবত একাধিক কারণ আছে। তবে সবচেয়ে যা প্রধান তা হলো এর গঠনগত বিশেষত্ব। মূল নাটককে কোনোভাবে আক্রমণ না-করে সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় এই ইংরেজ চরিত্রগুলোতে তাদের নিজস্ব ভাষায়, ইংরেজিতে কথা বলিয়েছেন। এর ফলে তাৎক্ষণিকভাবে ইংরেজ ও বাঙালির পরস্পরবিরোধী অবস্থান সুচিহ্নিত হয়েছে। স্পষ্ট হয়েছে তাদের অবস্থানগত দূরত্ব। এক পর্যায়ে এক সাহেব আধবাংলা ও উর্দু বলে সে দূরত্বকে আরো বাড়িয়ে এনেছেন। এই নাটকের প্রতিটি বাঙালি চরিত্রের সংলাপ নির্মিত ছন্দোবদ্ধ বাংলা, উত্তর বাংলার স্থানীয় ডায়ালেকটে। সে ভাষা প্রায়শ কাব্যধর্মী, ঊর্ধ্বগামী, এবং ফলত কখনো কখনো অতিরঞ্জিত। এই অতিরঞ্জন সম্ভবত ইচ্ছাকৃত, কারণ নূরলদীন ও তার সহযোদ্ধাদের ক্রোধ ও বেদনার ধ্বনিকে তীব্রতর করাই সৈয়দ হকের ইচ্ছা ছিল।
কবিতার ভাষায় হওয়ায় এই ধ্বনিকে আমরা যে যার মতো ‘ইন্টারপ্রেট’ করতে সক্ষম হই, তাতে সম্মিলিত হই নিজ নিজ গবাক্ষ পথে। এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও আমরা শেষ পর্যন্ত মিলিত হই এক সাধারণ ও অভিন্ন জলধারায়, ক্রোধের ও প্রতিবাদের এক রঙা জলপ্রপাতে। অথচ এর পাশাপাশি ইংরেজ চরিত্রসমূহের সংলাপ যে কেবল গদ্যে, তা-ই নয়, তা অতিরঞ্জনরহিত নিত্য ব্যবহার্য ভাষায়। ভাষার এই সমান্তরাল ভ্রমণ আমাদের একদিকে ইতিহাসমুখী ও রোমান্টিক করে, আবার অন্যদিকে বাস্তবের দিকে রাশ টেনে ধরে জানায়, এই কাহিনি আজকের, এই কাহিনি তোমার। অন্য কোনো বাংলা নাটকের এই ‘মাল্টি কালচারাল ট্রানসেনডেন্স’-এর কথা আমি জানি না।
সৈয়দ হক সম্ভবত আমাদের সময়ের সবচেয়ে পরিশীলিত ও আধুনিক বাঙালি লেখক ও নাট্যকার। একই সঙ্গে তিনি আশ্চর্য রকম রাজনীতিমনস্ক। গতকাল যে কেবল বিগত তা নয়, এর গর্ভেই আজ এবং আগামীকাল। এ কথা তারচেয়ে ভালো অনেকেই বোঝেন না। একমাত্র তিনিই অনায়াসে উচ্চারণ করতে পারেন এক নূরলদীন মরে গেলেও মানুষ তো বেঁচে থাকবে। জেগে উঠবে হাজারও নূরলদীন। মঞ্চায়িত নাটকে সংগ্রামের এই বহমানতা, তার অবিচ্ছিন্ন ধারা বোঝানোর জন্য একদম শেষ দৃশ্যে নূরলদীনের ঘনিষ্ঠ সখা আব্বাস নূরলদীনের ফেলে দেওয়া লাঠি তুলে নেয়। আর এইভাবে এক মানুষের মৃত্যু হলেও জেগে ওঠে মানব।
আমার মনে নেই মূল নাটকে এই ভূমিকার ঘটেছিল কিনা, তা হোক বা না হোক, এই ট্রানজিশন আমাদের আশ্বস্ত করে, আশান্বিত করে। নূরলদীনের মৃত্যুতে জল ভরে আসা চোখ নিয়েও একে অপরের দিকে তাকাই নির্লজ্জভাবে, কারণ জানি সে জল মোছার সময় সামনেই। তার গঠনগত বৈশিষ্ট্যের কারণে নূরলদীনের কাহিনির আন্তর্জাতিক ও সময়-উত্তর চেহারা একদিকে যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি এ কথাও ঢাকা পড়ে না যে, এই কাহিনি আসলে আজকের বাংলাদেশেরও। উপক্রমণিকায় বা মুখবন্ধে নাট্যকার নিজেই জানিয়ে দেন বিপদ যখন ঈশান কোণে দেখা দেয়, জাতিভেদ ও ধর্মভেদ যখন মাথা উঁচু করে, তখনই নূরলদীনের প্রয়োজন পড়ে। এবং বারবার এই নূরলদীনÑ যে গতকালের অথচ সর্বকালেরÑ আমাদের ডাক দিয়ে যায়, বলে, জাগো বাহে, কোনঠে সবাই।
ইংরেজি-বাংলার সমান্তরাল পরিবেশনার ফলে এই নাটকটি যে দুটি সমান্তরাল কাহিনি নিয়ে তৈরি, তাও এর আগে কখনো এত স্পষ্ট হয়নি। নাট্যকার নির্ঘাত ভেবেচিন্তে এই সমান্তরালতা নির্মাণ করেছেন। কিন্তু মূল নাটকে ভাষা ও পরিবেশগত বৈসাদৃশ্যহীনতার কারণে সেটি অনেকের চোখে না পড়ারই কথা। নাটকের একমাত্র ইংরেজ নারী চরিত্র লিজবেথ ও একমাত্র বাঙালি চরিত্র আম্বিয়ার প্রতি তুলনা করা যাক। নূরলদীনের স্ত্রী আম্বিয়া, লিজবেথ রংপুরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ফ্যাক্টরি নির্বাহীর স্ত্রী। আম্বিয়ার তুলনায় লিজবেথ অনেক সবাক ও উচ্চকণ্ঠ হলেও সামাজিকভাবে তারা দুজনেই প্রান্তিক শ্রেণিভুক্ত, কম অধিকারভোগী।
দুজনের জগৎই তাদের স্বামীকে ঘিরে, নিজস্ব কোনো জগৎ তাদের নেই। অথচ এর পাশাপাশি দুজনই নির্দোষ-বা কে জানে-হয়তো দুষ্ট-পরকীয়া প্রেমে সম্পর্কিত। সৈয়দ হক এই বিষয়টি খুব বেশি তালাশ করে দেখেননি, কিন্তু ক্যয়ারের মঞ্চায়নে তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণভাবে উপস্থিত। কোম্পানির ট্যাক্স কালেকটার এক সময় লিজবেথকে কোনো রকম রাখঢাক ছাড়াই জানায় যে দুটি যুবক এই ঈশ্বর পরিত্যক্ত দেশে ইংরেজের সেবায় উপস্থিত হয়েছে, লিজবেথের ওপর তাদের মনোযোগ কেবল যে নির্দোষ তা নয়, অন্য আরো উদ্দেশ্য আছে।
নাটকের এক পর্যায়ে লিজবেথের অশ্রুভেজা চোখ তার রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দেয় ইংরেজ মিলিশিয়ার প্রধান লেফটেনান্ট ম্যাকডোনাল্ড। ম্যাকডোনাল্ড চরিত্রের মার্কিন অভিনেতা ব্রায়ান ক্লোজ আমাকে পরে বলেছেন, রুমাল দিয়ে মোছার ঐ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আকস্মিক, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত। তবে তা যে মোটেই অসংগত বা কৃত্রিম ছিল না, দর্শকদের প্রতিক্রিয়া থেকেই তো তা স্পষ্ট। প্রায় একই রকম সমান্তরাল পরিস্থিতি রচিত হয় আম্বিয়া ও আব্বাসের মধ্যে। যুদ্ধে গেছে নূরলদীন, উদ্বেগাকুল ও একাকী আম্বিয়া তখন আশ্বাস খুঁজে পায় নূরলদীনের নিকট সহকর্মী আব্বাসের কাছ থেকে।
হাস্য-পরিহাসে আব্বাস তাকে আশ্বস্ত করে, আশান্বিত করে, এক সময় আম্বিয়া লাস্যময়ী হয়ে ওঠে, তারা ঘন হয়ে আসে। তাদের সম্পর্কের নির্দোষতার মাত্রা আম্বিয়ার বা আব্বাস কেউই অতিক্রম করেননি। তা সত্ত্বেও আম্বিয়ার চরিত্রে গার্গী মুখোপাধ্যায় এবং আব্বাস চরিত্রে শাহ খান পুরো সম্পর্কটির নিষিদ্ধতার একটি ইঙ্গিত বেশ স্পষ্টভাবে দিয়ে গেছেন। আমার আক্ষেপ, লেখক কেন এই মানবিক অনুষঙ্গটি আরো খুঁড়ে দেখলেন না। তাহলে বেশ হতো।
নীল আকাশের নিচে, এক ধবল পূর্ণ চাঁদের নিচে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। নিরাভরণ কিন্তু যথাযথ। এই চাঁদটিকে তারা ব্যবহার করেছেন সুপার টাইটেল প্রক্ষেপণে। বাংলা ও ইংরেজি কথোপকথনের সারসংক্ষেপ সুপার টাইটেলে প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় তার দিকে আমাদের নজর বারবার পড়েছে, আমরা ঐ স্মিত জোছনার দিকে তাকিয়ে আশ্বস্ত হয়েছি এই ভেবে যে, নিরানন্দ ও নির্মম সময়েও ঐ আকাশ থাকে, ঐ চাঁদ থাকে, থাকে আশার আলো। আমি জানি না শুধু কারিগরি গিমিক হিসেবেই পরিচালক ঐ চাঁদটি ব্যবহার করেছেন কিনা। তা করে থাকলেও এর ব্যবহারে যে আরেকটি দ্যোতনা সংযোজিত হয়েছে তা অস্বীকার করা যাবে না।
সৈয়দ হকের মূল নাটক যারা ঢাকায় দেখেছেন তারা জানেন লাল ও নীল এই দুই ধরনের কোরাস তিনি ব্যবহার করেছেনÍযথাক্রমে বিদ্রোহী নীল চাষী ও তাঁবেদার দালালদের চরিত্র বোঝাতে। মনে আছে নাগরিকদের মঞ্চায়নে লাল, নীল গেঞ্জি ব্যবহার করা হয়েছিল এই বৈপরীত্য বোঝাতে। নিউইয়র্কের মঞ্চায়নে কয়্যার ব্যবহার করেছে মাথায় বাঁধবার ফেট্টি। একই ফেট্টি, তার একদিকে লাল রঙ, অন্যদিকে নীল।
এক সময় যখন জমিদারের চরবৃন্দ দলত্যাগ করে নূরলদীনের পক্ষে চলে আসে, তখন এক মুহূর্তে নীল ফেট্টি হয়ে পড়ে লাল। নীল ও লালের মধ্যে তফাৎ যে খুব সামান্য, এর জন্য যে দরকার শুধুমাত্র একটু ঝাঁকুনির অথবা নূরলদীনের মতো কারও স্পষ্ট আহ্বানের, তা এক মুহূর্তের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে আসে। সম্ভাবনার অর্থে এর উল্টোটাও সত্য। সৈয়দ হক তা অবশ্য ঘেঁটে দেখেননি, তবে তা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না।
নামে নাটক হলেও ‘নূরলদীনের সারাজীবন’ আসলে একটি দীর্ঘ কবিতা। কখনো মুক্ত ছন্দে, কখনো পয়ারে কিন্তু আগাগোড়া প্রবল বেগের আবেগে তা নির্মিত। অসম সাহসী এক বাঙালি নায়কের প্রতি কৃতজ্ঞ এক বাঙালি কবির শ্রদ্ধাঞ্জলি। সেই নায়ক মানুষকে জাগাতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুর্যোগকে প্রতিহত করতে। ঘরে-বাইরে আমাদের এখনো সেই দুর্যোগ, এখনো সুযোগের অপেক্ষায় বর্গী। শলা-পরমর্শে রত বিদেশি অনুচর। কিন্তু বাহে, তোমরা সবাই কোথায়? কোনঠে?
৩
সৈয়দ শামসুল হক বসেছিলেন একদম প্রথম সারিতে, মূল মঞ্চ থেকে দেড় কদম দূরে। ১০ হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে তিনি মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে নিউইয়র্কে পৌঁছেছেন। একমাত্র উদ্দেশ্য তার লেখা ‘নূরলদীনের সারাজীবন’ নাটকের নিউইয়র্ক মঞ্চায়নে উপস্থিত থাকা। মুখে না বললেও তিনি যে ভেতরে ভেতরে ভীষণ উদ্বিগ্ন, সম্ভবত শঙ্কাগ্রস্ত, তা বেশ বুঝতে পারছিলাম। তিন সারি পেছনে আমি। নাটক দেখছিলাম ঠিকই কিন্তু বারবার চেষ্টা করছিলাম সৈয়দ হককে দেখতে, বুঝতে তার কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। সেদিন দুপুরেই তিনি বলেছিলেন, নিজের লেখা নাটক দেখতে গিয়ে তিনি নিজেকে দর্শক হিসেবে ভাবতেই ভালোবাসেন। আমি মাথা নেড়েছিলাম, বলেছিলাম, অতটা ‘ডিসপ্যাশনেট’ হওয়া নাট্যকার পক্ষে সম্ভব নয়। ‘আমি পারি’, বলেছিলেন সৈয়দ হক।
কমবেশি দেড় ঘণ্টার নাটক। মনে হলো যেন পলক পড়তে না-পড়তেই শেষ হয়ে গেল। হলঘরটি নেহায়েতই ছোট, বড়জোর ৭০-৭৫ জন দর্শকের স্থান সঙ্কুলান হবে। মঞ্চের শেষ আলোটি নিভে সব আলো আবার জ্বলে ওঠার আগে তারা সবাই সহর্ষে করতালিমুখর হলেন। একজন চেঁচিয়ে বললেন, ব্রাভো! আমি দেখছিলাম সৈয়দ হককে। তিনিও উঠে দাঁড়িয়েছেন, যোগ দিয়েছেন করতালিতে। যে শঙ্কা ও উদ্বেগ লক্ষ্য করছিলাম তা উধাও। তার বদলে চোখের কোণে উকি চিক চিক অশ্রুবিন্দু!
৪
নূরলদিন এখন ইতিহাস, আকবর হোসেনের মত মুক্তিযোদ্ধাও বিগত। কিন্তু নূরলদিন অথবা আকবর হোসেনদের প্রয়োজন এখনো শেষ হয়নি, বরং যে দুঃসময় বাংলাদেশের সামনে, তখন চাই মানব মুক্তির সংগ্রামে আত্ম-নিবেদিত সেই সব নায়কদের। প্রয়োজন সেই কবিকেও যে নূরলদিনকে মরতে দেন না। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে, কিন্তু মানবমুক্তির যুদ্ধ শেষ হয়নি। মৌলবাদের নগ্ন নখর এখন আঁধারে ঝলসায়, মুখ ব্যাদান করে দেখায় তার নোংরা তীক্ষè দাঁত। আমাদের ঘরের লাগোয়া ঘরে সে বাস করে, তাকেও চিনেও আমরা চিনি না। চোখ থেকেও যারা অন্ধ, কান থেকেও যারা শোনে না, হাওয়ায় ক্ষমতার লাঠি ঘোরায় তারা। এখনই তো দরকার কবিকে। আরিস্তোফানেস-এর কথা, ‘শিশুদের শিক্ষা দেবার জন্য আছে স্কুল শিক্ষক, আর প্রাপ্তবয়স্কদের আছে কবি।’ সেই রকমই একজন কবি সৈয়দ শামসুল হক। তিনি গলায় বেঁধেছিলেন মুক্তির গান।