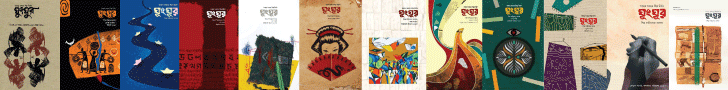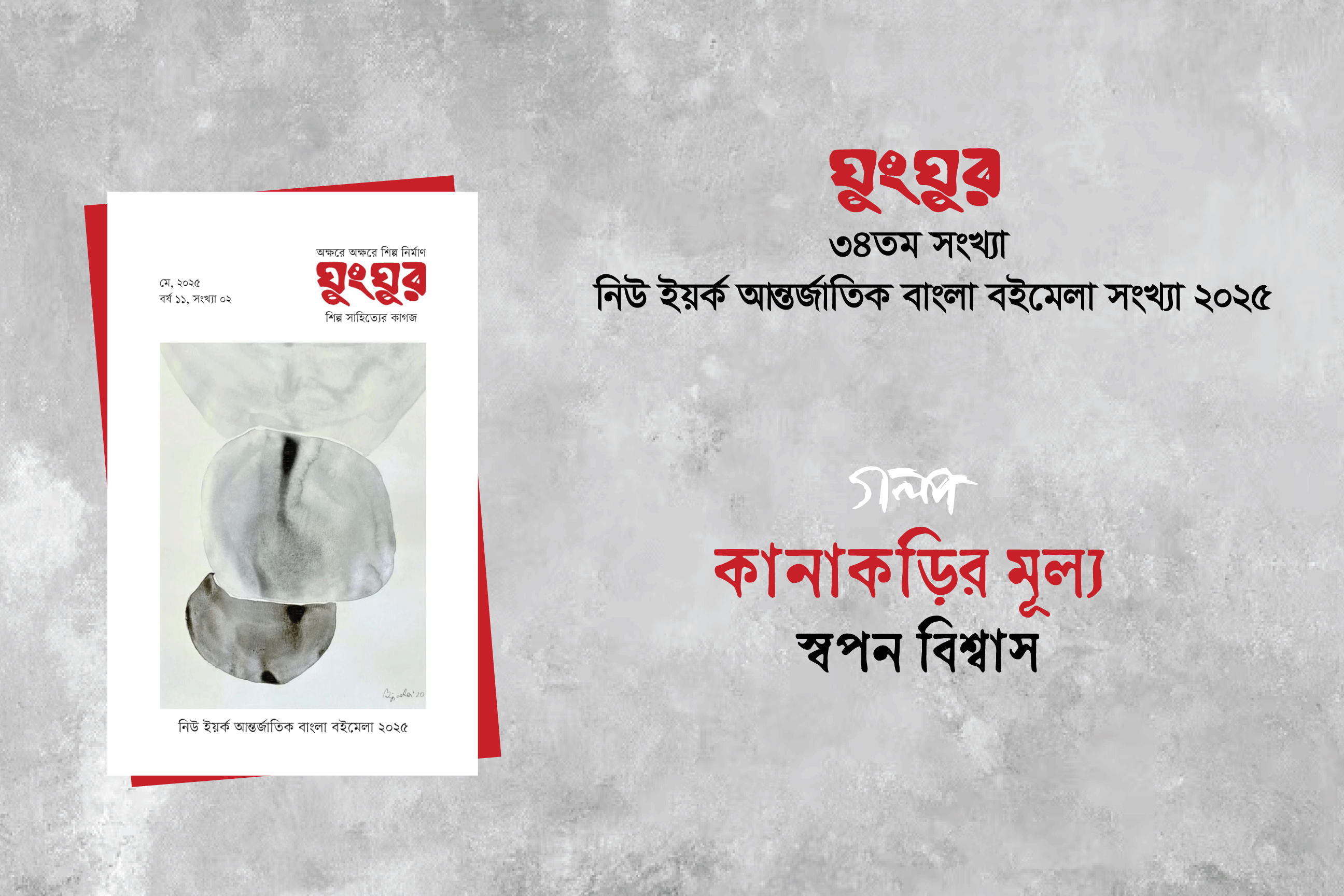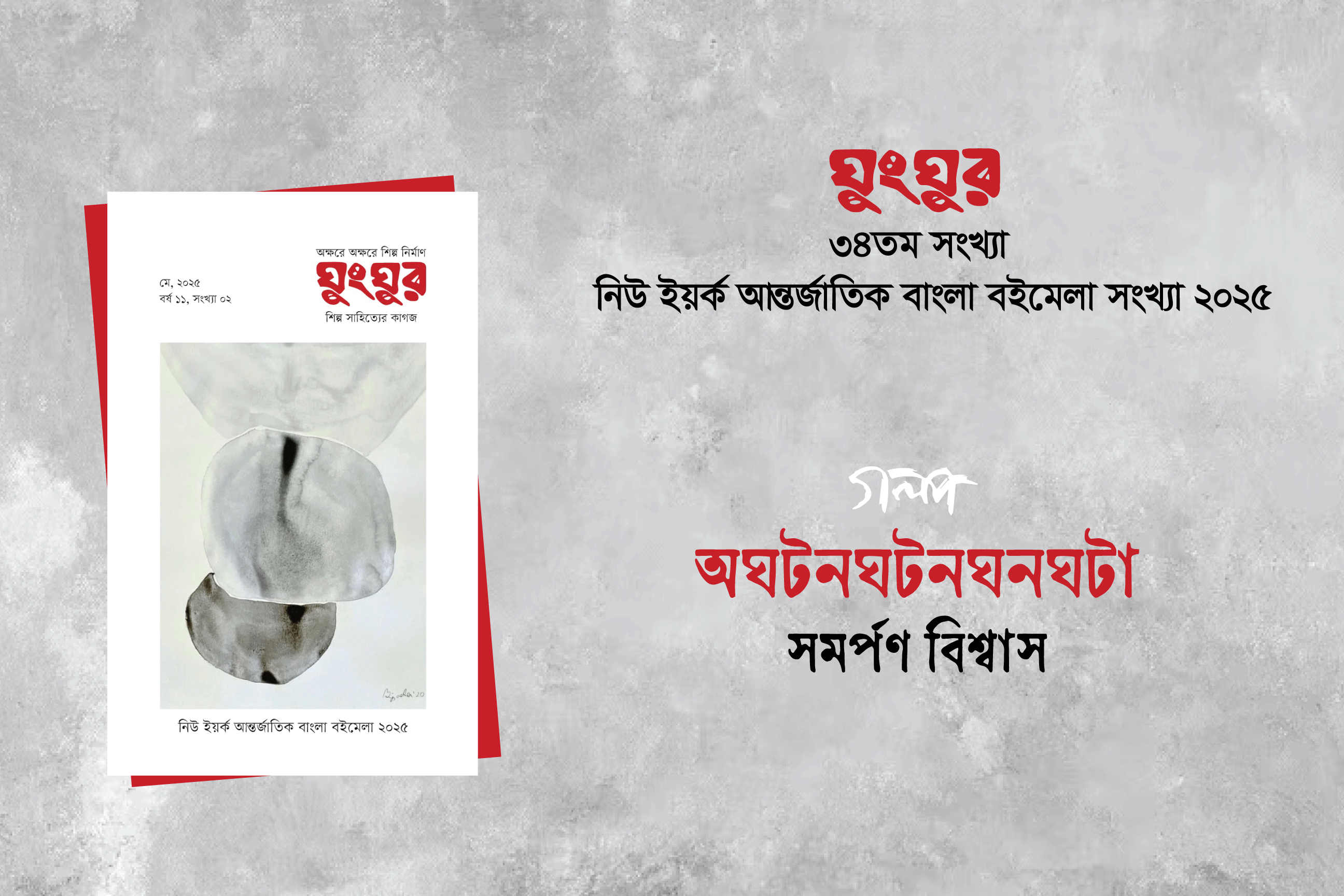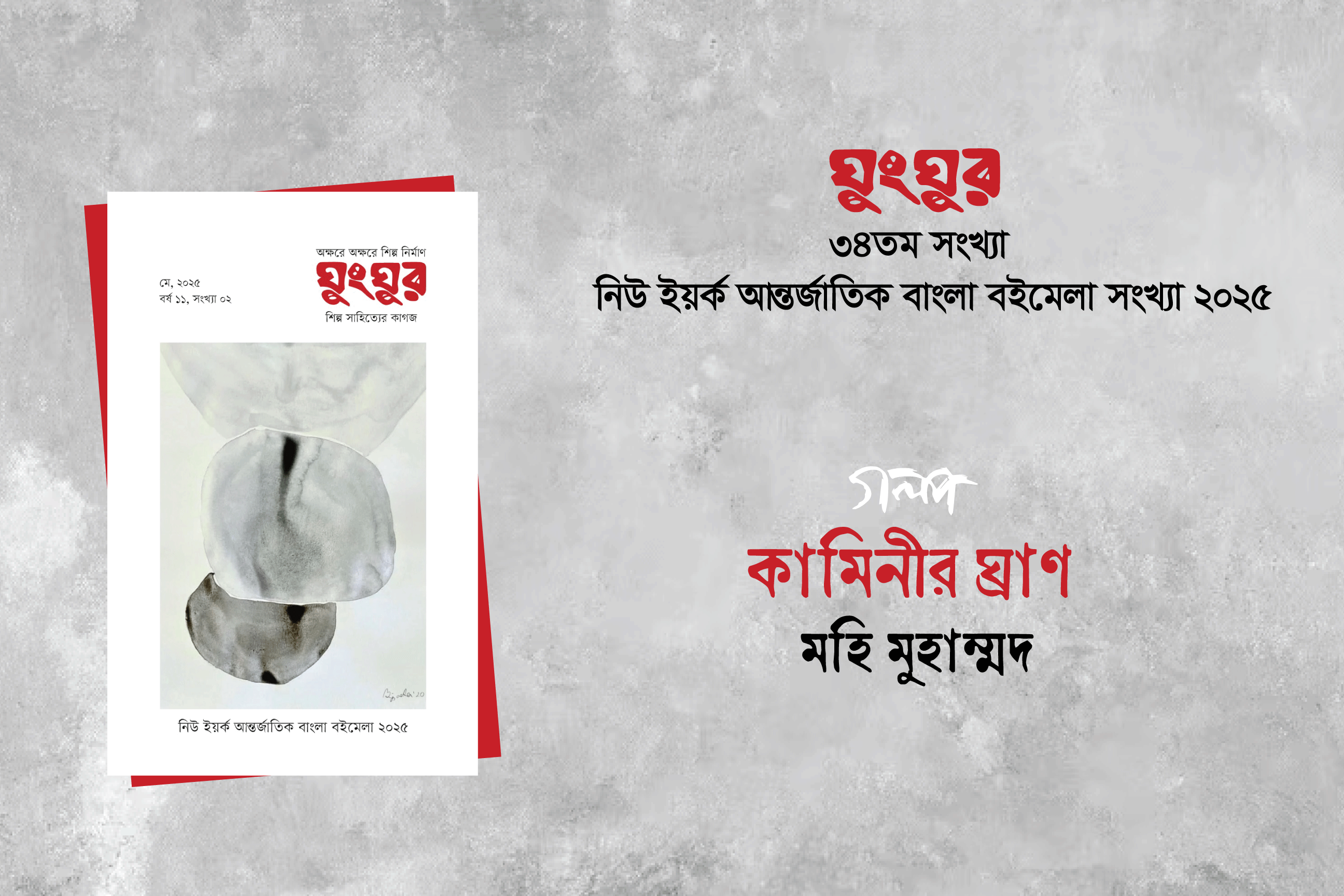রাতের তালগাছ

প্রত্যেক আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে আমাদের গোয়াল ঘরের পাশের লম্বা তালগাছটা ওর মাথার গোল গোল পাখা মেলে উড়তে বের হয়, শুধু ছায়াটাকে পেছনে রেখে যায়। গভীর রাতে ছানি পড়া চোখে দাদাভাই যখন পেশাব করতে বের হয় তখন হয়তো ছায়াটাকেই তালগাছ ভেবে আর রা শব্দ করে না। জংলাটার পাশে বসে ছ্যাড়্ছ্যাড় করে এক কলস পানি ছেড়ে আবার ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকে। এমন হাল্কা আলো-আঁধারিতে কিসের উপরে বসে পেশাব করে কে জানে! ওইখানে যদি পিঁপড়ার বাসা থাকে, যদি ইন্দুরের গর্ত থাকে, যদি সেই গর্তে সাপ থাকে! আমাদের মাদ্রাসার হুজুর বলছে, একবার নাকি একজন ভুল করে একটা গর্তের ভিতরে পেশাব করে ফেলছিল। আর ওই গর্তে থাকত একটা জ্বিন। গায়ে গরম পানির ছিটা পড়তেই জ্বিনটার সাধনা নষ্ট হয়ে গেছিল, আর সেজন্য রাগ করে জ্বিনটা নাকি লোকটাকে একেবারে জানে মেরে ফেলছিল। কী ভয়ের কথা!
এই যে আমি আমার ঘরের জানালা দিয়ে তালগাছটাকে চুপি চুপি উড়ে যেতে দেখলাম সেটাও তো কম ভয়ের নয়! আমার চোখের সামনে গাছটা প্রথমে ডাইনে বাঁয়ে একটু দুলল, ওর মাথার উপরের পাতাগুলো আকাশের দিকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, তারপর একটা ঝাঁকুনি খেয়ে গাছটা লম্বা শেকড়সহ সোজা উড়াল দিল আকাশের দিকে। ওকি তবে লক্ষীপুরা গ্রামে কার্তিক বাবুদের তালপুকুরের দিকে গেল, যেখানে সার বেঁধে আরও অনেকগুলো তাল গাছ এক পায়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে! গেছে হয়তো চাচিমার মতো পাড়া বেড়াতে, চাচার মতো চায়ের দোকানে খোশ-গল্প করতে, গাছদের দুনিয়ায় ঘটে যাওয়া যতসব ঘটন অঘটনের বিবরণী শুনতে…
দাদাভাই তার প্রাকৃতিক কর্ম সেরে উঠে পড়েছেন। এবার এগিয়ে আসছেন আমার ঘরের দিকে, জানতাম এটাই করবেন, ঘর্ঘরে গলায় প্রশ্ন করবেন, ‘কিরে সাজু, ঘুমাস নাই?’
কিন্তু আমি যে জেগে আছি সেটা দাদাকে জানতে দিতে চাই না মোটেই, সেজন্য চাদর মুড়ি দিয়ে চোখ বন্ধ করে নিঃশব্দে পড়ে আছি। ঘুমন্ত মানুষের পক্ষে কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দেয়া সম্ভব না। ঘুম আর মৃত্যুকে আমার প্রায় কাছাকাছিই মনে হয়। মরা মানুষেরাও ঘুমন্ত মানুষের মতো, ডাকাডাকি করলেও রা শব্দ করে না। নিঃসাড় পড়ে থাকে নিদ্রিত মানুষের মতোই চোখ বন্ধ করে নীরবে। বাবার মরদেহটা যখন এম্বুলেন্সের ভেতর থেকে নামানো হয়েছিল আমাদের উঠানে, তখন তাকে দেখে মনে হচ্ছিল ঘুমিয়েই আছেন। যেন মাথার নিচে বালিশ ছাড়াই অনেক শান্তিতে গভীর ঘুমে নিমজ্জিত একজন মানুষ তিনি। যেন ঘুম ভাঙলেই আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসবেন। তার বাদামি রঙের ব্যাগের ভেতর থেকে বের করে আনবেন হরেক কিসিমের মিঠাই মণ্ডা চকলেট। বেদানা, কমলা, আপেল। মার জন্য শাড়ি, দাদার জন্য লুঙ্গি। বাবার চারপাশে সেদিন কত মানুষের হইহল্লা, কত চিৎকার কান্না আর্তনাদ... তবু বাবার ঘুম আর ভাঙলো না। আর আমি তো ঘুমাই-ই নাই, দাদাভাইয়ের খুক খুক কাশি আর ছেঁচড়ে চলা পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই আমি উঠে পড়লাম। মাথার কাছে জানালার কপাট ফাঁক করে তাকিয়ে দেখলাম, তাল গাছটা এখনো ফিরে আসেনি। দাদা বলেন, এই গাছটার নাকি অনেক বয়স। অন্তত একশো বছর তো হবেই। দাদাভাইয়ের দাদিআম্মা (যাকে আমি কেনো, আমার বাবাও কখনো চোখে দেখেনি) বহু বছর আগে বাজার থেকে কেনা পাকা তালের পিঠা বানিয়ে তালের আঁটিগুলো অযত্নে ফেলে রেখেছিল মাটিতে। তার কয়েকটার ভেতর সাদা মিষ্টি শাঁস হয়েছিল, সেগুলো দাদার বাপ কেটে খেয়েও ফেলেছিল। শুধু একটা আঁটি সবার চোখের অগোচরে মাটিতে শেকড় গজিয়ে নিজে নিজেই গাছে রূপান্তরিত হয়েছিল আর পাখার মতো ধূসর সবুজ ডালপালা মেলে ধেই ধেই করে বড় হয়ে উঠেছিল। তাল গাছের নাকি এমনই নিয়ম, যে গাছ লাগায় সে কখনো ফল খেতে পারে না। ফল না দেখেই দাদাভাইয়ের দাদিআম্মা চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, অন্যরাও কখনোই এ গাছের ফল দেখেননি।
ছোটবেলায় কোন গাছটা মেয়ে আর কোনটা পুরুষ তাতো ঠিক বোঝা যায় না। যখন বড় হয়, ফল ফুল ধরার সময় হয় তখন তার আকৃতি-প্রকৃতি বিবেচনা করে পরিচয় ধরা পড়ে। এই গাছটাও যখন একটু একটু করে সব গাছের মাথা ছাড়িয়ে আকাশের দিকে বুক টান করে দাঁড়াল, তখন একদিন তার শাখায় সবুজাভ সাদা রঙের পাকানো দড়ির মতো দেখতে লম্বাটে ধরনের কয়েক গুচ্ছ ফুল এলো। সবাই ভাবল এই পুষ্পমঞ্জরির হাত ধরেই এবার বুঝি গাছে ফল আসবে। কিন্তু আশাই সার। গাছে তাল আর ধরল না। বরং ফুলগুলো ধীরে ধীরে শুকিয়ে কেমন কালচে খয়েরি রঙ ধরে লম্বা জটার মতো গাছের শাখায় ঝুলে রইল।
‘ওহোরে এত পুরুষ গাছ, বেটা-ছেইলে, ফল দেবে না ...’
গ্রামের মুরুব্বিরা দেখশুনে মাথা নেড়ে বলল। দাদাভাই তখন একবার ভেবেছিলেন গাছটা কেটে ফেলবেন কিন্তু দাদি তাতে রাজি হলেন না। ছেলে হোক আর মেয়ে হোক গাছ-ও তো একটা প্রাণ। শুধু শুধু প্রাণ-সংহারের দরকারটা কি বাপু? এতদিন ধরে আছে বাড়ির একধারে, পরিবারের সদস্যদের মতোই তো. ওর উপর বড় মায়া পড়ে গেছে আমার। থাকুক, কারও ক্ষতি তো আর করছে না। বরং রাজ্যের পাখ-পাখালির আশ্রয় হয়ে আছে।
তো দাদির জোর সুপারিশে পুরুষ তালগাছখানা টিকে গেল। ওর শুকনা পাতা কেটে হাত পাখা বানানো হতো। কয়েক জোড়া বাবুই এসেও ঘর বাঁধল। এরই মাঝে একদিন চৈত্র মাসের এক দুপুরে কোত্থেকে এক সাঁওতাল বুড়ো এসে হাজির। সে দাদাকে বলল, ‘ মহাজন, এ তো জটাধারি গাছ। এর জটা থেকে সুমিষ্ট রস হইবেক। তোমার গাছে হাড়ি বাঁধতে দেবে? তালের রস নেবো!’
দাদাভাই আপত্তি করলেন না। বরং বললেন, ‘বেশ তো বাঁধ না, পড়েই তো আছে।’
সেই থেকে চৈত্রে শুরু করে জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি মানে আষাঢ় মাসের আগে পর্যন্ত বুড়ো গনেশ হাঁসদা তার ছেলে সুনীল হাঁসদাকে নিয়ে এসে তালগাছের উপরের দিকে ওই কালো জটার মাথা কেটে সন্ধ্যাবেলা মাটির কয়েকটা কলসিতে বেঁধে রেখে যায়। আবার ভোরে অন্ধকার থাকতে সেই কলসি নামিয়ে নতুন কলসি বাঁধে। সকাল সকাল তালের রসের সেকি স্বাদ! মিষ্টি, সুশীতল, একেবারে মন প্রাণ জুড়ানো। কিন্তু যেই না রোদের তাপ বাড়ে, বেলা বাড়ে সেই স্বচ্ছ রসও তার গুণ হারিয়ে টক টক স্বাদে পাগলা হতে শুরু করে। নেশা ধরায়, শরীর বিবশ করে দেয়। সকালের শুদ্ধ নির্মল তালের রসের যেমন খদ্দের আছে, তেমন সন্ধ্যের সময় গেঁজিয়ে ওঠা ঘোলাটে পাগলা রসের খদ্দেরও আছে। তবে তারা ভিন্ন ভিন্ন জাতের মানুষ।
সকাল বেলার রস আমি খেয়ে দেখেছি, তবে সন্ধ্যারটা কখনো খাইনি।
সুনীল বলে, ‘ওটার নাম তাড়ি। তাড়ি তোমার চোখ ঘোলা করে দেবে। মাথায় ঝিম ধরিয়ে দেবে। একটা তাল গাছের জায়গায় তুমি তখন দেখবে দুইটা গাছ। সেই গাছ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসবে তাল পরী। তারা তালে তালে নেত্য করবে গীত গাইবে। বহুত মজা হবেক …’
দাদাভাই অবশ্য আগেই আমাকে সাবধান করেছে, ‘খবরদার ওইসব তাড়ি ফারি কিন্তু কখনোই খাবি না। মাথা ঘুইড়া যাবে। চোখে উল্টাপাল্টা দেখবি।’ তা আমি যদি এখন বলি চাঁদের আলোয় তালগাছকে উড়ে যেতে দেখেছি, তাহলে তো দাদা ভাববে আমি ঠিক তাড়ি খেয়ে মাতলা হয়ে গেছি।
জানি না, মা থাকলে হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করত। মা বলত, জানোস তো, ডাইনি বুড়িরা গাছ উড়াইতে পারে। বড় বড় গাছে বইসা ওরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়। মা আরো কত কিছুই না বলত! বলত, বাগানে যত ফুল ফোটে সব ফোটে পরীদের আঙুলের ইশারায়। আর মাঝে মাঝে আবছা ভোরবেলা কোহেকাফ পর্বত থেকে পরীদের মেয়েরা মাটির পৃথিবীতে আসে কোচড় ভরে বকুল ফুল কুড়াতে। বকুলের তীব্র সুবাস তাদের মাটিতে ডেকে আনে। মা বিশ্বাস করত, মানুষের সঙ্গে পরীদের বিয়ে হয়, জ্বিনদেরও বিয়ে হয়। তোকে আমি পরীর সঙ্গে বিয়ে দিবো। মাঝে মাঝে দুষ্টুমি করে বলত মা। দাদি শুনতে পেলে রাগ করতেন। ‘তওবা, তওবা, এইসব অলক্ষুণে কথা কেউ বলে?’ মা অবশ্য তারপরও বলতেন। বাবা মারা যাওয়ার এক বছর পর মায়েরও বিয়ে হয়ে গেল একটা লম্বা দাড়িওয়ালা লোকের সঙ্গে, নূরপুর গ্রামে। অনেক দিন পর একটা ছোট্ট ফুটফুটে বোন কোলে মা ওই দাড়িয়াল লোকটাকে সঙ্গে করে এই বাড়িতে এলো আমাকে তার সঙ্গে নূরপুর নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু দাদাভাই বুক চাপড়ে বলল, ‘আমি মরলে সাজুরে তোমার কাছে নিয়া যাইও গো বেটি। এখন ওই তো আমার হাতের লাঠি, ওই আমার আন্ধার ঘরের বাতি। আমি ওরে কাছ ছাড়া করব না।’
মা আমাকে জড়িয়ে ধরে অনেক কান্নাকাটি করল। সারা গায়ে দুধের গন্ধভরা ছোট বোনটাকে কোলে নিলাম আমি। ফোকলা মুখে আমার দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসল পিচ্চিটা। পেশাব করে আমার শার্ট ভিজিয়ে দিল। চলে যাওয়ার আগে দাড়িওয়ালা খুবই শরমিন্দা ভঙ্গীতে আমার হাতে কিছু টাকা গুজে দিয়ে বলল, ‘যখনই ইচ্ছা করে মাকে দেখতে নূরপুর আইসা পইড়ো, কেমন! কোনো কিছু লাগলে মাকে জানাইয়ো…’
নূরপুর কতদূর আমি জানি না। সুনীল হাঁসদা জানত। নুরপুর বাজারে তালের রস বিক্রি করতে যাইত ও। আমাকে মাঝে মাঝে বলত, ‘দেখো বাবু, আমি কেমন খালি কলস বেধে যাই। আর দিন শেষে ভরা কলস নিয়ে যাই। মানুষকেও কিন্তু পিথিবিতে এইরকম খালি কলসের মতোই পাঠায় ভগবান। দিনে দিনে এটা সেটা করে আমরা সেই কলস ভরে ফেলি। কলস পুন্ন হলে আবার ফিরে যাই তাঁর কাছে।’
সুনীলের কলস পূর্ণ হয়েছিল কিনা কে জানে! গত বছর বৈশাখ মাসে ভর সন্ধ্যায় রসের হাড়ি পাড়তে গিয়ে হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল ও। চিৎকার করারও সময় পায়নি, শুধু একটা ভোঁতা ‘থপ’ শব্দ করে মাটির ওপর দলামোচা হয়ে আঁছড়ে পড়েছিল ওর লম্বা কালো শরীরটা। অত উপর থেকে পড়লে কেউ আর বাঁচে নাকি? সুনীলও বাঁচে নাই। নাক, মুখ, মাথা শরীর থ্যাতলে রক্তে কাদায় মাখামাখি হয়ে ওকে আর মানুষ বলে চেনা যাচ্ছিল না। তার হাতের কাঁচি আর কোমরে বাধা চুনের কৌটা ছিটকে পড়েছিল দূরে গোয়াল ঘরের ছাই গোবরের স্তূপে। লোকে বলে, তাড়ি খেয়ে তালগাছে উঠতে গিয়েছিল সুনীল হাঁসদা। হাতে পায়ে বশ ছিল না। ঘোলা চোখে গাছ ভেবে হয়তো শূন্যেই পা ফেলেছিল সে!
গণেশ হাঁসদা কয়েক মাস পরে ছেলের মৃত্যুশোক বুকে চেপে দাদাকে এসে বলেছিল, ‘এটা অশুভ গাছ কত্তা। এরে কাইটে ফেলেন। আমার বেটাকে কেমন খেয়ে দিল, দেখেন!’
দাদাভাই মাথা নেড়ে বলেছিল, ‘গাছের কি আর শুভ অশুভ থাকেরে? গাছ তো গাছই, ভাষাহীন, নির্বাক জীবন! এতদিন ধরে আছে কিছু ক্ষতি তো আগে হয়নি… যাক্ তুই পুত্র হারিয়েছিস, আর বলছিস যখন যা, কেটেই ফেলব না হয়।’
আমি এক সুনসান দুপুরে বুড়ো তাল গাছটার মোটা খসখসে শরীর জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কিরে পচা বুড়ো, সুনীলকে মেরে ফেললি কেন? কেন ওকে ধাক্কা দিলি?’
বুড়োর মাথায় পাতাগুলো তখন শন্ শন্ ঝন্ ঝন্ আওয়াজ তুলে হাসল।
‘এখন যে তোকে কেটে ফেলবে, তুইও তো শালা মরবি…’
এবারে হাসি যেন আরও বাড়িয়ে দিল বুড়ো তালগাছ। পাতাগুলো আরও বেশি আন্দোলিত হলো, শোঁ শোঁ শব্দ হলো আরও জোরে জোরে।
তালগাছটা ফিরেছে কিনা দেখার জন্য জানালার কপাট খুলে আরেকবার তাকালাম আমি। না, গাছ বুড়োর আড্ডা এখনো শেষ হয়নি। ছায়াটা একাই পড়ে আছে। রাত পার করে দেবে নাকি বুড়োটা? নাকি বুঝে গেছে যে তার মৃত্যু ঘণ্টা বেজে গেছে! সুনীলের বাপের উত্তরোত্তর পীড়াপীড়িতে দাদাজান দুলাল করাতিকে খবর দিয়েছে আগামী শুক্রবার সকালে এসে তালগাছটা যেন কেটে ফেলে। পরশুই তো শুক্রবার। তার মহাপ্রয়াণের দিন। কিন্তু আজ রাতে তালগাছ যদি আর না ফেরে! তাহলে? গ্রামে রীতিমতো হৈ চৈ পড়ে যাবে না! রাতারাতি একটা জলজ্যান্ত গাছ পালিয়ে যাবার ঘটনা এর আগে কি কেউ কখনো ঘটতে দেখেছে? মাটি ছেড়ে গাছ কখনোই পালায় না কিন্তু মানুষ পালায়। ছোট ফুপু যেমন তার বিয়ের আগের রাতে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছিল। সেদিন রাতেও বুড়ো তালগাছের সঙ্গে আমি জেগে ছিলাম। ঘুমকাতুরে ছোট ফুপুকে জাগতে দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম সেদিন। পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলাম,
‘এত রাতে কই যাও ফুপু?’
আধো অন্ধকারে আমার গলা শুনেই ফুপু চমকে উঠে কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বাড়ির পেছনের দরজাটার খিলে হাত রেখে ফুপু ভেজা ত্রস্ত গলায় বলল, ‘…বল সাজু, বাবা কি কাজটা ঠিক করছে? যারে চিনি না জানি না, বয়সে আমার চেয়ে দ্বিগুণ তেমন একটা বয়স্ক লোকের সঙ্গে বিয়ে…! মানা যায় বল!’
আমি মাথা নাড়লাম তারপর ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম,
‘তুমি কি তাইলে পশ্চিমপাড়ার শুভ্রজিৎ দাদার সঙ্গে পালাইতেছো! সত্যি?’
ফুপু একটু থমকে গিয়েছিল। তারপর ঠোটের উপর আঙুল রেখে নিচু গলায় বলেছিল,
‘খবরদার, কাউরে কিন্তু কিচ্ছু বলিস না সাজু!...’
আমি কাউকে বলিনি। বরং সকাল হলে সবার সঙ্গে আত্মীয় স্বজনের বাসায় গিয়ে গিয়ে ফুপুর খোঁজ করেছি। তারপর যখন সব জানাজানি হলো, তখনো এমন ভাব করেছি যেন এইমাত্র জানলাম। আহা! কত বছর হয়ে গেছে ছোট ফুপুরে দেখি না!
মাটিতে লুটিয়ে পড়া জোছনাটা এখন কুয়াশার মতো ঘোলা হয়ে এসেছে। মেঘ এসে পাতলা কাঁথার মতো ঢেকে দিয়েছে জোছনা ছড়ানো চাঁদটাকে। চারিদিকে সুনসান নীরবতা। বাতাস গুমোট। একটা গাছের পাতাও নড়ছে না। ঝিঁঝিঁ পোকাগুলোও ডাকাডাকি থামিয়ে নিঃশব্দে বিশ্রাম নিচ্ছে। যেন দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে সবাই কিছু একটা ঘটার জন্য। একটা দুঃসহ শূন্যতা যেন হাহাকার করছে উঠান জুড়ে। অন্ধকারে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা খড়ের গাদাটাকে মনে হচ্ছে একটা অচীন পাহাড়। মনে হচ্ছে, এই শব্দহীন অনন্ত চরাচরে আমি আর ওই অর্বাচীন পাহাড়টা ছাড়া অন্য কেউ-ই কোথায়ও জেগে নেই। আমরা দুজন দুজনের দিকে ঘুমহীন শুকনো চোখে তাকিয়ে আছি, বোঝার চেষ্টা করছি কে বেশি একা? ও, না আমি?
মাস ছয়েক আগে ঘুমের মধ্যে হঠাৎ করে দাদি মারা যাওয়ার পর দাদাভাইও খুব একা হয়ে গেছেন। সেদিন শুনি উনি ঘরের চৌকাঠে বসে বিমর্ষ চেহারায় চোখ বন্ধ করে তার করুণ বিধুর ভাঙা গলায় দরবেশ হেদায়েৎ শাহের গান গাইছেন, ‘আমার দিনে দিনে সব ফুরালো, আমার ভরা ঘর হলো খালি, গুরু আমার ভরা ঘর হলো খালি... কোন অভাবের স্বভাব দোষে অচল হয়ে চলি…’ সুর যেমনই হোক গানের কথাগুলো যেন একেবারেই দাদার বুকের গভীর ব্যাথার জায়গা থেকে উঠে আসা। আর সেজন্যই বোধহয় তার বুজে থাকা চোখ থেকে টপ টপ করে পানি গড়িয়ে পড়ছিল।
আমাদের টিনের চালে এবার বৃষ্টির বড় ফোটা পড়ার টিপ টিপ আওয়াজ হচ্ছে, ভেজা বাতাসের নরম গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা দিচ্ছে। দাদাভাইয়ের প্রাচীন নড়বড়ে খাটটা কঁকিয়ে ওঠার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বুঝতে পারছি উনি এবার পাশের ঘর থেকে উঠে আসছেন আমার ঘরে।
‘ও সাজু! ঝড় বৃষ্টি শুরু হইছে! জানালা বন্ধ করছিলি? পানির ছাট আসবে তো !’
আমি এবারো চট করে জানালা বন্ধ করে নাক মুখ ঢেকে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছি। টের পাচ্ছি বৃষ্টির জোর বাড়ছে। কড়কড় শব্দ করে বজ্রপাত হচ্ছে। দাদাভাই তার নির্ধারিত টহল শেষ করে আবার ফিরে গেছেন নিজের ঘরে। একটু অপেক্ষা করে আবার উঠে বসি আমি। বুড়ো তাল গাছটা ফিরল কি না, সেটা না দেখে ঘুমাতে পারছি না। চিন্তা হচ্ছে বেচারার জন্য।
কিন্তু জানালা খুলতেই দমকা বাতাস আর বৃষ্টির ছাঁট তেড়ে এসে আচমকা আমাকে জাপটে ধরে প্রায় আধভেজা করে দিল। ওরে বাবা! এ যেন ‘চারি মেঘে জল দেয় অষ্টগজরাজ। সঘন চিকুর পড়ে বেঙ্গ-তড়কা বাজ’। দ্রুত জানালা বন্ধ করার আগে বিজলি চমকের চকিত চঞ্চল আলোয় দেখলাম বাবাজি ফিরে এসেছেন। নিজের জায়গায় এক পায়ে স্থির দাঁড়িয়ে শান্ত ভঙ্গিতে প্রবল বৃষ্টিতে ভিজছেন বৃক্ষসুন্দর। তার ফিরে আসায় স্বস্তি যেমন হলো, শংকাও হলো। বিনা বিচারে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত একজন আসামির মতো মনে হচ্ছে তাকে। একদিন পরেই করাতের শক্ত তীক্ষ্ম খাঁজ কাটা দাঁতে যার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।
বাইরে বিরামহীন বৃষ্টি আকাশ চেরা বিদ্যুৎ রেখা, সাথে ঘন ঘন বজ্রগর্জন। মাথার উপরের আসমান যেন একেবারে ভেঙে পড়ার উপক্রম। আমাদের জীর্ণ পুরোনো টিনের ঘরের ফাঁক ফোকড় দিয়ে বাইরে বিদ্যুতের ভয়ানক ঝলকানি টের পাচ্ছি। দূরে কোথাও বাজ পড়ার গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজও হচ্ছে। ঠান্ডা বাতাসে চোখ জুড়ে নেমে আসছে শান্তির ঘুম। এর মধ্যে দেখি খয়েরিসবুজ জোব্বা পড়া এক থুত্থুড়ে বুড়ো, কিভাবে যেনো ঘরে ঢুকে আমার মাথার কাছে জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খানিকটা চমকেই গেলাম ওকে দেখে। বুড়ো তার সবুজ চোখ কুঁচকে খনখনে গলায় বলল, ‘বহুদিন তো হলো, এবার যাবো। যাবার আগে বিদায় নিতে এলাম গো খোকা বাবু !’
‘যাবে?’ এবার উঠে বসলাম আমি, ‘কিন্তু, তোমার পাত্র কি পূর্ণ হয়েছে?’
‘আমরা পূর্ণ হয়েই আসি গো বাবু, শূন্য হলে যাই। শূন্যতাই আমাদের পূর্ণতা।’
‘যেও না বুড়া মিয়া। আমি দাদাভাইকে বলব যাতে তোমায় না কাটে। দাদি শুনলে কিছুতেই তোমারে কাটতে দিবে না…’
বুড়ো দাঁতহীন মুখ বাঁকা করে হো হো শব্দে হাসিতে ফেটে পড়ল, তার সেই হাসি থেকে, তার লম্বা জটা পাকানো একহারা শরীর থেকে একটা সবুজ আলো বিচ্ছুরিত হয়ে সারা ঘরে ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। সেই চোখ ঝলসানো নীলাভ সবুজ বিদ্যুতের একটা তীব্র চমক আর কান বিদীর্ণ করা বজ্রগর্জনের ভয়ানক শব্দে আমার ঘুম ভাঙল।
দেখি মাথার কাছে জানালাটা হা করে খোলা। মুহূর্তের জন্য চারদিক অস্বাভাবিক আলোকিত করে বিদ্যুত জ্বলে উঠলে সেই রুদ্র চকিত আলোয় ঘুমভাঙা হতবিহ্বল চোখে দেখতে পেলাম বুড়ো গাছটা মাথা দুলিয়ে খুব লড়াই করছে পাগলা বাতাসের সঙ্গে, আর এরই মধ্যে বিদ্যুতের আলো নিভে যেতেই আকাশ থেকে অভিশাপের মতো দ্রুতগতিতে নেমে এলো একটা বিশাল আগুনের গোলা, যেন এক ধারালো আলোর খড়গ। আর প্রচণ্ড শব্দে আমার কানে তালা লাগিয়ে নিমেষে ঝলসে দিলো বুড়ো তালগাছের লম্বা জটা পাকানো এক হারা দেহটিকে।
শাহ্নাজ মুন্নী কবি, কথাসাহিত্যিক এবং সাংবাদিক