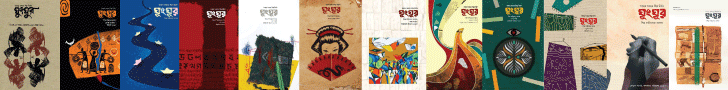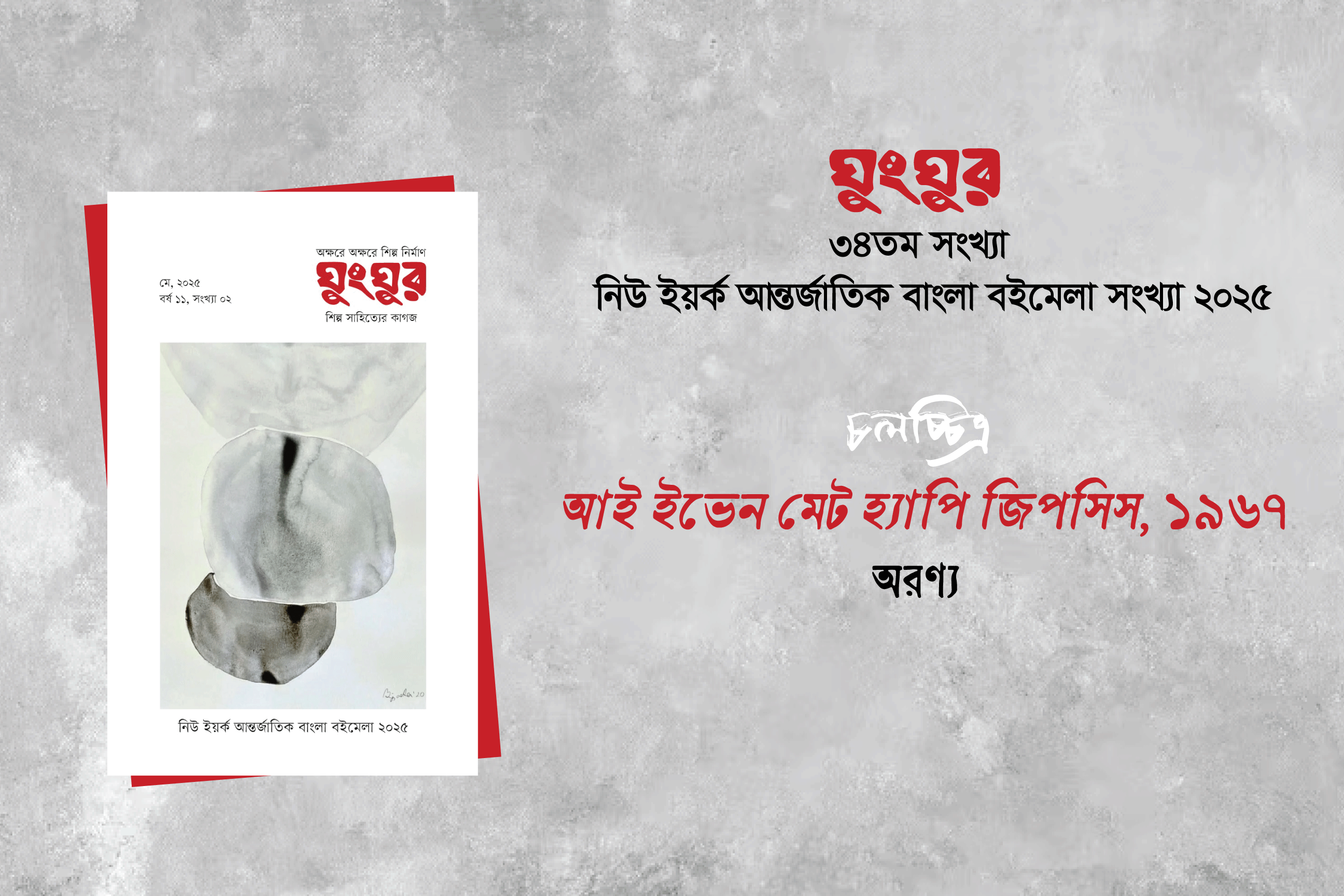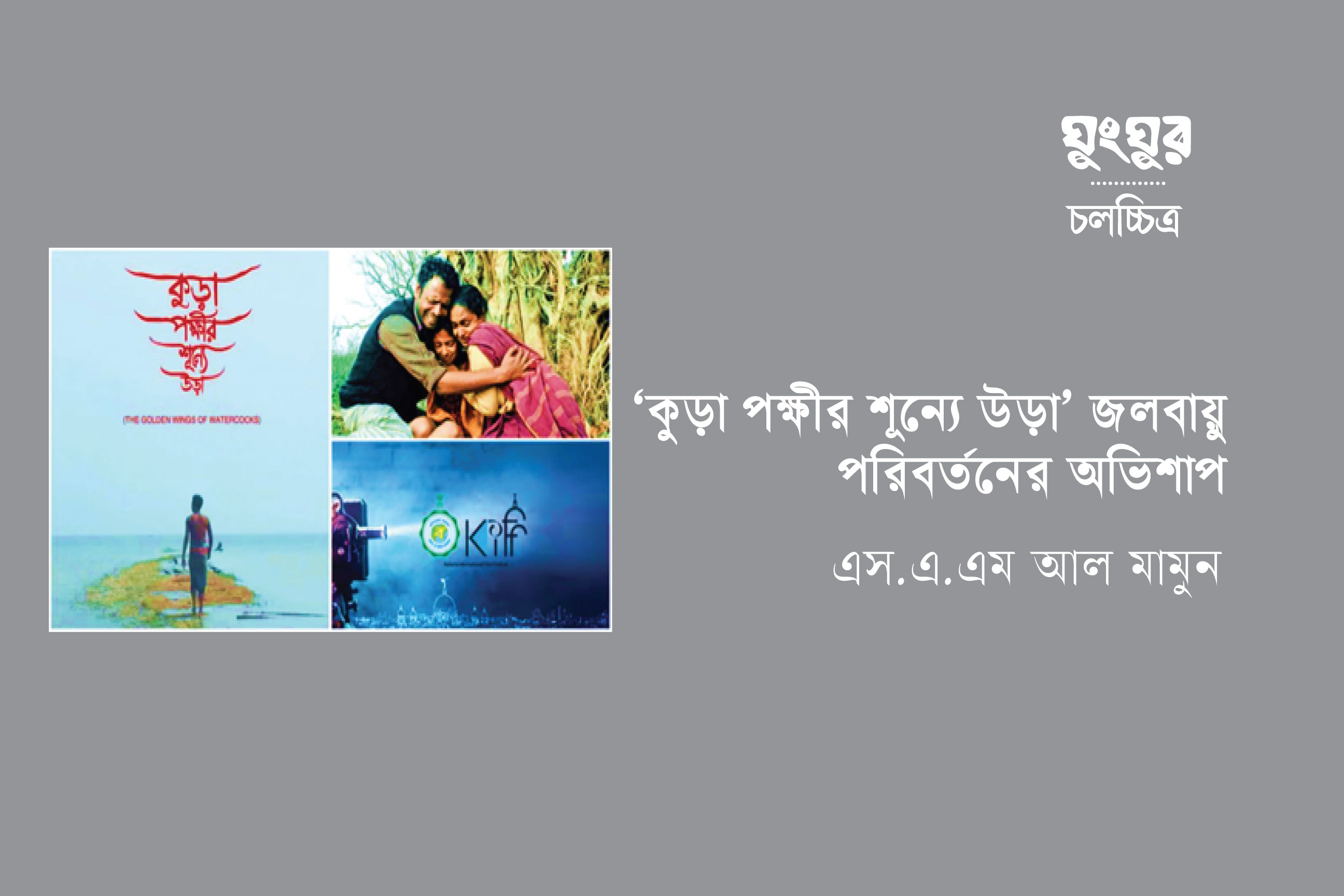আমাদের মুখ থুবড়ে পড়া চলচ্চিত্র শিল্প ও কিছু ভাবনা
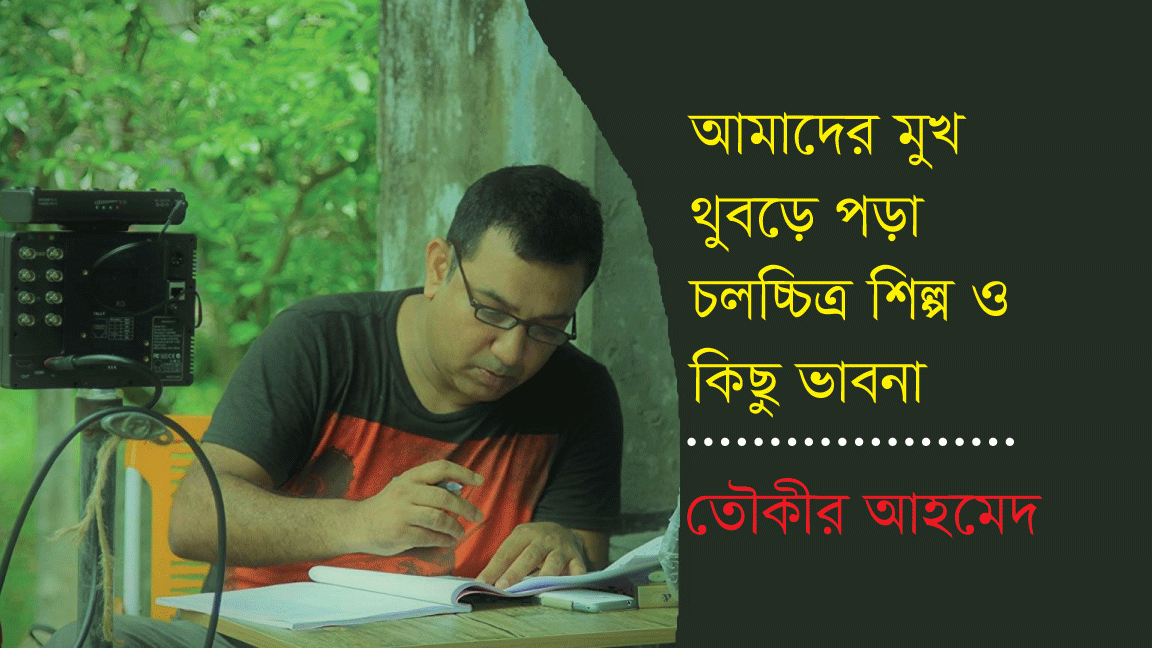
সময় কাল ১৯৭৫। বাবার সামরিক চাকরির সুবাদে তখন আমরা যশোর ক্যান্টনমেন্টের বাসিন্দা। স্কুলের পর খেলতে যাওয়া আর সন্ধ্যায় মেজবোনের নেতৃত্বে বিজ্ঞাপন তরঙ্গ নামের অনুষ্ঠানের গান শোনা। সপ্তাহে একদিন গ্যারিসন সিনেমা হলে অফিসার্স শো। সেই সন্ধ্যাটির জন্য সারা সপ্তাহ ধরে অপেক্ষা। কখনো ঈৎধহবং ধৎব ভষুরহম, মড়ড়ফ নধফ ধহফ ঁমষু কখনো বাংলা ছবি, একদম স্বপ্নের মতো আড়াই-তিন ঘণ্টা। ছবির সঙ্গে প্রেম বোধহয় তখন থেকেই প্রকট হয়। হঠাৎ একদিন সেই প্রেক্ষাগৃহে দেখে ফেলি কিছু ভারতীয় বাংলা ছবি, স্বাধীনতার পর ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে এসেছিল সেই ছবি গুলি। নি¤œমধ্যবিত্ত একটি পরিবার, বড় মেয়েটির উপার্জনেই সংসার চলে, শিল্পী হবার স্বপ্নে বিভোর ভাইটি ঝিলের ধারে গাছতলায় রোজ গলা সাধে, উচ্চাঙ্গ সংগীত না বুঝলেও আলোড়িত হই সেই সংগীত আয়োজনে, দার্শনিক পিতা আর সংসারের জোয়াল সামলে চুলার পাড়ে জীবনযুদ্ধ ক্রমেই ক্রর থেকে ক্ররতর মা, উচ্চাভিলাষী ছোট ভাই আর স্বার্থপর ছোট বোন।
টিউশনির পথে চটি ছিড়ে যায় মেয়েটির, দোকানির দেনা বাড়তে বাড়তে তিরস্কারের বান ছোটে সকাল বিকেল, কিন্তু থেমে থাকে না জীবন, অভাব আর দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে থাকে তারা। শত বঞ্চনার মধ্যেও স্বপ্ন উঁকি দেয়, ভোরের সূর্য। হ্যাঁ মেঘে ঢাকা তারা। ৪৩ বছর আগে দেখা একটি চলচ্চিত্র, কিন্তু দাগ কেটে আছে সেই ইমেজগুলি। আজ চার দশকের পথ পেরিয়ে আমি নিজেও একজন চলচ্চিত্রকর্মী। শৈশবের অনেক প্রেক্ষাগৃহে আমার নির্মিত ছবি প্রদর্শন হয় কখনো কখনো। কিন্তু ৪৩ বছর আগের মেঘে ঢাকা তারা বা সূবর্ণরেখা, সেই অভিজ্ঞতা ভুলতে না পারার কারণ আমাকে ভাবায়। ঋত্বিকের অসাধারণ নির্মাণ, নাকি আরও কিছু কি সেটা। চলচ্চিত্রের স্কেল? খধৎমবৎ ঞযধহ খরভব ঊীঢ়বৎরবহপব নাকি, চিত্র, কথা, গীত বাজনার সংমিশ্রণ, নাকি হৃদয় ছোঁয়া গল্প। সবটাই, নাকি কোনোটাই না, নাকি এই সব কিছু মিলে এক অনন্য সৃষ্টি, এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। অসংখ্য দৃশ্য আর শ্রুতির মধ্যে দিয়ে এক ইমেজের উত্থান যা হয়ে ওঠে সর্বোচ্চ শিল্প-চলচ্চিত্র। একই সময় দেখা হয়ে যায় আরও কিছু অসামান্য চলচ্চিত্র ইধষষধফ ড়ভ ধ ংড়ষফবৎ, নধঃঃষবংযরঢ় ঢ়ড়ঃবসশরহ, পথের পাঁচালী, দ্বীপ জেলে যায়, হারানো সুর, কিংবা এর পর মনে পড়ে রাজ্জাক কবরীর ছবি, উজ্জল, শাবানা, ওয়াসিম বা অলিভিয়ার ছবি। সামাজিক, অ্যাকশন বা ফ্যান্টাসি ছবি আর বম্বের সব নকল ছবি (তখন অবশ্য জানতাম না তা) আলমগীর কবিরের সূর্যকন্যা, সীমানা পেরিয়ে, আমজাদ হোসেনের গোলাপী এখন ট্রেনে, সুন্দরী কসাই, ভাত দে, সূর্য দীঘল বাড়ী।
বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগত তখন বর্ণিল এবং স্বপ্নীল, বছরে শতাধিক ছবি তখন একটি স্বাভাবিক ঘটনা, ইত্তেফাকের পুরো পাতা বা অর্ধ পাতা বিজ্ঞাপন আর রেডিওর “হ্যাঁ ভাই আসিতেছে রুপালি পর্দায় আপনার পাশের প্রেক্ষাগৃহে...।”
স্বাধীনতার পর মাত্র ৩ দশকের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়লো আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প। বক্স অফিস বাঁচাতে কখনো নকল কখনো সেক্স আর ভায়োলেন্স, কখনো ভাড়ামি, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। হল ওয়ালারা কখনো টিকেটে দুই ছবির প্রচারে রগরগে উন্মুক্তবক্ষা পশ্চিমা রমনীর ছবি কিংবা প্রদর্শনীর মধ্যে অশ্লীল কাট পিস যোগ করেও বাঁচাতে ব্যর্থ হলেন মুমূর্ষু এই শিল্পটিকে।
লক্ষণীয় বিষয়, সে এধরনের চলচ্চিত্রের ব্যর্থতার জন্য তারা দায়ী করলেন পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে ইলেক্ট্রনিক্স মাধ্যমের বিকাশ এবং স্বর্বগ্রাসী আকাশ সংস্কৃতিকে। ঈঘঘ, ইইঈ এর খ-কালীন প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আসলো ডিশ এন্টেনা, এলো দেশীয় বেসরকারি চ্যানেল, ৯০’র দশকের ঈউ, উঠউ-এর বিকাশ। কেবল এ প্রচারিত অসংখ্য অনুষ্ঠান উরংপড়াবৎু বা গড়ারব ঈযধহহবষ এর পাশাপাশি হিন্দি সংস্কৃতির সহজ লভ্যতা, এদেশের সংখ্যাধিক্য লোককে ভুলিয়েই দিলো আমাদের একটি শক্তিশালী ও সৃজনশীল চলচ্চিত্র শিল্প ছিল, ছিল যোগ্য এবং মেধাবী পরিচালক, লেখক, চিত্রগ্রাহক, গীতিকার বা গায়ক। এক সময়ের ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্মিত সিনেমা হলগুলি বা ঢাকা শহর বা জেলা শহরের বিলাশবহুল প্রেক্ষাগৃহগুলি বন্ধ হতে থাকলো একের পর এক। দেড় হাজারেরও বেশি রমরমা প্রেক্ষাগৃহ মাত্র তিন/চার দশকের ব্যবধানে কমে দাঁড়ালো ৩০০ তে। যার অর্ধেক সংখ্যক এখন অনিয়মিত।
বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প এখন ক্ষয়িষ্ণু এবং ধ্বংস প্রায় একটি ইন্ডাষ্ট্রি। ছবির সংখ্যা কমে এসেছে ৫০ এর ঘরে যার এক তৃতীয়াংশ শুধু নামেই চলচ্চিত্র। এগুলির না আছে কোন শিল্পমান বা ব্যবসায়িক সাফল্য। বাকি একাংশ হিন্দি তামিল বা বিদেশি চলচ্চিত্রের দুর্বল নকল নির্মাণ। হাতে গোনা দু’চারটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে বেশির ভাগ মৌলিক ছবিও সৃজনশীলতা ও প্রযুক্তিগতভাবে পশ্চাৎপদ এবং স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ। একই সঙ্গে সংকুচিত প্রদর্শন ব্যবস্থা মনোপলি সিন্ডিকেটের চাপে ভেঙে পড়া সার্বিক ব্যবস্থা।
সময় পরিবর্তনশীল, সময়ের সঙ্গে যেকোনো শিল্প বা বাণিজ্যও পরিবর্তন হবে সেটাই স্বাভাবিক তা হলে ঢাকাই চলচ্চিত্রের এই অবদমন এর কারণ কি। একটি মাধ্যমের বাণিজ্যের পাশাপাশি এর শৈল্পিক এবং তাত্ত্বিক দিকও বিকশিত হবে সেটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ঋউঈ এর ক্ষেত্রে সেটা হলো না কেন? সেখানে কি সে ধরনের দিক নির্দেশনা দেবার মত যোগ্য সৃজনশীল লোকের অভাব ছিল, নাকি সময়ের সঙ্গে তাদের বিতাড়িত এবং নিস্ক্রিয় করা হয়েছিল। ষাট সত্তরের দশকের জহির রায়হান, কাজী জহির, আমজাদ হোসেন, খান আতা, আলমগীর কবির-দেরকে কেন কাজে লাগাতে পারলো না এই ইন্ডাষ্ট্রি? কেন তাদের উত্তরসূরিরা মেধা ও মননে একই মান বজায় রাখতে পারলেন না। নাকি, বিকাশমান এই ইন্ডাষ্ট্রিতে ক্রমেই বেড়েছে কালো পুঁজির দৌরাত্ম আর দুর্বিত্যায়ন। এক ধরনের দর্শনশূন্য আদর্শহীন পুঁজি ও পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত মনোরঞ্জন আর ক্ষমতায়ন। বাণিজ্যিক ধারার (মুনাফার উদ্দেশ্যে) ছবি গুলিকে যদি মূলধারা বলি, তাহলে প্যারালাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্বাধীনধারা, বা বিকল্পধারা যে নামেই ডাকি না কেন, তারাই বা অবদান রাখতে পারলেন না কেন, যারা হয়তো ভিন্ন ধারার উত্থানের মাধ্যমে পরিবর্তন করতে পারতেন এই মাধ্যমকে, মহিউদ্দিন সাকের, শেখ নিয়ামত আলী, মোরশেদুল ইসলাম, তানভীর মোকাম্মেল বা তারেক মাসুদ-এর মতো শিক্ষিত নির্মাতা ইন্ডাষ্ট্রিতে আউট সাইডার রয়ে গেলেন কেন? ঋউঈ কেন্দ্রিক চর্চা তাদেরকে ডাকলো না কেন? ভয়ে, শঙ্কায়। নাকি তাদের মধ্যেও কাজ করলো স্বাভাবিক সংকোচ এবং নাক উঁচু একটি মনোবৃত্তি। কিন্তু এটাও তো সত্যি যে এদেশের পরিবেশকরা কখনোই উৎসাহিত করেননি অন্য ধারার কোনো চলচ্চিত্র। বরং কোণঠাসা করা হয়েছে এই সকল নির্মাতার প্রয়াস। এর পাশাপাশি চার দশকের নি¤œগামী চলচ্চিত্র আরও নি¤œমুখী করেছে আমাদের শিক্ষা বঞ্চিত দর্শকরুচি। যেই রুচির দোহাই দিয়ে অযোগ্য প্রযোজক আর পরিচালক ক্রমাগত নির্মাণ করে চলেছেন বস্তাপচা বাজে ছবি, নি¤œমানের অভিনয় আর অযৌক্তিক গল্পের বিপণনে আশ্রয় খুঁজেছেন অশ্লীলতা আর রুচিহীনতার মধ্যে। তা হলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন এসে যায় এদেশের চলচ্চিত্র শিক্ষা নিয়ে। দেশ বিভাগের পরপরই নেহেরু ভারতে প্রতিষ্ঠা করেন পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউট বা ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেখান থেকে শিক্ষিত প্রশিক্ষিত তরুণরা ধারাবাহিক ভাবে কাজ করে চলেছেন ভারতের বিভিন্ন ইন্ডাষ্ট্রিতে। আমরা কেন সে রকম কিছু পারলাম না। ধরে নিলাম ’৭১ পূর্ববর্তী পাকিস্তান শাসন আমলে পূর্ববঙ্গ অবহেলিত থেকে গেছে ২৪ বছর। কিন্তু স্বাধীনতার পর ৪৬ বছরই বা আমরা কী করলাম, আজো প্রতিষ্ঠিত হয়নি এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান। হালে যাও কিছু হচ্ছে সেগুলিতেও আছে যোগ্য শিক্ষক এবং সুবিধার অভাব। একটি জাতীয় চলচ্চিত্র ইনিস্টিটিউট বা ফিল্ম সেন্টার এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতো এদেশের চলচ্চিত্র কে। ফিল্ম সোসাইটি বা চলচ্চিত্র সংসদের কার্যক্রম ও সংকুচিত হয়েছে বর্তমান বাজার অর্থনীতির চাপে। তরুণরা এখন ফিল্ম সোসাইটি বা গ্রুপ থিয়েটারের চেয়ে ক্যারিয়ার কে গুরুত্ব দিচ্ছে অনেক বেশি। লিটল ম্যাগাজিন বা পাঠচর্চার বদলে সময় চলে যাচ্ছে ফেইসবুকের পাতায়। পড়া বা লেখাও সংখ্যা ঘরিষ্ঠ সামাজিক মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ করেছে। যুগকে অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে প্রজন্মকে দিক নির্দেশনা দেয়াও রাষ্ট্র এবং সমাজের দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন এসেই যায়। এদেশের নীতি নির্ধারকরা চলচ্চিত্র তথা শিল্প সংস্কৃতিতে কতোটা গুরুত্ব দিয়েছে। ভাষা আন্দোলন, ’৬৯-এর গণ আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ বা স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে তো এদেশে সংস্কৃতিকর্মীরা অগ্রণী ছিলেন, তাদের পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এই ভূখ-ের মানুষের মুক্তির পক্ষে কাজ করেছে। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতি, রাজনৈতিক অর্জন বা ক্রিকেট উন্নতি তো একটি জাতীয় সার্বিক উন্নতির সূচক নয়। একটি শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান জনগোষ্ঠী আসলে একটি জাতীর পূর্ণাঙ্গ উন্নয়নের চালিকা শক্তি। আর সেই সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও শিক্ষার দায়িত্ব কিন্তু রাষ্ট্রের ওপরই বর্তায়। সাহিত্য, গান, নাটক এবং চলচ্চিত্রই পারে জাতির মানস গঠন করতে, তাকে সুশৃঙ্খল, মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন, পরমত সহিষ্ণু করতে পারে একমাত্র সংস্কৃতি। স্কুল পর্যায়ের থিয়েটার-এর অন্তর্ভুক্তি বা হাইস্কুল থেকে চলচ্চিত্র সংসদ পারে একটি রুচিশীল ও সংস্কৃতিবান প্রজন্ম তৈরি করতে। এজন্য সংস্কৃতির এই শাখাগুলি বিশেষ গুরুত্বে দাবি রাখে। সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও শিক্ষাই আসলে এগিয়ে নিতে পারে আমাদের চলচ্চিত্রকে।
এক্ষেত্রে আর একটি বিষয় ও আলোচনায় আসতেই পারে। তা হলো ইনফ্রা ষ্ট্রাকনার। ৬০, ৭০ বা ৮০ এর দশকের নির্মিত প্রেক্ষাগৃহগুলি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আজ জীর্ণ ভঙ্গুর। তাদের কোনো উন্নয়ন হয়নি। হয়নি প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ, সেলুলয়েড থেকে ডিজিটাল প্রযুক্তির পরিবর্তনেও ভূমিকা রাখতে পারেনি রাষ্ট্র, বরং মাঝখান দিয়ে সুবিধাবাদী শ্রেণিই আবার রক্ষকের বেশে হাজির হয়ে নির্মাণ করেছেন এক নব্য পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা।
প্রযোজক ও পরিবেশক নীতিমালাও এখন ভারসাম্যহীন ছবি বানাবেন প্রযোজক, হলে নেবার জন্য প্রচারণাও তার দায়িত্ব, হলের ব্যানার পোস্টার সবই করতে হবে তাকে, সর্বোপরি প্রজেকশন সিস্টেমের ভাড়াও গুনতে হবে তাকে। অর্থাৎ সব খরচই তার। হল, শুধু প্রদর্শন করবে। অথচ সেই প্রযোজক পাবে ১০০ টাকায় (২১-২৬) টাকা। স্থান ভেদে আরও কম এবং একটি হিট ছবি তার লগ্নি উঠাতে পারছে না ইদানীং।
অথচ সিন্ডিকেট ও তার সহায়ক ব্যক্তি কামিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। স্বঘোষিত স্টার আর সুপারস্টারেরা আঙুল ফুলে কলা গাছ হবে আর জনগণ প্রতারিত হবে চলচ্চিত্রের নামে।
লক্ষণীয় বিষয় যে তাদের এই চাতুরি আর ব্যবসার বস্তাপচা মাল দর্শক আর গিলতে চাইছেন না। যারা জনরুচির দোহাই দিয়ে এই নি¤œমানের শিল্প বেঁচতে চাচ্ছেন তারাও এখন ব্যর্থ হচ্ছেন মানুষকে টানতে।
আশার কথা এদেশের বিশাল জনসংখ্যা বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও ছাত্ররা চলচ্চিত্র নিয়ে ভাবছেন, সিনেমার ভালো মন্দ নিয়ে কথা বলছেন। সমালোচনা শুধু নয়, অখাদ্য কুখাদ্য তারা চিহ্নিত করছেন সামাজিক মাধ্যমে। তারা সৃজনশীল সুনির্মিত ছবি দেখতে চান, চান তার দেশের ছবি, তার ভাষার ছবি। যতো প্রতিকূলতাই থাকুক তাদেরই এই চাওয়া পূর্ণতা পাবে নিঃসন্দেহে। কারণ একটি শিল্পের অর্ধেক যদি হন নির্মাতা বাকি অর্ধেক দর্শক।
তাদের চাহিদা রাষ্ট্র গুরুত্ব না দিলেও সময় দেবে, এদেশের তরুণ নির্মাতারা তৈরী হচ্ছেন সেই যুদ্ধের জন্য। যার দামামা শোনা যাচ্ছে, শুধু দেশের চলচ্চিত্রের শিল্পমান বা শিক্ষা নয় এর ইনফ্রা স্ট্রাকচার ও আজ যুগের দাবী। সে দাবীও পূরণ হবে অচিরেই। জেলা বা উপজেলা পর্যায়ক্রমে থানা বা ইউনিয়ন পর্যায়ে আবার তৈরি হবে নতুন আঙ্গিকে ছোট ছোট প্রেক্ষাগৃহ মাল্টিপ্লেক্স বা সিনেপ্লেক্স।
এদেশের চলচ্চিত্র শুধুমাত্র মাথা তুলে দাড়াবে তাই নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলা চলচ্চিত্র ছড়িয়ে দেবে আমাদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি। চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই তৈরি হবে বাংলাদেশের নতুন পরিচয় ও ভাবমূর্তি।