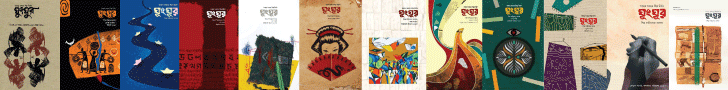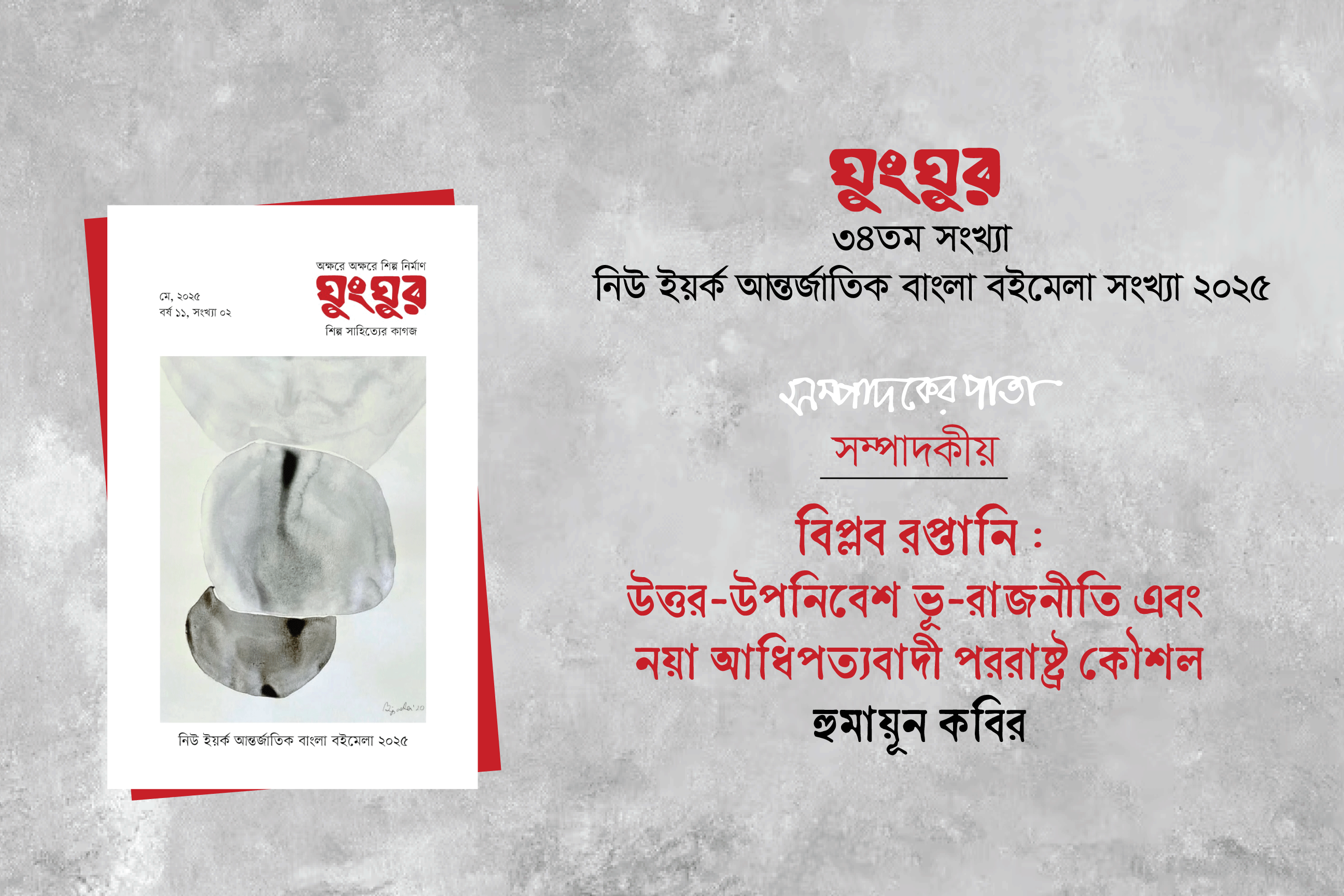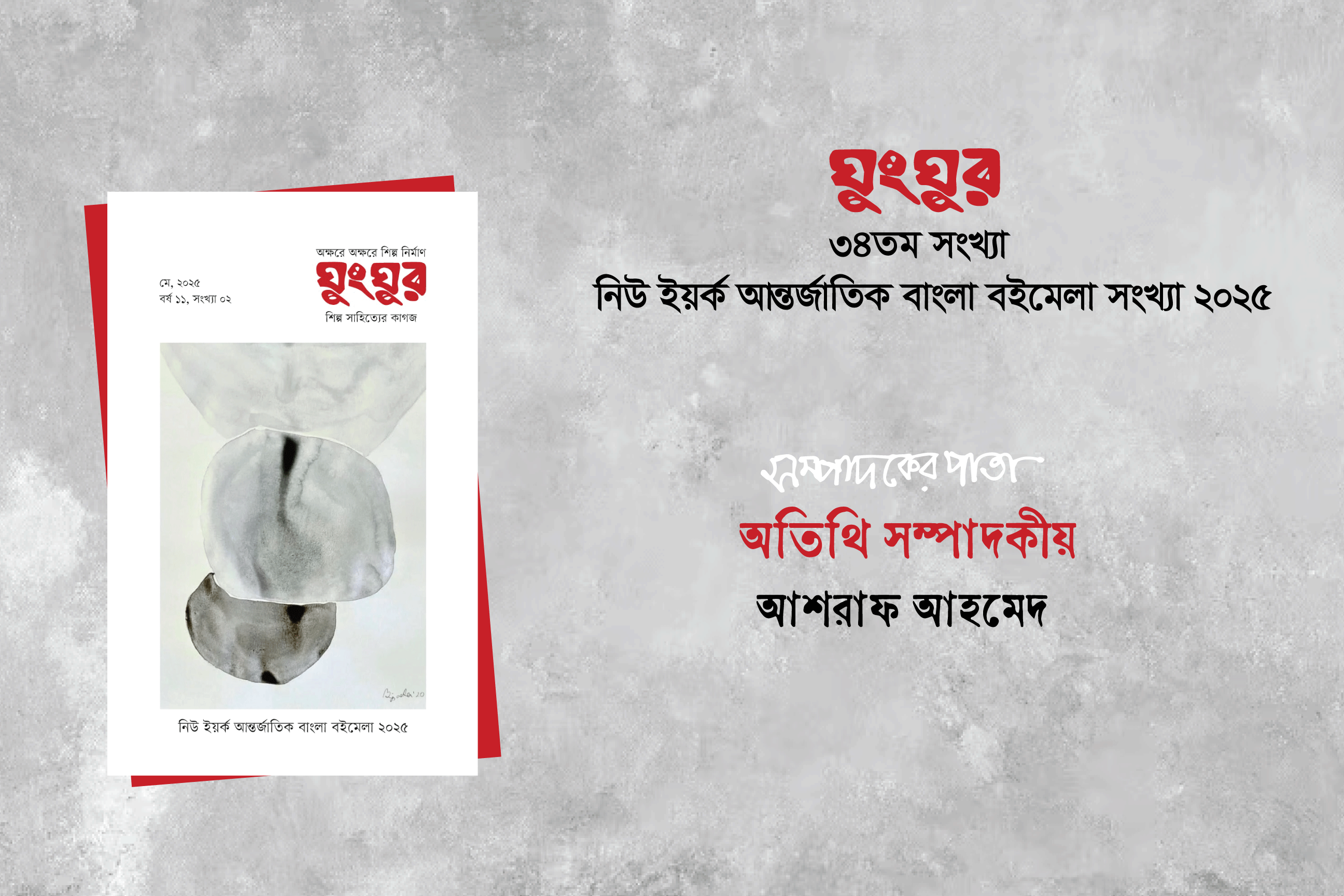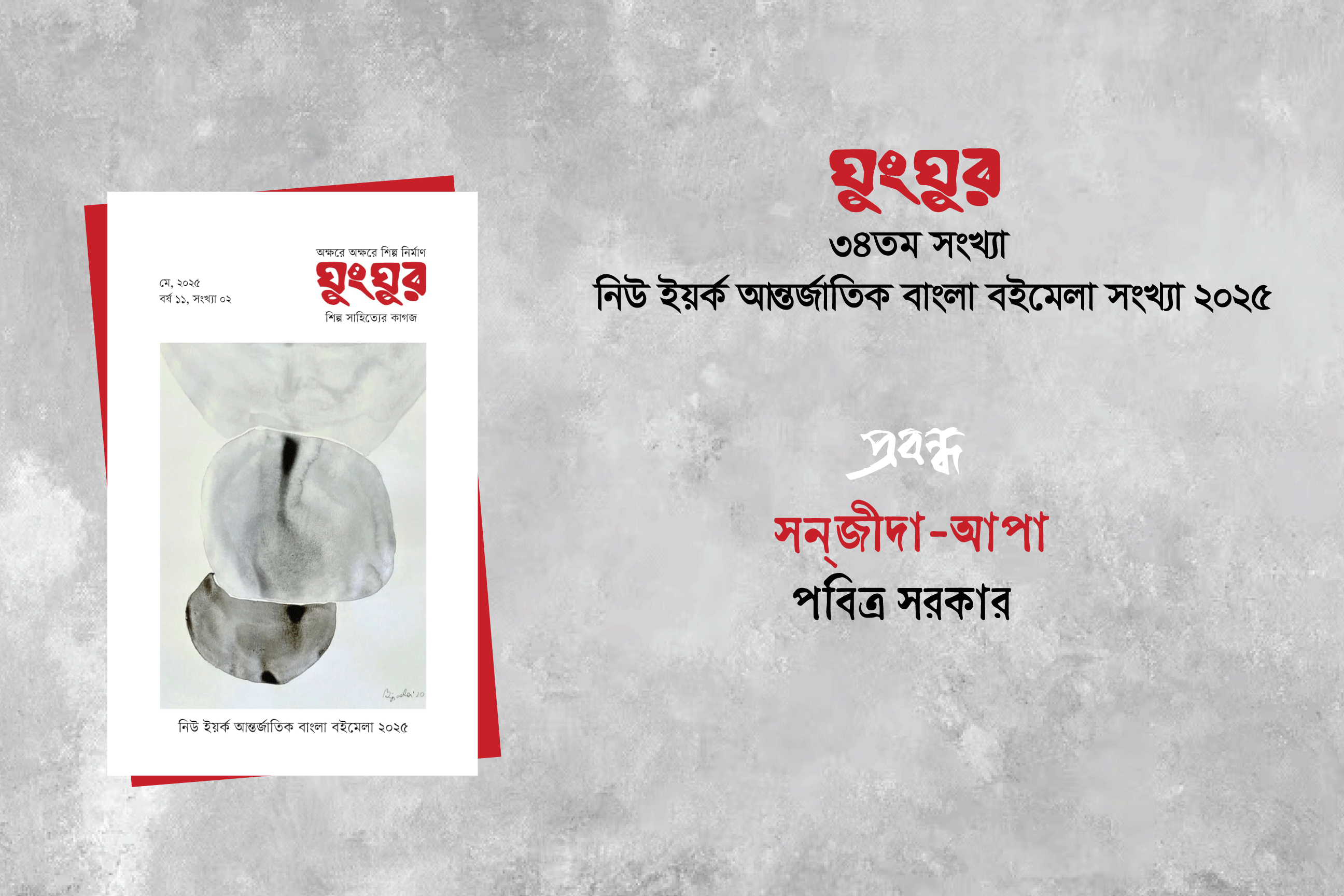মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতা এবং আধুনিক কাব্যভাষা

কবিতা এমন এক শিল্পমাধ্যম, যা আমাদের অবচেতন মনের কথা বলে। এই অবচেতন মনের প্রতিফলন দেখা যায় নানাভাবে। মানুষের প্রয়োজনে তৈরি হয় পথ। পথ পেরোনোর জন্য গড়ে নিতে হয় রাস্তা। তখন, ঘর ভেঙে চিরাচরিত হাসিকান্না সুখদুঃখ ভেঙে হাঁটা শুরু হয় গন্তব্যের দিকে। যেতে চাইলে যেতে হয় সেই পথে, আবার না চাইলেও যেতে হবে তাকে! সেই পথ সুন্দর, কারুকার্যমণ্ডিত, সেই পথ দৃশ্যের কাছে নত...সেই পথ বিরহের, দুঃখের, বিচ্ছেদের। কাহিনির পর কাহিনি সাজিয়ে হেঁটে যাওয়া পথের স্বপ্ন ঘিরেই যেন মানুষের যাত্রা শুরু। তাকে যেতেই হবে; থেমে থাকার, বসে থাকার কোনো উপায় নেই! শব্দ, অক্ষর, বাক্য আমাদের নিয়ে যায় সেইসব জীবন এবং বোধের কাছে। দার্শনিক প্লেটো বলেছিলেন, আদর্শ নাগরিকদের জন্য কবিতা ক্ষতিকর। কিন্তু তাও সারা বিশ্বে অসংখ্য কবি, কবিতা এবং লেখকের জন্ম হয়েছে।
বেড়ালটা সকাল থেকে কাঁদছে
কাল থেকে ওর বাচ্চাটা নিখোঁজ।
আমি রাতের বেলা রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করছিলাম,
সে শান্তির আশায় এসে দুই থাবা জোড় করে বসল।
কিন্তু হল না।
একটু পরেই সে মিউমিউ করে আবার কাঁদতে লাগল,
পাগলের মতো প্রদক্ষিণ করে ঘুরতে লাগল।
আর পুত্রশোক আগুনের মতো ঘিরে ধরল
রামকৃষ্ণদেবকে। (বিড়ালী, মণীন্দ্র গুপ্ত)
কী ভেবে লিখেছিলেন কবি মণীন্দ্র গুপ্ত এই কবিতাটি, তা আমরা যদি নাই বা জানি, তাহলেও এই কবিতাটি সম্পর্কে আমাদের পাঠ-প্রতিক্রিয়ার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। এখানেই কবিতার সৌরভ। কতগুলো আপাত অসংলগ্ন চিত্রকল্প একসঙ্গে গেঁথে এমন কোনো ভাবনার কাছে পৌঁছেছে যা একসঙ্গে এই কবিতাটি আবার এই কবিতাটি নয়ও। কবিতা এই অনুভূতিমালার কাছেই আমাদের নিয়ে আসে, যা কবিতাটিকে বাদ দিয়েও কবিতার বিষয়টিকেই ফুটিয়ে তোলে, আবার যা কবিতাটি ছাড়া অসম্ভব। কবিতার তেমনভাবে সামাজিক মূল্য আছে কি না জানা নেই, তবে সমাজ ছাড়া কবিতার মূল্য নেই। কিন্তু এটাও সত্য, সমাজকে কবিতা অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়েই দেখতে পারে। জীবনানন্দের কথা অনুসারে, এক ধরনের নিরভিসন্ধি কবিতার মধ্যে থাকে। অর্থাৎ, কবিতার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে না থাকলেও, পরোক্ষভাবে তার সমকালীনতা এবং চিরকালীনতাই ফুটে ওঠে। যে যে কবিতায় ফুটে ওঠে, সেগুলোই সার্থক কবিতা।
একটি বেড়াল মায়ের কথা এখানে বলা হয়েছে। যার বাচ্চা গতকাল থেকে নিখোঁজ। মায়ের সন্তান হারানোর বেদনায় একজন কীই বা করতে পারে? কোনো সান্ত্বনাবাক্য নেই। যে ব্যক্তিগত শান্তির বা দার্শনিক বীক্ষার জন্য কবি রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করছেন। তার সামনে শান্তির আশায় সেই বেড়ালটি দুই থাবা জোড় করে বসল। কিন্তু সে শান্তি পেল না। এই হলো আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড়ো ডায়েলেক্টিক্স। বেদনাও বলা যায়। কারণ মানুষ শোক থেকে শান্তির জন্য বারবার প্রার্থনা করে, কিন্তু যখন সে উদাসীন এবং নিস্পৃহ হতে চায়, তখনো তার মনে মায়ার প্রতি আকর্ষণ যায় না। নশ্বরতার সঙ্গে যে নশ্বর যোগাযোগ আমাদের রয়েছে, সে যোগাযোগ ছিন্ন হতে পারে না। এই কষ্ট ভোগের বা দুঃখের যে সংযোগ তা বজায় থাকে আমাদের আজীবন। এখানেই আমাদের আধ্যাত্মিকতার মধ্যে নশ্বরতার যোগসূত্রটি।
অথচ আমরা অবিনশ্বর এক ভাবনার দিকেই ক্রমশ ছুটে যাই। আমাদের জীবনের যন্ত্রণাই থাকে অবিনশ্বরতার জন্য। সমস্ত শিল্পের মূল কথা জীবদ্দশার সময় পেরিয়ে চিরসময়ের কথা কীভাবে ফুটে উঠছে আমাদের মধ্যে, সেই কথাগুলোকে খুঁজে পাওয়া। কবিতা সেই বৃহত্তর কথারই একটি অংশ। হয়তো একটিই কথা থাকে আমাদের। সেই দীর্ঘ এবং বৃহত্তর কথার খণ্ড খণ্ড কথাগুলোকে আমরা খুঁজে চলি। আর এই খুঁজে চলাই হলো আমাদের অভিযাত্রা। এর ফলেই কবিতাটির পরে আমরা পাচ্ছি, একটু পরেই সেই বেড়ালটি আবার পাগলের মতো শোকে অন্ধ হয়ে গেল। কবিতাটির শেষ লাইনটিতে রয়েছে একপ্রকার সংযোগ। পুত্রশোক আগুনের মতো ঘিরে ধরল রামকৃষ্ণদেবকে। এখানে এসেই আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই। কবিতাটি একলাফে সরলরৈখিক এক বাস্তবতা থেকে লাফ দিয়ে মিশে গেল অনন্তে। একটি বিন্দু সময়খণ্ড থেকে লাফ দিয়ে মিশে গেল বৃহত্তর সময়খণ্ডে। এই হলো প্রকৃত কবিতার বিষয়। অর্থাৎ একটি প্রকৃত কবিতা শুধুমাত্রই খণ্ড সময়কেই প্রতিনিধিত্ব করে না। সেই খণ্ড সময়কে অখণ্ড সময়ের আধারেই উপস্থাপনা করে। কারণ প্রতিটি খণ্ডই আসলে অখণ্ডের প্রকাশমাত্র। মণীন্দ্র গুপ্তের এই কবিতাটি যেমন। শেষ লাইনটা আমাদের নানান সম্ভাবনার মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছে। হতে পারে, পুত্রশোক যেমন আকুলতা, ঈশ্বরকে না পাওয়ার ব্যাকুলতা তৈরি করে, তেমনভাবে অগ্নিসম ঘিরে ধরল রামকৃষ্ণদেবকে। আবার রামকৃষ্ণদেব এখানে এক বৃহত্তম দর্শন, যাকে ঘিরে রয়েছে নশ্বরতার শোক, দুঃখ, যন্ত্রণাগুলো। অর্থাৎ, এইসব শোক দুঃখ যন্ত্রণাগুলো যদি আমাদের ঘিরে না থাকত, তাহলে কি আমরা প্রত্যেকেই প্রজ্ঞার স্তরে উন্নীত হতাম? তা নয়। কিন্তু আমরা জানি, যন্ত্রণা বা সহ্য করা দুঃখেরও একটি অর্থ আছে। আর তা হলো, তা ক্রমশ আমাদের প্রজ্ঞার কাছে নিয়ে যায়। প্রজ্ঞাই হলো সেই পথ, যা আমাদের ছোটো দুঃখকে অতিক্রম করে বড় দুঃখের কাছে নিয়ে যায়। বড়ো দুঃখের যে যাত্রাপথ, তা সহজ নয়। অনেক পতঙ্গের মতো পুড়তে পুড়তে মানুষ সেই অবিনশ্বর চেতনাপ্রবাহের স্বাদ পাওয়ার মতো একটা সম্ভাবনা তৈরি করে। কবিতা হলো একপ্রকার ধ্যানের মতো, যা আমাদের মুহূর্তেই মুহূর্ত থেকে চিরকালীন মুহূর্তের দিকে নিয়ে যায়।
কিন্তু কবিতার সঙ্গে ধ্যানের একটি পার্থক্যের জায়গাও আছে। আর তা হলো, ধ্যান যদি মুক্তিকে প্রত্যক্ষ করার জন্য হয়, তাহলে কবিতা মুক্তিকে বন্ধনের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য লিখিত হয়। সবরকম কবিতাতেই যে রূপের সাধনা করা হয় তা নয়। বরং কবিতাই বলি আমরা বা শিল্পের অন্যান্য আঙ্গিক, রূপের অন্তরালে যে অরূপ, তারই সাধনায় মগ্ন থাকি আমরা। এই অরূপ বা বাক্য ও মনের অতীত যে স্তরে, তাকে আমরা কতদিন ধরে পূজা করব অক্ষরে বা ভাস্কর্যে বা সুরের মধ্যে, যদি না সে এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের সেই চৈতন্যের স্বাদ না দেয়? রামপ্রসাদ লিখেছিলেন, আমার চেতনা চৈতন্য করে দাও। অর্থাৎ, আমার ব্যক্তিগত চেতনাও হলো সেই আধারের মতো, যা চৈতন্য নামক মহাজগতের এক কণা মাত্র ধরে আছে। বিশ্ব তো সত্যিই এক মুঠোর মধ্যে আসতে পারে না। কারণ আমি নিজেই সেই বিশ্বের এক ক্ষুদ্র অংশ। আমি আমার হাতের মধ্যে কখন আসতে পারি, যখন আমি ও আমার হাত আলাদা। কিন্তু এই দ্বৈত সম্পর্কটি আমরা বহন করছি না একপ্রকার অদ্বৈত সম্পর্ক বহন করছি, সে বিষয়ে তর্কে না গেলেও একটা জিনিস বোঝা যায়, মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে আমিও সেই মহাকালের এক টুকরো। কবিতা, সংগীত, শিল্পকলার লক্ষ্যই হলো সেই আদি ও অকৃত্রিম বা চিরপরিবর্তনশীল সাম্যকে অনুভব করাকে প্রকাশ করে যাওয়া। কারণ এ জগতের মূল কাজই হলো নিজেকে নিজেই সৃষ্টি করা এবং ধ্বংস করা। সে প্রকাশিত হতে চায় কারণ সে প্রকাশের পরে পুনরায় ধ্বংসও হতে চায়। আবার নতুন করে জাগ্রত হওয়ার জন্য তার এই বারবার ফিরে আসা, পুড়ে যাওয়া এবং ফিরে আসা।
কবি মণীন্দ্র গুপ্তর কবিতা এক ঝটকায় আমাদের নিয়ে যায় অনন্তকালীন সেই সত্তার কাছে, যে এক চিরকালীন অভিযাত্রী। কবি মণীন্দ্র গুপ্তর কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয় তিনি এক পথিকের মতো, যিনি, নিখুঁতভাবে তাঁর রাস্তাটিকে লক্ষ্য করতে করতে চলেছেন। কিছুই নজর এড়াচ্ছে না তাঁর। ছোট ছোট নানা ঘটনা, রাস্তার দুধারে নানান বসতি, নানান মানুষ, তাঁদের জীবনযাত্রা—তিনি দেখছেন আগ্রহভরে। কিন্তু মনের মধ্যে প্রবহমান রয়েছে এক বিস্ময়। এই বিস্ময় জীবনানন্দ কথিত ‘অন্তর্গত বিপন্ন বিস্ময়’ নয়। কোথাও এই বিস্ময় তাঁকে মহাজাগতিক সুন্দরের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি নিশ্চেষ্ট, নির্মোহ এবং উদাসীন এক দ্রষ্টার মতো শুধু পর্যবেক্ষণ করছেন।
তিনি সব চোখ মেলে দেখছেন আর আকাশের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছেন। মহাকাশের অন্ধকার দিয়ে তিনি দেখছেন আলোর পৃথিবী। আর এই রোদ্দুর দিয়ে তিনি দেখছেন মহাকাশের অন্ধকার। নিজের প্রবাহকেই করে তুলছেন মহাজাগতিক। তাই তাঁর কবিতা যেমন চিরকালীন, প্রবহমান, বা অনন্তসন্ধানী বলে সমকালীনতাকে পরিত্যাগ করে বিশুদ্ধ কবিতার দিকেই শুধু হাঁটেনি, তেমন বিশুদ্ধ কবিতাকে অস্বীকারও করেনি। কারণ এক প্রকৃত অনুসন্ধানকারীর মতো তিনি জানেন, এই অনুসন্ধানের নানা পথ। কোনো পথই মিথ্যা নয়, বরং সত্যের এক একটি রূপ। তাঁর কবিতায় এক সংযমী, সহিষ্ণু, স্থিতপ্রজ্ঞ ‘জেন’ অভিযাত্রীর পদশব্দ টের পাওয়া যায়। সমগ্রকে নিজের মধ্যে টের পাওয়ার, আর তাকে ছোট ছোট নানা রূপের মধ্যে আবিষ্কার করার এই যে কবিকৃতি, সেটিই কবি মণীন্দ্র গুপ্তের কাব্যব্যক্তিত্ব। তার সঙ্গে মিশে যায় তাঁর অভিযাত্রা। এই অভিযাত্রা যেমন ব্যক্তিকবির নিবিড়, একাকী সংলাপের এক আত্মজৈবনিক ভাষ্য, তেমন, এক দার্শনিক মেধাবী কাটাকুটি খেলাও। মেধা, মন এবং আবেগের (যদিও সবই মেধা, তবু এখানে বুদ্ধি, আবেগ ও বোধ—এগুলোকে আলাদাভাবে দেখার কথাই ভেবেছি) এই সামগ্রিক মিলনরেখাগুলোই তাঁর কবিতার মাইলফলক।
কিন্তু কেমন ছিল তাঁর কবিকৃতি? ষাট দশকের আশেপাশে তিনি যখন কবিতা লিখতে শুরু করেন, তখন তাঁর পাশাপাশি রয়েছে কৃত্তিবাসের কবিরা। সহজেই তিনি প্রভাবিত হতে পারতেন তাঁদের দ্বারা। প্রভাবিত হতে পারতেন কৃত্তিবাসের পাশাপাশি শতভিষা পত্রিকার আবহমান নিচুস্বরে গুরুত্বপূর্ণ কাব্যব্যক্তিত্ব দ্বারাও। কিন্তু কবি মণীন্দ্র গুপ্তের মধ্যে ছিল এক নতুন কাব্যভাষার খোঁজ। আর মানসিকভাবে তিনি বহুস্বরে বিশ্বাসী এক কবি ছিলেন। যখন নাগরিকতার চিত্রকল্প, একাকী মানুষের বিষাদ এবং প্রকৃতির সঙ্গে উচ্ছ্বসিত যাপনের এক ধারাবাহিক লেখার পৃথিবী ক্রমশ ছড়িয়ে যাচ্ছে বাংলা কবিতায়, তিনি একটু অন্য পথে হাঁটা শুরু করলেন। বাংলার দেশজ চিত্রকল্পের কাছে ফিরে গেলেন। ফিরে গেলেন মানুষের কাছে। মানুষের কথ্যভাষায় ব্যবহৃত নানা ঘটনা, লোককথা, লোকসংস্কৃতি, প্রবাদ, ধর্মীয় বিশ্বাস, টোটেম, আর এ সমস্ত কিছুর অনাবিল শব্দভাণ্ডার তাঁর জীবনকে এবং কাব্যভাষাকে গড়ে তুলল। তিনি অন্বেষণ করতে লাগলেন এমন সব শব্দের, এমন সব চিত্রকল্পের, যা আবহমান কাল ধরে বাংলার সংস্কৃতিকে পুষ্ট করেছে। সেই সব শিকড়ভেজা শব্দগুলোকে তিনি নতুন করে প্রাণ দিলেন তাঁর কবিতায়। কিন্তু এই প্রাণপ্রতিষ্ঠা পুরনোর কাছে ফিরে যাওয়া হলো না। বরং পুরনোকে, শিকড়কে নতুন ভাষার, নতুন ব্যাখ্যার এবং নতুন দৃষ্টিকোণের প্রেক্ষিতে হয়ে উঠল প্রকৃতই উত্তরাধুনিক এক কাব্যবীক্ষা। আলোচ্য গবেষণায় মণীন্দ্র গুপ্ত কীভাবে তাঁর অধুনান্তিক কাব্যভাষা গড়ে তুলেছিলেন এবং কেনই বা তাঁর কাব্যভাষাকে আধুনিকতার গণ্ডী ছাড়িয়ে অধুনান্তিকতার পথে উত্তীর্ণ বলে গবেষকের মনে হচ্ছে, তার এক যুক্তিগ্রাহ্য অনুসন্ধান থাকবে।
এই আলোচনার পরিসরে আলোচিত হবে তাঁর প্রথম থেকে শেষতম কাব্যগ্রন্থ, তাঁর কাব্যভাবনা, কবিতা সংক্রান্ত গদ্য এবং প্রবন্ধ। প্রাসঙ্গিকভাবেই, তাঁর সাক্ষাৎকারও আলোচিত হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর গদ্য থেকেও তুলে আনা হবে এই গবেষণার উপযোগী বিষয়। আমার এই গবেষণার উদ্দেশ্য মণীন্দ্র গুপ্তর এই কাব্যভুবন ও কাব্যমানচিত্রকে অনুসরণ করা। বাংলা কবিতার সরণ মণীন্দ্র গুপ্তর কাব্যভাষার হাত ধরেই আগামী কাব্যভাষায় প্রবেশ করতে চলেছে। তার বীজ এবং আলোকবর্তিকা রয়েছে মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতাতেই।
আর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, আধুনিকতার গণ্ডী ছাড়িয়ে ছয়ের দশকের কবিদের থেকে মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতার স্বর ভিন্ন, শুধু সে কথাই নয়, মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতা আগামী পাঁচ দশকের বাংলা কবিতার জগতে এক ভিন্ন স্বর আনয়ন করল।
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বা প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতার মধ্যে যে স্মার্ট নাগরিকতা এবং বিপন্ন অস্তিত্বের ভাষ্য আমরা খুঁজে পেলাম, তার একধরনের পরিবর্ধন দেখা যেতে লাগল ষাটের বা ছয়ের দশকে। আমরা পেলাম ‘বালক জানে না’-এর কবি সুব্রত চক্রবর্তীকে, পেলাম ‘ব্যান্ডমাস্টার’-এর কবি তুষার রায়কে, ‘অন্ধ স্কুলে ঘণ্টা বাজছে’-এর কবি দেবারতি মিত্রকে এবং অবশ্যই ‘শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা’র কবি ভাস্কর চক্রবর্তীকে। সঙ্গে এ কথাও মাথায় রাখতে হবে, পাঁচের দশকের কবিদের কবিতা অনেক বেশি সংহত রূপ ধারণ করল এই ছয়ের দশকেই। পাঁচের দশকের অনেকেরই প্রথম কবিতার বইও এই ছয়ের দশকেই বেরোল। ফলে, এ কথাও বলা যেতে পারে, যে ছয়ের দশক হলো পাঁচ-এর দশকের কবিদের নিজেদের ভাবনা ও কাব্যভাষা খুঁজে পাওয়ার দশক। অনেকটা আশ্চর্যরকমভাবেই, ভাস্কর চক্রবর্তী এবং তুষার রায় তাঁদের প্রথম কাব্যগ্রন্থেই খুঁজে পেয়েছিলেন এক অনন্য কাব্যভাষা। একদিকে তুষার রায়ের ব্যান্ডমাস্টারে যেমন ছিল এক নাগরিক কবির প্রবল অস্তিত্ব সংকটের ভাষ্যের সঙ্গে মৃত্যুবোধের অমোঘ মিথষ্ক্রিয়া, তেমন আরেকদিকে ভাস্করের কবিতায় ছিল জীবনানন্দ কথিত বিপন্ন বিস্ময়ের এক নাগরিক যাপনের ভাষ্য। 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা'র পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলোতে যেমন ভাস্কর অনেক বেশি তীক্ষ্ণ হয়েছেন।
কিন্তু ছয়ের দশকের এই কবিতাগুলোর বিপ্রতীপে যেন অবস্থান করছে মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতা। এর একটা কারণ কবি মণীন্দ্র গুপ্ত প্রথম থেকেই এই নাগরিক বিপন্নতার বাইরের লোক ছিলেন।
আর আরেকটা কারণ কবি মণীন্দ্র গুপ্তের ভাবনার ভিতরে কাজ করেছিল একধরনের অন্য বিপন্নতা। আর সেই বিপন্নতার নাম মৃত্যুবোধ। কিন্তু এই মৃত্যুবোধ কবি মণীন্দ্র গুপ্তকে মৃত্যুবিলাসী করে তোলেনি। বরং অনেক বেশি করে টেনে নিয়ে গেছে বাংলার স্বতন্ত্র ধারার যাপনের কাছে। মানুষের ভাবনা, চিন্তা, দর্শন, সংস্কৃতি, রীতি, আচার এবং নিজস্ব এক দর্শনের জগতে তিনি অবগাহন করেছিলেন। কবি মণীন্দ্র গুপ্তর কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয় তিনি এক পথিকের মতো, যিনি, নিখুঁতভাবে তাঁর রাস্তাটিকে লক্ষ্য করতে করতে চলেছেন। কিছুই নজর এড়াচ্ছে না তাঁর। ছোট ছোট নানা ঘটনা, রাস্তার দুধারে নানান বসতি, নানান মানুষ, তাঁদের জীবনযাত্রা দেখছেন তিনি আগ্রহভরে। কিন্তু মনের মধ্যে প্রবহমান এক কৌতুক, এক বিস্ময়। তিনি সব দেখছেন আর আকাশের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছেন। মহাকাশের অন্ধকার দিয়ে তিনি দেখছেন আলোর পৃথিবী। আর এই রোদ্দুর দিয়ে তিনি দেখছেন মহাকাশের অন্ধকার। নিজের প্রবাহকেই করে তুলছেন মহাজাগতিক। তাই তাঁর কবিতা যেমন চিরকালীন, প্রবাহমান, বা অনন্তসন্ধানী বলে সমকালীনতাকে পরিত্যাগ করে বিশুদ্ধ কবিতার দিকেই শুধু হাঁটেনি, তেমন বিশুদ্ধ কবিতাকে অস্বীকারও করেনি।
কারণ এক প্রকৃত অনুসন্ধানকারীর মতো তিনি জানেন, এই অনুসন্ধানের নানা পথ, আর কোনো পথই মিথ্যা নয়, বরং সত্যের এক একটি রূপ। তাই তাঁর কবিতায় এক সংযমী, সহিষ্ণু, স্থিতপ্রজ্ঞ ‘জেন’ অভিযাত্রীর পদশব্দ টের পাওয়া যায়। সমগ্রকে নিজের মধ্যে টের পাওয়ার, আর তাকে ছোট ছোট নানা রূপের মধ্যে আবিষ্কার করার এই যে কবিকৃতি, তা-ই হলো কবি মণীন্দ্র গুপ্তের কাব্যব্যক্তিত্ব। তার সঙ্গে মিশে যায় তাঁর অভিযাত্রা। এই অভিযাত্রা যেমন ব্যক্তিকবির নিবিড়, একাকী সংলাপের এক আত্মজৈবনিক ভাষ্য, তেমন, এক দার্শনিক মেধাবী কাটাকুটি খেলাও। মেধা, মন এবং আবেগের (যদিও সবই মেধা, তবু এখানে বুদ্ধি, আবেগ ও বোধ—এগুলোকে আলাদাভাবে দেখার কথাই ভেবেছি) এই সামগ্রিক মিলনরেখাগুলোই তাঁর কবিতার মাইলফলক।
শার্ল বোদলেয়ার কৃত অশুভ ও অমঙ্গলবোধের ধারণা, শিল্প বিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাব, বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী সমাজের ছিন্নভিন্ন অবস্থা, সাম্যবাদী ভাবনার প্রভাব, ফ্যাসিবাদী চিন্তাধারা ও তার বিরোধী শিল্পভাবনায় ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের আর্তনাদ—সমস্ত কিছু মিলিয়ে আধুনিকতা, তাঁর পূর্বজ রোমান্টিক ও আধ্যাত্মবাদের ধারণা থেকে সরে যেতে বাধ্য হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকেই। এই সময়ে যেমন ঝড়ের মতো পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যিক মানচিত্রেই এসে পড়ে শিকড়কে অস্বীকার করার প্রবণতা, তেমন শিকড়ের সঙ্গে যোগ রেখে, আবহমানের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে দৃষ্টিভঙ্গি, বলার ভঙ্গি এবং ভাষার মধ্যেই নতুনকে স্বাগত জানানোর ভাষাও সাহিত্যের ‘মডার্নিজম’-এর বা আধুনিকতাবাদের আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে। আধুনিকতাবাদের অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য হলো অস্তিত্ববাদ। অস্তিত্ববাদের হাত ধরেই সাহিত্যের উঠোনে এসে পড়ে সুররিয়ালজম বা পরাবাস্তবতা, দাদাইজম, ইম্প্রেশনিজম প্রভৃতি সাহিত্যিক এবং শিল্পের আঙ্গিক। দর্শনের দিক থেকে কমিউনিজমের প্রভাব পড়ে সর্বাত্মকভাবে। আবার কমিউনিজমের প্রভাবের পাশাপাশি পড়ে অস্তিত্ববাদের প্রভাব।
কমিউনিজমের ভাবাদর্শের সঙ্গে এক চিরাচরিত সংঘাত বাধে অস্তিত্ববাদের। কারণ কমিউনিজমের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ভাবনার কাছে ব্যক্তিগত বিষাদের চেয়ে সমষ্টিগত লড়াইয়ের প্রেক্ষিতে রচিত সাহিত্যই সাহিত্য হিসেবে গৃহীত হয় বেশি। অনেকটা এই জায়গা থেকেই আমরা যেমন অনেক মহান কবিকে, শিল্পীকে, সাহিত্যিককে পাই, তেমনই আবার অনেক মহৎ কবিতা বা সাহিত্য রচিত হয় যেগুলোর ওপর কোনো নির্দিষ্ট ভাবাদর্শের প্রভাব নেই।
আধুনিকতাবাদ বলা যেতে পারে একধরনের ইউরোসেন্ট্রিক ভাবনা। কিন্তু এই ইউরোসেন্ট্রিক ভাবনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সারা বিশ্বেই প্রভাব বিস্তার করে। বাংলা কবিতা বা সাহিত্য মাইকেলের সময় থেকেই সরে গিয়েছিল তার নিজস্ব যাত্রাপথ থেকে। বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, মঙ্গলকাব্যের যে বাংলা সাহিত্য নিজস্ব শিকড়ের থেকে ক্রমশ বনস্পতিতে পরিণত হচ্ছিল, তা তার অভিযাত্রার পথ বদল করে রেনেসাঁর সময় থেকেই। মাইকেল মধুসূদন পরবর্তী বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণই এক অন্য মানচিত্রের হদিস দেয় আমাদের।
রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অবশ্যই বাংলার পুরনো যে মানচিত্র তা প্রভাব ফেললেও, বাংলা মূল ধারার সাহিত্য এই ইউরোসেন্ট্রিক আধুনিকতাবাদকে অস্বীকার করতে পারেনি। যদিও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রোমান্টিক বা ভিক্টোরিয়ানদের প্রভাব অনেক বেশি ছিল, তিনি ইউরোপীয় আধুনিকতার অনেকের মর্মস্থলেই প্রবেশ করতে চাননি। কিন্তু বাংলা কবিতা এই আন্তর্জাতিক ফেনোমেননকে অস্বীকার করে উঠতেও পারেনি। অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নরেশ গুহ, বুদ্ধদেব বসুর হাত ধরে এই আধুনিকতাবাদ বাংলা কবিতাকে এক নতুন দিক দিতে থাকে। পাশে থেকে যান রবীন্দ্রনাথ। আর এই আধুনিকতাবাদের এক চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় জীবনানন্দ দাশের কবিতা এবং গল্প-উপন্যাসের মধ্যে। ‘আধুনিকতা’ এবং ‘আধুনিকতাবাদ’-এর মধ্যে যা পার্থক্য, তা হয়তো অনেককাল ধরেই বাংলা সাহিত্যে প্রকাশ পায়নি। কিন্তু প্রথমে জীবনানন্দ দাশ, তার পর সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁদের পর পাঁচের দশকের কবিদের মধ্য দিয়ে আধুনিকতাবাদ তার সর্বস্ব নিয়ে বাংলা কবিতাকে গ্রাস করে নিল। আধুনিকতাবাদকে ব্যবহার করা আর আধুনিকতাবাদের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়া—এই দুটি ভিন্ন বিষয়। কিন্তু এই দুই ভিন্ন বিষয়ই পাঁচ-এর দশকের পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা কবিতার ভুবনে তার ডালপালা বিস্তার করে এবং ছয়ের দশকে তুষার রায়, সুব্রত চক্রবর্তী এবং ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতার মধ্য দিয়ে তা মধ্যগগনে পৌঁছায়। মণীন্দ্র গুপ্ত তাঁর কাব্যভাষাকে ‘আধুনিকতাবাদ’ থেকে অধুনান্তিকতার পথে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা বলাবাহুল্য।
মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতা বাংলা লোকসংস্কৃতি এবং লোকায়ত সংস্কৃতিকে যেমন তুলে ধরে, তেমন ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ইতিহাসকেও তুলে ধরে। যখন নাগরিকতার চিত্রকল্প, একাকী মানুষের বিষাদ এবং প্রকৃতির সঙ্গে উচ্ছ্বসিত যাপনের এক ধারাবাহিক লেখার পৃথিবী ক্রমশ ছড়িয়ে যাচ্ছে বাংলা কবিতায়, তিনি একটু অন্য পথে হাঁটা শুরু করলেন। বাংলার দেশজ চিত্রকল্পের কাছে ফিরে গেলেন। ফিরে গেলেন মানুষের কাছে। মানুষের কথ্যভাষায় ব্যবহৃত নানা ঘটনা, লোককথা, লোকসংস্কৃতি, প্রবাদ, ধর্মীয় বিশ্বাস, টোটেম, আর এ সমস্ত কিছুর অনাবিল শব্দভাণ্ডার তাঁর জীবনকে এবং কাব্যভাষাকে গড়ে তুলল। তিনি অন্বেষণ করতে লাগলেন এমন সব শব্দের, এমন সব চিত্রকল্পের, যা আবহমান কাল ধরে বাংলার সংস্কৃতিকে পুষ্ট করেছে। সেই সব শিকড়ভেজা শব্দগুলোকে তিনি নতুন করে প্রাণ দিলেন তাঁর কবিতায়। কিন্তু এই প্রাণপ্রতিষ্ঠা পুরনোর কাছে ফিরে যাওয়া হলো না। বরং পুরনোকে, শিকড়কে নতুন ভাষার, নতুন ব্যাখ্যার এবং নতুন দৃষ্টিকোণের প্রেক্ষিতে হয়ে উঠল প্রকৃতই উত্তরাধুনিক এক কাব্যবীক্ষা।
সহায়ক গ্রন্থ এবং পত্রপত্রিকা
১. কবিতাসমগ্র, মণীন্দ্র গুপ্ত, আদম, প্রথম প্রকাশ- ২০১৭
২. গদ্যসমগ্র, মণীন্দ্র গুপ্ত, আদম, প্রথম প্রকাশ ২০১৭
৩. মণীন্দ্র গুপ্ত স্মরণ সংখ্যা, স্বকাল পত্রিকা, সম্পাদক : প্রকাশ দাশ, পানাগড়, বর্ধমান, ২০১৮
৪. মণীন্দ্র গুপ্ত স্মরণ সংখ্যা, আদম পত্রিকা, সম্পাদক গৌতম মণ্ডল, কৃষ্ণনগর, ২০১৮
৫. কৃত্তিবাস পত্রিকা, মার্চ-জুন সংখ্যা, সম্পাদক স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১৮
৬. হাওয়া ৪৯, আলোচনা সংখ্যা, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬
৭. অনুবর্তন পত্রিকা, ফাল্গুন সংখ্যা, সম্পাদনা : অনির্বাণ ধরিত্রীপুত্র, গৌতম বসু, কলকাতা, ১৯৯৭
৮. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, ২০১৪
৯. শিল্পিত স্বভাব, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রতিভাস প্রকাশনা, কলকাতা, ১৯৭৮
১০. আধুনিক বাংলা কবিতা, বুদ্ধদেব বসু, কবিতাভবন, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৪
১১. Sacred Wood, T.S. Eliot, Penguine Edition, 1994
১২. ঐতিহ্যের বিস্তার, শঙ্খ ঘোষ, দে’জ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫
১৩. আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, আবু সয়ীদ আয়ুব, করুণা প্রকাশনী, ১৯৫৫
১৪. Rhetoric of Images, Barthnes Rolland, Penguine, 1996
১৫. কবিতার কথা, জীবনানন্দ দাশ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৯৫২
বেবী সাউ কবি, গবেষক, অনুবাদক, ছোটগল্পকার এবং প্রাবন্ধিক। বাংলা, ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি স্কলার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা বাংলা আকাদেমি পুরস্কার-সহ বিভিন্ন পুরস্কারে পুরস্কৃত। তিনি ভারতের জামশেদপুর থাকেন।