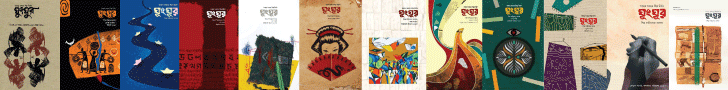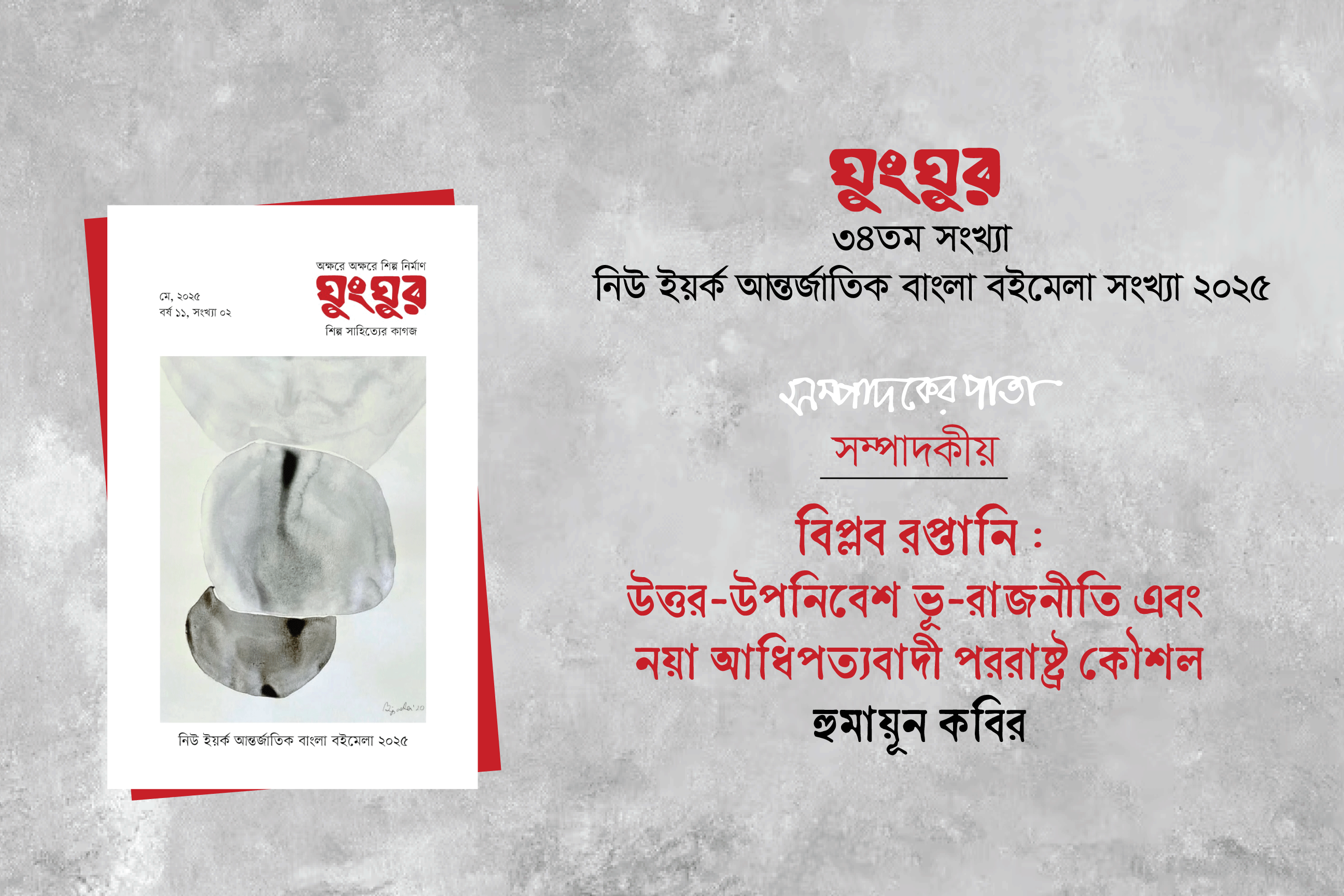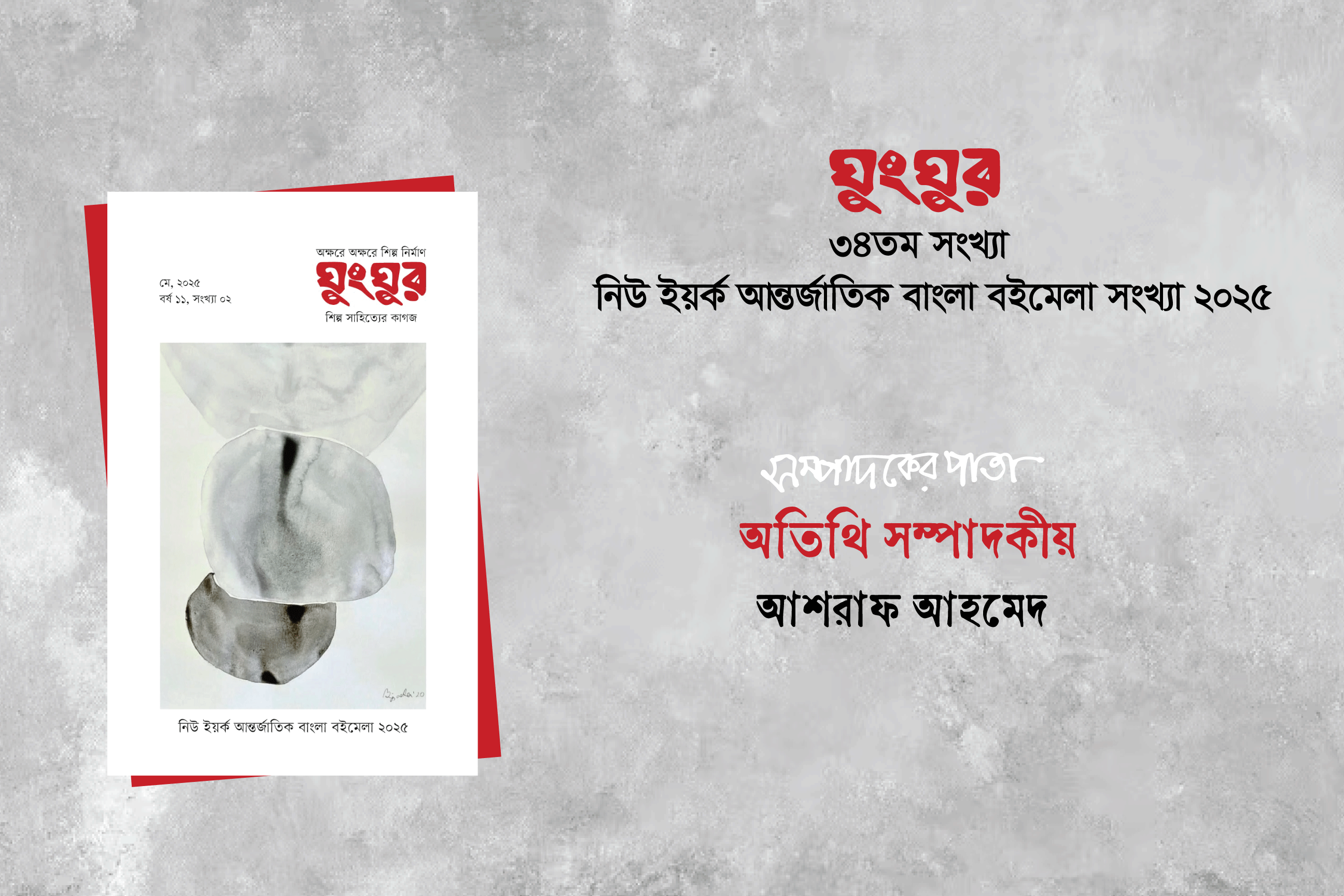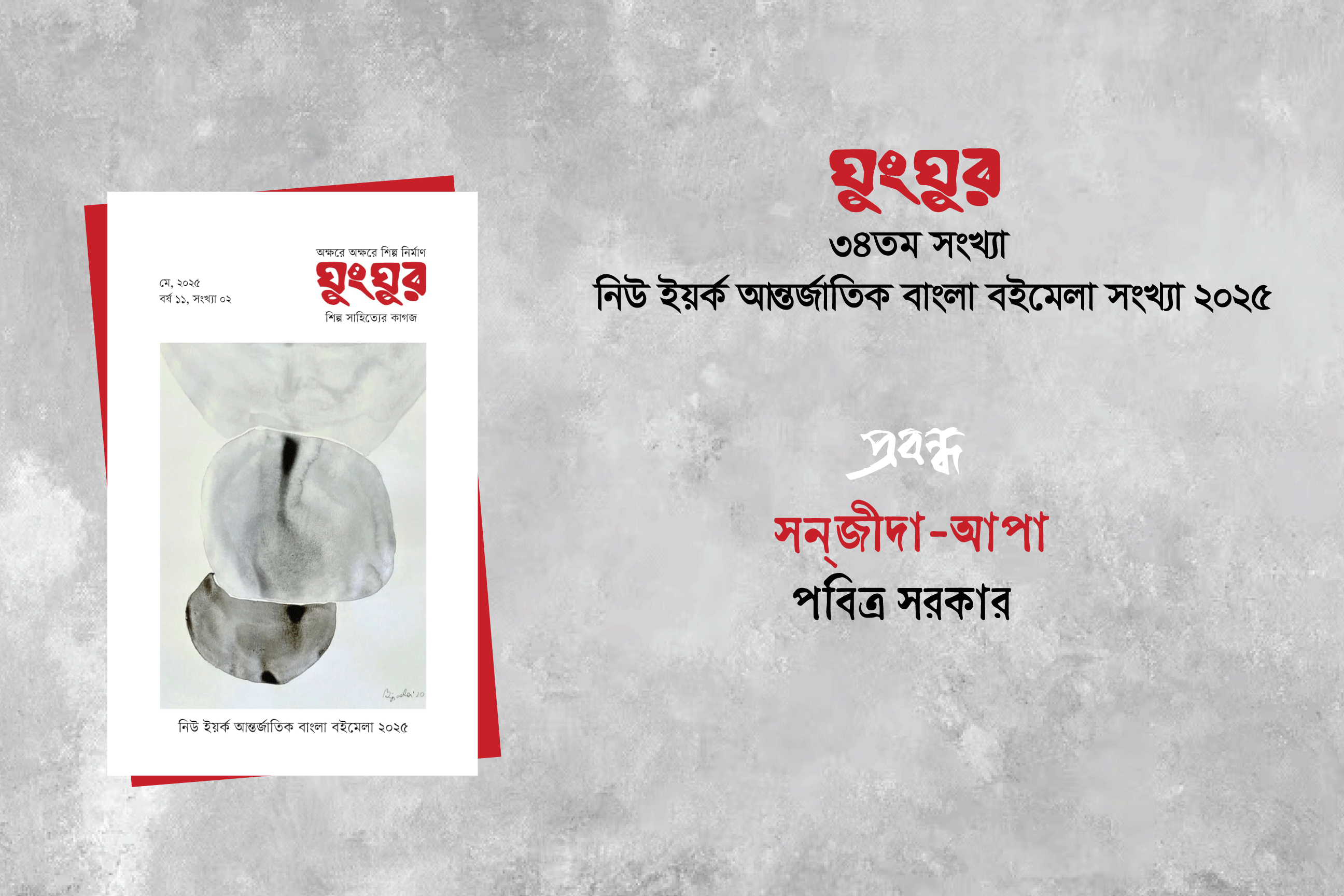জীবনানন্দ দাশ, অন্য রকম বিস্ময়
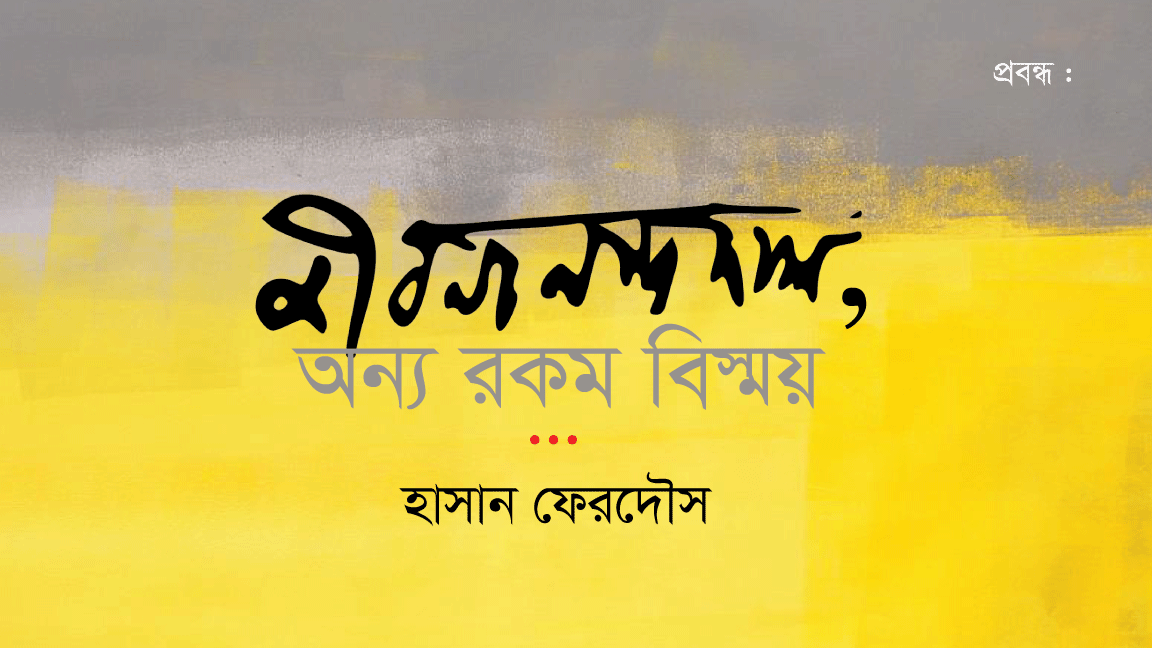
শাহাদুজ্জামানকে ধন্যবাদ, তাঁর ‘একজন কমলালেবু’ গ্রন্থটি (প্রথমা, ঢাকা ২০১৭) পড়ার পর বাংলা ভাষার সবচেয়ে জটিল ও অগম্য এক কবির কবিতার অনেক দূরায়ত গ্রন্থিগুলো খুলে গেল। এই গ্রন্থি-উন্মোচনের সূত্র যত না তাঁর কবিতার অন্তঃসলিল কাব্যধারার অর্থোদ্ধার, তারচেয়ে অনেক বেশি এই নির্জন ও একাকী মানুষটির জীবনের ভেতর-পর্দা খুলে দেখা। ঠিক এই কাজটিই করেছেন শাহাদুজ্জামান। জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় কথা বলেছেন সঙ্কেতে, খোলা চোখে সে সঙ্কেত প্রায়শ আমাদের আয়ত্বের বাইরে রয়ে গেছে। শাহাদুজ্জামান যেন এক রহস্যভেদী, কবির জীবনের গল্পের সাথে কবিতার সে সঙ্কেত মিলিয়ে আমাদের কাছে একই সাথে কবিতা ও কবিকে নিকটতর করেছেন। বাংলা ভাষায় এর আগে এমন বই লেখা হয়নি।
শুরুতে একটি প্রয়োজনীয় বিতর্ক সেরে নিতে চাই। শাহাদুজ্জামান বইটিকে উপন্যাস বলেছেন। আমার তাতে আপত্তি, এটি পড়তে উপন্যাসের স্বাদ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেটি শাহাদুজ্জামানের রচনা শৈলীর গুণে। গঠনগতভাবে ‘একজন কমলালেবু’ উপন্যাস নয়, এটি একটি সাহিত্য-চরিত, ইংরেজিতে লিটারেরি বায়োগ্রাফি। এই দুইয়ের তফাৎ নির্দেশ করা অপ্রাসঙ্গিক নয়, অতএব সেকথা থেকেই আলোচনা শুরু করা যাক।
কথাসাহিত্য বা ফিকশনের শুরু কোথায়, সে প্রসঙ্গে গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ একসময় মন্তব্য করেছিলেন, তিনদিন পর ঘরে ফিরে জোনাহ বউকে বললেন তার বিলম্বের কারণ এক তিমি মাছ তাঁকে গিলে ফেলেছিল। এই তিনদিন বাধ্য হয়ে তাঁকে তিমির পেটেই কাটাতে হয়েছে। ‘যেদিন জোনাহ বউকে এই গল্প শোনান, সেদিন থেকেই কথাসাহিত্যের শুরু।’
বাইবেলের এক পরিচিত কাহিনি নিয়ে বলা কথাটা কতটুকু মাস্টারসুলভ, কতটা পরিহাস জানি না, তবে মার্কেজের কথার মোদ্দা অর্থ, ‘ফিকশনের’ শুরু কল্পনায়, শেষও কল্পনায়। সত্য ঘটনা নিয়ে রচিত ফিকশনও আদতে কাল্পনিক। যদি শুধু সত্য ঘটনার বিবরণ প্রদানই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তিনি বড় জোর উত্তম সাংবাদিক হিসাবে আমাদের নজর কাড়বেন। অথবা পরিশ্রমী গবেষক হিসাবে আমাদের চোখে সম্মানিত হবেন। সেই একই গল্প যখন লেখকের কল্পনার গভীরতায় রঞ্জিত হয়, কাহিনির বহিরঙ ভেদ করে বর্ণিত চরিত্র সমূহের অন্তর্জগত আলোকিত হয়ে ওঠে, তা উপন্যাস হয়ে ওঠে। উভয়েরই রসদ ঘটিত বাস্তবতা, কিন্তু সালমান রুশদি যেমন বলেছেন—বাস্তব (রিয়েল অর্থে) এবং বাস্তবিক (রিয়েলিস্ট অর্থে) এক নয়। লেখকের কাজ বাস্তব উদ্ধার নয়, তার কাজ নির্মিত কাহিনিকে বাস্তবিক করে তোলা। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা জেনেছি, লেখক যে সত্য উদ্ধার করেন, কল্পিত হলেও তা সত্যের চেয়েও অধিক সত্য। একই কথা বলেছেন আলবেয়র কামু : ‘ফিকশন হচ্ছে সেই অসত্য যাকে আশ্রয় করে আমরা সত্যে পৌঁছাতে পারি।’
জীবনী গ্রন্থ বায়োগ্রাফি অর্থে কোন ব্যক্তির জীবনের নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ। এতে কল্পনার উপাদান যে থাকে না, তা নয়। তবে জীবনী লেখকের কাছে আমাদের প্রত্যাশা বস্তুনিষ্ঠতা। যে সত্য তিনি জানেন না তাকে সত্য বলে চালাবেন, এটি আমরা চাই না। আত্মজীবনীর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি লেখক নিজেই অনেক সত্য-মিথ্যা হয় যোগ করেছেন, নয়ত বিয়োগ। আত্মজীবনী হিসাবে সেটি লেখকের নিজস্ব অগ্রাধিকার, তার প্রিরোগেটিভ। আর সাহিত্যিকের জীবনী হলে তো কথাই নেই। সৈয়দ শামসুল হক এই প্রিরোগেটিভকে এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন যে নিজের আত্মজীবনী অথবা স্মৃতিকথা—তার নামে দিয়েছেন ‘প্রণীত জীবন’। জীবন অথবা সাহিত্য চরিতের ক্ষেত্রে এই স্খলন আমরা মেনে নেব বলে মনে হয় না, যদিও তার উদাহরণ মোটেই বিরল নয়।
গ্রীক লেখক প্লূটার্ক, যাকে পৃথিবীর প্রবীনতম জীবনীকার ভাবা হয়, তিনিও যে সত্যের সাথে বিস্তর কল্পনার ফানুস মিশিয়েছেন, তাঁর বিখ্যাত ‘জীবন সমূহ’ (ইংরেজিতে ‘লাইভস’) সেকথার প্রমাণ। প্লূটার্ক নিজেই স্বীকার করেছেন, তিনি জীবনী লিখছেন, ইতিহাস নয়। আর গ্রন্থবদ্ধ জীবনীসমূহ ‘বস্তুনিষ্ঠ’ করার প্রয়োজনেই তিনি কল্পনার ব্যবহার করেছেন। গ্রীক নৃপতি আলেকজান্দারের জীবনীর ভূমিকায় প্লূটার্ক জানিয়েছেন, হাজার হাজার সৈন্য নিহত হয়েছে সে কাহিনি উদ্ধারের বদলে আলেকজান্দারের কোন একটি কথা, এমনকি তাঁর একটি দীর্ঘশ্বাস মানুষটিকে জানার জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
আমার মনে হয়, পরবর্তিকালে যারা ইতিহাস-ভিত্তিক উপন্যাস লিখেছেন, প্লূটার্ক এই যুক্তিকে আদর্শ হিসাবে মেনে নিয়েছেন। যেমন; তলস্তয়ের ‘ওয়ার এন্ড পিস’। তলস্তয় ইতিহাস লেখেননি, লিখেছেন ইতিহাস-ভিত্তি করে পৃথিবীর সেরা একটি উপন্যাস। একই মাপকাঠি ব্যবহার করে বোধহয় একথা বলা যায় যে, নথি হিসাবে প্লূটার্ক জীবনীসমূহ যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, তারা মোটেই প্রামাণ্য নয়, ফলে তার ঐতিহাসিক মূল্য বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। পক্ষান্তরে, আধুনিক জীবনী গ্রন্থের প্রধান শক্তিই হল তার প্রামাণিক চরিত্র। রিচার্ডসনের লেখা তিনখণ্ডের ‘পিকাসো’ অথবা প্রশান্ত পালের নয় খণ্ডের অসমাপ্ত ‘রবি জীবনী’ তাই অনায়াসে প্রামাণিক ইতিহাসের মর্যাদা বহন করে। প্রতিটি তথ্যের, এমনকি প্রতিটি উদ্ধৃতির সূত্র তাঁরা চিহ্নিত করেছেন। কল্পনার ব্যবহার যে নেই তা নয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে ফর্মটি তাঁরা অনুসরণ করেছেন, তার প্রয়োজনেই কল্পনার মইটুকু তাঁরা মাঝেমধ্যে ধার করেছেন। সত্যি বলতে কি, প্রশান্ত পাল তেমন ধার গ্রহণের প্রয়োজনও বোধ করেননি।
একথার অর্থ এই নয় ‘জীবনী’ গ্রন্থ হিসাবে নন্দিত হলেই তাকে নির্ভেজাল সত্য বলে মেনে নিতে হবে। প্রকৃত ইতিহাস যেমন প্রকৃত সত্যের অবিকৃত উদ্ধার নয়, জীবনীও উদ্ধারকৃত জীবনের সকল অধ্যায়ের বিবরণ নয়। ইতিহাসবিদ যেমন, জীবনীকারও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, ভালো-মন্দের ধারণা ও প্রয়োজন—অপ্রয়োজন দ্বারাই পরিচালিত হন। সত্য উদ্ধার লক্ষ্য হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তারা দুজনেই ইতিহাসকে বিকৃত করেন—কখনো কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে, কখনো বা অজ্ঞাতসারে। জেমস বসওয়েলের লেখা স্যামুয়েল জনসনের জীবনী, অনেকের বিবেচনায়, প্রথম আধুনিক জীবনী গ্রন্থ। বসওয়েল জনসনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, ফলে আঠারো শতকের এই প্রধান লেখকের জীবনের অনেক তথ্যই তিনি জানতেন। এই জ্ঞান বইটির গুরুত্ব নির্মাণে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু তাদের বন্ধুত্ব বইটিকে কণ্টকিতও করেছে। এখন আমরা জানি, নিজের বন্ধুর প্রতি আনুগত্য স্বরূপ বসওয়েল শুধু সেইসব তথ্য গ্রন্থভুক্ত করেছে যা তাঁর বিবেচনায় জনসনকে মহান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবে। বসওয়েল জনসনের সাথে তাঁর বন্ধুত্বকে সাহিত্যিক হিসাবে নিজের স্বীকৃতি আদায়ে ব্যবহার করেছিলেন, এমন অভিযোগও রয়েছে। সত্যের সাথে কল্পনার দূষণ ও তথ্যের নির্বাচিত ব্যবহারের কারণে পরবর্তি কালে একজন মার্কিন লেখক সকল জীবনীকারকে ‘স্কাউন্ড্রেল’ নামে এককথায় বাতিল করেছিলেন।
সাহিত্য-চরিত উপরিউক্ত দুই সাহিত্য-ধারা থেকে পুরোপুরি স্বতন্ত্র, এমন কথা বলি না। সাহিত্য-চরিত অনিবার্যভাবেই কোন সাহিত্যিকের জীবনী। সাহিত্য চরিতকারের লক্ষ্য একদিকে তার অবলোকিত লেখকের জীবন কাহিনি নির্মাণ, যে কাজে তিনি যাপিত জীবনের প্রামাণিক তথ্যসমূহ অন্য সকল জীবনীকারের মতই যথাসম্ভব বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবহার করেন। কিন্তু তার কাজ সেখানে থেমে থাকে না। ব্যবহারিক তথ্যের পাশাপাশি সেই লেখকের রচিত সাহিত্যকেও তিনি ব্যবহার করেন তাঁর অপ্রকাশিত-অনালোকিত অন্তর্জীবনের ওপর টর্চ বাতিটি মেলে ধরার জন্য। অন্যকথায়, একই সাথে দুটি রচনা-ধারা অনুসরণ করতে হয় সাহিত্য চরিতকারকে—মাইকেল বেনটন যাকে বলেছেন লাইফ ন্যারেটিভ ও লিটারেরি ন্যারেটিভ। এই দুই সমান্তরাল রচনা ধারার কারণে কেউ কেউ সাহিত্য-চরিতকে উপন্যাস ও প্রামাণিক জীবনীর মাঝামাঝি—হাইব্রিড—একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই দুইয়ের মিশ্রণের ফলে আমরা একদিকে লেখকের জীবনী পাই, সাথে পাই তার সাহিত্য। ধরা যাক শেক্সপীয়রের সাহিত্য জীবনীর কথা। পৃথিবী সেরা এই নাট্যকারের জীবনের অনেক তথ্যই ধোঁয়াটে। আধুনিক জীবনীকারেরা সেই অভাবটুকু পূরণের জন্য তথ্যানুসন্ধান করেন তাঁর রচিত সাহিত্যে। বলা হয়, সব লেখকই বস্তুত একটি গল্প বা কবিতা লেখারই চেষ্টা করেন, যা তার নিজের গল্প। খোলা চোখে সে ধাঁধা উদ্ধার সম্ভব হয় না, সেজন্য প্রয়োজন পড়ে একজন সাহিত্য-রহস্য সন্ধানীর। জনাথন বেইটের ‘দি জিনিয়াস অফ সেক্সপীয়র’ যেমন। যে উপমা বা রূপক সেক্সপীয়র ব্যবহার করেছেন, বেইট আমাদের ধরিয়ে দিয়েছেন কিভাবে সেখানেই ধরা রয়েছে এই নাট্যকারের নিজের জীবনের মন্ত্রগুপ্তি।
সাহিত্য চরিত বিষয়ে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আমাদের জীবনী ও জীবন অভিন্ন নয়, এই কথাটা মাথায় রাখা জরুরি। উদাহরণত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘প্রথম আলো’ কোন জীবনী গ্রন্থ নয়, কিন্তু এখানে রবীন্দ্রনাথের জীবন অনুসরণ করে এই মানুষটিকে উদ্ধারের সচেতন একটি প্রচেষ্টা রয়েছে। এই গ্রন্থ রচনায় সুনীল তথ্যের লক্ষ্যণীয় বিকৃতি না ঘটিয়ে মানুষ রবীন্দ্রনাথের মনোজগত নির্মাণ করেছেন। এই নির্মাণে তিনি পুরোপুরি নির্ভর করেছেন কল্পনার ওপর। সে কারণে এটি একটি উপন্যাস, একে কেউ জীবন-চরিত বলে না। এখানে রবীন্দ্রনাথের জীবন রয়েছে, তার জীবনী নয়।
আগেই বলেছি সাহিত্য চরিতকার নিজের কল্পনার বদলে অবলোকিত চরিত্রের রচিত সাহিত্য কর্মকে ব্যবহার করেন, একদিকে মানুষ হিসাবে তাঁর অন্তর্জগত নির্মাণে—অন্যদিকে যাপিত জীবনের ঘটনা সমূহের আলোকে সেই লেখকের সাহিত্য কর্মের অগম্য ইঙ্গিতসমূহ বোধগম্য করাতে। বলাই বাহুল্য, কাজটি সাহিত্য-চরিতকার সম্পন্ন করেন যদৃচ্ছ বা আরবিট্রারিলি। তিনি আলোচিত লেখকের পূর্ণ জীবন অথবা সমগ্র সাহিত্য জীবন পুণঃনির্মাণ করেন না। তার কাজটিকে ইতিহাস-ভিত্তিক ঔপন্যাসিকের যদৃচ্ছ কল্পনার সাথে তুলনীয়, যদিও গুণগত ভাবে এই দুইয়ের স্পষ্ট তফাৎ রয়েছে। ঔপন্যাসিকের প্রকৃত ঘটনাবলির ওপর নিঃশর্ত বশ্যতার কোন দায়-দায়িত্ব নেই। কন্যার মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ সত্যি কি প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ছিলেন, তার অবিকল তথ্য উদ্ধারে কোন আগ্রহ তাঁর নেই, শুধু তার একটি বিশ্বাসযোগ্য পুনঃনির্মাণেই তিনি সন্তুষ্ট। কিন্তু সাহিত্য-চরিতকার যখন সেই একই মুহূর্ত নির্মাণে ব্রতী হন, প্রমাণযোগ্য রসদ হিসাবে তিনি ব্যবহার করেন সমসাময়িক সময়ে লেখকের রচিত সাহিত্য, কোন স্মৃতি তথ্য অথবা ভিন্ন কোন নথি। ডিটেকটিভের মতো তিনি সেই সাহিত্য ও নথিতে ‘ক্লু’ খোঁজেন। এই কাজের পুরোটাই চরিতকারের ব্যক্তিগত নির্বাচন—বিয়োজন দ্বারা নির্ধারিত। সেই কারণে সাহিত্য চরিতের প্রকৃত গুরুত্ব যত না তার প্রামাণিক গুরুত্বের জন্য, তারচেয়ে অনেক বেশি সাহিত্য মূল্যায়নের জন্য।
বলাই বাহুল্য, এই পদ্ধতি অনুসরণে বিপদ রয়েছে। ইতিহাসের সকল ঘটনার ও সকল ব্যক্তির ব্যাপারে আমাদের প্রত্যকের কিছু পূর্ব-নির্ধারিত ধারণা বা অনুমান কাজ করে। সাহিত্য-চরিতের ক্ষেত্রেও একথা সমান ভাবে প্রযোজ্য। সকল সাহিত্যচরিতই এক অর্থে আমাদের চোখে ‘হিরো’। তাদের ব্যাপারে সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে একধরনের আগাম ধারণা দ্বারাই আমাদের অধিকাংশ বিশ্বাস ও ব্যাখ্যা পরিচালিত হয়। সাহিত্য-চরিতকারই বা এই নিয়মের ব্যতিক্রম কেন হবেন। নিজের অনুসরিত ‘সত্য’ প্রতিষ্ঠায় তিনি সম্ভবত সে ‘সত্য’কে প্রত্যায়িত করেন, যা তার মনে আগে থেকেই স্থান করে নিয়েছে। একজন মার্কিন গবেষক এই প্রবণতার নাম দিয়েছেন ‘বায়োমিথোলজি’।
একথা বলা বাহুল্য নয় যে বাংলায় লিটারেরি বায়োগ্রাফির কোন চল নেই। প্রভাত মুখোপাধায়ের রবীন্দ্র জীবনকথা বা প্রশান্ত পালের রবি জীবনীতে রবীন্দ্রনাথের জীবনের কাহিনী হয়ত আছে, কিন্তু সেকেবল সালতামামি। জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে সেতু নির্মাণের কোন সচেতন চেষ্টা নেই। গোলাম মুরশিদ দুটি চমৎকার লিটারেরি বায়োগ্রাফি লিখেছেন—মধুসূদন ও নজরুল। উভয়ে গ্রন্থেই জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা রয়েছে। জীবনানন্দকে নিয়ে ক্লিনটন সিলির ‘এ পোয়েট অ্যাপার্ট’ এখন বাংলায় অনূদিত হয়েছে, সেটিও চমৎকার সাহিত্য জীবন। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই কাজটাকে গবেষকের প্রেষণা দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। পাঠক হিসাবে আমি সেখানে উপন্যাসের আনন্দ ও উত্তেজনা অনুভব করিনি, ঠিক যে অনুভূতি ও আনন্দ শাহাদুজ্জামানের বই পড়ে আমি পেয়েছি।
শাহাদুজ্জামানের ‘একজন কমলালেবুর’ বৈশিষ্ট্য এখানে যে তিনি যোগ্যতার সাথে জীবনী ও সাহিত্য এই দুই ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছেন। এই দুইয়ের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহারের ফলে গ্রন্থটি উপন্যাস হয়নি বটে কিন্তু উপন্যাস পড়ার স্বাদ তাতে মেলে। এই গ্রন্থের ‘মেটা ন্যারেটিভ’ নির্মাণে তিনি ঐতিহাসিক—প্রামাণিক অর্থে—তথ্যের ওপর নির্ভর করেছেন। কোথাও কোন ফুটনোট ব্যবহার করেননি সেকথা ঠিক, কিন্তু আগ্রহী পাঠকের পক্ষে ব্যবহৃত তথ্যের সূত্র উদ্ধারে সহায়ক নির্দেশিকা ঠিকই রেখে গেছেন। কিন্তু শুধু সন-তারিখ মিলিয়ে জীবনী নির্মাণ করলে জীবনানন্দকে বোঝা যাবে না, যে কবিতা তিনি লিখেছেন তার পেছনে যে অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাস রয়েছে, সেটি জানাও প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাতে শাহাদুজ্জামান আশ্রয় নিয়েছেন তিন ধরনের ‘ক্লু’র—কবির ব্যক্তিগত ডায়েরি, চিঠি ও অপ্রকাশিত গল্প-উপন্যাস। প্রথম দুই ক্লু অবশ্যই প্রামাণিক, শুধু তৃতীয়টি প্রস্তাবনামূলক বা ইন্টারপ্রেটিভ।
কোন কবি অথবা ঔপন্যাসিককে নিজের কথা বলতে কেন ইঙ্গিতের আশ্রয় নিতে হয়? প্রথমত, এটি শিল্প হিসাবে সাহিত্যের চরিত্র, সে একটি আড়াল চায়। অন্য কারণ, কবি অথবা লেখক নিজেই নিজেকে আবৃত রাখতে চান। নিজের অপূর্ণতা, ব্যর্থতা ও পরাজয়-গ্লানি তাকে অবশ্যই আক্রান্ত করে, সে গ্লানির কথা উচ্চ স্বরে বলার মতো নয়। তাই তাকে এক ধরনের চাতুরির আশ্রয় নিতে হয়। এই যে সাহিত্যের ধাঁধাঁ, পাঠকের সাথে সে কাজটুকু লেখক অনেক সময় করেন সচেতন ভাবে, কখনো বা অবচেতন ভাবে। জীবন ও সাহিত্যকে সমান্তরালভাবে অনুসরণের মাধ্যমে যে জীবন চরিত শাহাদুজ্জামান পুনঃনির্মাণ করেছেন তাতে এই চেতন-অবচেতনার দূরত্ব কিছুটা হলেও ঘুচেছে।
দুই
জীবনানন্দ দাশকে আমরা কবি হিসাবেই চিনি, যদিও তাঁর মৃত্যুর পর উদ্ধারকৃত খসড়া থেকে আমরা জানি তাঁর অপ্রকাশিত গল্প-উপন্যাসের সংখ্যাও বিপুল। উভয়ক্ষেত্রেই তিনি রয়ে গেছেন ভীষণ রকম ‘ব্যক্তিগত’। তাঁর রচনার কোন ‘পাবলিক ভয়েস’ যে নেই তা নয়, প্রথম দিকের অনেক কবিতাতেই দেশ-সমাজ-সংসার নিয়ে তাঁর উদ্বেগ ও উত্তেজনার প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু কবি হিসাবে সেসবের জন্য কেউ আমরা জীবনানন্দকে চিহ্নিত করি না। আমাদের কাছে তিনি পরিচিত সেই বিপন্ন বিস্ময়ের কবি হিসাবে, যার পরিচয় সর্বদা সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের কাছে ধরা পড়ে না, অথচ যার অধরা তন্ময়তা আমাদের নিরন্তর বিদীর্ণ করে। কেমন ছিলেন জীবনানন্দ, কবিতার জগতেই বা কিভাবে এলেন, গ্রন্থের শুরুতেই এই প্রচ্ছন্ন প্রশ্নের উত্তরে শাহাদুজ্জামান জানাচ্ছেন, শৈশবে জীবনানন্দের অবলম্বন ছিল মা কুসুমকুমারী। মায়ের উৎসাহে স্কুলের খাতায় কবিতা লিখলেও কবিতার আসল সিন্দাবাদ তার ঘাড়ে চেপেছে অনেক পরে। ‘কুসুমকুমারীই তাকে হাঁস মায়ের মতো ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসিয়ে দিয়েছেন কবিতার হাংড়ভরা সমুদ্রের পথে।’ কবিতার পথ যে একটি অন্বেষণ—একটি দীর্ঘ যাত্রা—এবং সে যাত্রা খুব কুসুমাস্তির্ণ নয়, গোড়াতেই লেখক আমাদের সেকথা জানিয়ে দেন।
একথা এখন আর কোন গোপন রহস্য নয় যে জীবনানন্দের ব্যক্তিগত জীবন ছিল নানা ব্যর্থতায় ও হতাশায় আকীর্ণ। এই জীবনের দুটি দিক—কামহীনতা ও প্রেমহীনতা। প্রথম জীবনে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া শোভনা—যার ডাক নাম বেবি—তার সাথে একতরফা প্রেমে জড়িয়ে পড়েছিলেন জীবনানন্দ। তাকে জীবনে পাননি, কিন্তু মনের ভেতর অহোরাত্রি লালন করেছেন। অন্যদিকে কলেজ পড়ুয়া তরুণী লাবণ্যের সাথে পারিবারিক যোগাযোগে জীবনানন্দের যে বিয়ে তা মধুর হয়নি। বিয়ের পরপরই জীবনানন্দ তার কলেজের চাকরিটি হারিয়ে ফেলেন। তিনি খাদে পড়ে যান। অসন্তুষ্ট স্ত্রীর সাথে তার বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। সহবাসও কার্যত বন্ধ। এই অবস্থায় তার লেখা গল্প ‘আঘ্রাণের শীত’। এক ব্যর্থ বেকার স্বামী ও তার অসহিষ্ণু স্ত্রীর গল্প। এই গল্পের অর্থ শাহাদুজ্জামান আমাদের ধরিয়ে দিচ্ছেন এই ভাবে :
‘জীবনানন্দ গল্পে লিখেছেন গ্রামে ফিরে শস্য খেতে উজ্জ্বল রোদে মৌমাছিদের দেখার অভিজ্ঞতার কথা। প্রশ্ন করেছেন, তাদের উজ্জ্বল চঞ্চল জীবন সত্যি না মুখোস, কারণ তিনি তো দেখেছেন মৌমাছিকে দাঁড়কাকে ঠুকরে খাচ্ছে। জীবনানন্দ জানিয়ে দিচ্ছেন জীবনের বাঁকে বাঁকে লুকিয়ে থাকা বীভৎসতা, নির্মমতার খোঁজ তিনি পেয়েছেন। পতঙ্গের জীবনের আনন্দকেও তিনি সন্দেহ করছেন, তার মনে হচ্ছে এসবই মুখোস। জীবন জগত সবকিছুর মধ্যেই একটা গভীর অসহায়ত্ব আছে, আছে আশ্রয়হীনতা।’
এই রকম উদাহরণ পুরো বইটিতে অসংখ্য। কবিতার কোমল ও নির্জন বহিরাবরণে যে সত্য আমরা উদ্ধারে ব্যর্থ হই, গল্প-উপন্যাসের উদাহরণে শাহাদুজ্জামানের ব্যাখ্যা তা আমাদের উপলব্ধির নিকটতর করে।
জীবনানন্দের ব্যক্তিগত চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট, শাহাদুজ্জামানের বিবরণ পড়ার পর আমার মনে হয়েছে, তিনি যুবা বয়স থেকেই যৌন তাড়িত ছিলেন, ইংরেজিতে যাকে বলে সেক্সুয়ালি রিপ্রেসড। তাঁর কবিতার ও গল্প-উপন্যাসের একটা প্রধান ভাব বিষয় পুরুষের প্রেমহীনতা। এর সাথে যুক্ত করুন কামহীনতা। এই দুই ভা-ারই যখন শুকিয়ে যায়, কি থাকে পুরুষের জীবনে? জীবনানন্দের ডায়েরিতে তার উত্তর রয়েছে। শাহাদুজ্জামান জীবনানন্দের ডায়েরি থেকে এই উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করেছেন : back aching after much night through corruption, so a morning. শাহাদুজ্জামান ধরিয়ে না দিলে আমরা হয়ত বুঝতেই পারতাম না জীবনানন্দ ‘করাপশন’ বলতে স্বমেহনের কথা বলছেন। “স্বমেহনের যৌন আনন্দের ভেতর দিয়ে তিনি বুঝি নিজেকে ভারমুক্ত করতে চাচ্ছিলেন।”
এটি কোন বৈকল্য কিনা জানি না, সে বিতর্ক এখানে অর্থহীন, তবে জীবনানন্দের কবিতায় যে অস্থিরচিত্তের ছায়া ধরা পড়ে, কখনো কখনো তা বৈকল্যের পর্যায়ে পড়ে। উদাহরণ হিসাবে ‘ক্যাম্পে’ কবিতাটি বিবেচনা করা যাক। এই কবিতাটি জীবনানন্দের সেরা কবিতার অন্তর্গত, কি তার অর্থ তা নিয়ে আমরা এখনো বিতর্ক করি। শাহাদুজ্জামান এই বিতর্ক থেকে তর্ককে ছেটে ফেলেছেন। প্রায় স্কুল শিক্ষকের মতো এই দুই কবিতার গোপন সুড়ং পথে আমাদের ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন তার অন্তর্চরিত্র। একটি শিকারের গল্প, যেখানে ঘাই হরিণী একটি টোপ, যাকে ব্যবহার করে শিকারী পুরুষ-হরিণকে ডেকে আনে। প্রেম ও কামের প্রাবল্যে ছুটে আসে যে হরিণ, সে নিহত হয় শিকারীর গুলিতে। এই গল্প কি জীবনানন্দের নিজের জীবনের? শাহাদুজ্জামান প্রশ্নের আকারে এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।
“জীবনানন্দের জীবনে ঘাই হরিণী নামক টোপ তাহলে কোনটি? শোভনার প্রেম, লাবণ্যের রূপ নাকি কবিতা ও সাহিত্য সৃষ্টির ইচ্ছা? সেসব হরিণীর ডাকে বাস্তবে কোন চিতাবাঘের ভয় না করে তিনি ছুটে গেছেন সেই দিকে, তারপর কোথাকার কোন অদৃশ্য শিকারি তাকে পরিণত করেছে এক বেকার, চালচুলাহীন, অকর্মণ্য মেসবাসীতে।”
বাঙালির কাছে জীবনানন্দ সবচেয়ে পরিচিত তাঁর রূপসী বাংলা পর্যায়ের কবিতা গুলোর জন্য। বিস্ময়ের কথা, এই কবিতা গুলো, যা তার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি, এমন এক সময়ে লেখা যখন কবি বেকার, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে দূরে কোলকাতায়। কিভাবে সম্ভব এমন দুর্যোগময় সময়ে রূপসী বাংলার মতো পেলব, প্রায় অবাস্তব রকম সুন্দর কবিতা লিখতে? শাহদুজ্জামান তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।
“নিরালম্ব এই কোলকাতার জীবনে এ সময় হঠাৎ তার মনের আশ্রয় হয়ে উঠল বাংলার প্রকৃতি। তিনি কলকাতার মেসের ওই কংক্রিটের নিরেট বেকার জীবন থেকে মনে মনে ছুট নিয়ে হাজির হলে তার আজন্ম চেনা নিমপাখি, বইচি, জলাঙ্গির দেশে। প্রকৃতির ভেতর তিনি যেন খুঁজে পেলেন বেঁচে উঠবার, বেঁচে থাকবার নতুন প্রেরণা।”
রূপসী বাংলা পর্যায়ের এই কবিতাগুলি অবশ্য ভিন্ন অর্থ নিয়ে আমার কাছে হাজির হয়। আমার বিবেচনায় জীবনানন্দ প্রকৃতিকে গ্রহণ করেছেন নারী হিসাবে। আমরা জানি—শাহাদুজ্জমান সেকথার বিস্তর উদাহরণ দিয়েছেন—তাঁর মধ্যে নারী ও তার দেহে আত্মসমর্পনের গভীর বাসনা ও বশ্যতা কাজ করত। জীবনে সর্বদা সে সুযোগ ঘটেনি, কবিতায় প্রকৃতির শরীরে সে আত্মসমর্পণ নির্মাণ করলেন। রোমান্টিক পিরিয়ডের অধিকাংশ কবি, যেমন কিটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও বায়রন, তাদের কবিতায় নারী ও প্রকৃতি সমার্থক হয়ে এসেছে। সাহিত্য বোদ্ধারা একে বলেছেন প্রকৃতির ‘ফেমিনাইজেশন। ‘রূপসী বাংলা’য় জীবনানন্দ সেই ধারাটিকেই আরো খানিকটা সম্প্রসারিত করলেন।
বিষয়টিকে আরো খানিকটা ভেঙে দেখা যাক। জীবনানন্দের কবিতার কেন্দ্রে রয়েছে প্রকৃতি, একথা আমরা অনেকেই বলি। এমনকি বুদ্ধদেবের মতো শিক্ষক কবিও জীবনানন্দকে প্রকৃতির কবি বলেছেন। আমি বলতে চাই, প্রকৃতি নয়, জীবনানন্দের কবিতার প্রধান বিষয় নারী—অথবা আরো স্পষ্ট করে বলি, নারীর শরীর। তিনি কেবল প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন সে শরীরের নিষিদ্ধ উত্তেজনা নিজ মনোজগতে পুনঃনির্মাণ করতে। আর এই প্রক্রিয়াটি তিনি আহরণ করেছেন ইউরোপীয় রোমান্টিক ধারা থেকে।
শুরু থেকেই জীবনানন্দের কবিতার কেন্দ্রে ‘আমি’। অর্থাৎ ব্যক্তি। আমাদের কবিতার যে সামাজিক স্বরের সাথে আমরা পরিচিত, তাতে এই আত্ম-নিমগ্নতা নতুন। ইউরোপীয় কবিতায় নয়। উনিশ শতকের শিল্প বিপ্লবের পর যে আধুনিকতার উদ্ভব, তার দুটি প্রকাশ—এক নগরায়ন, দুই আত্মকেন্দ্রীকতা, যা প্রায়শই ব্যক্তি-বিচ্ছিন্নতায় পর্যবসিত হয়। মানুষ যত নাগরিক হয়েছে, ততই সে আত্মকেন্দ্রীক, নির্জন ও জনবিচ্ছিন্ন হয়েছে। ঠিক যেমন জীবনানন্দ, যার কাব্য ভাবনার দুই প্রধান প্রেরণা রোমান্টিক যুগের কিটস ও সিম্বোলিস্ট আন্দোলনের প্রধান পুরুষ ইয়েটস। জীবনানন্দের কবিতার প্রকৃতি-প্রেম, যাকে আমরা ইন্দ্রীয় জিগীষা নামে অভিহিত করতে পারি, তা তিনি আহরণ করেছিলেন এই দুই কাব্যধারা থেকে। তাঁর ইউরোপীয় পূর্বসূরিদের মতো জীবনানন্দও প্রকৃতিকে নির্ভর করেছেন নিজের মনোচেতনার বর্ণনায়, যার কিছুটা আরোপিত, কিছুটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ধূসর, বিবর্ণ ও ঝরে পড়া পাতা অথবা পালক, এসব প্রকৃতি থেকে আহরিত, অথচ তার ব্যবহার হয়েছে কবির নিজের জীবন ও মনোজগত—বর্ণনায়, সেই মনোচেতনার মানচিত্র নির্মাণে।
তোমারি নিজের ঘরে চলে যাও, বলিল নক্ষত্র চুপে হেসে
অথবা ঘাসের পরে শুয়ে থাকো আমার মুখের রূপ ঠায় ভালবেসে।
(নিরালোকে)
এর সাথে তুলনা করুন ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই কথাগুলো :
Nature never did betray
The heart that loved her.
নারীকেই তিনি স্পর্শ করতে চান কিন্তু সে নারী অধরা। অগত্যা তাকে আশ্রয় করতে হয় প্রকৃতিকে যার ভেতর তিনি নারী দেহের কোমল সোঁদা গন্ধ খুঁজে পান। প্রকৃতি তাকে প্রত্যাখান করে না, আশ্রয় দেয়।
পৃথিবীর বেদনার মত ম্লান দাঁড়ালাম
হাতে মৃত সূর্যের শিখা
প্রেমের খাবার হাতে ডাকিলাম
অঘ্রাণের মাঠের মৃত্তিকা
হয়ে গেল
নাই জ্যোৎস্না—নাই মল্লিকা।
(মনোবীজ)
কি প্রবল বুভুক্ষা নিয়ে জীবনানন্দ নারীর শরীর স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন, শাহাদুজ্জামান তার প্রমাণ হিসাবে ডায়েরি ও গল্প-উপন্যাসের একাধিক উদাহরণ আমাদের দিয়েছেন সেকথা আগেই বলেছি। কবিতায় সে ক্ষুধার প্রকাশ ঘটেছে অতি সংগোপনে, বহুস্তর বিশিষ্ট ইঙ্গিতময়তায়। ডায়েরি তার ‘অলটার ইগো’, এখানে তিনি নিজের সাথে নিজে কথা বলেন। গল্প-উপন্যাস, যা তিনি চক্ষুর আড়ালে রেখেছেন বরাবর, সেখানেও ইঙ্গিতের আশ্রয় নেবার কোন প্রয়োজন নেই। কেউ কখনো এই লেখা পড়বে, এমন একটি গোপন বাসনা তিনি নিশ্চয় লালন করেছেন, অন্যথায় দেশভাগের সময় বরিশাল থেকে তোরঙ্গ বোঝাই করে তাদের সাথে করে নিয়ে আসতেন না। কিন্তু এখন নয়, যে মনোভঙ্গ ও ক্ষুধার বিবরণ সেসব গল্প-উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন, এই মুহূর্তে তা কেবলই নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। যে অব্যাহত আততি তাকে গ্রাস করেছিল, সম্ভবত তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার এছিল এক কলা-কৌশল, ডিফেন্স মেকানিজম। শাহদুজ্জামান বলেছেন, গল্পগুলো যেন তাঁর জীবনের গোপন ডকুমেন্টেশন।
এই ডকুমেন্টশনের অংশ হিসাবেই শাহাদুজ্জামান বহুপঠিত ও আলোচিত ‘সফলতা-নিস্ফলতা’ উপন্যাসের দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন, এই উপন্যাসের অন্তর্চরিত্র নিয়ে তাঁর অভ্যাস-বিরুদ্ধ একাডেমিক আলোচনাতেও অংশ নিয়েছেন। ব্যর্থ, অসম্পূর্ণ ও আহত মানুষ হিসাবে জীবনানন্দকে বুঝতে এই উপন্যাসটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এই উপন্যাস নিয়ে কেতকী কুশারী ডাইসনের গবেষণা গ্রন্থ সেকথার প্রমাণ। তাঁর আরেকটি গল্প, সঙ্গ-নিঃসঙ্গ, যার উদাহরণ শাহাদুজ্জামান ব্যবহার করেননি, আমাদের প্রতিপাদ্য অনুধাবনে আরো অধিক অর্থপূর্ণ বলেই মনে হয়। তার কয়েকটি লাইন পড়া যাক :
‘তোমার মনে আছে কিনা জানি না, তুমি এখানে থাকিতেও আমার নিজের ঘরের ভিতর একটা জলের কলসি সব সময়েই রাখিতাম; তৃষ্ণা পাইলে নিজেই গড়াইতা নিয়া জল খাইতাম, তোমাকে কোনদিন জল ঢালিয়া দিতে অনুরোধ করি না। তুমিও অনুগ্রহ করিয়া ঢালিয়া দিয়াছ বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ইহাই আমার ভাল লাগিয়াছে। এখনো যখন মনে হয়, বুঝিতে পারি, তোমার সঙ্গ আমাকে গভীর নিঃসঙ্গতার নিস্তার দিয়াছিল। সেই নিস্তারের পথে এখনো চলিতেছি। চিরকালই চলিব। ... অবিশ্যি, আট বছর আগে আমার অন্য ধারণা ছিল। তখনো আমি বিবাহ করি নাই। মনে হইত বধূকে দিয়া পা টিপাইয়া লইব, কপালে চুল বিলাইয়া দিবে সে, পাখা দিয়া বাতাস করিবে। আরো কতকি। কিন্তু তুমি যখন আসিলে, দেখিলাম এসব কিছুই করিলে না তুমি। আমিও চাহিলাম না। ধীরে ধীরে হৃদয়ের ভেতরে সাপ-খেলানো বাঁশীর সুর কেমন যেন বাজিয়া উঠিল আমার ভিতরে। বুঝিতে পারিলাম না, এই সুর কাহার নিকট হইতে আসে। দিন-রাত্রির ভিতর হইতে, গ্রামের পথের প্রান্ত হইতে, এই সুর কে পাঠায় ভাবিয়া অবাক হইতাম।’ কবি যে সারা জীবন ভালবাসার এক সাগ্রহ ও সস্নেহ হাতের অপেক্ষায় ছিলেন, এই গল্পে সে কথা স্পষ্ট। কবিতাতেও সে প্রমাণ রয়েছে, যদিও তার প্রকাশ কিছুটা ধোঁয়াটে। উদাহরণ হিসাবে ‘বনলতা সেন’ কবিতাটির কথা ভাবা যাক। এই কবিতার প্রধান সুর প্রতীক্ষার ও প্রার্থনার। ‘বলেছে সে, এতদিন কোথায় ছিলেন? পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।’ পাখীর নীড় কেন? কারণ কবি আশ্রয় খুঁজছেন—শুধু ভালবাসার প্রশ্রয় নয়, আশ্রয়ের নির্ভরতা, যার খোঁজে মনের জাহাজে তিনি সারা বিশ্ব চষে বেড়িয়েছেন। প্রতিটি পাতা, প্রতিটি পত্রকুট গভীর যতেœ আহরণ করে পাখি নির্মাণ করে তার কুটির। সেখানে কেবল আশ্রয় মেলে তাই নয়, মেলে আস্থা। মেলে ভালোবাসার চাদর।
বাস্তব জীবনে সেই ভালোবাসা বা আশ্রয় কোনটাই মেলেনি, মিলেছে এক কল্পিত বনলতা সেনে। হোক না কল্পিত, তার জন্য যে ব্যাকুলতা তা মোটেই কল্পিত নয়। এই যে আশ্রয় ও আস্থার বুভুক্ষা, তার অবশ্যইএকটি জৈব-শারীরিক চেহারা রয়েছে। জীবনানন্দের আগে বাংলা ভাষায় কেউ সেই জৈব প্রয়োজনের কথা এত কোমল ও তীব্র ভাবে প্রকাশ করেনি। এজন্য কবিকে কম ধিকৃত হতে হয়নি। ‘ক্যাম্পে’ কবিতাটির কথা ভাবুন। অবসন্ন পুরুষের শরীরে যে ঘাই হরিণীর ডাক শোনা যায়, শুধু একজন একাকী ও একাকী একজন পুরুষের পক্ষেই সম্ভব সে ডাকের অর্থ উদ্ধার। অথবা সম্ভব তার বেদনার ও নৈঃশব্দের সঙ্গে সংহতি অর্জন।
দোনলার শব্দ শুনি
ঘাইমৃগি ডেকে যায়,
হৃদয়ে ঘুম আসে নাকো একা একা শুয়ে থেকে
অন্য সকল কবিতার চেয়ে এই ‘ক্যাম্পে কবিতায়, আমার বিবেচনায়, প্রকৃত জীবনানন্দ ধরা পড়েন অনেকে বেশি প্রবলভাবে। উপেক্ষিত একাকী পুরুষ, যার হৃদয়ে ঘুম আসে নাকো একা একা শুয়ে থেকে। জীবনানন্দের ডায়েরির সূত্রে এখন আমরা বলতে পারি, জীবনানন্দ অসুখী ছিলেন, এই অসুখের একটি বড় উপসর্গ ছিল শরীরী ক্ষুধা।
তোমার শরীর
তাই নিয়ে এসেছিল একবার, তারপর মানুষের ভীড়
তারি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোনদিকে জানিনিয়া তা, হয়েছে মলিন
চক্ষু এই, ছিঁড়ে গেছি—পৃথিবীর পথে হেঁটে হেঁটে
কতদিন রাত্রি কেটে গেছে।
‘বনলতা সেন’ নিয়ে একটি বিচিত্র সমালোচনার সূত্রপাত করেছেন শাহাদুজ্জামান। কলকাতায় বেকার জীবনের এক পর্যায়ে লেখা এই কবিতাটি নিয়ে শাহাদুজ্জামান শুধু এই কথা বলেই সেরেছেন যে, পৃথিবীর নানা দিগন্ত হাজার বছর ধরে চষে বেড়ানো এক পথিক নাটোরের এক নারীর কাছে আশ্রয় পেয়েছিল, পাখির নীড় যেমন তার আশ্রয়, সে নারীর চোখ হয়ে দাঁড়ায় সেই রকম আশ্রয়।
এর বিপরীতে ক্লিন্টন সিলি শুধু কবিতার পশ্চৎপটই বিবেচনা করেননি, কবিতার গঠন ও তার শৈল্পিক কলাকৌশল নিয়েও প্রায় তিন পাতা ব্যয় করেছেন। এই ব্যাখ্যা শাহাদুজ্জামানের কাছ থেকেও প্রত্যাশিত ছিল। বিস্ময়ের কথা হল, সে আলোচনায় না গিয়ে আকবর আলী খান নামের একজন আমলার লেখার ব্যাখ্যা নিয়ে প্রায় তিন পাতা ব্যয় করেছেন তিনি। আকবর আলী খান উদ্ধার করেছেন বনলতা সেন আসলে একজন বারবনিতা, নাটোরেই তার বাস। শাহদুজ্জামান তার সেকথার অলক্ষিক সমর্থনে নানা তথ্য প্রমাণ হাজির করেছেন, কবে কখন জীবনানন্দ দাশ নিজে বেশ্যা বাড়ি গেছেন, তাঁর কোন গল্পে বেশ্যা বাড়ি যাবার অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ আছে, সেসবের অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। আমার মনে হয়েছে, এই কবিতার অন্তর্গত হীরন্ময়তা, বোধের অন্তরালে বেদনার যে নিঃসরণ, এমন একটি অর্থহীন ব্যাখ্যা হাজির করে আকবর আলী খান ও শাহাদুজ্জামান উভয়েই তাকে হরণ করেছেন। এই অধ্যায় পড়ার পর আমার মনে হয়েছে পৃথিবীর সকল আমলাদের সাহিত্য নিয়ে গ্রন্থ লেখার ওপর একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত।
সেই তুলনায় ‘আট বছর আগে’ কবিতাটি নিয়ে শাহাদুজ্জামানের আলোচনা ‘মাস্টারলি’। পাণ্ডিত্য তার লক্ষ্য নয়, এই বইয়ের কোথাও তিনি সে চেষ্টা করেননি। তাঁর লক্ষ্য কবিকে জীবনের সাথে মিলিয়ে জীবনানন্দের কবিতার মর্মার্থ উদ্ধার। ‘আট বছর আগে’ কবিতাটির কেন্দ্রে রয়েছে একটি আত্মহত্যার গল্প, কিন্তু কোন ক্রমেই আত্মহত্যার স্বপক্ষে কবিতা এটি নয়। জীবনানন্দ নিজে বলেছেন এটি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্প নয়, একটি ‘রিপ্রেজেন্টেশন’ মাত্র। কিন্তু অনুমান করা যায় গভীর বেদনাবোধে তাড়িত হয়ে আত্মহননের কথা হয়ত তিনি নিজেও ভেবেছিলেন, কিন্তু সেপথে তিনি অগ্রসর হননি। উল্টো, এই কবিতায় জীবনের পক্ষেই রায় দিয়ে গেছেন। যেন ক্লাসরুমের ছাত্রদের বুঝিয়ে বলছেন, এই ভাবে শাহাদুজ্জামান কবিতার ব্যাখ্যায় বলছেন :
আত্মহত্যা করা মানুষটাকে কবি ব্যঙ্গ করছেন, তাকে বলছেন তুমি মর্গে গিয়ে পচে মর, আমি বরং ওই অন্ধ প্যাঁচার কাছে যাই। যে কিনা অশত্থ নামের সংসার-বৃক্ষে বসে এখনো ইঁদুর খোঁজে।
এই কবিতার ব্যাখ্যা জীবনানন্দ নিজে দিয়েছেন, দিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু। একজন বিদেশি, এডয়ার্ড ডিমকও দিয়েছেন, যা এদের তুলনায় ভিন্ন। ডিমকের ভাষ্যে, জন্ম ও মৃত্যু তাৎপর্যার্থে অভিন্ন, ভারতীয় দর্শন চিন্তার এই কথাটি এক প্রতীকী আড়ালে প্রকাশ করেছেন জীবনানন্দ দাশ। এই বক্তব্যের সূত্র হিসাবে ডিমক উপনিষদের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, বাংলায় যার অর্থ দাড়ায়, আমি খাদ্য, আমি খাদ্য, আমি খাদ্যের খাদক। অন্যকথায়, যা খাদ্য সেই খাদক। ডিমকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, কবি শুধু একবার মর্গ শব্দটি ব্যবহার করেন, যা মৃত্যুর সমার্থক। অন্যথায় তার ব্যবহৃত শব্দ হল লাশকাটা ঘর। লাশকাটা ঘরে মৃত পুরুষটি অপেক্ষা করে শব ব্যবচ্ছেদের। আর সে ব্যবচ্ছেদের লক্ষ্য জীবনকে দীর্ঘায়িত করার সম্ভাবনার অন্বেষণ। ডিমক স্মরণ করেছেন, মৃত্যুর এক অর্থ অন্ধকার, কিন্তু এই অন্ধকারেই পেঁচা খুঁজে নেয় তার শিকার ইঁদুরকে, যে ইঁদুর তার জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে। অন্ধকারের কোন রঙ নেই, অথচ সেই অন্ধকারেই জোনাকি আলো ছড়ায়। তার মানে যাই জীবন, তাই মৃত্যু।
গ্রন্থের শেষাংশে শাহাদুজ্জান যত্নের সাথে জীবনানন্দের জীবনের শেষ বছর দুয়েকের বিবরণ তুলে ধরেছেন। তার কাছ থেকেই প্রথম জানলাম, ট্রামে চাপা পড়ে মৃত্যুর একটি আভাস কবি আগেই পেয়েছিলেন। দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ট্রামে এক ব্যক্তির আহত হওয়ার কথা শুনে কিছুটা উন্মত্তের মতো ছোট ভাইয়ের বাসায় হাজির হয়েছিলেন। পরপর দুই দিন। এর দুই দিন পর, ১৪ অক্টোবর ১৯৫৪ সালে নিজেই ট্রামের ক্যাচারে আটকে পড়ে আহত হলেন কবি। জীবন-মৃত্যুর সাথে লড়াই করে এক সপ্তাহ পর, ২২ অক্টোবর তিনি চলে গেলেন। আমাদের মনের প্রশ্নটি তুলে ধরেছেন শাহাদুজ্জামান : একি এক্সিডেন্ট না আত্মহত্যা?
এই গ্রন্থের সবচেয়ে সুন্দর অনুচ্ছেদ লিখিত হয়েছে গ্রন্থের প্রায় অন্তিমে, জীবনানন্দের মৃত্যুর বর্ণনায়। লজ্জা নেই বলতে, লাইন কয়েকটি পড়তে গিয়ে আমি চোখের জল সামলাতে পারিনি। শুধুমাত্র কবির জীবনের ও নিজ গ্রন্থের এই অন্তিম পর্যায়ে এসেই শাহাদুজ্জামান কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। এই ‘পোয়েটিক লাইসেন্সের’ ফলে তথ্যের কোন বড় হেরফের হয়েছে একথা মনে হয় না। বরং বাংলা ভাষার একজন প্রধান কবির অন্তিম মুহূর্তের এই বিবরণ আমাদের একটি কঠিন ও নির্জন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করায়।
“পুরো পথ ঘুরে আবার রাসবিহারীর মোড়ে এসেছেন তিনি। বালিগঞ্জ ডাউন ট্রাম একটা প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের মতো দ্রুত ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে। ট্রাম দ্রুত এগিয়ে আসছে, তিনিও এগিয়ে যাচ্ছেন।”
চমৎকার, সত্যি চমৎকার।