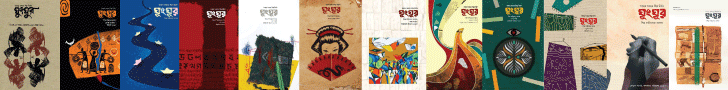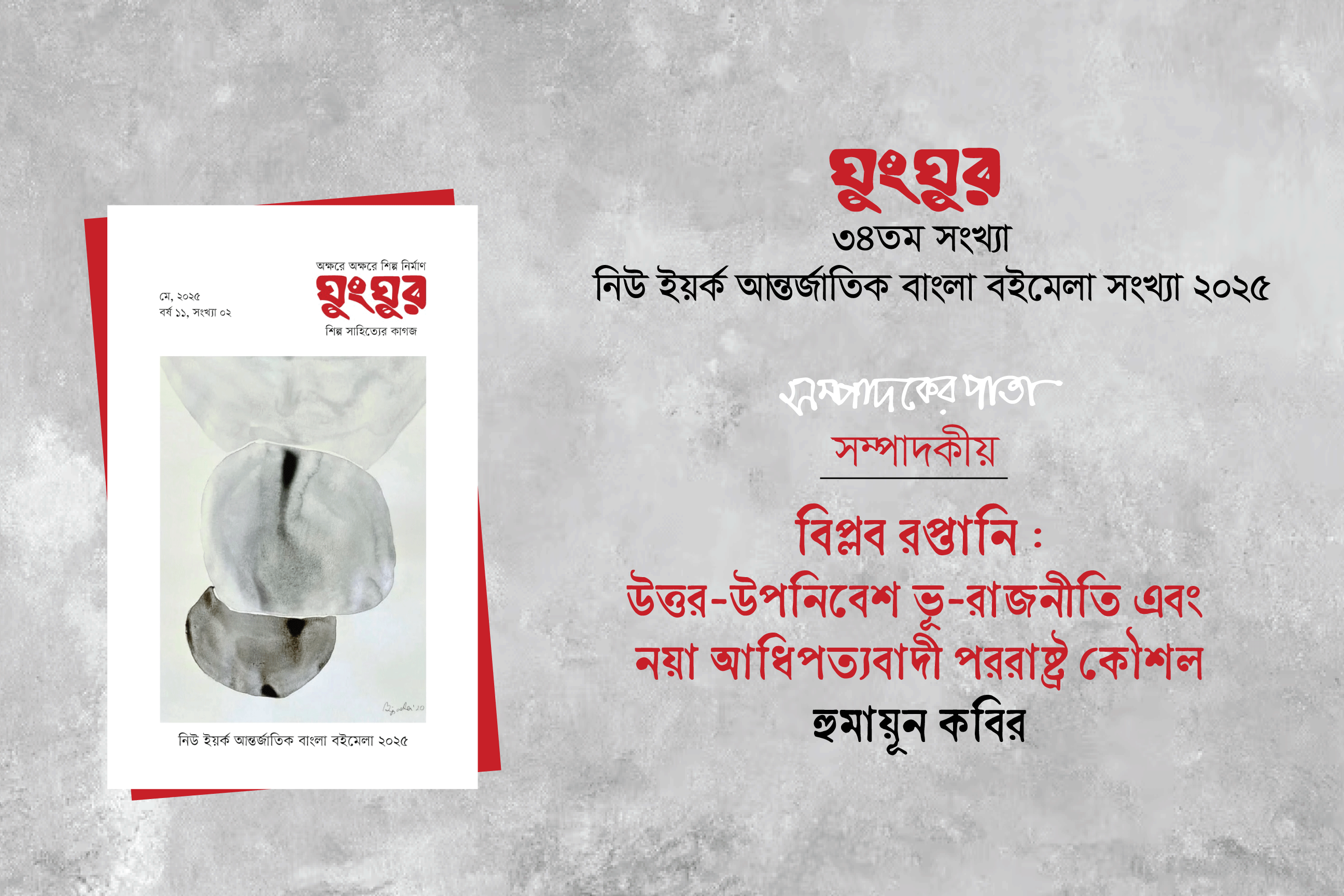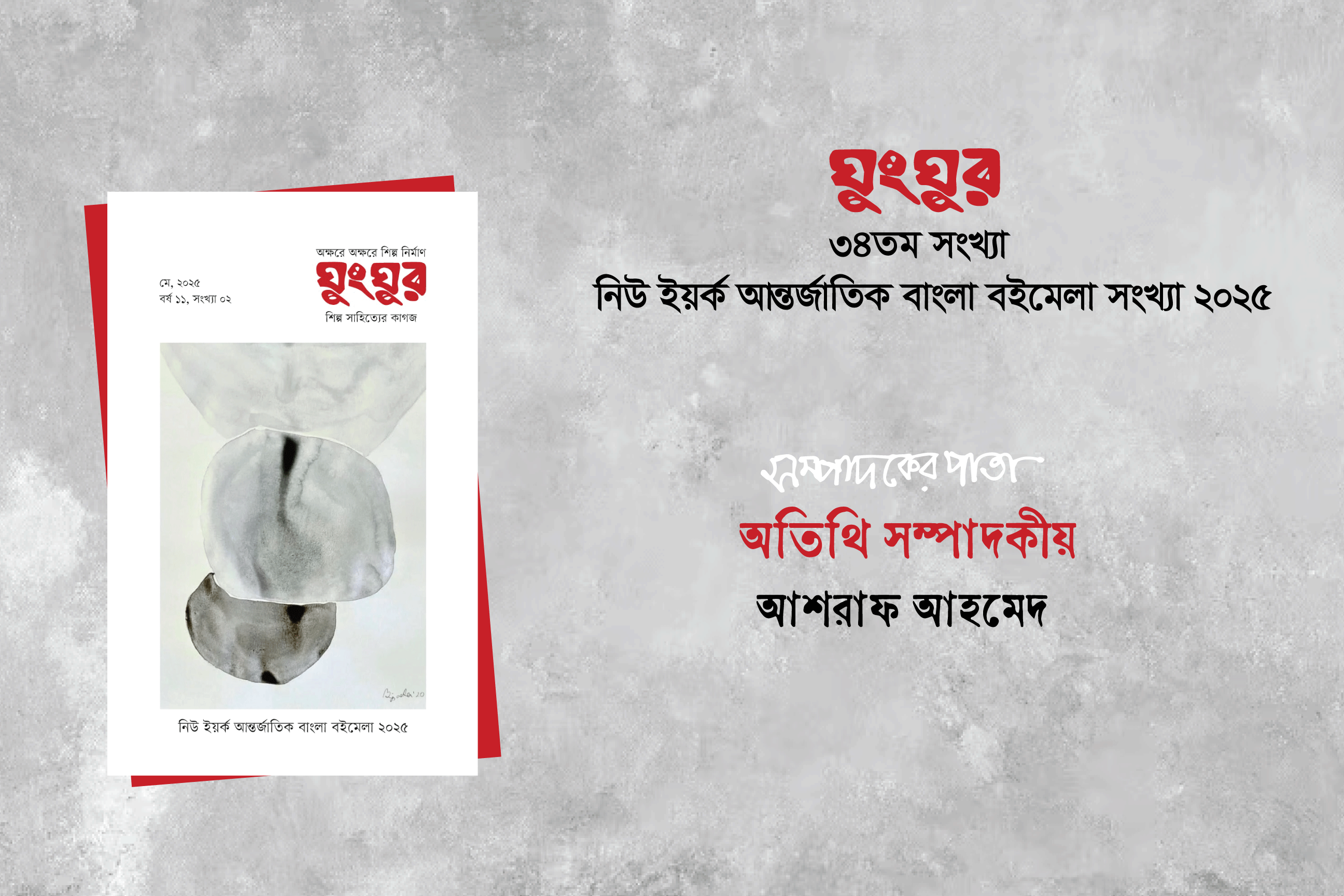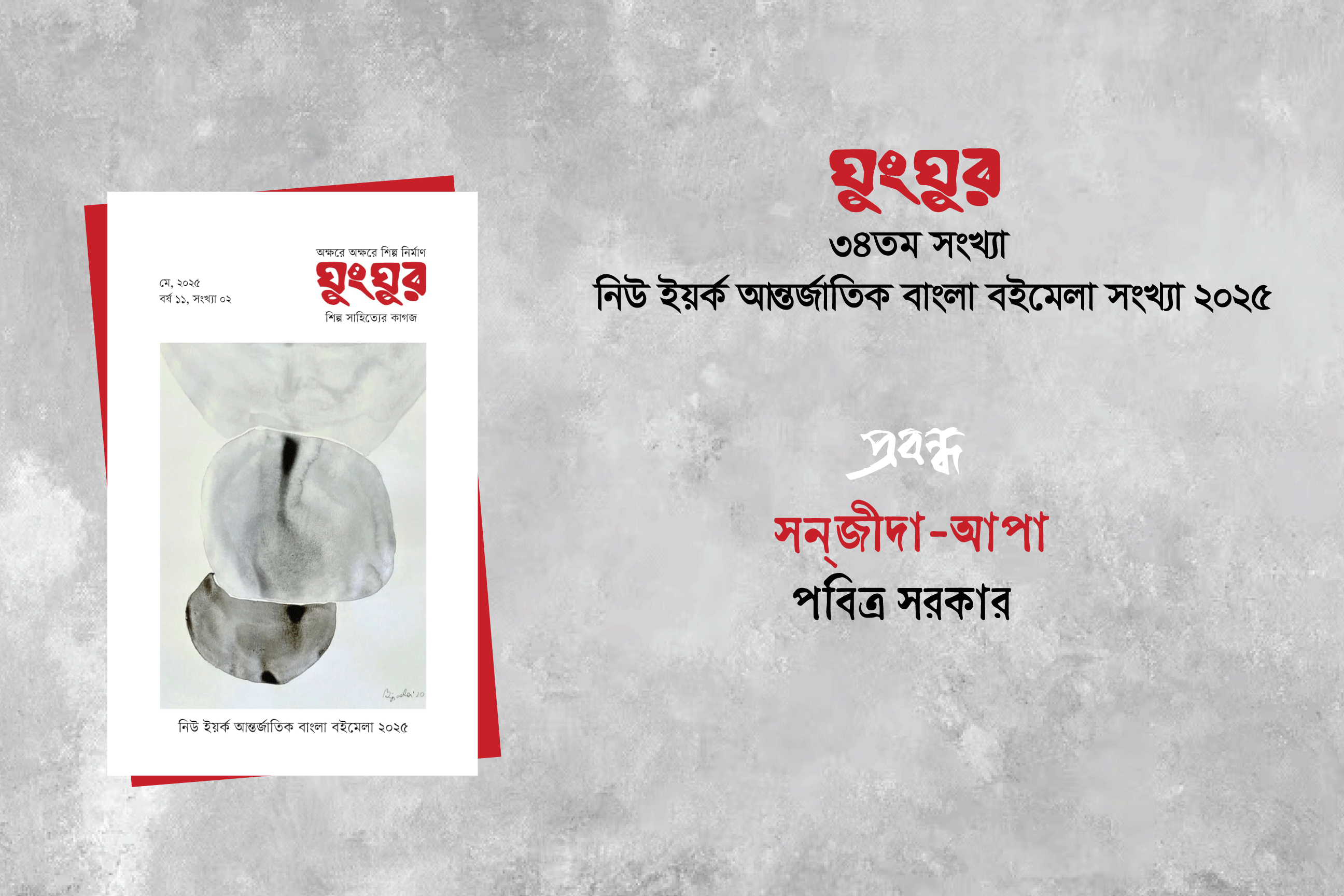‘কথার কথা’ ও ‘অক্ষরে অক্ষরে’ : ভাষাতত্ত্বের সহজপাঠ

আমরা কেউ ব্যাকরণ পড়ে ভাষা শিখি না। একজন নিরক্ষর লোকও বলেন ‘আমি করি’, কখনোই বলেন না ‘আমি করেন’। তার হয়তো কর্তা-ক্রিয়ার ধারণা নেই কিন্তু কর্তার সঙ্গে ক্রিয়ার সংগতি বা সাযুজ্য রক্ষার পদ্ধতিটি তিনি ভালো ভাবে জানেন। আসলে মানুষ ভাষা শেখে পরিবেশ থেকে, তার চারপাশের পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে। এখন প্রশ্ন, এমন স্বাভাবিকভাবেই আমরা যদি ভাষা শিখে যাই, তাহলে আমাদের ব্যাকরণ পড়া বা আলাদা করে ভাষা শিক্ষার দরকারটা কোথায়? এবারে বলি, ওই নিরক্ষর লোকটি কিন্তু কোনভাবেই নিজের চিন্তা ভাবনা লিখে প্রকাশ করতে পারবেন না বা সভা-সমিতিতে নিজের বক্তব্য ব্যক্ত করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন না। এই ধরনের কাজ করার জন্য তাকে শিখতে হবে ব্যাকরণ বা ভাষার নিয়ম-কানুন। অর্থাৎ মান্য কথ্য বা মান্য লেখ্য উপভাষা শেখার জন্য তাকে আবশ্যিকভাবে ভাষার তথা ব্যাকরণের নিয়মগুলো জানতে হবে।
এই কারণে বিদ্যালয় স্তর থেকেই আবশ্যিক ভাষা-শিক্ষা তথা ব্যাকরণ আমাদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাকরণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের একটি সহজাত বিতৃষ্ণা বা ভীতি কাজ করে থাকে। এর অন্যতম কারণ প্রাচীনপন্থী গতানুগতিক শিক্ষণ কৌশল; অনেক খ্যাতনামা বহুল প্রচলিত লেখকের বইও তাতে ইন্ধন জুগিয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই সে ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে না বুঝে মুখস্থ করার একটি প্রবণতা দেখা যায়, যার ফল হয় মারাত্মক। অথচ ব্যাকরণও যে পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে গঠিত এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি বিষয়, তা তারা কখনোই উপলব্ধি করতে পারে না। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাকরণের জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনার অন্যতম উপায় হতে পারে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ব্যাকরণ শিক্ষণ ও সেই অনুযায়ী পুস্তক প্রণয়ন।
ব্যুৎপত্তি বিচারে ‘ব্যাকরণ’ (বি-আ-কৃ+অনট্ = ব্যাকরণ) কথাটির অর্থ ব্যাকৃত করা বা বিশ্লিষ্ট করা; ভাষার গঠনের বিভিন্ন উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করা। কোন একটি ভাষার মান্য শিষ্ট রূপের নিয়ম-কানুন বিশ্লেষিত হয় এখানে। এখানে ‘শিষ্ট’ কথাটির অর্থ ‘শুদ্ধ’ নয়, কারণ আঞ্চলিক উপভাষাগুলি ভাষার কোন অশুদ্ধ রূপ নয়, এগুলি ভাষার বৈচিত্র্য মাত্র। এই মান্য লেখ্য বা কথ্য উপভাষাকে নিপুণভাবে অনুশীলন করার নির্দেশ দেয় ব্যাকরণ। ব্যাকরণে আলোচ্য পাঠ্যাংশকে সাধারণ ভাবে চার ভাগে ভাগ করা যায়। কোন ভাষার ধ্বনি পদ্ধতি, ধ্বনি পরিবর্তন, এককথায় ধ্বনি স্বভাব ব্যাকরণের যে অংশে আলোচিত হয় তা হলো ধ্বনিতত্ত্ব (phonology)। ধ্বনির পরবর্তী স্তর অর্থাৎ অর্থ যুক্ত একক বা রূপ, শব্দ, নতুন শব্দের উৎপত্তি ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনা হয় ব্যাকরণের রূপতত্ত্বে (morphology)। আবার শব্দ থেকে পদ, পদ থেকে বাক্য গঠন, বাচ্য, তার প্রকারভেদ হলো অন্বয়তত্ত্বের (syntax) আলোচ্য বিষয়। এছাড়া ভাষার শব্দভাণ্ডার, শব্দার্থ ইত্যাদির আলোচনা হয় শব্দার্থতত্ত্বে (semantics)। সামগ্রিকভাবে এই হলো ব্যাকরণের বিষয়বস্তু। এই সম্পূর্ণ বিষয়টি যদি ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রমোচ্চ স্তর অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শেখানো হয়, তাহলে শিখন প্রক্রিয়াটি অনেক বেশি অর্থপূর্ণ ও কার্যকরী হতে পারে।
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘কথার কথা’ আর ‘অক্ষরে অক্ষরে’ বই দুটিকে বলা যেতে পারে ভাষা শেখার সহজপাঠ। বাংলার শিশু-কিশোরেরা যাতে নিজের ভাষাকে আনন্দের সঙ্গে জানতে পারে, তার গঠনকৌশল ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত হতে পারে, সেই জন্য তাদেরই চেনা-পরিচিত জগৎ থেকে অজস্র দৃষ্টান্ত হাজির করে বিষয়টি বোঝানোর অত্যন্ত সযত্ন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় গ্রন্থ দুটিতে। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলার ক’জন শিশু-কিশোরের হাতে বই দুটি আজ অবধি পৌঁছে দেওয়া গেছে? বিদ্যালয় স্তরে অবশ্যপাঠ্য হয়েছে কয়টি ক্ষেত্রে? উত্তর কিন্তু নেতিবাচক। বাজার চলতি নিম্নমানের অজস্র বইয়ের বাঁধাধরা সংজ্ঞা-উদাহরণের ফাঁদে পড়ে হাঁসফাঁস করছে বর্তমান প্রজন্মের ভাষাশিক্ষা; ফলত ব্যাকরণ বইটি তাদের কাছে হয়ে উঠেছে শুষ্ক, নীরস ও জটিল। এহেন ব্যাকরণ ভীতি বা ব্যাকরণ বিমুখতার একমাত্র প্রতিষেধক হতে পারে ‘কথার কথা’ ও ‘অক্ষরে অক্ষরে’র মতো সরস, সুখপাঠ্য বই দুটি।
‘কথার কথা’ বইটির সূত্রপাত হচ্ছে ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাকে কেন্দ্রে রেখে। স্বল্প আয়াসে বহুসংখ্যক সংবাদ অনেককে জানানো অর্থাৎ অন্যের সঙ্গে সংযোগ সাধনই ভাষার প্রধান শর্ত। এই উদ্দেশ্য পূরণের তাগিদে ভাষায় যাবতীয় ভাব ও বস্তুজগতের নামকরণ করতে হয়েছে অর্থাৎ নতুন শব্দ সৃষ্টি করতে হয়েছে; তো, নতুন শব্দ কীভাবে গড়ে উঠবে? লেখকের বয়ান অনুযায়ী নতুন শব্দ গড়ে উঠবে ‘আলাদা আলাদা আওয়াজ গুছিয়ে বেঁধে’। তবে শুধু বাঁধলে বা জুড়লেই হবে না, তার অর্থ থাকতে হবে। তবেই যোগাযোগ ঘটবে; খবর পৌঁছে দেওয়া যাবে। আবার সেই অর্থ কেবল একজন জানলে চলবে না, বক্তা-শ্রোতা উভয়কেই তা জানতে হবে। এভাবেই পরিচালিত হয় ভাষা সংবিধি। তবে শব্দের সঙ্গে অর্থের কোন কার্যকারণগত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। ‘গাছ’ শব্দটি উচ্চারিত হলে যে অর্থটি আমরা বুঝি বা যে ধারণা বা ছবিটি আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে, তার সঙ্গে ‘গ্+আ+ছ্’ এই নির্দিষ্ট ধ্বনিসমষ্টিযুক্ত শব্দটির কোন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই; দীর্ঘদিন ধরে বহু সংখ্যক মানুষ দ্বারা গৃহীত হলে কোন শব্দ কোন নির্দিষ্ট বস্তুর প্রতীক হয়ে ওঠে।
একারণেই একই বস্তু বা পদার্থ বোঝানোর জন্য বিভিন্ন ভাষায় পৃথক-পৃথক ধ্বনিসমষ্টি যুক্ত ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে বা একই শব্দের অর্থ ভাষা ভেদে পরিবর্তিত হয়ে যায় : ‘একজন আমাকে জিজ্ঞেস করল, ‘ওখানে কী হচ্ছে, মশাই?’ আমি চেঁচিয়ে বললাম, ‘গান’। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক সাহেব। সে হঠাৎ আমার কথা শুনতে পেয়ে সেখান থেকে দে-ছুট। ‘গান’ মানে সে ভেবেছে বন্দুক আর সেই সঙ্গে অত ভিড় দেখে ভেবে নিয়েছে—নিশ্চয়ই ও জায়গায় কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে! ‘আকাশ’ বললে তুমি আকাশ বুঝবে, ‘গান’ বললে তুমি গান-গাওয়া বুঝবে—তার কারণ, আমাদের ভাষা এক। ঘরে-বাইরে আমাদের মাথার ওপর যে খোলা জায়গাটা— আমাদের ভাষায় তার নাম ‘আকাশ’; ইংরিজি ভাষায় তার নাম ‘স্কাই’। একই জিনিস, কিন্তু আলাদা-আলাদা ভাষায় আলাদা-আলাদা নাম।’ এভাবেই মজার ছলে ব্যক্ত হয়েছে ব্যাকরণের আপাত কঠিন পাঠ।
শব্দ নিছক চিহ্ন ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর চিহ্নের একমাত্র কাজ হলো চিনিয়ে দেওয়া : ‘‘বাঘ’—এই কথাটা যখন আমি উচ্চারণ করছি, তখন তার মূলে থাকছে সত্যিকার বাঘ, শুধু তার সূত্র হিসেবে কাজ করছে ‘বাঘ’ কথাটা। সূত্রের কাজই হলো মূল জিনিসটা ধরিয়ে দেওয়া।’ লেখকের এরূপ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী ফের্দিনা দ্য সোস্যুরের ‘চিহ্নায়ন’ (signification) তত্ত্ব। যেখানে চিহ্ন (sign) ধারণা (concept) ও ধ্বনি প্রতীকের (sound image) সমন্বয়ে তৈরি। এখানে ধারণা হলো signified ও ধ্বনি প্রতীক হলো signifier। অর্থাৎ ‘গাছ’ শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে লতাপাতাকাণ্ড যুক্ত যে ধারণাটি আমাদের মনে গড়ে উঠছে তা হলো signified ও ‘গ্+আ+ছ্’ ধ্বনি জুড়ে গঠিত ‘গাছ’ শব্দটি হলো signifier। প্রতিটি চিহ্ন এই দুই অংশের সম্পর্কে আবদ্ধ; একটি চিহ্ন অন্য চিহ্ন থেকে আলাদা হয়ে যায় এই উপাদানদ্বয়ের বৈচিত্রের জন্য। একটি চিহ্নের সঙ্গে অন্য চিহ্নের সম্পর্ক বৈপরীত্যের। এই বৈপরীত্যকেই বলা হয় চিহ্নমূল্য এবং এভাবেই চিহ্নায়ন (signification) প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
একারণেই ‘একালে সেকালে’ অধ্যায়ে লেখক বলেছেন শব্দ অর্থাৎ নাম ‘আসলে একটা বাইরের লেবেল’; ‘ওটা শুধু চেনবার উপায়’; ‘ওটা কারও পরিচয় নয়’। নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বস্তু বা প্রাণীর কোন সম্পর্ক নেই; বস্তু বা প্রাণীর বৈশিষ্ট্য বা স্বরূপ তার নামের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় না। কিন্তু প্রাচীনকালে কিছু মানুষ মনে করত নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাণীটি অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত। যে ধারণা থেকে উৎপত্তি হয়েছিল মন্ত্র বা তুকতাক জাতীয় সংস্কারের : ‘হাত ধরে মুচড়ে দিলে যেমন কেউ জখম হয়, নাম ধরে মন্ত্র পড়লেও তেমনি সে জখম হয়—এই ছিল সেকালের ধারণা’। কিংবা কুশপুত্তলিকা দহনের প্রথা, তারও উৎস উক্ত বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত। এভাবেই আবির্ভাব ঘটেছে জলপড়া, ঝাড়ফুঁক, বাণমারা, স্বপ্নাদ্য অষুধ, মন্ত্রপড়া মাদুলি, কিছু বা কারোর নাম না নেওয়া ইত্যাদি লোকবিশ্বাসের। অর্থাৎ প্রাচীন যুগে সৃষ্ট এজাতীয় প্রথা বা সংস্কারের প্রেরণা লুকিয়ে আছে নামের সঙ্গে পদার্থের ওতপ্রোত সম্পর্কের মধ্যে।
ভাষায় নির্দিষ্ট ধ্বনিসমষ্টি বা শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্পর্কহীনতার কথা বলা হলেও সবসময় তা ঘটে না। কখনো কখনো ধ্বনির সঙ্গে অর্থের মূলীভূত যোগ খুঁজে পাওয়া যায়। প্রতিটি সংস্কৃত শব্দের মূলে একটি ধাতু থাকে। সেই ধাতুর একটি মূল অর্থ আছে। ধাতুর মূল অর্থের সঙ্গে ওই ধাতু থেকে উৎপন্ন প্রতিটি শব্দের অর্থের যোগ থাকে। ধাতু থেকে শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ার এই প্রক্রিয়াটিকে লেখক তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : ‘কাজ যেমন সমাজের ভিত্তি, তেমনি ক্রিয়া—বোঝানো মূলধাতুগুলো আবার মানুষের ভাষারও ভিত্তি’। কিছু শব্দের নাম লেখক দিয়েছেন ‘আওয়াজ নকল করা শব্দ’, অর্থাৎ ধ্বনিগত অনুষঙ্গ থেকে যে শব্দগুলি সৃষ্টি হয়েছে; যেমন ‘টিকটিকি’, ‘কাক’, ‘কোকিল’, ‘ঝিঁঝি’, ‘ঘুঘু’।
আবার কিছু শব্দের মধ্যে আওয়াজ লুকিয়ে থাকে, তাকে খুঁজে বের করে নিতে হয়; যেমন: ‘দুঃখ’ শব্দটির মধ্যে আছে ‘উঃ’ ধ্বনি (দ্+উঃ+খ+অ); যে ‘উঃ’ ধ্বনি মানুষের ব্যথা-যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। অর্থাৎ ধ্বনির সঙ্গে অর্থের সংযোগের বিষয়টি সব সময় খেয়ালখুশি (arbitrary) যেমন নয়, আবার সুনির্বাচিতও নয়। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে দুটি দল গড়ে উঠেছে; যারা বলেন ধ্বনি-অর্থের সূক্ষ্ম সাদৃশ্য আছে বা অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে তাঁরা হলেন analogist আর যারা বলেন কোন অপরিহার্য যোগ নেই তাঁরা হলেন anomalist।
পৃথিবীর প্রতিটি ভাষার নির্দিষ্ট গঠন কাঠামো আছে। প্রতিটি ভাষার কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। তবে সব ভাষারই কিছু সাধারণ ধর্ম রয়েছে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী আব্রাহাম নোয়াম চমস্কির বৈশ্বিক ব্যাকরণ ও বিশেষ ব্যাকরণ তত্ত্বের মধ্যে এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। বাঙালি শিশু-কিশোরদের মধ্যে বিদেশি ভাষা শেখা বিশেষত ইংরেজি শেখার একটি ব্যাপক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ভাষা শেখার অন্যতম অংশ নতুন শব্দ শেখা তথা শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা; লেখক শিক্ষার্থীদের অভয় দিয়ে জানিয়েছেন কোন ভাষায় সাবলীল কথোপকথন চালানোর জন্য ভাষার শব্দভাণ্ডারের সামান্য একটি অংশ শেখাই যথেষ্ট। ইংরেজির দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেছেন : ‘ইংরেজিতে শব্দের সংখ্যা পাঁচ লক্ষের মতো। কিন্তু একজন সাধারণ ইংরেজ জানে তার মোটে পাঁচ ভাগের এক ভাগ। সেদেশে ফলের বাগানে যেসব অশিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিত মালী কাজ করে, তাদের মধ্যে খোঁজখবর নিয়ে দেখা গেছে, রোজকার কথাবার্তায় পাঁচশোর বেশি শব্দ তারা ব্যবহার করে না।
শহরে লোক-চলাচলের বড়ো বড়ো ঘাঁটিতে নমুনা নিয়ে দেখা গেছে সারা জীবনে হাজার কিংবা বারোশো শব্দের বেশি লোকের কাজে লাগে না। সাধারণ মানুষের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। শুধু কথা নিয়েই যাদের কারবার, সেই লেখকরাই বা জীবনে কত শব্দ কাজে লাগান? তাও হিসেব করা হয়েছে। শেক্সপীয়র মোটে ষোল হাজার আলাদা আলাদা শব্দ কাজে লাগিয়ে নাটক লিখেছিলেন। মিল্টন তাঁর মহাকাব্যে ব্যবহার করেছেন মোট আট হাজার শব্দ। ভিক্টর হুগো তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছেন বিশ হাজার শব্দ। বাংলা ও ইংরেজি উভয়ই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ উদ্ভূত ভাষা। তবে উভয় ভাষার বাক্য গঠন কৌশল পৃথক। বাংলা ভাষার স্বাভাবিক অন্বয়ক্রম যেখানে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV) গঠনবিশিষ্ট, ইংরেজিতে তা কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম (SVO) গঠনবিশিষ্ট; বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক এই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে বিশেষণ, ক্রিয়াপদ ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রয়েছে। বিভিন্ন ভাব, অবস্থা বোঝানোর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিশেষ্যের সঙ্গে বিভিন্ন বিশেষণ ব্যবহার করে বহুবিধ ভাব জ্ঞাপন করা যায় : ‘লাল কুকুর, কালো কুকুর, বড় কুকুর, শুয়ে-থাকা কুকুর, বসে থাকা কুকুর—প্রত্যেকটা বোঝাতে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন আলাদা আলাদা শব্দের দরকার হয় না। লালই হোক, কালোই হোক, ছোটোই হোক, বড়োই হোক, শুয়েই থাক, বসেই থাক—কুকুর ছাড়া তো কিছুই নয়। কাজেই ‘কুকুর’ কথাটার সঙ্গে গুণ-বোঝানো লাল, কালো, ছোটো, বড়ো, শুয়ে থাকা, বসে থাকা, জুড়ে দিলেই অনেক রকমের ভাব বুঝিয়ে দেওয়া চলে। এই শব্দগুলোকেই আবার অন্য যেকোনো জায়গায় লাগানো যায়।’
একইভাবে একই ক্রিয়া বিভিন্ন বিশেষ্যের সঙ্গে ব্যবহার করা যায় : ‘মানুষ ছুটছে, কুকুর ছুটছে, ঘোড়া ছুটছে—এ থেকে ছোটার ভাবটুকু শুধু ছিঁড়ে নিয়ে তার নাম দেওয়া হলো ‘ছোটা’। যেই ছুটুক, তার সঙ্গে ‘ছোটা’ কথাটাকে জুড়ে দিলেই হলো।’ লেখকের মতে, ‘পৃথিবীতে বস্তু যেমন অসংখ্য, তার ভাবও তেমনি অসংখ্য। তাদের প্রত্যেকের জন্যে যদি আলাদা আলাদা শব্দ ঠিক করতে হতো তাহলে কোটি কোটি শব্দেও কুলোতো না। সে বিপদ থেকে মানুষকে বাঁচিয়েছে।’ এখানে ভাষায় শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈকল্পিক (paradygmatic) ও উপস্থিতির (syntagmatic) ধারণা যে কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ, তার আভাস পাওয়া যায়।
লেখকের কাছে ব্যাকরণ হলো ‘ভাষার লাগাম’ এবং ভাব প্রকাশের জন্য ব্যাকরণের শাসন মেনে চলা অনিবার্য। বাক্যে একটি শব্দের পর অন্য শব্দ পাশাপাশি বসিয়ে গেলে চলে না; শব্দগুলি কীভাবে বাক্যে বসবে ব্যাকরণই তা ঠিক করে দেয়। শব্দকে লেখক অভিহিত করেছেন ‘ভাষার ইঁট’ অভিধায়। সেগুলি বসানোর সময় তাদের আকারে অনেক সময় বদল ঘটে অর্থাৎ বিভক্তি যুক্ত হয়ে শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি শব্দের অবস্থানের বিভিন্ন শর্ত রয়েছে, তা নির্ণীত হয় ব্যাকরণে। বইতে কারক, বাচ্য, বচন, পুরুষ, লিঙ্গ, ক্রিয়ার ভাব ও কাল, ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয়গুলি প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
ধ্বনি-রূপ-অন্বয়, এই তিনটি মূল বিষয় ছাড়াও ব্যাকরণে শব্দভাণ্ডার, শব্দার্থ ইত্যাদি আলোচিত হয়; যেটি শব্দার্থতত্ত্ব নামে পরিচিত। বাংলা শব্দভাণ্ডার বা বাংলা শব্দের অর্থ পরিবর্তনের ধারার ক্ষেত্রে বাংলা ও বাঙালি জাতির বিবর্তনের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, যার মাধ্যমে ভাষায় বিভিন্ন শ্রেণির শব্দের আগমনের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে কালক্রমে প্রাকৃত-অপভ্রংশের বিবর্তনের ফলে যেহেতু বাংলা ভাষার জন্ম, তাই বাংলা ভাষায় সংস্কৃতমূল শব্দের আধিক্য বেশি। আবার মধ্যযুগে বিস্তীর্ণ সময়কাল বাংলা মুসলিম শাসনের অধীনে থাকায় বাংলায় আরবি ফারসি শব্দের প্রাবল্য লক্ষণীয়। শব্দার্থ পরিবর্তনের ইতিহাসের অন্তরালে জাতির সামাজিক ইতিহাসের বহুবিধ সূত্র যে লুকিয়ে থাকে, তা বলা বাহুল্য। দু’একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। ‘কলম’ শব্দের মূল অর্থ ‘শর’ বা ‘খাগ’, যা থেকে অনুমান করা যায় অতীতে শরের কলম ব্যবহৃত হতো। স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে ইংরেজ সাহেবরা কলকাতা থেকে হাওয়া বদল করতে যেতেন মধুপুর, গিরিডি, সাঁওতাল পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে। সেখানে শাকসবজির কম দাম দেখে তারা বলতেন ‘ড্যাম্ চিপ’। এই শব্দ ব্যবহার থেকে স্থানীয়ভাবে তাঁরা পরিচিত হলেন ‘ড্যাঞ্চিবাবু’ নামে। এভাবেই কোন একটি শব্দের উৎপত্তির সূত্র ধরে যে সব অজানা তথ্যের সন্ধান মেলে তা স্থানীয় বা লোক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।
লেখক আজীবন ছোটদের জন্য ভেবেছেন; ছোটরা কী চায়, কেমন ভাবে চায়, শিশু সাহিত্যের প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত, তা নিয়ে তিনি ভাবিত ছিলেন সর্বদা। ছোটদের মন পাওয়ার জন্য যে পৃথক ভাষাশৈলী প্রয়োজন, তা তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। একারণেই আলোচ্য বই দুটিতে দেখি বিষয় গুরুগম্ভীর হলেও তিনি তৈরি করেছেন একটি বৈঠকী আমেজ, যেন ছোটদের সঙ্গে গল্প করতে বসেছেন। গল্পের ছলে বুঝিয়ে চলেছেন ভাষার কারিকুরি।
তাছাড়া শব্দ চর্চার প্রতি আশৈশব তাঁর ছিল একটি অমোঘ আকর্ষণ : ‘ছোটোবেলায় আমাদের বাড়িতে বই বেশি ছিল না। একটা অভিধান ছিল। এই বইটা হয়ে উঠল আমার প্রধান পাঠ্য। শব্দ আর তার মানে, শব্দের সঙ্গে শব্দ যোগ করে নতুন শব্দ, শব্দের সঙ্গে ছোট্ট অংশগুলো যোগ করে মানে বদলানো—সবই কেমন অবাক করে দিত। অভিধান হয়ে উঠল আমার নিত্যসঙ্গী। হয়তো শব্দকৌতূহল এর থেকেই।’ ‘কথার কথা’ ও ‘অক্ষরে অক্ষরে’র প্রেরণার উৎসও আমরা উক্ত উদ্ধৃতি থেকে খুঁজে পাই। আকর্ষক শিরোনাম আর প্রাসঙ্গিক ছবি বই দুটিকে করে তুলেছে চিত্তাকর্ষক। বই দুটি শিশু-কিশোরদের মনে বাংলা ভাষা সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ধারণা গড়ে তোলার সামর্থ্য রাখে।
কৌশিক কর্মকার প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রতিভা বসুর কথাসাহিত্য : শৈলী প্রসঙ্গ। তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করেন।