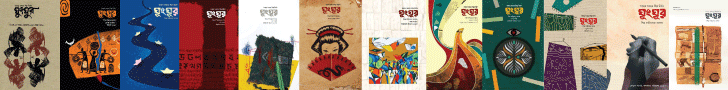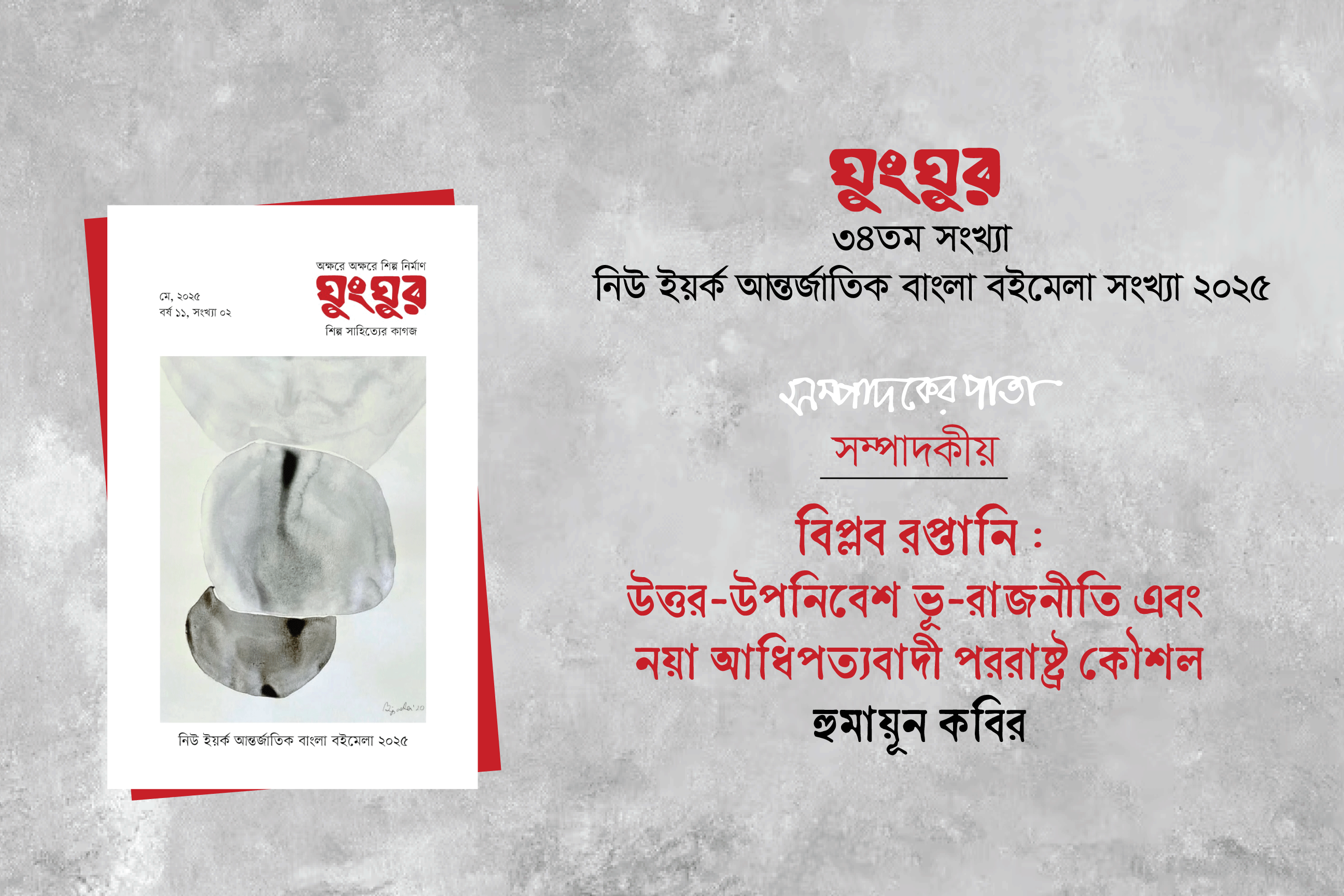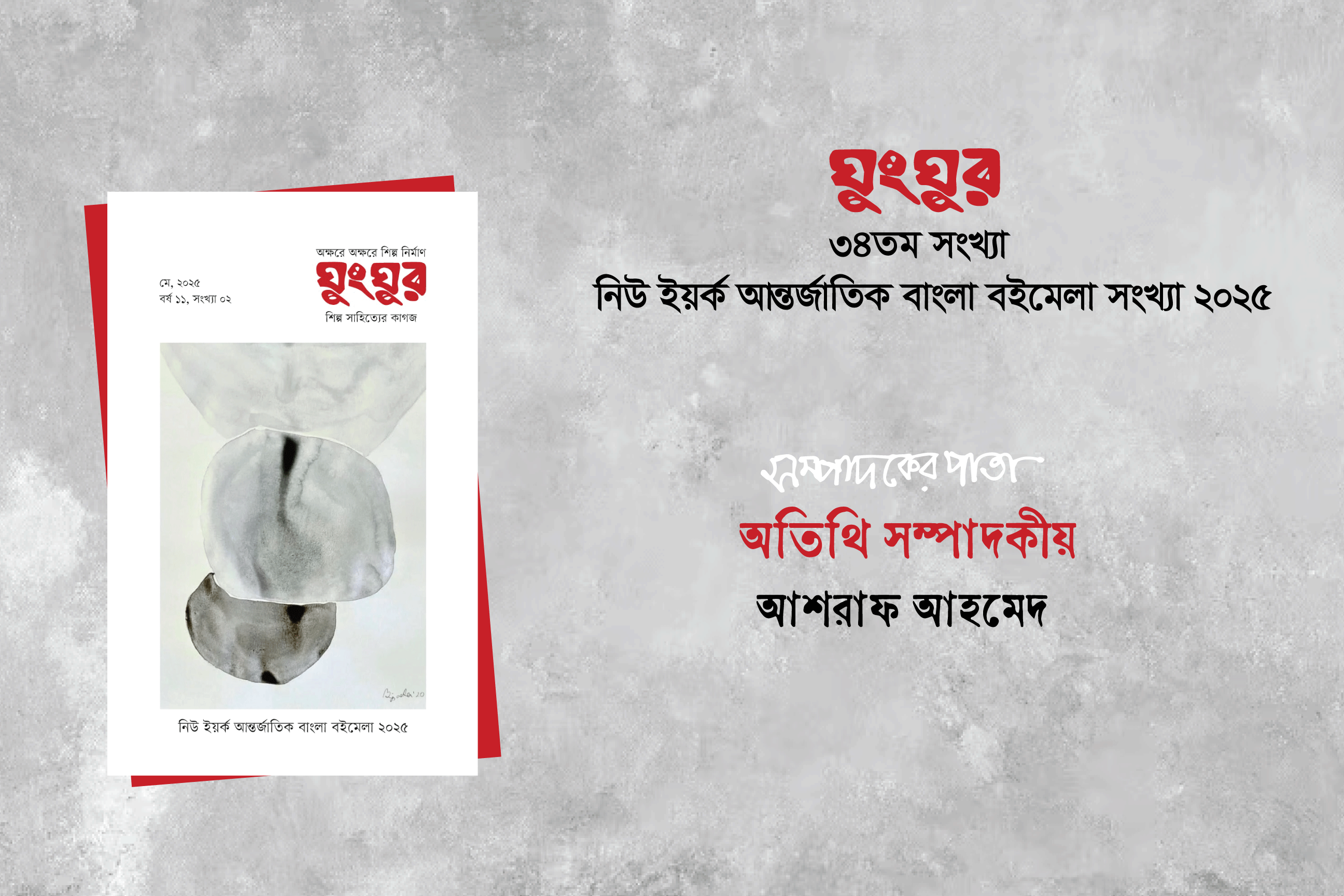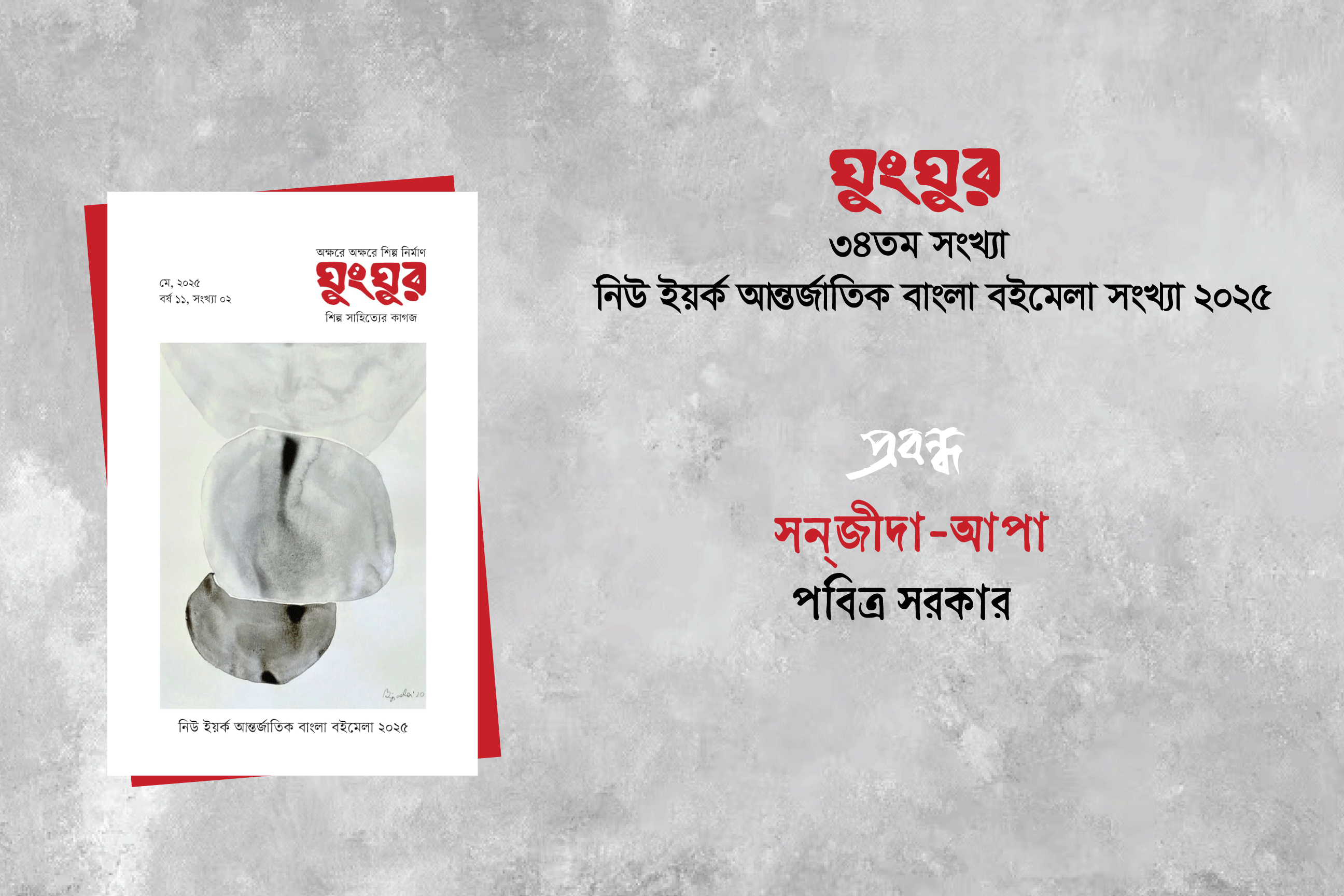দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি সময়ের অগ্রদূত : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
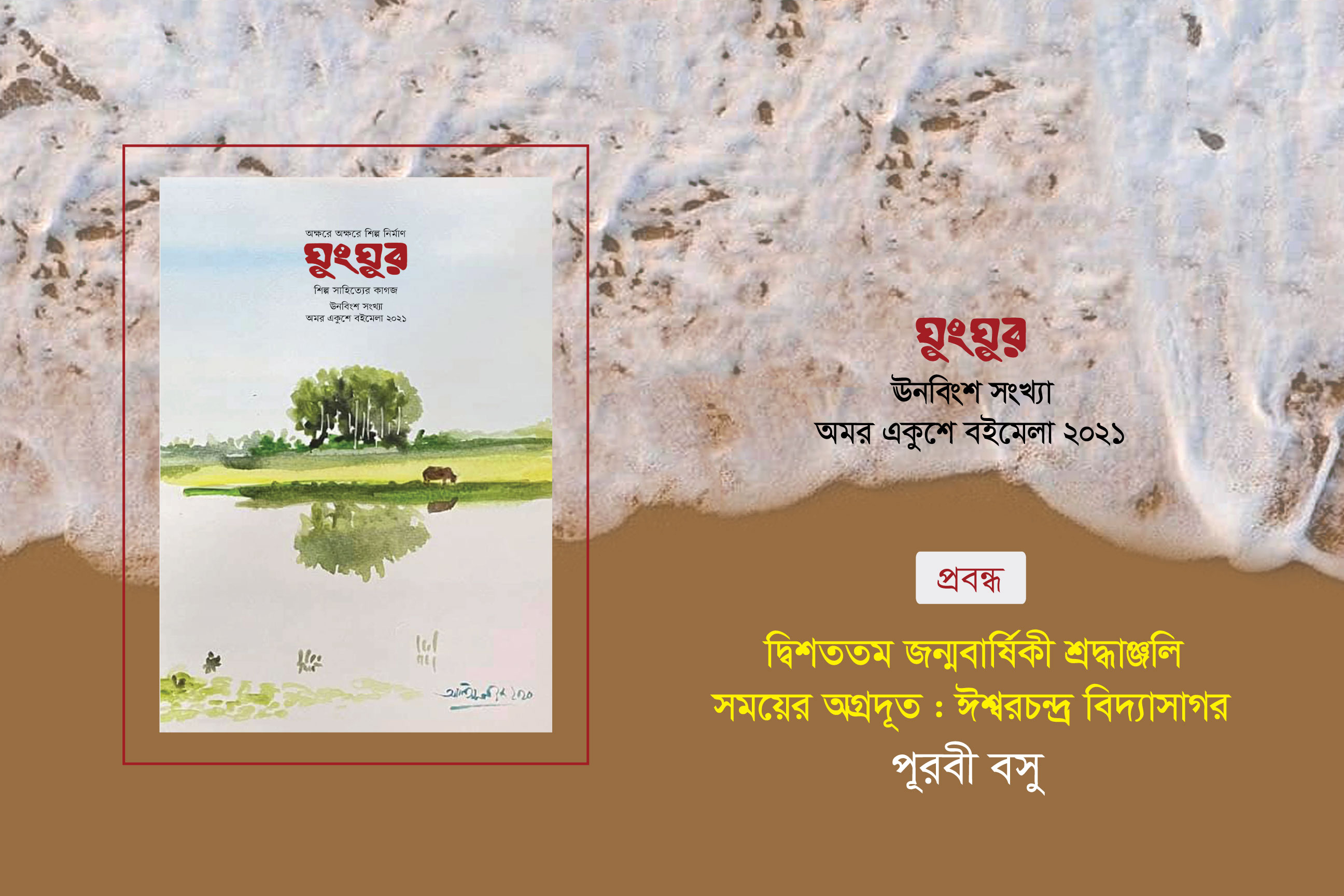
(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্যে সংস্কৃত কলেজ তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধি দান করে।)
বিধবা নারীর জন্যে একটি মানবিক জীবন-সৃষ্টি করাই শুধু নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের ইতিহাসে এবং জনশিক্ষা বনাম নারী শিক্ষার প্রসারতায় মানবদরদি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) অবদান রয়েছে অপরিসীম। তাঁর পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব এবং বিপুল ও বহুমুখী কর্মক্ষমতার উৎস ও চালিকাশক্তি ছিল মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ সহমর্মিতা ও ভেদাভেদহীন দৃষ্টিভঙ্গিতে সকলের কল্যাণকামিতা। তাঁর এই অসাধারণ মানবিক কর্মকাণ্ডকে চারটি ধারায় ভাগ করা চলে :
সমাজ সংস্কারের রূপায়ন ও বাস্তবায়ন : বিধবা বিবাহ আইন-পাস
তাঁর কৃত সমাজ সংস্কারের মধ্যে রয়েছে, নারীর জীবনের মান উন্নয়ন, হিন্দু বিধবা বিবাহ আইনসঙ্গত করা, বাল্যবিবাহ রোধ, বহুবিবাহ স্থগিত, ও কৌলীন্যপ্রথার তিরোধান।
ঊনবিংশ শতকের সমাজে নারীর অবস্থা দেখে হতাশ ঈশ্বরচন্দ্র বলেছিলেন, ‘যে দেশে পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকতা রক্ষাই প্রধান ধর্ম ও পরম ধর্ম; আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।’
আমরা সকলেই অবগত যে ১৮১৮ সালে রামমোহন রায় কলকাতায় সহমরণ এবং সতীদাহ প্রথা বিলোপের জন্য জনমত তৈরি করেন, এবং এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিং কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই প্রথা বিলোপ করে আইন পাস করেন। এর পর কালোত্তীর্ণ, মহান এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫০ থেকে ১৯৫৫ সাল অবধি বিধবা বিবাহের সপক্ষে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালে ভারতবর্ষে বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইন পাস হয়। বিধবা বিবাহের সামাজিক স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে ১৯৫৬ থেকে ১৮৬৭ সাল নাগাদ ৬০টি বিধবা বিবাহের আয়োজন করেন। হুমায়ূন আজাদ ঠিক-ই বলেছিলেন, সতীদাহ প্রথা বাতিল করে রামমোহন বাংলার মেয়েদের জীবন দান করেছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিদ্যাসাগর, বিধবা বিবাহের মাধ্যমে।
তখনকার দিনে বাল্য বৈধব্যের আধিক্য ছিল সমাজে। বাল্যবৈধব্যের অন্যতম প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ। প্রধানত বিদ্যাসাগরেরই চেষ্টায় ১৮৭১ সালে রোধ হয় বাল্যবিবাহ। সহবাসসম্মত বয়স ১২-এর কম নয় বলে সাব্যস্ত হয়। সমাজ থেকে আরও দুটি কুপ্রথা বিদায় করতে সচেষ্ট ছিলেন বিদ্যাসাগর যা দূর করতে আরও বেশ কিছু সময় লেগেছিল। তার একটি বহুবিবাহ যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল আরেকটি কুপ্রথা—আর সেটি হলো বৈবাহিক ব্যাপারে কৌলীন্যপ্রথা পালন।
বহুবিবাহ, যা কেবল পুরুষের জন্যেই প্রযোজ্য, সমাজের আরেকটি ব্যাধি সমাজ থেকে দূর করার জন্যে বিদ্যাসাগর বহুরকম চেষ্টা করেন, আইনের সহায়তা কামনা করেন। কিন্তু কার্যত বাংলায় বহুবিবাহ রোধের আইনি অনুমতি মিললেও (১৮৭১) ভারতের অন্যান্য জায়গায় তখন পর্যন্ত সামাজিকভাবে এই প্রথা রহিতের ছাড়পত্র মেলে না। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে আইন করে তা বন্ধ করা না গেলেও সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজে ও ব্যক্তির মনস্তত্ত্বে সাহিত্য আর যাত্রা-নাটকের (বিশেষত প্রহসন) মাধ্যমে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণে ও মূল্যবোধে বহুবিবাহের গ্রহণযোগ্যতা এতোটাই হ্রাস করে দেওয়া হয় যে এই অসুস্থ প্রক্রিয়াটি আইনি সাহায্য ছাড়াই সমাজ থেকে ধীরে ধীরে উচ্ছেদ হতে শুরু করে। এছাড়া, কৌলিন্য কিংবা বর্ণ বা জাতিভেদের মতো কুসংস্কারকে পুনঃ পুনঃ আঘাতে নির্মূল করে দিয়ে মানবতার জয়গান গাইতে প্রস্তুত হয়েছিলেন তখনকার কয়েকজন প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারক। বিদ্যাসাগর তাঁদের অগ্রদূত। মানবতাবাদী বিদ্যাসাগরের কাছে সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদপ্রথা, মানুষে মানুষে বিভাজন, বৈষম্য ও অবিচার পুরোপুরি অগ্রহণীয় ছিল।
এদিকে সতীদাহ প্রথা নিবারণের ফলে বহু অল্পবয়স্কা নারী বিধবা হয়। তাদের অসহায়ত্ব, নিরাপত্তাহীনতা এবং উঠতি বয়সের স্বাভাবিক শারীরিক চাহিদা, কিংবা এই চাহিদার প্রতি তাদের প্রাকৃতিক আসক্তি ও দুর্বলতার কারণে পরবর্তীকালে কোনো কোনো তরুণী বিধবা পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করে, অনেকে সংসারে বা বাড়ির বাইরে অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হয়। গুপ্ত ভ্রূণ হত্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রামমোহন রায়ের মতোই টের পেলেন অকাট্য যুক্তির জোরে নয়, শাস্ত্রীয় কুসংস্কার দিয়েই এদেশের মানুষের অন্ধ বিশ্বাস ও কর্মধারা পরিচালিত হয়। ফলে সতীদাহ নিবারণের জন্যে রামমোহন যেমন শাস্ত্র থেকেই মালমশলা যোগাড় করে শাস্ত্রকেই ঘায়েল করেছিলেন, বিদ্যাসাগরও একই পথ বেছে নিলেন। শাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রের সংস্কারকে প্রতিহত করেন। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে মনোসংযোগ করেন বিভিন্ন ধরনের শাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্যে। সহমরণের বদলে ব্রহ্মাচার্য্য পালনের মধ্য দিয়ে বিধবা নারী যে জীবন ধারণ করে, বিদ্যাসাগর তাকে বলেন মৃতবৎ। এই জীবন যে প্রকৃত বেঁচে থাকা নয়, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে শুধু প্রাণটা কোনোমতে টিকিয়ে রাখা, চিতার আগুনের মতোই প্রতিদিন এই জগৎ সংসারের জ্বলন্ত আগুনে একটু একটু করে পুড়ে মরা, তা তিনি ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন। অথচ তিনি নারীকে দিতে চেয়েছিলেন একটি পরিপূর্ণ জীবন, স্বাভাবিক মানুষের জীবন, একটি উপভোগ্য জীবন। নারীর শরীরকে তিনি নারীর হাতেই ফিরিয়ে দিয়ে তাকে পরিতৃপ্ত রাখার অধিকার নারীকেই দিতে চেয়েছিলেন বিধবা বিবাহের মাধ্যমে। সেই হিসেবে বিদ্যাসাগর প্রকৃতই প্রগতিশীল ও আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন একজন নারীবান্ধব পুরুষ বলে নিজেকে প্রমাণ করেন। বিদ্যাসাগর যখন শ্লেষের সঙ্গে উচ্চারণ করেন, “তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না... দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়!”, তখন নারীর শরীর অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাকে আর উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করার উপায় থাকে না। অথচ সেই শরীরের ওপর যখন নিজেরই অধিকার থাকে না, কর্তৃত্ব থাকে না নারীর, তখন তার আর কোনো অধিকার বা আর কোনো দাবীই স্বীকৃত হতে পারে না।
বহু অধ্যয়ন শেষে—বহু শাস্ত্র ঘেঁটে তবে বিধবাদের, বিশেষ করে বাল্য বিধবাদের, সমস্যার সমাধান এনেছিলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর আবিষ্কার করেছিলেন পরাশরের বিধান। এই বিধানে স্বামী মারা গেলে বিধবাদের সামনে তিনটি পথ খোলা থাকে : পুনঃবিবাহ, ব্রহ্মচারিত্ব, স্বামী সহগমন বা সতীদাহ। সতীদাহ যেহেতু তখন আইন বহির্ভূত হয়ে গেছে রামমোহনের নেতৃত্বে চালিত আন্দোলনের ফলে, বিদ্যাসাগর বিধবাদের ওপর রামমোহনের মতো ব্রহ্মচারীর জীবন চাপিয়ে দিতে চাননি। তিনি রামমোহনের মতো কেবল প্রাণটুকু নয়, রক্তমাংসে গড়া স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মানুষের মতো জীবন দিতে চেয়েছেন বিধবাদের। ফলে বহু কষ্টে তিনি বিধবা বিবাহ আইন পাস করিয়ে এইসব বিধবা মেয়েদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের পথ খুলে দেন। আর জন-মানসে সেটা ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করতে তিনি যুক্তি বা আইনের ভয় দেখালেন না। ধর্মীয় শাস্ত্র ঘেঁটেই প্রমাণ করলেন, লোকজনকে আশ্বস্ত করলেন যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত।
সেই সময়ে অল্প বয়সে যারা বিধবা হতো, তাদের নিরাপত্তাহীনতার সুযোগ নিয়ে তাদের ওপর শ্বশুর বাড়ির, পাড়া-পড়শির, এমন কি নিজের পিতৃ পরিবারের সদস্যরাও নানারকম অত্যাচার করত। বিধবাদের অসহায়ত্বের কারণে প্রকাশ্যে বা গোপনে তাদের ওপর অহরহ দৈহিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন চলত। সেই সঙ্গে আরও বহুভাবে অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল সমাজে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অবশেষে ভারতবর্ষে ‘বিধবা বিবাহ আইন’ পাস হয় ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই। তিনি নিজে উপস্থিত থেকে সামাজিকভাবে সানন্দে বিবাহ দেন নিজ পুত্রকে এক বিধবা নারীর সঙ্গে।
শিক্ষার, বিশেষত নারী শিক্ষার, প্রসার ও অগ্রগতি
বহুমুখী কর্মকাণ্ডের ভেতর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কালীকৃষ্ণ মিত্র, তাঁর সহোদর নবীনকৃষ্ণ মিত্র, প্যারিচাঁদ সরকার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার সহকারে বারাসতে জেলা স্কুলসহ একাধিক উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, বারাসতে বাংলার সর্বপ্রথম এবং অভিন্ন শিক্ষাক্রমের ও অসাম্প্রদায়িক (মিশনারি, মাদ্রাসা ও টোল বহির্ভূত) চেতনার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ভারতের স্বাধীনতা বা ভারত বিভাগের একশো বছর আগে অর্থাৎ ১৮৪৭ সালে। এর আগে উনিশ শতাব্দীর বিশের দশক থেকেই মিশনারিদের গড়া মেয়েদের স্কুল কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কিন্তু সেখানে হিন্দু-মুসলমান ঘরের কোনো মেয়েই পড়তে যেত না ভয়ে যে তাদের খ্রিস্টান করে দেবে এই স্কুল। তাদের সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক ছিল না এজন্যে যে স্কুলের কারিকুলামে যথেষ্ট খ্রিস্টান ধর্মের কথা লিপিবদ্ধ ছিল। দু’চারজন বস্তিবাসী শিশু যেত সেসব স্কুলে যাদের প্রধান আকর্ষণ ছিল সেই স্কুলে পরিবেশিত বিনা পয়সার খাবার ও উপহার। ফলে সেসব স্কুল অচিরেই ঝরে পড়েছে। বারাসতে বালিকাদের জন্যে এই উচ্চ বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন বিদ্যাসাগর স্বয়ং। কিন্তু স্কুলঘর নির্মাণের আগেই, মানে ১৯৪৬ সালেই, বিস্তর আলাপ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নবীনকৃষ্ণের বাড়ির একটি ঘরে মাত্র তিনটি মেয়ে নিয়ে স্কুল শুরু করে দেন বিদ্যাসাগর। নবীনকৃষ্ণ মিত্রের কন্যা বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহের পাত্রী কুন্তিবালাই এই স্কুলের প্রথম ছাত্রী এবং সর্বপ্রথম ক্লাসের তিন ছাত্রীর অন্যতম।
১৯৪৮ সালে স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুলটিকে সরকারি নথিভুক্ত করতে দরখাস্ত করলে কলকাতা থেকে যে পরিদর্শক দল স্কুল ও তার কার্যক্রম পরিদর্শন ও যাচাই করে দেখতে বারাসত আসেন, তাদের মধ্যে ছিলেন জন ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন। স্কুল পরিদর্শন করে খুবই সন্তুষ্ট হন স্কুল পরিদর্শকদল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সরকারি নথিভুক্ত হয়ে যায় সেই স্কুল। এরপরে কলকাতা গিয়েই বেথুন মেয়েদের জন্যে একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন পরে যা বেথুন স্কুল নামে বিখ্যাত হয়ে যায়। বারাসতের মেয়েদের স্কুলের কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসাবে দক্ষতার সঙ্গে স্কুল পরিচালনা ও শিক্ষকতার জন্যে কলকাতা থেকে বারাসত পায়ে হেঁটে আসতেন বিদ্যাসাগর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বেথুন স্কুল (কলেজ) স্থাপনেরও আগে ১৯৪৬ সালে বারাসতে মেয়েদের জন্যে অভিন্ন কারিকুলামের এই হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে সকলেরই তা চোখে পড়ে। ফলে গোঁড়া হিন্দু সমাজ মিত্র ভ্রাত্যদ্বয়সহ মেয়েদের এই হাইস্কুলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে সমাজচ্যুত করে দেয়। তারপরে আরও প্রায় পৌনে দুশো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু সেই মেয়েদের স্কুল আজো “বারাসত কালীকৃষ্ণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়” নামে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে স্বস্থানে—মাথা উঁচু করে। যদিও অধিকাংশ মানুষই জানে না এর জন্মকথা, এর সুদীর্ঘ ইতিহাস, জানে না এটাই এই সমগ্র অঞ্চলের সর্বপ্রথম সর্বসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।
শিক্ষাবিদের ভূমিকায় বিদ্যাসাগর অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। বাংলা ভাষার প্রসার ও উন্নয়নে এবং অন্যান্য ভাষা, বিশেষ করে ইংরেজি ও সংস্কৃত থেকে মণিমুক্তো আহরণ করে অর্থাৎ বিদেশি ভাষায় রচিত মনোগ্রাহী পাঠ্যবস্তু বাংলায় অনুবাদ করে বাংলার ছেলেমেয়েদের নতুন কিছু উপহার দিতে তিনি এতটাই সময় ব্যয় করেছেন, যে তাঁর নিজের সৃজনশীল ও মৌলিক লেখার জন্যে ততটা সময় দিতে পারেননি। এটাই ছিল বিদ্যাসাগরের বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব। নিজের খ্যাতি বা সুনামের চাইতে সমাজের কল্যাণ ও অগ্রগতির দিকে তাঁর নজর ছিল অনেক বেশি।
বাংলা ভাষার সংস্কার ও আধুনিকায়ন
বিদ্যাসাগরই প্রথম বাংলাকে আধুনিক ও ব্যবহারযোগ্য ভাষা হিসেবে গড়ে তোলেন। তার আগে বাংলা ভাষার ব্যবহার ছিল মধ্যযুগীয়। সেই বাংলা দিয়ে ধোপাবাড়িতে পাঠানো পোশাকের তালিকা তৈরি করা যেত। তৈরি করা যেত বাজারের ফর্দ, কাঁচাবাজারের রশিদ। কিন্তু সেই ভাষায় রোমান্টিক প্রেমপত্র বা আধুনিক সাহিত্য রচনা ছিল প্রায় অসম্ভব। বিদ্যাসাগর তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার সঙ্গে সার্বক্ষণিক চিন্তা ও মননের সংমিশ্রণে এক অসাধ্য সাধন করেন। তিনিই প্রথম ‘বাংলা লিপি’ সংস্কার করে তাকে সংস্কৃতের নাগপাশ থেকে—কতগুলো অপ্রয়োজনীয় বর্ণ থেকে—বেছে বেছে বাংলার জন্যে প্রয়োজনীয়, গতিশীল ও পরিচ্ছন্ন বর্ণমালা প্রণয়ন করেন। যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলার শব্দ ও পদ সাজিয়ে বাক্য রচনা করে তিনি এই ভাষাকে যুক্তিবহ, সহজতর, শ্রুতিমধুর ও অপরবোধ্য করে তোলেন। অর্থাৎ বাংলা ভাষাকে বিশেষ করে বাংলা গদ্যকে মসৃণ, মধুর ও সকলের বোধগম্য করে পরিবেশনের চেষ্টা করেন বিদ্যাসাগর। বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক রূপকার তিনিই। বিদ্যাসাগরের অমর কীর্তি তিনি রচনা করেছেন যুগান্তকারী শিশুপাঠ্য বর্ণপরিচয় বইটি। ১৮৫৫ সালে লেখা হয়েছিল বর্ণপরিচয় যা ১৬৫ বছর পরে, আজও অনেক বাঙালি শিশুর প্রথম পাঠ্য পুস্তিকা। বর্ণপরিচয় ছাড়াও একাধিক পাঠ্যপুস্তক ও ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তিনি। গদ্যের ভেতরেও এক ধরনের ছন্দসৃষ্টি করেন বিদ্যাসাগর। প্রতিটি বর্ণ দিয়ে শিশুর উপযোগী সহজ শব্দ জুড়ে দিয়েছেন তিনি বর্ণপরিচয়ে যাতে প্রতিটি বর্ণের সঙ্গে পরিচিত হতে হতে বাংলা ভাষার বিভিন্ন শব্দের ঝংকার টের পায় ও ভাষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয়। বাংলায় শিশুর প্রথম পুস্তুক হিসাবে—বাংলা বর্ণের সঙ্গে সানন্দে প্রাথমিকভাবে পরিচিত হতে আজ থেকে ১৬৫ বছর আগে যেমন ছিল, আজও তেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ই সেরা। এছাড়া তিনি মান বাংলাকে সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, শ্রুতিমধুর এবং সংহত করে মানুষের কাছে নিয়ে আসেন। সংস্কৃত বর্ণমালা থেকে বাংলায় অপ্রয়োজনীয় বর্ণ বাদ দিয়ে বাংলা বর্ণকে ভারমুক্ত করেছেন। আজ প্রায় পৌনে দুশো বছর ধরে অগণিত বাঙালি শিশুর নিজ মাতৃভাষার সঙ্গে প্রথম বা প্রাথমিক যোগাযোগ বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয়ের মাধ্যমে।
এছাড়া তিনি বাংলা ভাষার একটি অতি মৌলিক, প্রয়োজনীয় ও জটিল কর্ম সম্পাদন করেছিলেন। বাংলায়, বিশেষ কর গদ্যে, প্রথম যতি চিহ্ন যোগ করে তিনি ভাষাটিকে শুধু প্রাঞ্জল করেননি, বক্তব্যকে অর্থপূর্ণ ও লেখনিকে পাঠযোগ্য করে তোলেন। পাঠকের পক্ষে তখন পুরো বাক্যটি হৃদয়াঙ্গম করা সহজতর হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষাকে অন্য ভাষার সঙ্গে তুলনীয়, আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও বোধগম্য করে তুলেছেন বিদ্যাসাগর। বিশেষ করে তাঁর ব্যবহৃত দাড়ি (।), সেমিকোলন (;), কমা (,), বিস্ময়বোধক (!), প্রশ্নবোধক (?) যতি চিহ্ন বা বিরাম চিহ্নের সংযোজন, দীর্ঘ বাক্যকে যথাস্থানে ভেঙে বা বিরতি দিয়ে গোটা বাক্যকে কম দুরূহ ও জটিলতামুক্ত করে ফেলে।
বাংলা গদ্যকে তিনি সাহিত্য গুণসম্পন্ন ও সকল রকম ভাব প্রকাশে সক্ষম একটি সমৃদ্ধ ভাষা হিসাবে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন বলেই বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের এক নতুন চেহারা দিয়েছিলেন, যার জন্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আধুনিক বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের ‘প্রথম শিল্পী’ বলে অভিহিত করেছেন। বিদ্যাসাগরের কয়েকটি বিখ্যাত গদ্যগ্রন্থের নাম বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস ও ভ্রান্তিবিলাস । তাঁর বেশিরভাগ লেখায় উদাহরণস্বরূপ তিনি তাঁর প্রস্তাবিত যতি চিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন ও সুসংহত বাক্য গঠনের জন্য পদ ও শব্দকে সুবিন্যস্ত করেছিলেন।
কিংবদন্তিসম দয়ার সাগর
জ্ঞানের সাগর বিদ্যাসাগর কেবল তাঁর প্রজ্ঞা দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাই নয়। অন্যের প্রতি সহমর্মিতা ও মানবিকবোধে আচ্ছন্ন এই সমাজ সচেতন মানুষটি সমাজে স্বামীহারা নারীদের দুরবস্থা মোচনে অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন বিধবাবিবাহের মতো আধুনিক সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে, বাল্যবিবাহ রোধ করে, বহুবিবাহ ও কৌলীণ্যপ্রথা উচ্ছেদের অভিযান চালিয়ে। এ ছাড়া বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত এই ব্যক্তিত্ব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে ‘দয়ার সাগর’ নামে পরিচিত ছিলেন। গরিব, আর্ত ও পীড়িত কোনো ব্যক্তি কখনোই তাঁর দুয়ার থেকে শূন্য হাতে ফিরে যেত না। এমনকি তাঁর নিজের চরম অর্থসঙ্কটের সময়ও তিনি নানাভাবে আর্থিক ও বিভিন্ন রকম পার্থিব সাহায্য দিয়ে পরোপকার করেছেন। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তসহ অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তিকে তিনি তাঁদের চরম দুর্দিনের সময় বিভিন্ন পন্থায় আর্থিক সহযোগিতা করেছেন, তাদের দুঃসময়ে পরম স্বজনের মতো পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। পিতামাতার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক ভক্তি ও বিরল নিষ্ঠা বাংলায় প্রবাদপ্রতিম। ছোটবেলায় পাঠ্যপুস্তকে আমরা পড়েছি, মার কাছে যাবেন সেদিন কথা দেওয়া থাকায় নদীপাড়ে এসে যখন দেখলেন, আসন্ন ঝড়ের জন্যে কোনো নৌকোই নেই ঘাটে, তিনি আর দেরি না করে উত্তাল নদীতে ঝাঁপ দিয়ে এই ঝড়ো হাওয়ায় প্রচণ্ড ঢেউ আর প্রবল স্রোতে ভেসে যেতে যেতে সাঁতার কেটে দমোদর নদী পার হয়ে গিয়ে উঠেছিলেন মাকে দেয়া কথা পূরণ করতে।
মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিদ্যাসাগরের মধ্যে দেখেছিলেন ‘প্রাচীন ঋষির প্রজ্ঞা, ইংরেজের কর্মোদ্যম ও বাঙালি মায়ের হৃদয়বৃত্তি।’ বিদ্যাসাগরের অফুরন্ত অর্জন ও বৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বিদ্যাসাগরচরিত’সহ চারখানি প্রবন্ধে বিভিন্নভাবে স্মরণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন বিদ্যাসাগরের মধ্যে ইহজাগতিকতা, যুক্তিবাদী শিক্ষা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও নারীশিক্ষার প্রসার, নতুন গদ্যরীতি, সমাজসংস্কার, বিধবাবিবাহ, পাঠ্যসূচি থেকে অলৌকিকতার বিলুপ্তি, জ্যোতিষ শাস্ত্রের পরিবর্তে জ্যোতির্বিদ্যার শিক্ষা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, মানবমুখিনতার মতো বৈশিষ্ট্য আবির্ভূত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি বাংলাভাষার পূর্ণাঙ্গ অবয়ব নির্মাণ। রবীন্দ্রনাথ বলেন, ‘বঙ্গ প্রতিমায় “চক্ষুদান” করেছিল বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় ।’
সবশেষে, বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সার্বিক মূল্যায়ন। ১৮৯৫ সালের ২৯ জুলাই। বিদ্যাসাগরের জন্যে আয়োজিত এক স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠচিত্তে এই অসাধারণ মহান ব্যক্তিটির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন যা পরে সাধনা পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি অতি শ্রদ্ধাশীল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেদিন বিদ্যাসাগরের চরিত্রের ও কর্মের ওপর বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ‘আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি। দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ। তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।’
বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ এই অতি বিরল, ক্ষণজন্মা, প্রগতিশীল সমাজসংগঠক, দয়ার সাগর ও সৃজনশীল মানুষটির তুলনা কেবল তিনি নিজেই।
পূরবী বসু, প্রাবন্ধিক এবং কথাসাহিত্যিক, যুক্তরাষ্ট্র