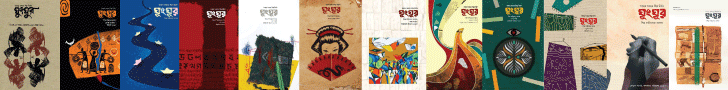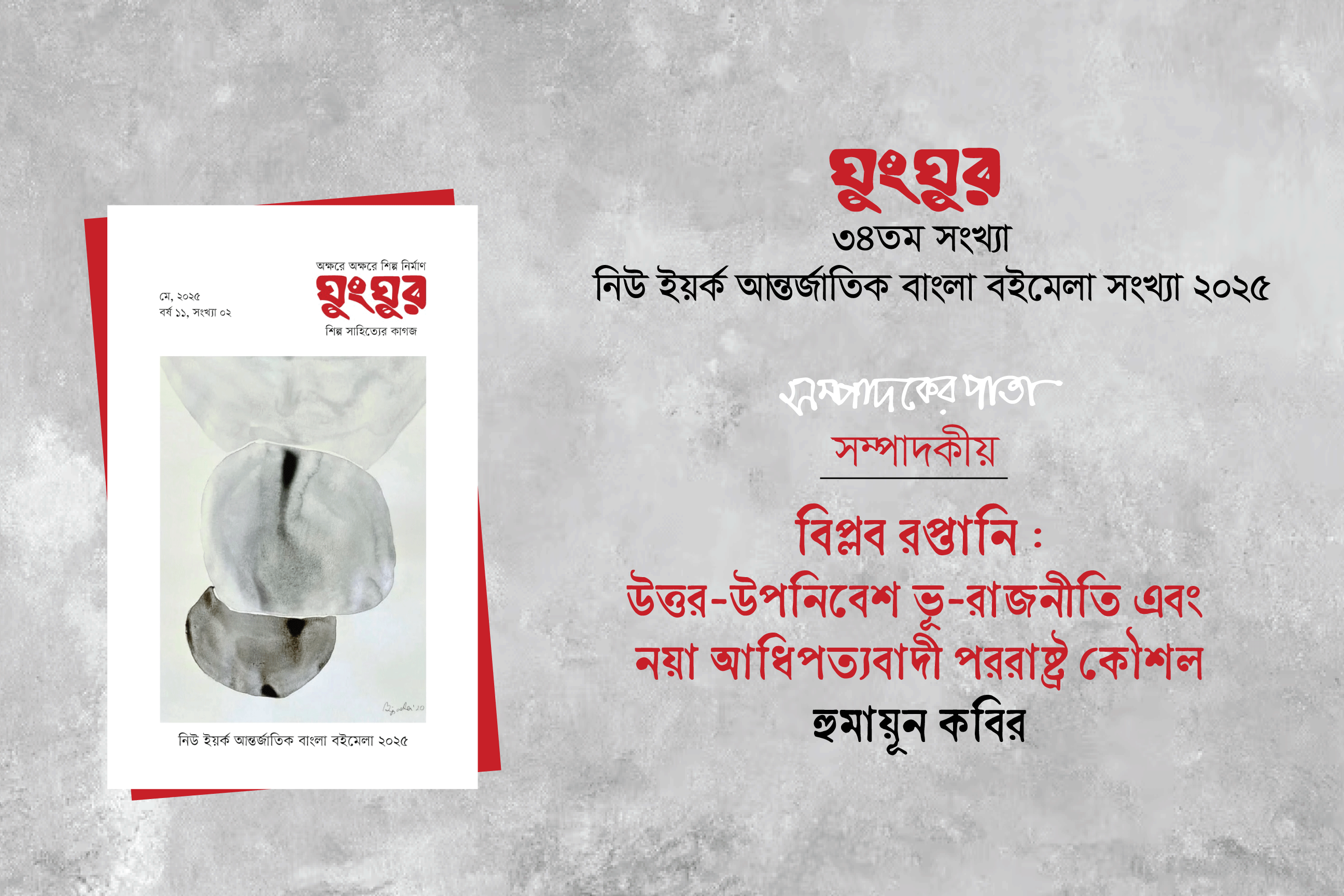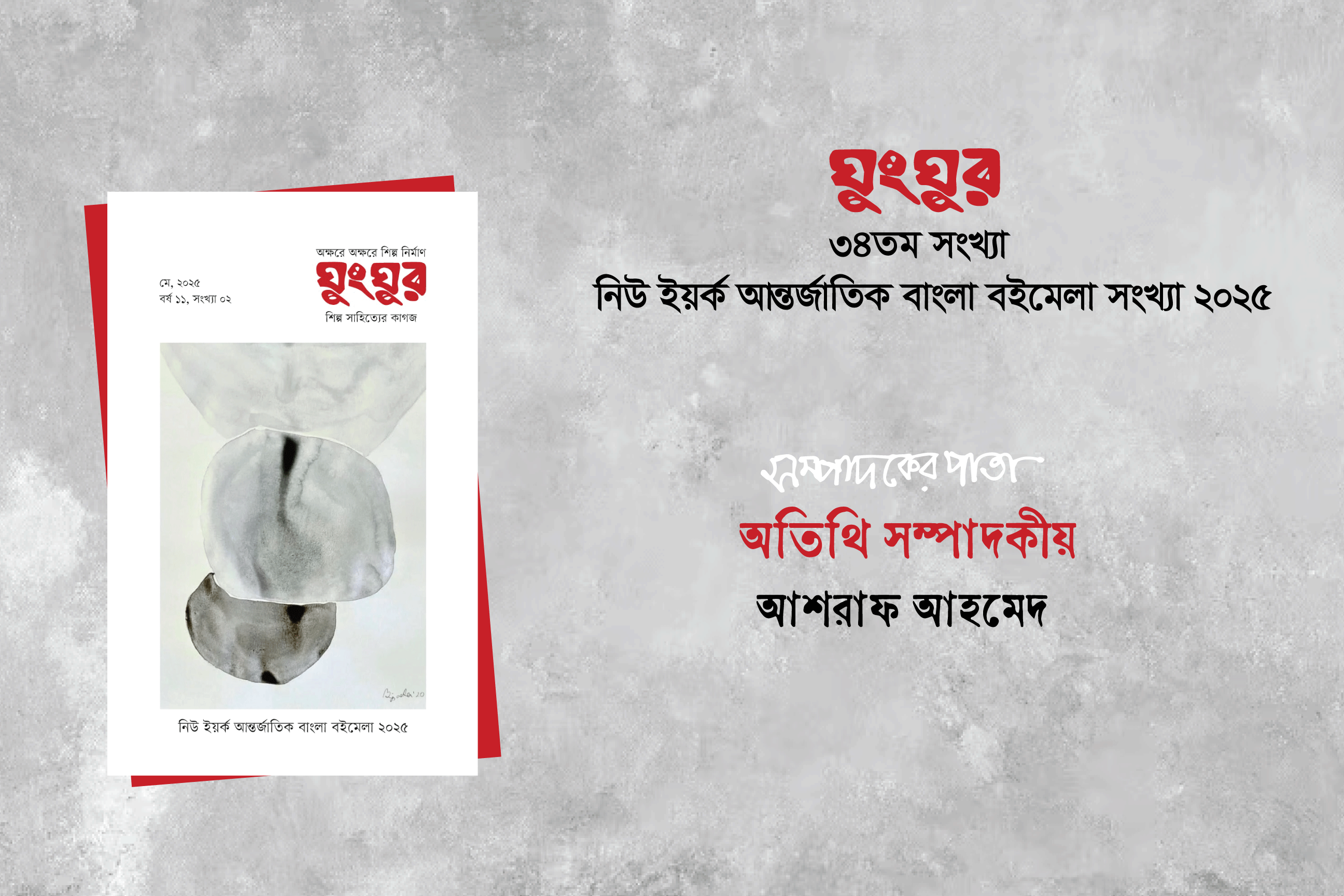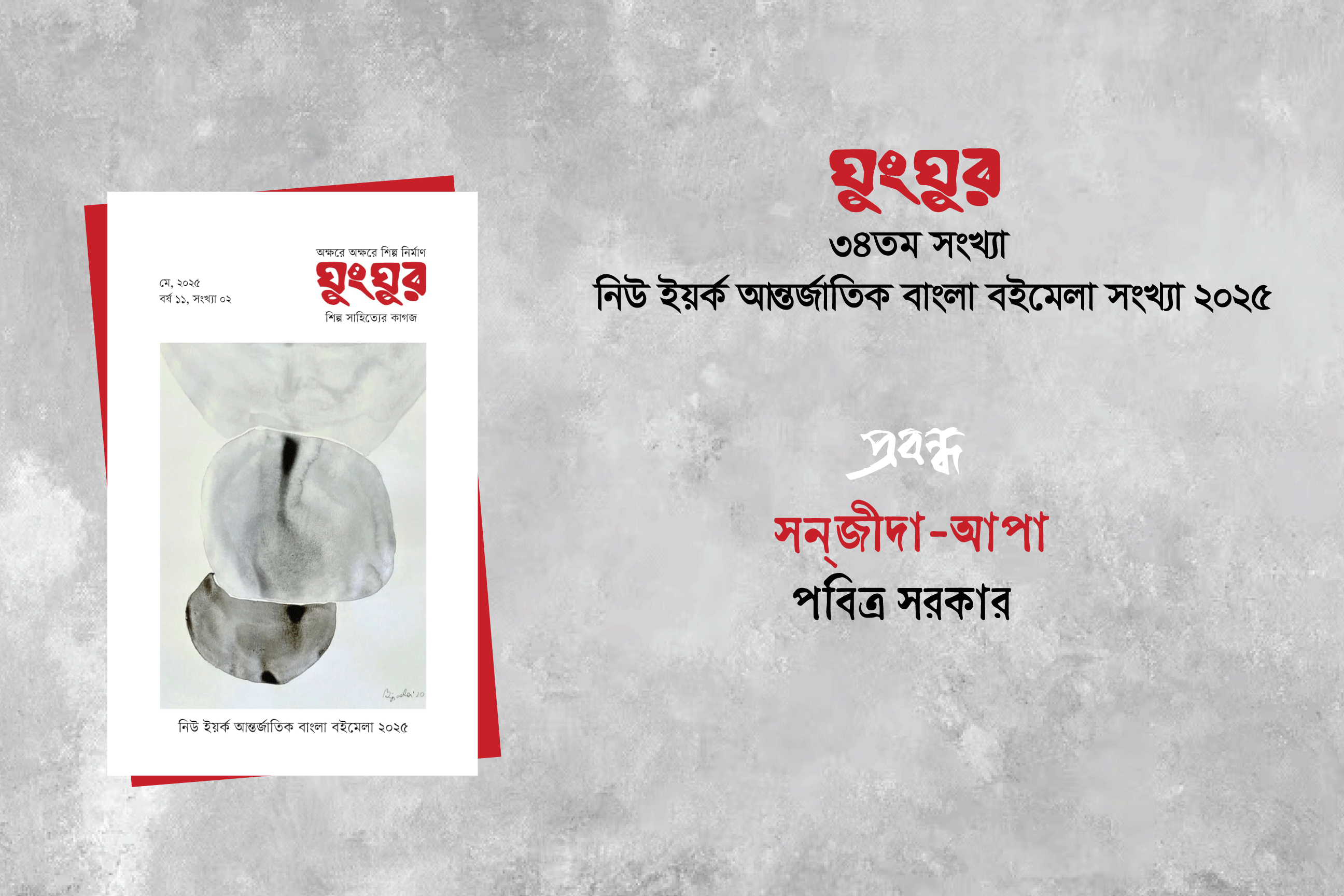কালীঘাটের জন্মকথা
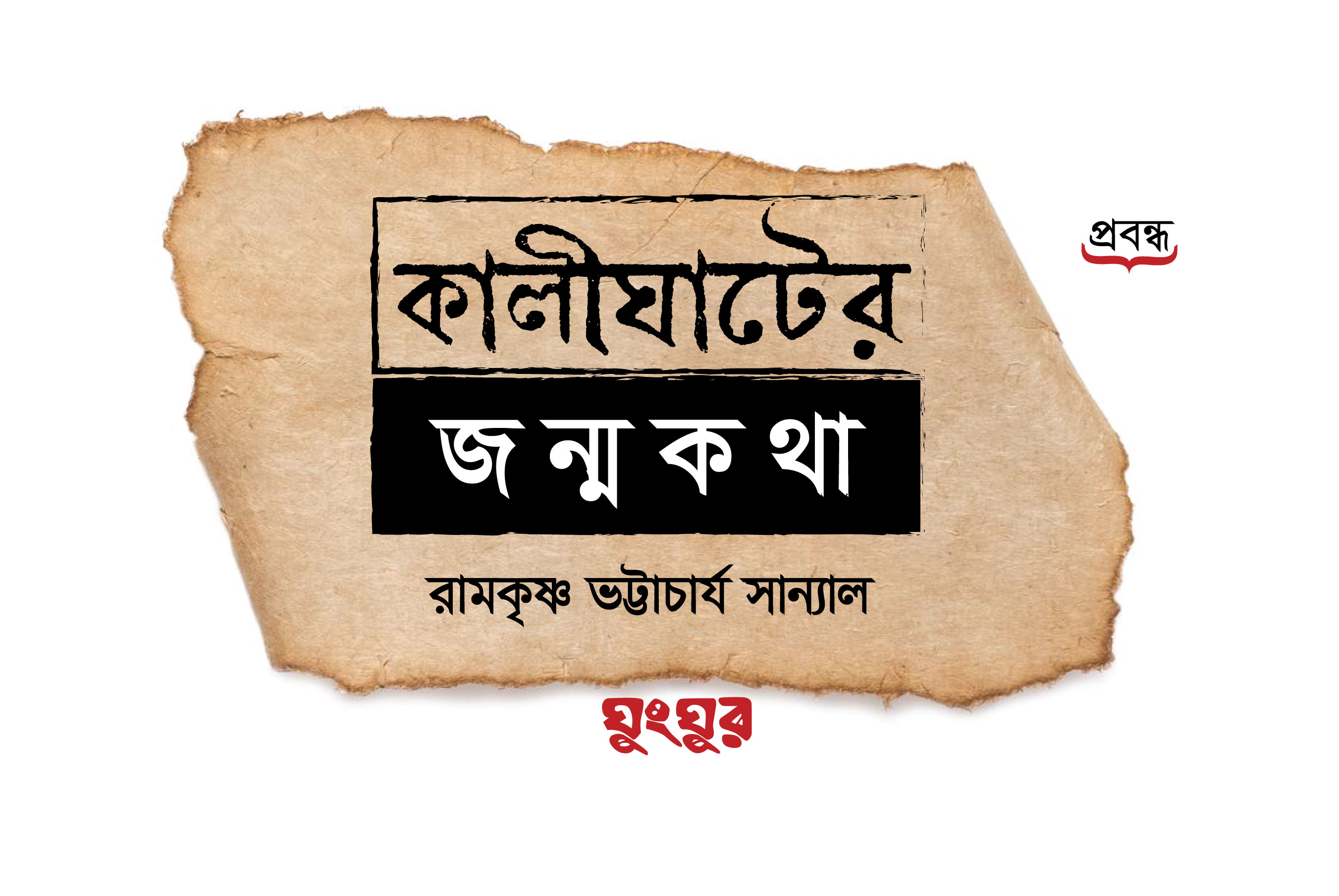
খোদ কলকাতায় যে-কোনো বর্ণের লোক এবং ব্রাহ্মণদের ভাত খাওয়া বারণ? কারণ? মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি। মহারাজা নন্দকুমার ছিলেন ব্রাহ্মণ। মুর্শিদাবাদী এই ব্রাহ্মণের ফাঁসি সকলে মেনে নিতে পারেননি। খিদিরপুরের কুলি-বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রাজা নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। আজ পর্যন্ত ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে কারও প্রাণ এভাবে নেওয়া হয়নি, মহারাজা নন্দকুমার ছাড়া। তবে, পলাশি যুদ্ধের সময় নন্দকুমারের ভূমিকাটা আজও অস্পষ্ট। ইংরেজরা তাঁর নাম লিখতেন— NUNCOOMAR — সে কালের রীতি অনুযায়ী।
১৮৮৬ সালে প্রকাশিত ‘দ্য ট্রায়াল অব মহারাজা নন্দকুমার’ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, মিডলটনের পত্রালাপ দাখিল করা হলে ওয়ারেন হেস্টিংস ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হতেন। ওয়ারেন হেস্টিংস, তাঁর বন্ধু ইলাইজা ইম্পের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ বের করেন। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি ওয়ারেন্ট হেস্টিংসের জীবন ও কর্মকাল এবং কলকাতার একটি বিতর্কিত অধ্যায়। মাত্র ২৩ বছর বয়সে সিরাজউদ্দৌলা ১৫ এপ্রিল ১৭৫৬ সালে নবাবি লাভ করেন। তাঁর নবাবির সময়কাল ছিল মাত্র ১ বছর ২ মাস ৮ দিন অর্থাৎ ৪৩৪ দিন। এ সময়ের মধ্যে নবাব সিরাজউদ্দৌলা দু-দুবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে কলকাতা অভিযানে স্বয়ং নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং ইংরেজদের পরাজিত করেছেন। পূর্ণিয়ার যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করেছেন। প্রধান সেনাপতি মিরজাফর, সেনাপতি রাজা দুর্লভরাম, উমিচাঁদ, রাজা রাজবল্লভ, ইয়ার লতিফ, জগৎশেঠ, ঘসেটি বেগম, ইংরেজ সেনাপতি ওয়াটসন, ওয়াটস, ক্লাইভ প্রমুখ সিরাজউদ্দৌলার নবাবির প্রথম দিন থেকে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকতা, রাজদ্রোহ ও দেশদ্রোহিতায় লিপ্ত থেকে নবাবকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল। তাতে একদিনের জন্য তরুণ নবাবের ব্যক্তিগত জীবনে কোনও আরাম-আয়েশ ভোগ-বিলাসের সময়-সুযোগ ছিল না। কিন্তু পলাশির প্রহসনের যুদ্ধে ইংরেজরা ক্ষমতায় আসার পর তাদের এদেশীয় চাকরবাকর, বুদ্ধিজীবী ও লেখকরা বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে চরিত্রহীন লম্পট অপদার্থ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে, তাদের বক্তব্য ইতিহাস বা জনগণ বিশ্বাসই করেছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগের মূল কারণ বাংলার স্বাধীনতা হরণের চক্রান্তকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে পরিকল্পিত চরিত্রহনন ও অপপ্রচার।
যদিও তুর্কি সিরাজের বঙ্গপ্রীতি কেন থাকবে, এটা নিয়ে অনেকেরই প্রশ্ন আছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়— সিরাজের মনোগত ইচ্ছে ছিল, দিল্লির মসনদ দখল করা। ইংরেজরা এটা মেনে নিতে পারেনি। অন্ধকূপ হত্যা, যেটা আদতে ঘটেইনি, নবাব সিরাজউদ্দৌলার ওপর সেটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।
বাংলার নবাব তখন ইব্রাহিম খান৷ নবাব বলতে মুঘল সম্রাটের কর আদায়কারী। তাঁর আমন্ত্রণে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মাধ্যক্ষ জোব চার্নক ফিরে এলেন বাংলায়৷ সুতানুটি (মতান্তরে, সুতালুটি) কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম ইজারা নিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম বানাতে শুরু করলেন ব্যবসার প্রয়োজনে৷ গোড়াপত্তন হলো কলিকাতা শহরের৷ দিনটি ছিল ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ অগস্ট রবিবার৷ তবে কলিকাতা অবশ্য আরও অনেক প্রাচীন৷ ১৫৯৬ সালে সম্রাট আকবরের রাজস্ব আদায়ের নকশায় কলিকাতা বা কলিকাটা দেখানো হয়েছে৷ ইংরেজরা এর নাম দিয়েছে ‘ক্যালকাটা’৷ ইংরেজ আমলে কলিকাতা ছিল রাজধানী শহর৷ এখন কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের রাজধানী৷ আগেই বলেছি, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে জোব চার্নক নামে একজন ইংরেজ তিনটি স্নিগ্ধ গ্রাম গোবিন্দপুর, সুতানুটি আর কলকাতার তীরে পৌঁছোলেন এবং নবাবের সৈন্যদল কর্তৃক লুণ্ঠিত তাঁর কর্মস্থল হুগলিতে আর ফিরে গেলেন না। তিনি চাইলেন এই গ্রামগুলিতেই শুরু হওয়া ব্যাবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করবেন। এইখান থেকেই কীভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শুরু হলো— তার একটা নমুনা পেশ করি। সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা গ্রাম তিনটি ছিল মুঘল সম্রাটের খাসমহলের অন্তর্গত। এই গ্রাম তিনটির জায়গিরদারি সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের হাতে ছিল। ব্রিটিশ বসতি অন্যান্যদের অধীনে থাকা আরও আটত্রিশটি গ্রাম দিয়ে ঘেরা ছিল।
১৭১৭ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল সম্রাট ফারুকশিয়ারের কাছ থেকে এইসব গ্রামের জমিদারি সত্ত্ব কেনার অধিকার অর্জন করলেও, তৎকালীন জমিদারদের কাছ থেকে তারা এই গ্রামগুলি ক্রয় করতে পারেনি। সাবর্ণ রায়চৌধুরীরাও ব্রিটিশদের এই তিনটি গ্রাম ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। জানা যায়, ব্রিটিশরা মুঘল রাজদরবারে ঘুষ দিয়ে এই গ্রাম তিনটির ইজারা কেনার অনুমতি আদায়ে সমর্থ হন। ১৬৯৮ সালে সাবর্ণরা ইংরেজদের হাতে গ্রাম তিনটি তুলে দেন। ইংরেজরা বার্ষিক ১,৩০০ টাকা রাজস্বের বিনিময়ে গ্রাম তিনটির ইজারা ক্রয় করে নেন। চুক্তিপত্রটি ফারসি ভাষায় লেখা হয়েছিল। এর একটি নকল বড়িশার সাবর্ণ সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। এইভাবে শুরু হলো এক ইতিহাস। প্রথমেই কাঁচা বাড়িগুলি ভেঙে পাকা বাড়ি উঠতে দেখা গেল, ব্রিটিশরা ইজারা নেওয়া গ্রামগুলিকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলল এক দুর্ভেদ্য দুর্গে। দরবারি উত্থান-পতন আর ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর থেকে কলকাতা বিকশিত হতে শুরু করল দ্রুত। কিন্তু সেই সময়কার দলিল বলছে, এটা আদপেই কোনো প্রামাণ্য শহর ছিল না। না ছিল রাস্তায় আলো, না ছিল পাকা রাস্তা, না ছিল পরিস্রুত জল বা পাকা নর্দমা। অকালমৃত্যুর হার ছিল অত্যধিক বেশি। তবু এ-শহর অনেককে কাছে টানল। তার কারণ একটাই! এই শহরের অবস্থান! জলপথে বাণিজ্য করবার সুবিধা! শেঠ আর বসাকরা আগে থেকেই এখানে সুতার ব্যবসা করতেন। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পর্তুগিজদের বাণিজ্য-ঘাঁটি ছিল সুতানুটি। পরবর্তীকালে ডাচ (ওলন্দাজ) হুগলি নদী থেকে খাল কেটে এখনকার মধ্য কলকাতাকে সুরক্ষিত করে। ইংরেজদের সুরক্ষিত করতে তৈরি হয় পুরোনো ফোর্ট উইলিয়াম ১৬৯৬-এ। ১৭৫৬ সালে বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লা এই শহর অবরোধ ও অধিকার করলে খোদ ইংল্যান্ডেও এই শহর খ্যাতিলাভ করে। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতে সিরাজ প্রায় ৪৩ জন ব্রিটিশ বাসিন্দাকে একটি ছোটো গুদামঘরে গুমখুন করান। এই গল্পটা একেবারেই বানানো!
রবার্ট ক্লাইভ পরের বছরই কলকাতা পুনরুদ্ধার করেন। হুগলি নদীর জলপথে ইংরেজ যাত্রী এবং বাণিজ্যপোতের প্রসার ঘটে। ১৮৫০-এর দশকে রেলপথ চালু হলে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ বৃহত্তর মাত্রা পায়। এই শহর দেশের বৃহত্তম বাণিজ্যস্থল এবং পাশ্চাত্য ঘরানার ব্যবসায়িক ঔপনিবেশিক এই শহরে নির্দিষ্টভাবে ঘিঞ্জি আর অপরিকল্পিত এলাকায় দেশীয় বাসিন্দাদের জন্য আলাদা পাড়া ছিল মূল শহরের পূর্ব আর উত্তর ঘেঁষে। সুপরিকল্পিত এবং ফাঁকা জায়গায় বসতি ছিল ইউরোপিয়ানদের দক্ষিণ তথা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। স্বাধীনতার পরে এই সাহেবপাড়াগুলি দেশীয় ধনীদের বাসস্থান বা পার্ক স্ট্রিট প্রভৃতির মতো বাণিজ্যিক অঞ্চল হয়ে ওঠে। পার্ক স্ট্রিটের আগের নাম ছিল— বেরিয়াল গ্রাউন্ড রোড। লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ১৫৭০ সালের কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন। তাঁর জন্মের তৃতীয় দিনে তাঁর মা, পদ্মাবতী মারা যান। স্ত্রীর মৃত্যুতে লক্ষ্মীকান্তর বাবা জিয়া গঙ্গোপাধ্যায় ভেঙে পড়েন, আর সংসার ত্যাগ করে তপস্বী হবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। ছেলে লক্ষ্মীকান্তর ভার তিনি নিজের দীক্ষাগুরু আত্মারাম ব্রহ্মচারীর হাতে সঁপে, বেরিয়ে পড়েন তীর্থ-পরিব্রাজক হয়ে, আর ধর্মপ্রচারক রূপে থিতু হন কাশীতে। সন্ন্যাস নেবার পর তাঁর নামকরণ হয় কামদেব ব্রহ্মচারী। ব্রিটিশ ইতিহাসকারদের নথিতে তিনি এই নামেই পরিচিত। প্রকৃতি, বুদ্ধিতত্ত্ব, অহংকার, পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় ও পুরুষ ইত্যাদি তত্ত্বমূলক দর্শনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের কারণে কামদেবের খ্যাতি ছিল।
লক্ষ্মীকান্তকে স্তন্যদানের জন্য আত্মারাম ব্রহ্মচারী যাঁকে ধাত্রী নিয়োগ করেন, তিনি অব্রাহ্মণী ছিলেন। ব্যাপারটি বৈপ্লবিক ছিল নিশ্চয়ই, কেন-না কামদেবের ঊর্ধ্বতন একাদশতম পুরুষ পীতাম্বর গঙ্গোপাধ্যায়কে কুলীনত্ব দিয়েছিলেন বল্লাল সেন। তা ছাড়া দক্ষিণ-রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের মেলবন্ধন-কর্তা দেবীবর ঘটক তখন এতই ক্ষমতাসম্পন্ন যে, তিনি ফতোয়া দিলে, একজন ব্রাহ্মণ কুলীন থেকে অকুলীন হয়ে সমাজের আধিপত্য-কাঠামোয় নিচের স্তরে চলে যেতে পারতেন।
কামদেব ব্রহ্মচারীর ঠাকুর্দা পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন কাটোয়ার আমাটি গ্রামের নিবাসী। পরে তিনি হুগলি জেলার গো-হাট্য-গোপালপুরে চলে যান, এবং বাবা পরমেশ্বরের অধ্যাপনা, যাজন ও মন্ত্রদানের পারিবারিক পেশা গ্রহণ না করে, ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করে হুমায়ুনের সৈন্যবাহিনীতে আফগানবাহিনীর স্থানীয় অধিপতি হিসেবে যোগ দেন। এখন জায়গাটির নাম গোঘাট। পঞ্চাননের সময়ে গোরুর হাট বসত বলে গোহট্ট। বিভিন্ন যুদ্ধে ঘোড়ায় চেপে সাহসী লড়াইতে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন, এবং সমরনায়ক হিসাবে সম্রাটের কাছ থেকে ‘শক্তি খান’ উপাধি পান। পরবর্তীকালে আফগানদের আনুগত্য কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত সহায়ক ছিল। ইতিহাসে তিনি ‘পাঁচু শক্তি খান’ নামে খ্যাত। তুর্কি ভাষায় শব্দটি হলো ‘সখৎ খাঁ’, অর্থাৎ দুর্ধর্ষ রাজকুমার। সৈন্যবাহিনী থেকে অবসরের পর পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় হালিশহরে বসত গড়েন। তিনি বিক্রমপুর থেকে বৈদ্য, কঙ্গোর থেকে কায়স্থ, উড়িষ্যা ও তামিলনাড়ু থেকে যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ এনে সবাইকে আলাদা আলাদা পল্লি বা পট্টিতে থাকার ব্যবস্হা করে দেন। সেসব ওড়িশি আর তামিলদের আজ আর আলাদা করে চেনা যায় না। অন্যান্য পেশার লোকজনও এনেছিলেন তিনি, যাঁদের মধ্যে পরবর্তীকালে খ্যাতি পান মাটির কাজের লোক বা কুমোরেরা; ফলে হালিশহর (প্রকৃতপক্ষে ‘হাবেলি শহর’) কুমারহট্ট নাম পেয়ে যায়। ষোলো বছরের কম বয়সের যে-সমস্ত শূদ্র ছেলেদের উনি যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দি করতেন, তাদের অনেককে কায়স্থ বর্ণে উন্নীত করে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন।
ওলন্দাজ পর্যটক ভান-দ্রেন ব্রুক ১৫৬০ সালে হালিশহরের প্রতিপত্তিতে বেশ অবাক হয়েছিলেন। হালিশহরের কালী কাতলা ঘাট থেকে ছিল পূর্ববঙ্গে ভূষণা যাবার জলপথ। পাঁচু শক্তি খানের পর তাঁর ছেলে শম্ভুপতি, এবং নাতি জিয়া বা কামদেব ব্রহ্মচারী, হালিশহরকে শিক্ষা এবং বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। অষ্টাদশ শতকে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে নবদ্বীপের প্রতিপত্তির আগে, পাঁচু শক্তি খান প্রতিষ্ঠিত হালিশহর শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে নিম্নবঙ্গে সর্বাধিক খ্যাতিপ্রাপ্ত ছিল। বহু টোল এবং পণ্ডিতমশায় ছিলেন সেখানে। এমনকি চৈতন্যদেব যে হালিশহরের জনৈক পণ্ডিতমশায়ের কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন, সে প্রসঙ্গ আছে বৈষ্ণব সাহিত্যে। সম্ভবত কামদেবের সন্ন্যাস, আর তাঁর মুঘল-খেতাব প্রাপ্তির পর, লক্ষ্মীকান্ত হালিশহরে বসবাস না-করায়, বসতটি ক্রমশ গুরুত্ব হারিয়ে ফ্যালে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত জিয়া গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৫৩৫-১৬২০) কোনো ছেলেপুলে হয়নি। তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতীর বয়স, লক্ষ্মীকান্তর জন্মের সময়ে ছিল কুড়ি। রজঃস্বলা হবার সাত বছর পরও পদ্মাবতীর সন্তান না হওয়ায়, আত্মীয়স্বজনরা বিরক্ত, ক্রুদ্ধ আর হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তা সত্ত্বেও জিয়া আবার বিয়ে করেননি, কেন-না পদ্মাবতী সত্যিই সুন্দরী ছিলেন। অতীব সুন্দরী ছিলেন বলেই, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকন্যা হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ছেলের বউ করে এনেছিলেন শম্ভুপতি। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণরা কুলীনের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু কুলীন কন্যাকে বিয়ে করতে পারতেন না। কুলগুরুর পরামর্শে জিয়া ও পদ্মাবতী দুজনে তাঁদের পারিবারিক ঈশ্বরী কালীক্ষেত্রের কালীমূর্তির কাছে তিন দিন তিন রাত্রি সাষ্টাঙ্গ প্রার্থনা জানাবার পর, তৃতীয় রাতে, পদ্মাবতী, মন্দিরসংলগ্ন জলাশয়ের উপরিতলে, মন্দিরের পূর্বদিকে, ভাসমান জ্যোতির্মণ্ডলীর দিকে স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পদ্মাবতী জিয়াকে জানান, তিনি স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন যে, জলাশয়টিতে আলোর বৃত্ত দেখা দেবার পর তাতে স্নান করলে, তাঁর একটি ছেলে হবে। পরের দিন, জলাশয়টিতে স্নান করতে গিয়ে, পদ্মাবতী দেখতে পেলেন যে, জলের ভেতর থেকে একজন মহিলার ডান বাহু তাঁকে ইশারা করছে। তিনি ওই নারীর নির্দেশ শুনতে পেলেন যে, ওই জলাশয়ের তলদেশে সতীর ডান পায়ের অংশটি আজও পড়ে আছে, আর সে-কথা যেন তাড়াতাড়ি সেবায়েতদের জানানো হয়।
পদ্মাবতী ছোটোবেলায় শুনেছিলেন যে দক্ষযজ্ঞের সময়ে বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্রের দ্বারা সতীদেহের একান্নটি টুকরো কনখল থেকে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যার একটি, ডান পায়ের কড়ে আঙুল, এসে পড়েছিল, কালীক্ষেত্রের কালীমন্দির যে জায়গাটিতে, ঠিক সেখানে। পদ্মাবতীর নির্দেশে সেবায়েতরা পুকুরে নেমে একজন মহিলার অশ্মীভূত ডান পা আবিষ্কার করেছিলেন। সেটি কালীমন্দিরের লোহার সিন্দুকে চিরকালের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছিল বলে কিংবদন্তি। ঘটনাটির এক বছর পর ৯৭৭ বঙ্গাব্দে, আশ্বিন মাসের লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন বিকাল চারটে পনেরোয় লক্ষ্মীকান্তর জন্ম হয়, আর সে-কারণেই তাঁর অমন নামকরণ। তারপর থেকে জলাধারটিতে স্নান করলে ছেলেপুলে হয়, এমন গল্প ছড়িয়ে পড়ে সুবে বাংলায়।
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সার্বভৌমের লেখা ‘কালীঘাট ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থে ক্রমবর্ধমান স্নানার্থিনীদের ভিড়ের কথা বর্ণনা করা হয়েছিল। উনি গ্রন্থটিতে তাঁর নিজের বিশ্বাস এবং স্নানার্থিনীদের সন্তানপ্রাপ্তির সাফল্যের কাহিনি লিখে গেছেন। লক্ষ্মীকান্তর সময়ে অবশ্য কালীঘাট শব্দটির উদ্ভব হয়নি। বলা হতো— কালীক্ষেত্র কালীপীঠ। দক্ষিণে বেহালা থেকে উত্তরে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কালীক্ষেত্র এলাকাটি। ইংরাজদের আঁকা মানচিত্র থেকে অনুমান করা যায় যে লক্ষ্মীকান্তর ছেলেদের নাতিনাতনিদের সময়েও আদিগঙ্গা, যা এখন অত্যন্ত নোংরা টালির নালায় রূপান্তরিত হয়েছে, তা হুগলি নদীর চেয়ে চওড়া ছিল। অর্থাৎ, কিংবদন্তিটির পবিত্রতা বহাল ছিল বহুকাল পর্যন্ত। পাঁচু শক্তি খান, শ্যামরায় এবং কালী, দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাবকল্পের পূজার প্রচলন করেন পারিবারিক স্তরে। চৈতন্যদেবের প্রভাবের কারণে শ্যামরায় আর যোদ্ধা ছিলেন বলে কালী। কালীঘাটের বর্তমান বিগ্রহটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জিয়া গঙ্গোপাধ্যায়, লক্ষ্মীকান্তর জন্মের কারণে। সংলগ্ন ঘাটটি বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন লক্ষ্মীকান্তর মেজো ছেলে গৌরীর (১৬০০-১৬৬৯) নাতি কেশবরাম (১৬৫০-১৭২৬) এবং সেই সূত্রে কালীঘাট আখ্যাটির উদ্ভব। মন্দিরটি তৈরি করানো আরম্ভ করেন কেশবরামের ছেলে শিবদেব (১৭১০-১৭৯৯), আর তা ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণ করেন তাঁর উত্তরাধিকারী রাজীবলোচন। খরচ হয়েছিল তিরিশ হাজার টাকা। তাঁর বংশধর, বড়িশা-নিবাসী কালীকান্ত, উনিশ শতকের শেষাশেষি পর্যন্ত মন্দিরটির পুজো এবং অন্যান্য কাজ নিয়ন্ত্রণ করতেন। বিড়লাদের হিন্দুস্তান চ্যারিটি ট্রাস্ট মন্দিরকে সারিয়ে তোলে দেশভাগের পর। পুজো দিতে উনিশ শতক থেকেই বহু লোক আসতেন বটে, কিন্তু পরিবেশ এখনকার মতন বীভৎস ছিল না, যা টের পাওয়া যায় সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ‘কালীক্ষেত্র দীপিকা’ গ্রন্থটি থেকে। লক্ষ্মীকান্তর প্রতি শ্রদ্ধায় কালীঘাটে দক্ষিণাকালিকা কার্তিকী অমাবস্যার রাতে লক্ষ্মীরূপে পূজিত হন। পরবর্তীকালে অব্রাহ্মণরা মহালয়ার পরবর্তী কার্তিকী অমাবস্যার রাতে কালীপূজার প্রচলন করেন।
• রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সান্যাল, প্রাবন্ধিক, কলকাতা