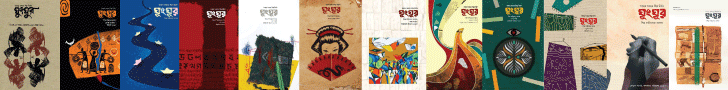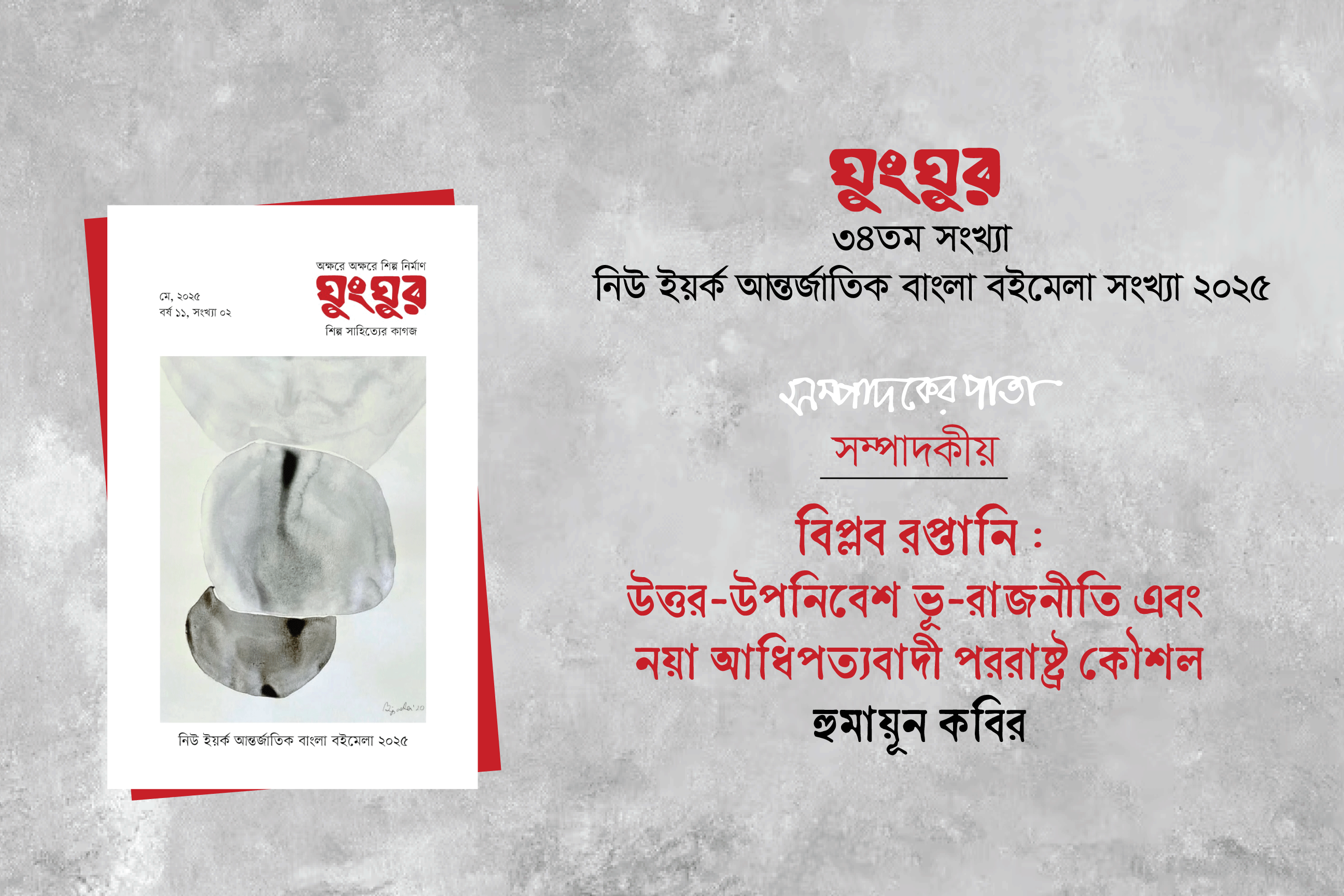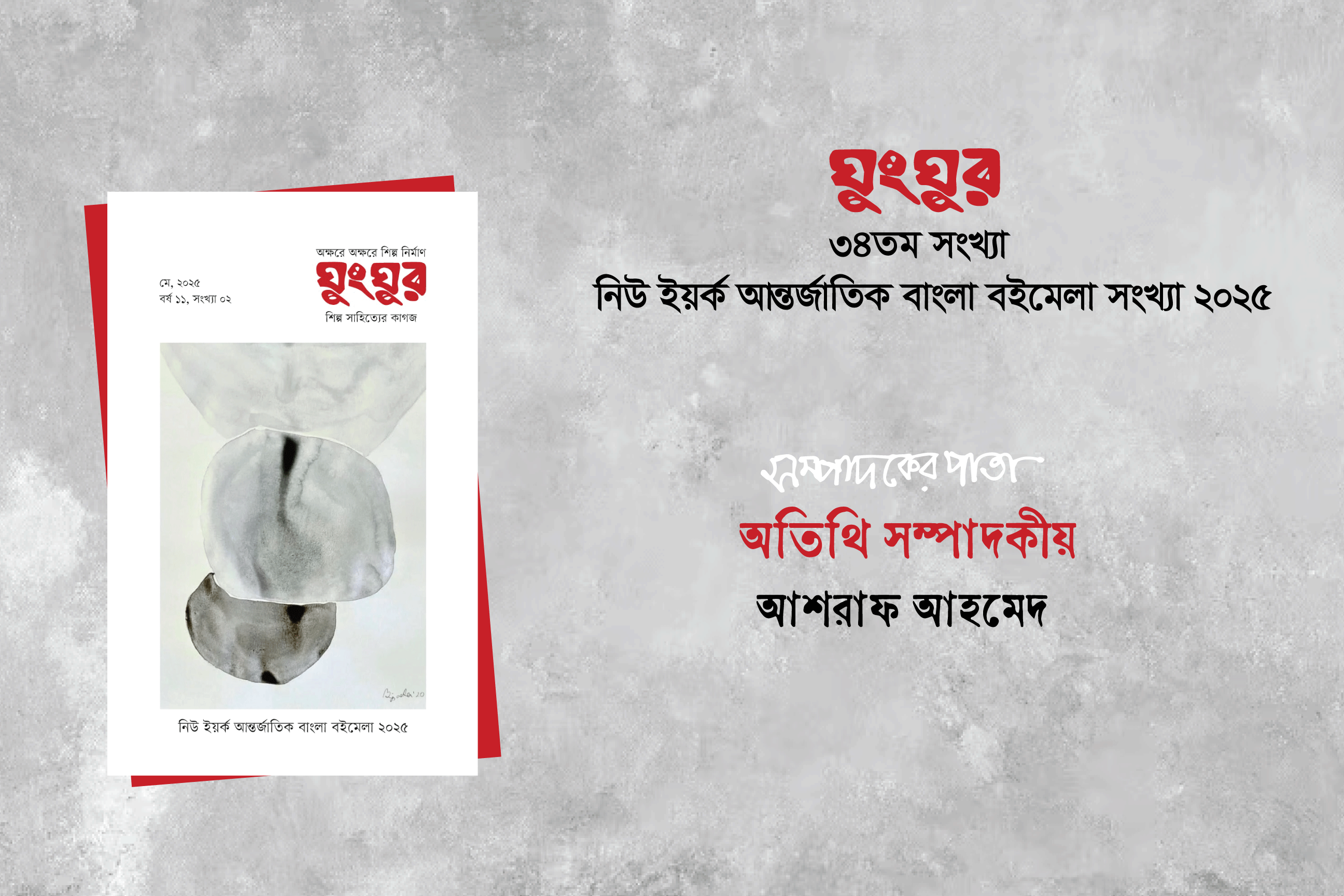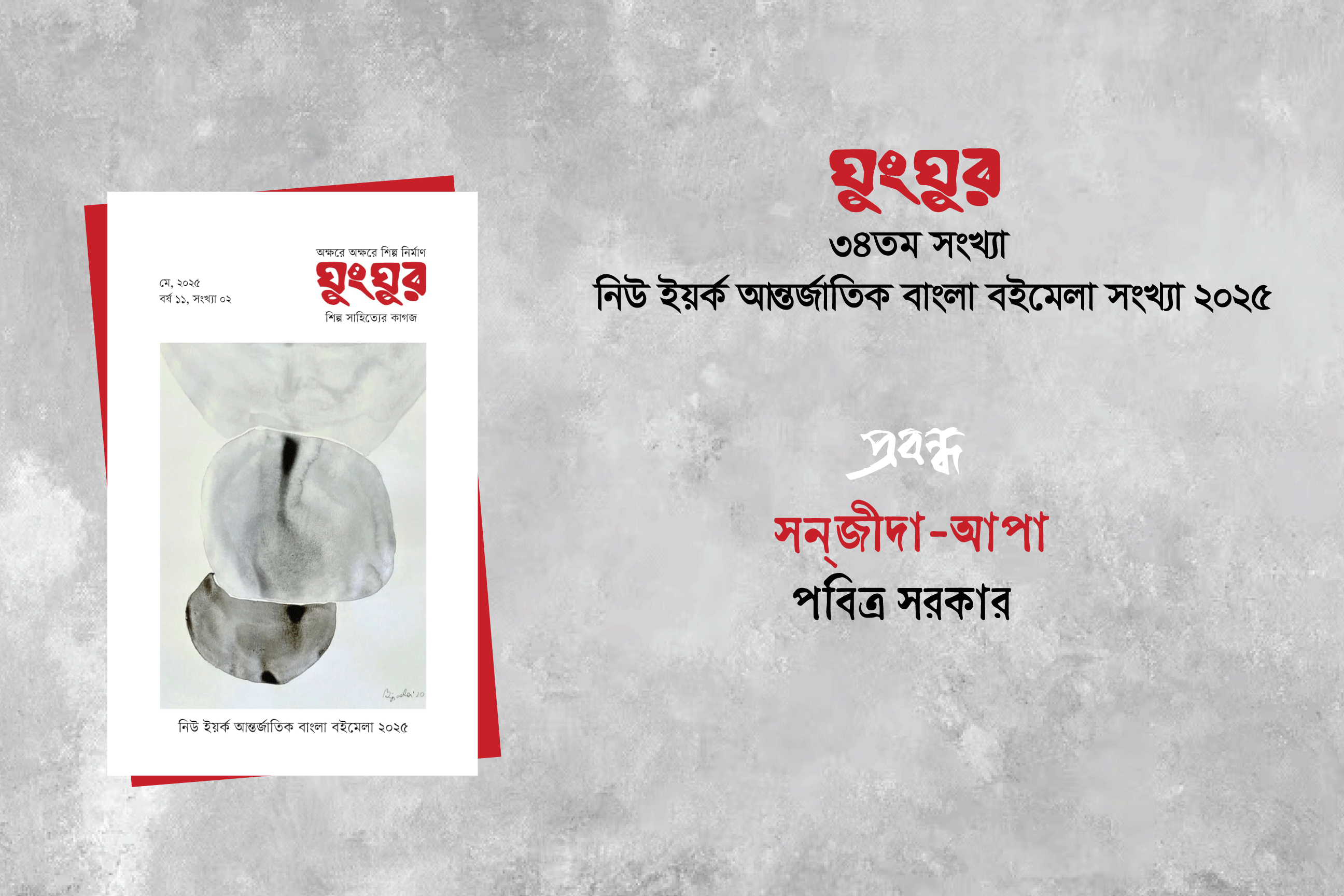জীবনানন্দের কবিস্বভাব ও কবিভাষা : ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’

রূপসী বাংলা কাব্যের দুই-খচিত কিন্তু আদতে তিন নম্বর কবিতার দ্বিতীয় পংক্তির মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়েছে একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি—চলেছে ঢিমে-তেতালে, দুইবার বাইশ মাত্রা অতিক্রম করে, একেবারে গদ্যের ঢঙে। আমাদের অতি চেনা টুকরাটি আরেকটু চেনার খায়েশে একবার উদ্ধৃত করা যাক :
অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে ব’সে আছে
ভোরের দোয়েল-পাখি—
কতটা নির্দিষ্ট আর বিশিষ্ট হতে পারে কবিতার ভাষা? আর্টকে তো শেষ পর্যন্ত যেতে হয় সার্বিকে। অতি-বিশেষ থেকে সার্বিকে যাওয়ার পথটি কেমন? কথাটা বলার অন্তত দুটো কারণ আছে। দুনিয়ার বড় সাহিত্যিকদের অনেকেই বিশেষের তুলনায় সার্বিকেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। আমাদের রবীন্দ্রনাথ তো সার্বিকের রাজা। কোনো কোনো লেখক যে সামষ্টিকভাবে ভোগ্য শিল্পকর্ম রচনায় অধিকতর কামিয়াবি হাসিল করেন, কোনো কোনো শিল্পী যে নিমিষেই স্পর্শ করতে পারেন দশের আবেগ, তার এক কারণ তো এই নির্বিশেষ বা সার্বিক নিয়ে বেশি কারবার করা। যদিও মনে রাখা দরকার, শিল্পীমাত্রকেই তার নিজস্ব বিশেষ উপকরণ আর বিশেষ উচ্চারণভঙ্গি নিয়েই রাজত্ব এবং বড়ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হয়। তার উপস্থাপনায় বিশেষ নাকি সার্বিক প্রাধান্য পাবে, সেটা এর পরের ধাপ।
আমরা কবিতার ভাষার বিশিষ্টতার কথা বলছিলাম। নির্দিষ্টতা অর্থে। প্রসঙ্গটা তোলার দ্বিতীয় কারণের কথা এবার বলা যাক। ভাষা নিজেই কাজ করে নির্বিশেষ ভঙ্গিতে। বিশেষ হলে তার চলে না। ‘দোয়েল’ কথাটা কোনো বিশেষ দোয়েলকে ইঙ্গিত করে না, সমস্ত দোয়েলের একটা সাধারণ নাম প্রস্তাব করে মাত্র। ফলে ভাষার স্বভাবের মধ্যেই নির্দিষ্ট বাস্তব থেকে বিচ্যুত হয়ে সার্বিকে চলে যাওয়ার প্ররোচনা আছে। এ কারণেই হয়তো মানুষের উচ্চারণে—বলায়, লেখায় বা এমনকি শিল্পকর্মে—গড়ের প্রতিফলন যতটা পাওয়া যায়, ব্যক্তিত্বের চিহ্ন ঠিক ততটাই দুর্লভ। বলা যায়, যিনি চিন্তায় বা শিল্পিতায় বড়, তার সাধনার একটা বড় দিক ভাষার অর্থ-ব্যবস্থায় বিদ্যমান সার্বিকতার মধ্যে যথাসম্ভব ব্যক্তিত্বের চিহ্ন এঁকে দেয়া।
কিন্তু জীবনানন্দের কবিভাষার যে দিকটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজনে আমরা কথাগুলো তুললাম, তার যুক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের আরেকটি আলাপ সেরে নিতে হবে। সে প্রসঙ্গটি রবীন্দ্রনাথের, এবং এমনকি নজরুলেরও। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ বিশেষের তুলনায় নির্বিশেষকে এবং বর্তমানের তুলনায় চিরকালকে প্রণিধানযোগ্য করে তাঁর কথা সাজাতেন। ফলে তাঁর রচনায় বিশেষ বাস্তবের মহিমা কীর্তিত হয়নি, বরং চিরকালীন বাস্তব উপস্থাপিত হয়েছে। ‘সমাপ্তি’ গল্পে অপূর্ব যখন মৃন্ময়ীকে নিয়ে মৃন্ময়ীর বাপের কাছে যাচ্ছিল, তখন মৃন্ময়ী খুশিতে আটখানা। মনের হাউস চাপতে না পেরে অপূর্বকে জিজ্ঞাসা করে, ওই নৌকায় কী, সেই নৌকায় কী? ওখানটায় কী? ইত্যাদি। অপূর্ব কালবিলম্ব না করে উত্তর দেয়, তিল বা তিসি অথবা জমিদারের কাছারি বা মুনশেফের অফিস। লেখক-জবানিতে এরপর বলা হচ্ছে, বলা বাহুল্য উত্তরগুলোর সঙ্গে বাস্তবের বিশেষ সামঞ্জস্য ছিল না। কিন্তু প্রশ্নকারিণীর সে বিষয়ে খুব একটা মাথাব্যথাও ছিল না। সে আসলে তার প্রাপ্তিটুকু উপভোগ করছিল আর অপূর্বের সঙ্গে তা ভাগাভাগি করছিল। ‘সমাপ্তি’ গল্পের এই অংশটিকে সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের ন্যারেটিভের ধরনের একটা ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করা চলে। মৃন্ময়ীর মতো রবীন্দ্রনাথেরও বিশেষ তিল বা বিশেষ তিসির দরকার হতো না। ‘যেতে নাহি দিব’ কবিতায় যেমন দুয়ারে গাড়ি প্রস্তুত, কিন্তু কোনো বিশেষ গাড়ি নয়; তরুশ্রেণি উদাস ছায়া বিলাচ্ছে, কিন্তু বিশেষ কোনো তরু নয়; গিন্নি সঙ্গে কী কী দিয়ে দেবে তার একটা জিভে-জল-আসা তালিকা আছে, কিন্তু যেকোনো সচ্ছল গৃহস্থের জন্য সে তালিকাটা সার্বিক, কোনো বিশেষ গৃহিণীর বিশেষ পছন্দের কোনো ছাপ তাতে থাকাটা জরুরি ছিল না।
প্রশ্ন হলো, উপকরণগত নির্বাচনের মধ্যে যদি ব্যক্তিত্ব না থাকে, তাহলে রবীন্দ্রনাথের এই গভীর-গহন সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব কোত্থেকে এল। এ প্রশ্নের উত্তর খুব জটিল নয়, এবং আমাদের অজানাও নয়। শব্দের বিন্যাস আর অর্থলোকের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নির্মাণই রবীন্দ্রলোকের অবিনাশী আয়োজন। নজরুল প্রসঙ্গে বলে রাখা যাক, বস্তুর বস্তুগুণ ও বাস্তবগুণ নজরুলে অনেক বেশি মূল্য পেয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যাক, ধূমকেতু বা উল্কা উপকরণ হিসাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে নিশ্চয়ই তাদের বিশৃঙ্খল উপাদান এবং ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার কারণে। কিন্তু এ দুই উপকরণ নজরুলের কবিতায় বাস্তব বিবরণীর অংশ নয়, বরং ভাবগত বিবরণীর পোষক। ওই ভাবগত বিশিষ্টতাই নজরুলের কবিতার ব্যক্তিত্ব। এই সরল-সোজা কথাগুলো বলে রাখতে হলো এই কারণে যে, জীবনানন্দের কবিতার যে বৈশিষ্ট্যকে আমরা তাঁর অন্যতম অজরামর বিশিষ্টতা হিসাবে সামনে আনতে যাচ্ছি তাতে মনে হতে পারে, শিল্পভাষায় ব্যক্তিত্ব হাসিলের এটাই একমাত্র পন্থা। মোটেই তা নয়। তবে একমাত্র না হলেও বাংলা কবিভাষার বড় পরিসরটিতে জীবনানন্দের যে প্রবল প্রতাপ, তার অন্যতম উৎস নিশ্চয়ই এ বিশিষ্টতা। নবীন কবিদের নতুন পাতে সে ভাষার ভোজ যে শেষ হতেই চাচ্ছে না, তার রহস্যও হয়তো লুকিয়ে আছে এখানেই।
একটু লম্বা ভণিতা শেষ করে ফের আসা যাক দোয়েল পাখির দরবারে। দোয়েল নামের পাখি নয়, আমাদের জাতীয় পাখি তো নয়ই—পাখিটির কোনো জাতীয় তকমা তখনো জোটেনি যেহেতু, একটি বিশেষ দোয়েল পাখি, যেটি অসংখ্য বিশেষে গড়া এক মহার্ঘ ক্ষণে কবি দেখেছিলেন, অথবা দেখেননি আদৌ, কিন্তু দেখা সম্ভব, এখানে, কেবল এই বাংলাদেশেই। তাতেই বা কী? এটা তো শিল্পভাষার প্রায় সাধারণ বৈশিষ্ট্য—‘হতে-পারত’ স্বভাবকে ‘হয়েছে’ স্বভাবে প্রকাশ করা। ঠিক এখানেই এ কবিতার দোয়েল পাখিটির অন্যরকম প্রকাশ। এত এত বিশেষের সমন্বয়ে সে ছবিটি আঁকা যে, কিছুতেই তার রূপটি সার্বিক হতে চায় না। আরও বিশিষ্ট হয়ে উঠতে চায়। ভাষার যে সার্বিক স্বভাবের কথা আমরা আগে বলেছি, সাহিত্যিক ভাষায়, মরিস ব্লাশোঁ যেমনটি দেখিয়েছেন, তার দুই ধরনের রূপান্তর ঘটে। একদিকে সাহিত্যে ভাষার সার্বিক স্বভাবটি বিশেষ হয়ে ওঠে। হেমিংওয়ের মাছ, শরৎচন্দ্রের কুকুর, রবীন্দ্রনাথের বালক কিংবা বিভূতিভূষণের পুঁইচারা কিছুতেই ভাষার নির্দিষ্ট করে দেয়া মাছ-কুকুর-বালক-পুঁই নামের সার্বিকতায় বদ্ধ না থেকে হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। একেবারেই বিশেষ একটি। বলা যায়, ভাষার মূল স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে বিশেষকে দাগিয়ে দেয়াই সাহিত্যিক ভাষার প্রাথমিক লক্ষণ। ব্লাশোঁ-কথিত দ্বিতীয় রূপান্তরটি ঘটে ঠিক এর বিপরীত মুখে। ওই বিশেষের আধারেই সাহিত্যে-শিল্পে ঘটে এক ব্যাপক সার্বিকায়ন। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে স্থানকাল-অতিক্রমী এমন এক সার্বিক প্রকাশ শিল্পীর উদ্দিষ্ট হয়ে ওঠে যে, আগের স্তরে বিশেষ হয়ে ওঠা উপকরণরাশির বিশেষত্ব ছিন্নভিন্ন করে দিতে তার বিন্দুমাত্রও বাধে না। তখন মাছ আর হাঙ্গরে ফারাক থাকে না, কুকুরের জায়গায় বিড়াল হলেও ক্ষতি হয় না। সাহিত্যভাষার এই বৈশিষ্ট্যকেই আমরা আদর দেখিয়ে রূপক, ব্যঞ্জনা ইত্যাদি নামে ডেকে থাকি।
আমাদের আজকের কাব্যিক দোয়েল পাখিটির ক্ষেত্রে প্রথম রূপান্তরটি যে খুব হয়েছে তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দ্বিতীয়টি অর্থাৎ সার্বিকায়নটি ঠিক যেন জমতেই চাচ্ছে না। অনেকগুলো বিশেষের জালে পাখিটি এমনভাবে আটকা পড়েছে যে ঠিক ধ্রুপদি ছবির পাখি হয়ে সে সেখানটাতেই থেকে যেতে চাইছে, উড়াল দিয়ে বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করে ওই ছবিটিকে নষ্ট হতে দিতে চাইছে না। এই ছবিটা আরেকটু কাছ থেকে দেখার তাগিদে একবার রওয়ানা হওয়া যাক খোদ কবির সঙ্গে। যেতে হবে কিন্তু ভোরে। আলোকোজ্জ্বল সকাল নয়; অন্ধকার ভোর। অন্ধকারই ভালো। তবে কিনা দেখার ব্যাপার আছে। কে না জানে, অন্ধকারের সঙ্গে দেখার একটা বিরোধ আছে। কাজেই অন্ধকার কথাটাকে বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে একটু অন্যদিকে নিতেই হচ্ছে —যেটুকু আলো হলে দেখার কাজটাও চলে, আবার অন্ধকারটাও বজায় থাকে, সেদিকে। ওই অন্ধকার বা আলোয় বা আলো-অন্ধকারে দেখা যাবে দোয়েল পাখি। বসে আছে ডুমুর গাছে। জানি আমরা, ডুমুরের পাতা আকারে বড় হয়। জানি, ডুমুরের পাতার কোনো অমসৃণ বৈশিষ্ট্যের কারণে হয়তো, পাখির বাসা বানানোর সঙ্গে এ গাছ ও পাতার একটা সখ্য আছে। এ কবিতার ডুমুর গাছ হয়তো ওই বস্তুস্বভাবের দৌলতেই নির্বাচিত হয়েছে। কিংবা একেবারেই দৈবচয়ন। কারণ যাই হোক, আমাদের ওই অভিজ্ঞতা কিন্তু কবির প্রশ্রয় পায়নি। পাখিটি বাসায় বসে নেই। বসে আছে বোধহয় কোনো ছোট্ট ডালে। তার মাথার উপর একটা পাতার ছায়া। ‘ছাতার মতন’। ডুমুর গাছের পাতা বড়ই হয়। কিন্তু ছাতা বস্তুস্বভাবে একটু বড় আকৃতির হলেও ওটাই ছাতার প্রধান গুণ নয়। গুণ তার আশ্রয় দেয়া, ছায়া দেয়া, রক্ষা করা। এদিক থেকে ডুমুরের পাতাটিকে ছাতার মতন দেখতে গেলে দোয়েলের চোখ দিয়েই দেখতে হয়। দোয়েল নিশ্চয়ই পাতার আশ্রয় পাওয়ার জন্য এ জায়গাটি নির্বাচন করেছিল। আর ওই আশ্রয়সমেত দোয়েলটিকে দেখতে পারলে নিশ্চয়ই ভাবগতভাবে গোটা দোয়েলটিই বদলে যাবে। আশ্রয় ও সুরক্ষার নিশ্চয়তায় থাকা একটা পাখিই বড় হয়ে উঠবে। এখানেই শেষ নয়। দোয়েলের আগে আবার ‘ভোরের’ শব্দটি জুড়ে দিয়ে নির্দিষ্টতার মাত্রা আরও কতক ভার যোগ করা হলো। আমরা আগের উল্লেখসূত্রেই জানি, এই ভোরে আলোর চেয়ে আঁধারের মাত্রাই প্রবল। কিন্তু মাত্রা যাই হোক, সে বিশেষ আলোয় দোয়েল পাখিটি দেখা নিশ্চয়ই একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা। আর ওই ভোরে পাখিটি হয়তো এখনো জাগে নাই। সমস্ত চাঞ্চল্য আর সক্রিয়তা মুলতুবি রেখে স্থির হয়ে আছে চারপাশের প্রকৃতির মাঝে, চারপাশের প্রকৃতির মতোই।
এই সবটা যদি হয় একটা চিত্র, তাহলে তার পটভূমিও তৈরি আছে আগে ও পরে। এটা কিছুতেই আমাদের নজর এড়াতে পারে না যে আমাদের উদ্ধৃত ছবিটির আগে আছে এক কোলন চিহ্ন—কবিতায় ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন হিসাবে বেশ বিরল; আর পরে আছে ড্যাশ—জীবনানন্দের বহু-ব্যবহৃত পছন্দের বিরামচিহ্ন। কোলনচিহ্নটি আমাদের নিশ্চিত করছে, আগের প্রস্তাবটির প্রমাণপত্র বা যুক্তি হিসাবে এসেছে দোয়েল-প্রসঙ্গ। প্রস্তাবটি কী? :
বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর :
দ্বিতীয় পংক্তির ‘খুঁজিতে’ ক্রিয়াটি আমাদের ভাবতে বাধ্য করে, বাংলার মুখ যেভাবে কবি দেখেছেন, তা-ও খোঁজাখুজিরই ফল। এই মুখ বা মুখের কোনো বৈশিষ্ট্য কারো দেখার জন্য আগে থেকেই হাজির ছিল না; একে আবিষ্কার করতে হয়েছে। আর এ পংক্তির উচ্চারণভঙ্গি আমাদের নিশ্চিত করে, নিজের প্রস্তাব সম্পর্কে কবির কোনো সন্দেহ নাই। এ ধরনের সন্দেহাতীত উচ্চারণ জন্মলগ্ন থেকেই কবিতার নিত্যসঙ্গী। এ কবিতায় বাড়তি যা পাচ্ছি তা হলো, কবি নিজের পক্ষে দস্তুর মেনে যুক্তি উপস্থাপন করছেন। রীতিমতো কোলন চিহ্ন দিয়ে নিজের কথাটার পক্ষে সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁর প্রস্তাবটি কেবল আবেগের দিক থেকে নয়, যুক্তির দিক থেকেও অন্যের কাছে উপস্থাপনযোগ্য। এ বস্তু কবিতায় খুব সুলভ নয়। কিন্তু জীবনানন্দের বহু কবিতায় প্রায় গদ্যধর্মী যুক্তিক্রমকে কবিভাষার বশীভূত হতে দেখি। আধুনিক বাংলা কাব্যভাষায় যুক্তিকে বশ মানানোর একটা কৃতিত্ব জীবনানন্দ অবশ্যই পাবেন। আর বিনয় মজুমদারের কবিতায় পাই এর পরবর্তী ধাপের উৎসারণ।
আমাদের দোয়েল পাখিটির বাঁয়ে যেমন আছে কোলন, ডানে তেমনি আছে ড্যাশ। জীবনানন্দীয় ড্যাশের যে বিপুল তাৎপর্য, তার কোনো কোনোটি নিশ্চয়ই এ ড্যাশও পালন করছে। কিন্তু একইসঙ্গে দেখছি, বিরামচিহ্ন হিসাবে ড্যাশের যে সাধারণ কাজ, এ ড্যাশ সে দায়িত্বেও অবহেলা করছে না—বাঁয়ের প্রসঙ্গটিকে ডানে প্রসারিত করে দিচ্ছে :
—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম— বট — কাঁঠালের—হিজলের—অশথের ক’রে আছে চুপ;
প্রথম পংক্তির ‘স্তূপ’ কথাটা ‘চুপ’ বা ‘রূপ’ শব্দের আমন্ত্রণে যদি এসে থাকে, খারাপ হয়নি। অন্ত্যমিলটা বেশ হয়েছে। কিন্তু জীবনানন্দীয় শব্দস্বভাবের বহু বহু নজির নিশ্চিত সাক্ষ্য দেয়, শুধু শরীরী নয়, ভাবগত মিলের দিক থেকেও আসতে পারে শব্দটি। ওই অন্ধকার ভোরে ঘুম ঘুম চোখে ঘুমন্ত বৃক্ষরাশির জমাট পল্লবকে স্তূপাকার বললে শুধু প্রাচুর্যই বোঝায় না, তাদের সম্মিলিত বিশেষ চরিত্রধর্মও প্রচারিত হয়। এরকম অন্তর্গত ধর্মকে শব্দবিন্যাসের চাপে প্রকাশ্যে নিয়ে আসা-যে জীবনানন্দের অন্যতম প্রধান কবিধর্ম, সে কথা তো আজকাল আর বিশেষ গোপন নাই। যাই হোক, যে গাছগুলোর নির্বাচিত অন্বয়ে চারপাশের এই সজ্জা, তাতে একদিকে ছন্দের মাত্রাগণনাটা দেখতে পাচ্ছি; অন্যদিকে দেখছি কবির পছন্দের গাছগুলা এসে ভিড় করেছে। একেবারে মাত্রা গুনে হাজির হয়েছে আম, বট, কাঁঠাল, হিজল আর অশত্থ। এ ধরনের সমাবেশ ঠিক ‘বাস্তবসম্মত’ কি না, সে প্রশ্ন উঠতে পারে। উঠতে যে পারে সে বোধ দেখছি কাব্য-রচয়িতারও পুরোমাত্রায় হাজির। নামগুলোর পাশে ড্যাশের নৈঃশব্দ্য বা বিস্তার এঁকে দিয়ে কবি বাস্তবতার দাবিটা প্রতিষ্ঠিত করলেন। ফাঁকগুলোতে ঢুকে পড়ল অকথিত উদ্ভিদরাশি বা বৃক্ষসকল, যাদের যৌথ অস্তিত্ব বাংলা অঞ্চলটাকে সাধারণভাবে সবুজ অভিধার মহিমা দিয়েছে।
তাহলে দাঁড়াল এই : দোয়েল পাখিটার বামে কোলন চিহ্ন একটা কার্যকারণসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছে; আর ডানে ড্যাশের প্রসারধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ছবিটির পটভূমি। এক নির্বিশেষ বিপুল সবুজ পটভূমিকায় অঙ্কিত হয়েছে বিশেষ পট। তাতে আলো-ছায়া এবং রঙ মাত্রামতো আছে; অন্তরঙ্গ যে পরিসরে সাবজেক্ট তার অন্তর্নিহিত অস্তিত্বে বাঙ্ময় হয়, তার যথাবিহিত এনতেজাম আছে। সব মিলিয়ে রচিত হয়েছে এমন এক ছবি, যা এই পৃথিবী একবারই কেবল পায়। জিজেক তাঁর ইভেন্ট নামের কেতাবে প্লেটোর ‘আইডিয়েল’-এর এক তুখোড় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, প্লেটোর আদর্শ গোলাপ আসলে স্বর্গে থাকে না, তা এমন কিছুও নয় যে দুনিয়ার গোলাপগুলোকে গড় করে কল্পনা করলেই কেবল তাকে পাওয়া যাবে, বরং কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে প্রতিবেশ আর মনের অমিত মেলবন্ধনে একটা গোলাপই আবির্ভূত হতে পারে এমন এক মহিমা নিয়ে যা অন্তত ব্যক্তির দিক থেকে আইডিয়েলের মর্যাদা পেতে পারে। আদর্শ রূপ আসলে বিশেষ মুহূর্তের প্রকাশ, আর দুনিয়াতেই লভ্য। জীবনানন্দের এই দোয়েল সেরকম বিশেষ আইডিয়েল, বাংলা নামের দেশ বা বাংলা নামের অঞ্চলের জন্য সম্ভাব্য মহত্তম প্রশস্তিগাথা। ‘মহত্তম’ বলে আমাদের এ শনাক্তি যে কথার কথা নয়, সে কথা বোঝাতে এখানে কিছু সাফাই সাক্ষ্যের বন্দোবস্ত করছি।
২
রবীন্দ্রনাথের ‘আমার সোনার বাংলা’ আর দ্বিজেন্দ্রলালের ‘ধনধান্য পুষ্প ভরা’ রচনা দুটিকে বলতে পারি বাংলা অঞ্চল নিয়ে লেখা সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি প্রশস্তি-সঙ্গীত। প্রথম গানটি রচিত হয়েছে স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে, অখণ্ড বাংলার পক্ষে পরিচালিত রাজনৈতিক তৎপরতার সহযোগী হিসাবে। দ্বিতীয়টিও প্রায় একই পটভূমিতে, যদিও সাজাহান নাটকে গানটি দেয়া হয়েছে রাজপুত রমণীদের মুখে। বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ড গান দুটির রচনাকালীন লক্ষ্য ছিল না বলে বাংলাদেশে এ দুটির বিশেষত প্রথমটির রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রায়ই অনেককে বলতে শোনা যায়। এই বলাটা অশৈল্পিক; অনৈতিহাসিক তো বটেই। শিল্পকর্ম, অন্য যেকোনো মানবিক উৎপাদনের মতো, জন্মসূত্র মনে রাখে বটে, কিন্তু জন্মকালীন পটভূমি তার ব্যবহার ও ভোগের প্রধান শর্ত কিছুতেই হয় না। সে রকম হলে দুনিয়ার বেশিরভাগ মানবিক উৎপাদন আমাদের ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে উঠত। অন্যদিকে, এ গান দুটি জন্মের পর থেকে সাধারণভাবে বাংলা অঞ্চলে আর বিশেষভাবে বাংলাদেশে এত বেশিবার উচ্চারিত হয়েছে, বিশেষত পাকিস্তান রাষ্ট্রবিরোধী বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কালে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে এত অন্তরঙ্গ কেতায় ব্যবহৃত হয়েছে যে, এগুলোর পুরনো তাৎপর্যের চেয়ে নতুন অর্জিত তাৎপর্য অনেক বড় হয়ে উঠেছে। বস্তুত, স্বাধীনতার পরপরই জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে ‘আমার সোনার বাংলা’ যে গৃহীত হলো, তাতে পূর্ববর্তী অন্তত দুই দশকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এতটাই কার্যকর ছিল যে এ সম্পর্কে কোনো দ্বিধাই দেখা যায়নি। আমরা অবশ্য গান দুটির এই ঐতিহাসিক পটভূমি টানলাম রাজনৈতিক প্রয়োজনে নয়, বরং জনপ্রিয়তার ইশারা দেবার জন্য। কথাটা আমাদের পরে কাজে লাগবে।
‘ধনধান্য পুষ্প ভরা’ গানটি শুরু হয়েছে অতিশায়ন দিয়ে। দুনিয়াটা ফুলে-ফসলে টইটম্বুর—এ কথা প্রমাণ করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি এ ধরনের কথা আসলে প্রমাণের অপেক্ষাও করে না। আমার দেশটাই দুনিয়ার সেরা—এ কথাটাও একই রকম। কেন আমার দেশ দুনিয়ার সেরা, সে কথার পক্ষে কিছু প্রমাণপত্র উপস্থাপিত হয়েছে কবিতার পরের অংশে। কিন্তু এর মধ্যে এমন একটাও নাই, যা বিশেষভাবে বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য। অবশ্য যে উপাদানগুলোর কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর ভালোত্বটা বাদ দিয়ে শুধু উপকরণগুলো একত্র করলে বাংলা অঞ্চলের একটা আবহ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই যুক্তির ওপর দাবিটা নির্ভরশীল নয়। দাবিটা স্ব-উৎপাদিত; অনেকটা ব্যক্তিনিষ্ঠ। বস্তুনিষ্ঠতা তার জন্য জরুরি নয়। আমার দেশের চাঁদ-সূর্য অন্য দেশের চেয়ে যদি উজ্জ্বল হয়ও, এ কবিতায় তার কোনো তথ্যগত প্রমাণের ভিত্তি ব্যবহৃত হয় নাই। ব্যবহৃত হয়েছে ব্যক্তিনিষ্ঠ আবেগ। এর ফলে অবশ্য কাব্য হিসাবে এর গুরুত্ব কমে না। সে কেবল ‘স্বপ্ন দিয়ে তৈরি’ আর ‘স্মৃতি দিয়ে ঘেরা’র মতো দুর্দান্ত কাব্যিকতার জন্য নয়; কবিতাটির সামগ্রিক আবহ আর বয়ানের ক্রম-অগ্রসর শৃঙ্খলাও দারুণ উপভোগ্য। শেষাংশে মায়ের সঙ্গে আর জন্মের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে দেশ আসলে অস্তিত্বের এক অনিবার্য অংশ হয়ে ওঠে। তখন পুরো রচনাটাই একটা অন্যরকম তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়। বোঝা যায়, এটা ঠিক আবিষ্কার নয়, বরং জন্মসূত্রে পাওয়া অনিবার্য অস্তিত্বের বেহিসাবি উদযাপন।
‘আমার সোনার বাংলা’ উচ্চারণে যে অতিশায়ন আছে তা আসলে পুরনো এক মিথ। এ মিথ রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কার নয়, আর এ গান ঠিক ‘সোনার বাংলা’ মিথের ওপর প্রতিষ্ঠিতও নয়; তবে এ গানের মধ্য দিয়ে কথাটা হয়ত বেশ স্থায়ী একটা রূপ পেল। প্রায় শুরু থেকেই দেশকে ‘মা’ সম্বোধন করায় মা-কথাটির যে সাংস্কৃতিক-ধর্মীয়-আবেগি বিস্তার, তার সুবিধা পেয়েছে রচনাটি। মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কের অন্তরঙ্গতা গভীরভাবে সঞ্চারিত হয়ে আছে পুরো কবিতায়। নদী ও ধানের মতো যে উপাদানগুলো দুটি কবিতাতেই আছে, তাদের ব্যবহারের ধরন তুলনা করলেই বোঝা যাবে, ‘আমার সোনার বাংলা’ অধিকতর অন্তরঙ্গ—ব্যক্তিনিষ্ঠ; আর ‘কি আঁচল বিছায়েছ’-র মতো মনোহারী কাব্যিক আয়োজনের বাইরেও সম্পর্কজনিত স্বস্তি ও মিষ্টতা আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এ কবিতার আয়োজন রীতিমতো উল্লেখযোগ্য।
তার মানেই হলো, কাব্যিক এনতেজামের দিক থেকে দুই কবিতায় মিলের পাশাপাশি বেশ খানিকটা অমিলও আছে। আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য দরকারি তথ্য এই যে, যে নামশব্দগুলো কবিতা দুটির শিরদাঁড়া, যেমন, নদী, মেঘ, ফুল, আমের মুকুল, বটগাছের মূল, পাহাড় ইত্যাদি, সেগুলো ‘ধনধান্য পুষ্প ভরা’ কবিতায় গেছে অতিশায়নের দিকে, আর ‘আমার সোনার বাংলা’য় গেছে ব্যক্তিনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার দিকে; কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই ভাষার স্বাভাবিক ‘সাধারণধর্ম’—যে সম্পর্কে আমরা আগে বলেছি—মোটামুটি অক্ষুণ্নই থেকেছে। কথাটা আরেকটু খুলে বলা যাক। প্রথমোক্ত কবিতায় যখন বলা হয়েছে, ‘কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে’, তখন ‘তড়িৎ’, ‘কালো’ এবং ‘মেঘ’ —এই তিনটি নাম ‘এমন’ শব্দের প্রশ্রয়ে একটা অতিশায়িত মহিমা প্রকাশ করেছে বটে, কিন্তু নাম তিনটির এমন কোনো অর্থগত পরিবর্তন হয় না যা থেকে ‘সাধারণধর্ম’ বিশেষধর্মে উপনীত হওয়ার ইশারা মেলে। ভাষার মধ্যে ঠিক যে ধরনের অর্থ-ব্যবস্থায় শব্দ তিনটি বিদ্যমান আছে, এ কবিতায়ও মোটামুটি সেভাবেই আছে। মরা শব্দ ব্যবহারের কারণে জিন্দা হলে অর্থের যেরকম বিশেষত্ব অর্জিত হয়, সেটুকু হয়েছে মাত্র। এর বেশি নয়। ‘আমার সোনার বাংলা’ কবিতায়ও প্রায় অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। ‘ওমা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে’ পংক্তিটিকে উদাহরণ হিসাবে নিলে দেখব, সামগ্রিকভাবে উপকরণ নির্বাচন এবং তার বিশিষ্ট প্রকাশে ব্যক্তিত্বের যে অভিব্যক্তি আছে, ‘ফাগুন’, ‘আমের বন’, ‘ঘ্রাণ’ ইত্যাদি নামশব্দে এবং এমনকি ‘পাগল করে’ ক্রিয়ায়ও সে বিশেষত্ব নাই। শব্দগুলো ভাষায় বিদ্যমান সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আরেকটু এগিয়ে বলা যেতে পারে, এ ধরনের উচ্চারণের রচনা জনপ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে।
কবিতা ও গানে শব্দসঞ্চয়ের যে ফারাক আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখে আসছি, সেকথা বিবেচনায় রেখেও বলা যায়, এ গান দুটিতে কাব্যভাষার একটা সাধারণ ঢঙ আছে, যাকে ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’ কবিতার ঢঙের সঙ্গে মেলানো যায় না। প্রশস্তিগীতি হিসাবে প্রথমটিতে পাই ঘোষণা ও স্বীকৃতি; আর পরেরটিতে দেখি আবিষ্কার। প্রথমটি ভাষায় বিদ্যমান বস্তুর সাধারণধর্মকে প্রসারিত করে, কিন্তু বস্তুর এমন কোনো গুণ তালাশ করে না, যা অন্যের জন্য প্রমাণসাপেক্ষ। অন্যদিকে, পরের কবিতা বস্তুর গুণ আবিষ্কার করে তাকে এমন বিশেষ ভঙ্গিতে উপস্থাপন করে, যা বোধগম্যতার সীমায় আসার পরেও বিশিষ্টই থেকে যায়। কেন আমরা এই দ্বিতীয় ভঙ্গিটির প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখিয়ে রেখেছি, সে কথা বিশদ করার প্রয়োজনে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার শরণ নেব।
আমেরিকা দুনিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ বা সুইজারল্যান্ড বসবাসের জন্য অতি উৎকৃষ্ট জায়গা —এ ধরনের কথা বলার জন্য আমাদের হাতে বিপুল তথ্য-উপাত্ত আছে। একটু অন্যরকম অভিজ্ঞতা বা তথ্য ব্যবহার করে কেউ হয়েতো এ কথাও বলতে পারে, নিউজিল্যান্ডের ওই এলাকা বসবাসের জন্য তুলনাহীন। মানুষ যখন পর্যটনে যায়—বনে, পাহাড়ে, সমুদ্রে-নদীতে—তখন সে বিশেষভাবে নিজের পছন্দেই যায় তা নয়; বরং জায়গাগুলো যাওয়ার মতো, এরকম একটা প্রতিষ্ঠিত পছন্দ তার পছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ ধরনের জায়গাগুলোর মধ্যে একটির চেয়ে অন্যটি কারো কাছে মনোহর মনে হতে পারে। এবং তা নিয়ে মনোহারী রচনাও সম্ভব। কিন্তু দুনিয়াজুড়ে ভ্রমণকাহিনি হিসাবে ওই রচনাগুলোরই সুখ্যাতি, যেগুলো কোনো অঞ্চলের, সে যে অঞ্চলই হোক না কেন, সাধারণ্যে অনালোকিত এলাকা আবিষ্কার ও অন্তরঙ্গ কায়দায় তার প্রকাশ ঘটাতে পেরেছে। বলা হয়তো বাহুল্য হবে না, বাংলা মুলুকে মুজতবা আলীর খ্যাতি এ গুণের দৌলতেই চাউর হয়েছিল। পর্যটন এক বস্তু, আর সকাল-সন্ধ্যা যে পথে নিত্য যাতায়াত, সে পথের কোনো বিশেষ গাছের সঙ্গে স্মৃতি, অভিজ্ঞতা বা অকস্মাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনাহেতু যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার অনুভূতি অন্য বস্তু। কথাটা হয়তো ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের নিরিখেও প্রকাশযোগ্য। পরিচিত বা নিম-পরিচিত কারো প্রশংসা করা খুবই সম্ভব, সে প্রশংসা হয়ত সত্য, আর বহু মানুষের সাক্ষাৎ সমর্থনও তা পাবে। কিন্তু একজনের সঙ্গে বহুদিন অন্তরঙ্গ জীবনযাপনের ফলে এমন বিশিষ্টতা তার মধ্যে আবিষ্কৃত হতে পারে, যা হয়তো দুনিয়ায় আর কারো কাছে কখনোই উন্মোচিত হবে না। সে আবিষ্কারের জন্য অবশ্য আবিষ্কারকের ব্যক্তিত্ব চাই, অনুভূতির গভীরতা চাই, আর প্রকাশের সামর্থ্য চাই। তাহলে বিশেষ পটভূমি উন্মোচনপূর্বক সে আবিষ্কারের বার্তা উপস্থাপন করা সম্ভব অন্যদের সামনে, যেখানে শ্রোতা সে বিশিষ্টতার হদিশ না পেলেও মুহূর্তেই ওই বিশিষ্টতার মহিমা বুঝে উঠতে ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’ কবিতার বাংলা-প্রশস্তি এই ঘরানার। এখানে আবিষ্কারটা এতই মুখ্য, আর সে আবিষ্কার ব্যক্তিত্বের দিক থেকে এতই স্বতন্ত্র, তদুপরি প্রকাশের দিক থেকে এর বিশিষ্টতা এতটাই প্রগাঢ় যে একে অন্য কারো সাথে মিলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা নাই। বাংলার এ প্রকারের প্রশস্তিগাথা আর কিছু পাওয়া যাবে ওই জীবনানন্দেরই কবিতায়—রূপসী বাংলার কিছু পঙ্ক্তিতে। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই এমন নয় যে, জীবনানন্দ হঠাৎ করে ভিন্নরকম ভাষায় লেখার খেয়ালে এরকম পঙ্ক্তি বা ছবি রচনা করে ফেললেন। পুরো ব্যাপারটা জীবনানন্দের কবিভাষার কিছু বিশিষ্টতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, আর বাংলা সাহিত্যিকভাষার যে পর্বের ভিতর থেকে এ ভাষার জন্ম, তার ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত। আমরা এবার সেদিকটা একটু করে দেখে নেব।
৩
এ কবিতার প্রথম ছবিটা প্রস্তাব এবং পটভূমিসহ পাঁচ পংক্তির। পরের পংক্তি চরিত্র-বিচারে এই পাঁচ পংক্তির সঙ্গেই পাঠ্য। তবে আগের ছবির সঙ্গেই ওই ছবিটার প্রত্যক্ষ যোগ থাকলেও পরিষ্কার বোঝা যায়, সময় পাল্টে গেছে। সময় পাল্টানো মানেই হলো, আলো-ছায়ার খেলা পাল্টে যাওয়া : ‘ফণীমনসার ঝোপে শটি-বনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;’। সূর্য-যে এরই মধ্যে আগের অন্ধকার ছেড়ে বেশ খানিকটা উপরে উঠে এসেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। আর এই ফারাক জীবনানন্দের মতো অতি ‘বাস্তববাদী’ কবির কাছে যে অনেক বড় কিছু, এ কবিতাতেই তার বিস্তর সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে।
কবিতার এ ছয় নম্বর লাইনে আপাতদৃষ্টিতে তুলনামূলক নিরীহ একটা ছবি আছে। সম্ভবত যে কারো চোখে পড়বে। চোখে পড়বে, যদি কেউ দেখতে চায়; কিন্তু উল্লেখ করার মতো কিছু মনে হবে কি? নন্দনতাত্ত্বিক দিক থেকে এ প্রশ্নের একটা অন্যরকম গুরুত্ব আছে। সে কথায় যাওয়ার অংশ হিসাবে এখানে উল্লেখ করতে চাই, ‘ফণীমনসার ঝোপ’ বা ‘শটি-বন’ অন্তত সৌন্দর্যের বার্তাবহ হিসাবে—বিশেষত ওই কবিতায়, যেখানে এই সৌন্দর্যের বরাতে বাংলা অঞ্চল বিশেষভাবে মূল্যবান হিসাবে আবিষ্কৃত হবে—ব্যবহারের ঝুঁকি খুব কম শিল্পীই নিতে চাইবেন। অন্তত জীবনানন্দের সমকালে বা আগের জমানায়। জীবনানন্দের প্রায় সমকালে আরেকজন সাহিত্যিক সমধর্মী সাহস দেখিয়েছেন, এবং নিশ্চিতভাবে জীবনানন্দের মতোই গুণে-মানে ও সাফল্যের সঙ্গে। বাংলা সাহিত্যের পাঠকমাত্রই জানেন, এই শিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষকে পরম মূল্য দিয়ে প্রাত্যহিক ও উপস্থিত বাস্তব তৈরির ঝোঁক বিভূতিভূষণেরও ছিল। বলতে কী, এই দুই গুণ—অনুল্লেখ্যকে উল্লেখযোগ্য করে তুলতে পারা, আর বিশেষ বাস্তবকে নান্দনিক দিক থেকে গুরুত্ব দিতে পারা—বাংলা সাহিত্যের আসরে জেঁকে বসেছিল কল্লোলের কালে। কল্লোলীয় কথাসাহিত্যের জন্য এ বস্তু জরুরি ছিল; কারণ, বিশেষত গরিব মানুষের নিখুঁত প্রতিবেশ অঙ্কন করে প্রবৃত্তি আর নিয়তির মতো ব্যাপারগুলোর নিরীক্ষা তাঁদের সাহিত্যকর্মের প্রধান লক্ষ্য ও চর্চা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। কারণ যাই হোক, এই বাস্তববাদই বাংলা সাহিত্যে কল্লোলের প্রধান অবদান।
ব্যাপারটা মিথ-রোমান্স-রোমান্টিকতা শাসিত বাংলা সাহিত্যে কী ভীষণ সন্ত্রাস হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল, তার সাধারণ পরিচয় পাই ‘আধুনিকতা’র পক্ষে-বিপক্ষে বিস্তর অকারণ বাগবিতণ্ডায়, আর বিশেষ পরিচয় পাই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের স্বরূপ বইয়ের কয়েকটি প্রবন্ধে। আদতে রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই মানতে পারেননি বা বুঝে উঠতে পারেননি, বস্তুর গুণ ও বাস্তবকে অবলম্বন করেও ‘সৌন্দর্য’ নির্মাণ করা সম্ভব। এমনকি গরিবি এবং বিশ্রীকে অবলম্বন করেও। ‘সাহিত্যের স্বরূপ’ ইত্যাদি প্রবন্ধে তিনি এ ব্যাপারে শুধু বিরক্তি নয় রীতিমত উষ্মা প্রচার করেছেন। অথচ কল্লোলীয় এবং তৎপরবর্তী বাংলা সাহিত্য—কী কাব্যে কী গদ্যে—সে পথেই গেছে। আমি দুটি উদাহরণ তুলে দিচ্ছি :
১. ছইয়ের গায়ে আটকানো ছোট হুঁকাটি নামাইয়া টিনের কৌটা হইতে কড়া দা-কাটা তামাক বাহির করিয়া দেড় বছর ধরিয়া ব্যবহৃত পুরাতন কল্কেটিতে তামাক সাজিল কুবের। (পদ্মানদীর মাঝি, প্রথম পরিচ্ছেদ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)
২. ‘স্ত্রী অন্নপূর্ণা খড়ের রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া শীতকালের সকালবেলা নারিকেল তেলের বোতলে ঝাটার কাটি পুরিয়া দুই আঙুলের সাহায্যে ঝাটার কাটিলগ্ন জমানো তৈলটুকু সংগ্রহ করিয়া চুলে মাখাইতেছিলেন।’(‘পুঁইমাচা’,বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)
এ উদাহরণগুলো নিখাদ বাস্তবকে সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতম উল্লেখের সূত্রে পরিপাটি করে উপস্থাপন করতে চায়। দার্শনিক দিক থেকে এর তাৎপর্য এই যে, যদি পারিপার্শ্বিক বাস্তবই মানুষকে অন্তরে-বাহিরে চিহ্নিত করতে পারে, তাহলে সে বাস্তবের উপস্থাপনা নিখুঁত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেকালের লেখকদের মধ্যে গণহারে এ প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। আর জীবনানন্দের মধ্যে দেখি তার বিশিষ্ট কাব্যিক রূপ। কিন্তু শুধু এটুকুই আমাদের ষষ্ঠ পংক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। গ্রাম-বাংলা বা বাংলার প্রকৃতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ না হয়ে উঠলে ওই উপাদানগুলো ওই গুরুত্ব কিছুতেই পেতে পারে না, যা কবিতায় উঠে আসার জন্য জরুরি। সেদিকটা একবার সংক্ষেপে দেখে আসা যাক।
আগে বা পরে কখনোই নয়, বিশ শতকের তিরিশের দশক নাগাদই যে বাংলা সাহিত্যে অকস্মাৎ গ্রামজীবন এবং প্রকৃতি-বন্দনার জোয়ার আসল, তা নিশ্চয়ই কোনো আসমানি পয়দা নয়। বাংলা সাহিত্যের সৃজনশীল-মননশীল মুরুব্বিরা আধুনিকতা বিচড়ানোর কাজে অতিমাত্রায় মশগুল থাকায় মোটেই খেয়াল করেননি, আগের জমানার অর্থাৎ উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে অন্তত পঞ্চাশ বছর, অতীতের ‘সোনালি ভারত’ যেমন বাংলা সাহিত্যের মূল ভিত্তি ছিল, বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকেও তেমনি নতুন ভিত্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল এক নতুন ভারত। মুখ্যত গান্ধির ভাবগত ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে ব্রিটিশ ভারতীয় রাজনীতির নতুন যুগের প্রেক্ষাপটে বিকশিত সেই নতুন ভারতে ক্রমশ প্রবেশ করছিল বৃহৎ-ভারতীয় জনগোষ্ঠী। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দরকারে কাজটা করতেই হয়েছে। ভারত-আবিষ্কার প্রকল্পের অংশ হিসাবে কলোনির ছোঁয়া লাগেনি যে গ্রামে সেই গ্রামের গভীর-ব্যাপক মহিমায়ন হয়েছিল ওই সময়টাতে। ‘গ্রামে ফিরে যাও’ শ্লোগান বহু তরুণকে গ্রামে ফিরিয়েছিল বৈকি। কিন্তু তারচেয়ে বড় কথা, ‘দেশ’ আবিষ্কারের অংশ হিসাবে গ্রামকে চেনার ও চেনানোর প্রকল্প তখন যে মহিমা পেয়েছিল, তার তুলনা আগে-পরে এ অঞ্চলে আর পাওয়া যায় না। বাংলা সাহিত্যে ওই সময়ের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক তৎপরতার মহত্তম প্রতিফলন নজরুল; আর গ্রাম-আবিষ্কারের এই ভাবগত তৎপরতার প্রতিফলন ঘটেছে তিন মহৎ শিল্পীর কলমে—তিনভাবে। বাঙালি মুসলমান হিসাবে জসীমউদ্দীনের কবিতায় দেখি প্রকৃতি আর মানুষের যৌথতা; বাঙালি হিন্দুর গ্রামীণ জীবনের প্রতিনিধি হিসাবে বিভূতিভূষণের রচনায় দেখি ব্যক্তির চোখে প্রকৃতি ও গ্রামীণ জীবনের সুন্দরমাখা বাস্তব উপস্থাপন; আর ‘আধুনিকতাবাদী’ জীবনানন্দের কবিতায় মানুষ ও যাপিত জীবনকে উহ্য রেখে প্রকৃতিকে লীলা ও লাস্যে অপরূপ হয়ে উঠতে দেখি। জীবনানন্দ যে ‘প্রকৃতির কবি’ হয়েও ‘নির্জনতম’ কবি, সে কথা অতি-প্রচারিত সত্যই বটে।
এখানে উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়, অন্তত তিন দশক আগে রবীন্দ্রনাথের রচনায় বাংলার গ্রাম ও প্রকৃতি এক অনুপম সৌন্দর্যে মূর্তিমান হয়েছিল। সোনার তরী-চিত্রা কাব্যে, গল্পগুচ্ছে আর ছিন্নপত্রের ছত্রে ছত্রে সে সৌন্দর্য ক্লাসিক মহিমায় চিরকালের মতো ধরা রইল। সে উনিশ শতকের শেষ দশকের কথা। আমরা এখানে যে পর্বের আলাপ তুলেছি, তার ওপর রবীন্দ্রনাথের গ্রাম-বাংলা আর প্রকৃতির প্রভাব থাকা খুবই সম্ভব; কিন্তু এ দুইয়ের ফারাক বিস্তর। শুধু বস্তু ও বাস্তবধর্মকে ব্যবহারের দিক থেকে নয়, শুধু বিশেষকে নন্দনতাত্ত্বিকভাবে গুরুতর করে তুলতে পারার দিক থেকে নয়, মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কগত প্রস্তাবের দিক থেকেও বটে। রবীন্দ্রনাথের গ্রাম-বাংলা সংস্কৃতির বিপরীতে প্রকৃতি হিসাবে প্রকল্পিত অস্তিত্ব; রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি তপোবনশাসিত আদর্শ জীবনপ্রণালির অংশ; তাঁর রচনায় মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কটিও মুখ্যত দর্শনাশ্রয়ী। ‘সোনালি ভারতে’র সঙ্গে রোমান্টিক ভাবাদর্শ আর নন্দনতত্ত্ব মেলালে রবীন্দ্রনাথের গ্রাম ও প্রকৃতির এক প্রকার দিশা মিলবে। বিশ শতকের বিশের দশকে নতুন রাজনৈতিক ও নন্দনতাত্ত্বিক প্রস্তাবের ভিত্তিতে নতুন লেখকদের লেখায় গ্রাম ও প্রকৃতির যে নতুন অভিসার, তাতে নতুনত্বের ভাগই বেশি।
জসীমউদ্দীন যখন লেখেন ‘কচি লাউয়ের ডগার মতন বাহু দুখান সরু’, তখন তিনি আসলে বস্তুর অন্তর্নিহিত ধর্মকে পরম মূল্য দিয়েই কথাটা সাজান, যে ধর্ম তাঁকেই আবিষ্কার করতে হয়েছে। যখন লেখেন ‘কলাপাতা দোলায় চামর, শিশির ধোয়ায় পা’, তখন বস্তু ও বাস্তবধর্মের পাশাপাশি গৌণকে মহিমান্বিত করে তোলার ঘটনাও ঘটে। দুই ক্ষেত্রেই মানুষ গুরুত্বপূর্ণ থেকে যায়; কারণ, প্রকৃতি ও মানুষের যৌথ জীবনের প্রাত্যহিকতা জসীমউদ্দীনের কাব্যকলার ভিত্তি। বিভূতিভূষণও গৌণকে মুখ্য করেন। মহিমান্বিতও করেন। ‘পুঁই মাচা’ গল্পে যখন লেখেন ‘তেলাকুচো লতার থোলো থোলো সাদা ফুলের মধ্যে জোছনা আটকিয়া রহিয়াছে’, তখন অনুল্লেখ্যকে অভাবনীয় কায়দায় উপস্থাপনের পাশাপাশি অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের বিবরণীও তৈরি হয়। ক্ষেন্তির পুঁইচারা রোপণের জায়গা নির্দেশ করতে গিয়ে যখন লেখেন ‘ভাঙা পাঁচিলের ধারে যে ছোট খোলা জমিতে কতকগুলা পাথরকুচি ও কণ্টিকারীর জঙ্গল হইয়াছিল’, তখন বোঝা যায় প্রকৃতি ও গ্রামের গৌণ বস্তুনিচয় সেকালে কী ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এ গল্পের অন্য এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, ‘সকালে উঠিয়া সহায়হরি উঠানে বাতাবী লেবু গাছের ফাঁক দিয়া যেটুকু নিতান্ত কচি রাঙা রৌদ্র আসিয়াছিল, তাহারই আতপে বসিয়া আপন মনে তামাক টানিতেছেন।’ এখানে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কটা প্রাত্যহিক বাস্তবের টানে এমন অন্তরঙ্গতা পায়, সহায়হরি, ক্ষেন্তি ও গল্পের সারসত্য হয়ে তা খোদ লেখকের জীবনদৃষ্টির অনিবার্য অংশ হয়ে ওঠে।
গ্রাম ও প্রকৃতির মহিমা ঘোষণার সেই ক্ষণের অন্য বড় শিল্পী জীবনানন্দের সঙ্গে এ দুজনের পার্থক্যটা বেশ পরিষ্কার। জীবনানন্দে মানুষ ও প্রকৃতির কোনো প্রকার যৌথতা ছিল না। তাঁর প্রকৃতি বিশুদ্ধ উপভোগের; সুবিধাজনক দূরত্বে থেকে আবিষ্কার ও ভোগের সামগ্রী। কবিতার বাকি অংশের আলাপে আমরা এ প্রসঙ্গে বাগবিস্তার করব। আপাতত বলা যাক, একটা বিশেষ কালে গ্রামীণ জীবনের আর প্রকৃতির তুচ্ছ ও অনুল্লেখ্যকে মহিমান্বিত করার যে প্রবল সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল, শিল্পের উৎপাদক ও ভোক্তা দুই দিক থেকেই এর প্রতি যে গভীর অনুরাগ দেখা গিয়েছিল, জীবনানন্দ দাশ সে কালের অন্যতম প্রধান কলাকার। জীবনযাপনের সামগ্রিক আবহের মধ্য দিয়ে অচেতনে জমা না হলে নিছক ব্যক্তিগত আগ্রহের জায়গা থেকে এ মাপের নতুন আবিষ্কার ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। কল্লোলীয় সাহিত্যিক আবহে জসীমউদ্দীন এবং বিভূতিভূষণ থেকে আমরা যে উদাহরণ চয়ন করলাম, তাতে পরিষ্কার বোঝা যায়, যুগধর্মের প্রতাপেই জীবনানন্দের পক্ষে বাংলা অঞ্চলের প্রতিনিধিস্থানীয় সৌন্দর্য হিসাবে ‘ফণীমনসা’ ও ‘শটি-বন’কে নির্বাচন করা সম্ভব ছিল; আর নিজ বিশ্বাসের আশ্বাসেই এ কাব্যকলায় পাঠককে বশীভূত করাও দুরূহ হয়নি।
৪
কবিতার বাকি আট পংক্তি কাজ করেছে বিস্তারের—সনেটের ধর্ম ঠিক রেখে, কিন্তু পংক্তিবিন্যাস না মেনে; আর বিস্তারের কাজে আশ্রয় করেছে বাংলা অঞ্চলের সবচেয়ে প্রভাবশালী লোক-মিথকে। চাঁদ সওদাগর বাংলার যে রূপ দেখেছে তাতে নুতনত্ব নাই, বরং পুনরাবৃত্তি আছে। ‘নীল ছায়া’ কথাটার বিশেষত্ব সত্ত্বেও তাতে মর্মের দিক থেকে কোনো বদল আসেনি। শুধু বদলেছে দেখার দৃষ্টিকোণ। চাঁদ সওদাগর এ দৃশ্য দেখেছে তার ডিঙা থেকে। নদীর বুকে দাঁড়িয়ে। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি, দ্রষ্টার অবস্থান দ্রষ্টব্যের নির্ণয়ের জন্য জরুরি, অন্তত জীবনানন্দের কবিতায়। কিন্তু এ দুই পংক্তিতে প্রেক্ষকের অবস্থানের সুস্পষ্ট বদল হলেও প্রেক্ষিতের বদল খুব একটা হয়নি। বরং ‘এমনই’ শব্দের ওপর জোর দিয়ে কবি চেয়েছেন বদল যে হয়নি সে বোধ যেন পাঠকের মনে বিশেষভাবে কাজ করে।
এ উচ্চারণের মধ্যে ‘আবহমান বাংলা’র একটা বোধ তৈরির চেষ্টা হয়তো কাজ করেছে। পুরানা বাংলার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে হয়তো একথাও বলা গেছে যে, আজকের এই বাংলাদেশ আর তার ভূ-প্রকৃতি মোটেই ভুঁইফোঁড় কোনো ব্যাপার নয়। ‘না জানি সে-কবে’ কথাটা চাঁদ সওদাগরকে অনির্দিষ্ট অতীতের সঙ্গে সম্পর্কিত করে। আর সেই অচিহ্নিত অতীতের একজন মানুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বাংলার একই রূপ দেখেছিল, এ কথা খোদ বাংলার রূপকেই মহিমান্বিত করে। কিন্তু এই দাবির পেছনে অন্য এক দার্শনিক উপলব্ধিও কাজ করেছে। মাত্র এক কবিতা আগে, রূপসী বাংলা কাব্যের ভূমিকা-কবিতায় জীবনানন্দ এই দার্শনিকতা প্রস্তাব করেছেন :
পৃথিবীর এই গল্প বেঁচে রবে চির কাল;
এশিরিয়া ধুলো আজ—বেবিলন ছাই হয়ে আছে।
প্রকৃতি তার স্বভাবের কারণে, তুলনামূলক দীর্ঘজীবিতার কারণে কিংবা পুনরুৎপাদনের ক্ষমতার কারণে অন্তত মানুষের তুলনায় বা মনুষ্যনির্মিত সভ্যতার তুলনায় অনেক বেশি ঘাতসহ। একে আক্ষরিক অর্থে চিরকালীন বলা না গেলেও প্রতীকী অর্থে বলা খুবই সম্ভব। এই বলাটা সেকালে, আমাদের পূর্বকথিত বিশ-তিরিশের দশকে, খুবই জরুরি হয়ে উঠেছিল। উপনিবেশিত কেন্দ্রের বিপরীতে ‘দেশ’-এর দাবিটা জানাতে হচ্ছিল প্রান্তকে ঘিরে। সেই দাবিতে বড় হয়ে উঠেছিল গ্রাম ও প্রকৃতি। চাঁদ সওদাগরের বরাতে প্রকৃতির চিরকালীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে বস্তুত দেশের অজরামর সত্তাই জোরালোভাবে ঘোষিত হলো।
এই ঘোষণা অব্যাহত থাকবে পরের ছয় পংক্তিতেও। চাঁদ সওদাগর থেকে খানিকটা সরে কবি যাবেন বেহুলার দিকে। বেহুলাকে আবিষ্কার করবেন নদীতে আর স্বর্গে—দুটি ছবিতে। প্রথম ছবিতে বেহুলা দেখবে বাংলার মুখচ্ছবি, আর আমরা দেখব বেহুলাসমেত তার দেখা চিত্রকলা; পরের ছবিতে নৃত্যরত বেহুলা নিজেই হয়ে উঠবে ছবির সাবজেক্ট—দূরে, বহু দূরে বাংলার প্রতিনিধি হয়ে। বিশেষ উপকরণের স্বরচিত মহিমা বাংলার বিশিষ্টতার সঙ্গে মিলে এ দুই ছবিতে যে গভীরতা আর মাধুর্যে মূর্তিমান হয়েছে, তার তুলনা যেকোনো ভাষার যেকোনো সাহিত্যেই বোধ করি দুর্লভ।
বেহুলার দেখা এই ছবিতে বিশেষের মহিমা ফুটেছে এমনকি কবির দেখা দোয়েলের চেয়েও নিপুণ ভঙ্গিতে। বেহুলা ছিল গাঙুড়ের জলে, ভেলায় ভাসমান। তখন কৃষ্ণা দ্বাদশীর জোছনা মরে গেছে। রহস্যময় আলো-আঁধারের সেই আবছায়া একেবারেই নির্দিষ্ট আবহ পেয়েছে স্থানের নির্দিষ্টতায়। উন্মুক্ত বিল, ধানক্ষেত আর নদীর চড়ার পটভূমিতে চাঁদ ডুবে যাওয়ার পরেও যে আলো অবশিষ্ট থাকে, তারই প্রশ্রয়ে বেহুলা দেখবে ‘সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট’। বেহুলার চোখে এই সাবজেক্ট আর পাঠকের চোখে বেহুলাসহ তার দেখা উপকরণগুলো আলো এবং দৃষ্টিকোণসমেত ফ্রেম করলেই এই চিত্রকলার বিশেষত্ব এবং মহত্ত্ব যুগপৎ উপলব্ধি করা যাবে। সঙ্গে এও চোখে পড়বে, কবিতার প্রথমাংশের ছবির সঙ্গে এ ছবির নির্মাণগত সাযুজ্য বিস্তর। কিন্তু এই পরের ছবিটিই মহত্তর। একদিকে এক পৌরাণিক চরিত্রের দ্রষ্টব্য হয়ে এ ছবি সময়ের দিক থেকে পেয়েছে বিপুল বিস্তার। অন্যদিকে, দ্রষ্টার অবস্থানটা পৌরাণিক গল্পের সঙ্গী হয়ে এবং খোদ দ্রষ্টাই দ্রষ্টব্য হয়ে সাবজেক্টের জটিলতা বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। তদুপরি, ‘শ্যামার নরম গান’কে যদি পট-সঙ্গীত হিসাবে দেখি, তাহলে বহুস্তর ছবিটিতে যুক্ত হয় আরেক নতুন মাত্রা। তাতে সঞ্চারিত হয় চলচ্চিত্রের গুণ। প্রশস্তিগীতির এ এক বিরল কাব্যিক আয়োজন।
পরের ছবিতে ইন্দ্রের সভায় নৃত্যরত বেহুলাকে দেখি। ‘খঞ্জনার মতো’ উপমায় দেশীয় অনুষঙ্গ আছে, তারচেয়ে অনেক বেশি আছে জান-বাজি-রাখা মরিয়া নৃত্যের আভাস। যাকে মৃত স্বামীর জান বাঁচাতে ইন্দ্রের মন গলাতে হবে, তার নাচের একাগ্রতা ফুটে উঠেছে এ উপমায়। ‘ছিন্ন’ বিশেষণটি হয়ত কাটা মুরগির ছটফটানির কথা মনে করিয়ে দেয়; বা চঞ্চল খঞ্জনার তুরীয় চাঞ্চল্যের বার্তা বহন করে। পরের পংক্তির ‘কেঁদেছিল’ কথাটাও বেহুলার কান্নারই এক অতি-শিল্পিত প্রকাশ। কিন্তু পরের পংক্তির অন্য উপকরণগুলো বাংলার চিরকালীন অস্তিত্বের সঙ্গে বেহুলাকে আর বেহুলার নাচকে যেভাবে একাত্ম করে তুলেছে, তার কাব্যকৌশলগত এবং তাৎপর্যগত তুলনা বিরল।
এই শেষ পংক্তিতে কবি আবার নির্বাচন করেছেন এমন এক তৃণ যা মানুষের পায়ের নিম্নভাগের সঙ্গে সম্পর্কিত বটে, আর সেদিক থেকে হয়তো ঘুঙুরের তুলনা হিসাবেও মানানসই, কিন্তু ভাঁট-ফুলকে আর যাই হোক প্রতিনিধিস্থানীয় উপকরণ হিসাবে গণ্য করা চলে না। জীবনানন্দ কেন এবং কোন প্রেরণায় একে সম্ভবপর করেন, তার এক প্রস্ত ফিরিস্তি আমরা আগেই দাখিল করেছি। বাংলার নদী-মাঠের সঙ্গে মিলে এই ভাঁটফুল বেহুলার সমব্যথী হয়ে যদি শোকাতুর হয়ে ওঠে অমরার নৃত্যসভায়, তাহলে বলতেই হয়, পরিবেশের সঙ্গে জীবনযাপনকারী ব্যক্তির অন্তরঙ্গ খাতিরের নমুনা হিসাবেই তা পাঠ্য। কিন্তু লক্ষণবিচারে মনে হয়, এই খাতির শুধু সমব্যথী হওয়াতেই সীমিত নয়, এর অন্য শৈল্পিক তাৎপর্য আছে।
বেহুলা ইন্দ্রের সভায় নেচেছিল, একথা সত্য হলে বলতেই হবে, সে নৃত্যপটীয়সী নারী। আর তার নাচে যদি ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়েই থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, নৃত্যের ভঙ্গিমায় ইন্দ্রসভার অপ্সরীদের সঙ্গে পাল্লা দেয়ার মতো কলা বেহুলার দখলে ছিল। কিন্তু মানুষের আর দশ উৎসারণের মতো নৃত্যকলারও তো স্থানিকতা আছে। প্রাকৃতিক যেসব বিশিষ্টতার কল্যাণে মানুষের সাংস্কৃতিক ফারাক হয়, সেগুলোর বিশেষ চিহ্ন তো অমোচনীয় ছাপ এঁকে দেবে নৃত্যকলায়। তার মানেই হলো, বেহুলার নাচের মুদ্রায় যে ঐশ্বর্যের প্রকাশ ঘটেছে, বাংলার প্রকৃতি তার অনিবার্য অঙ্গ। বাংলার নদী-মাঠ বা ভাঁটফুলের মতো উপকরণগুলোই ওই মুদ্রার আদি উৎস। বিপরীতে এও বলতে হয়, কোনো ভূমির প্রাকৃতিক সত্তার সঙ্গে সে ভূমিজ মানুষের অস্তিত্বের সম্পর্ক অন্তরঙ্গ—আকস্মিক কিছু নয়। সেই অন্তরঙ্গতা সঙ্গী হলেই কেবল শিল্পভাষার রহস্য হয়ে উন্মোচিত হতে পারে এরকম অনালোকিত সুন্দর। বেহুলার নাচেও, জীবনানন্দের কবিতায়ও।
• প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপক, বাংলাদেশ।