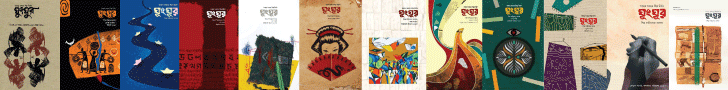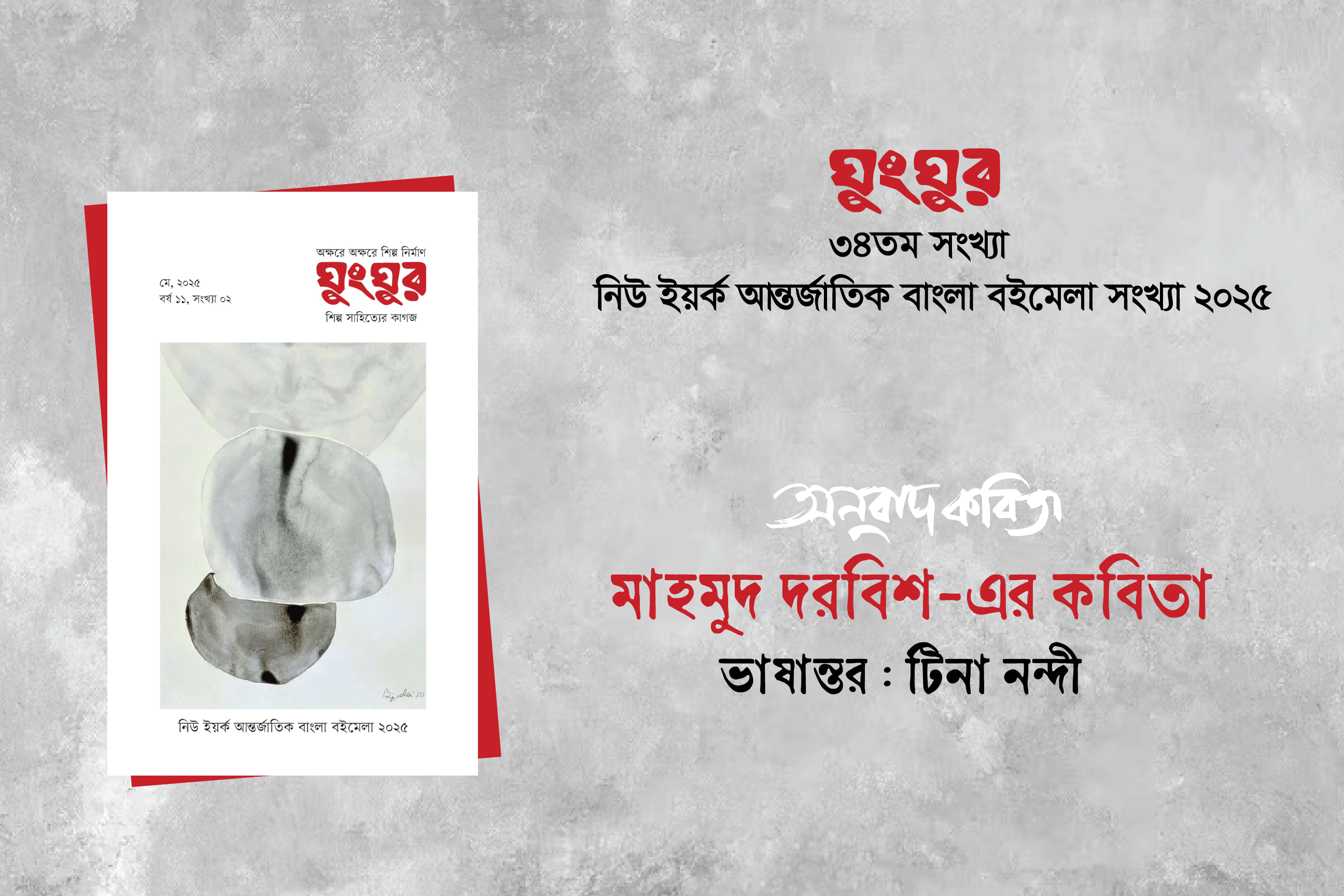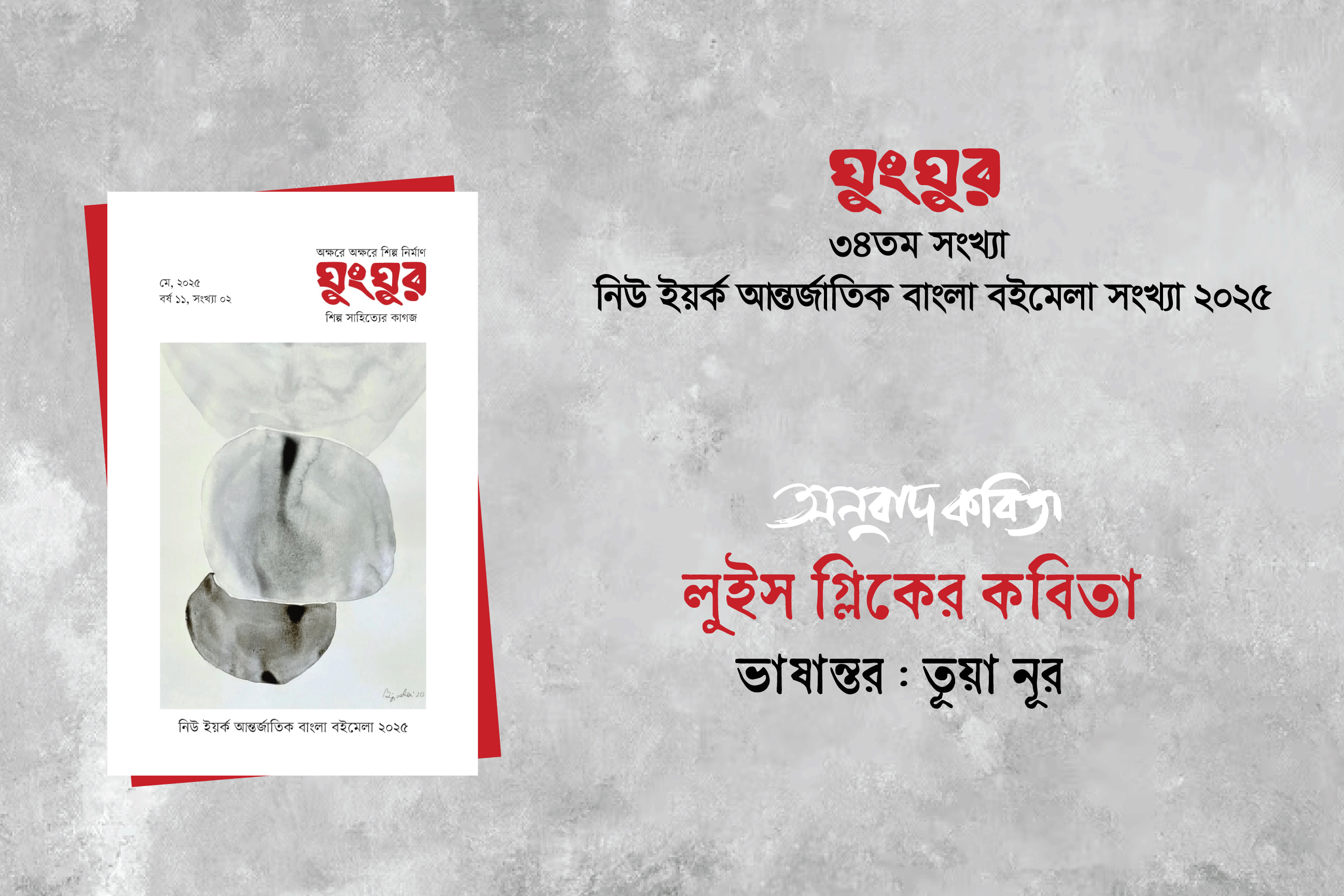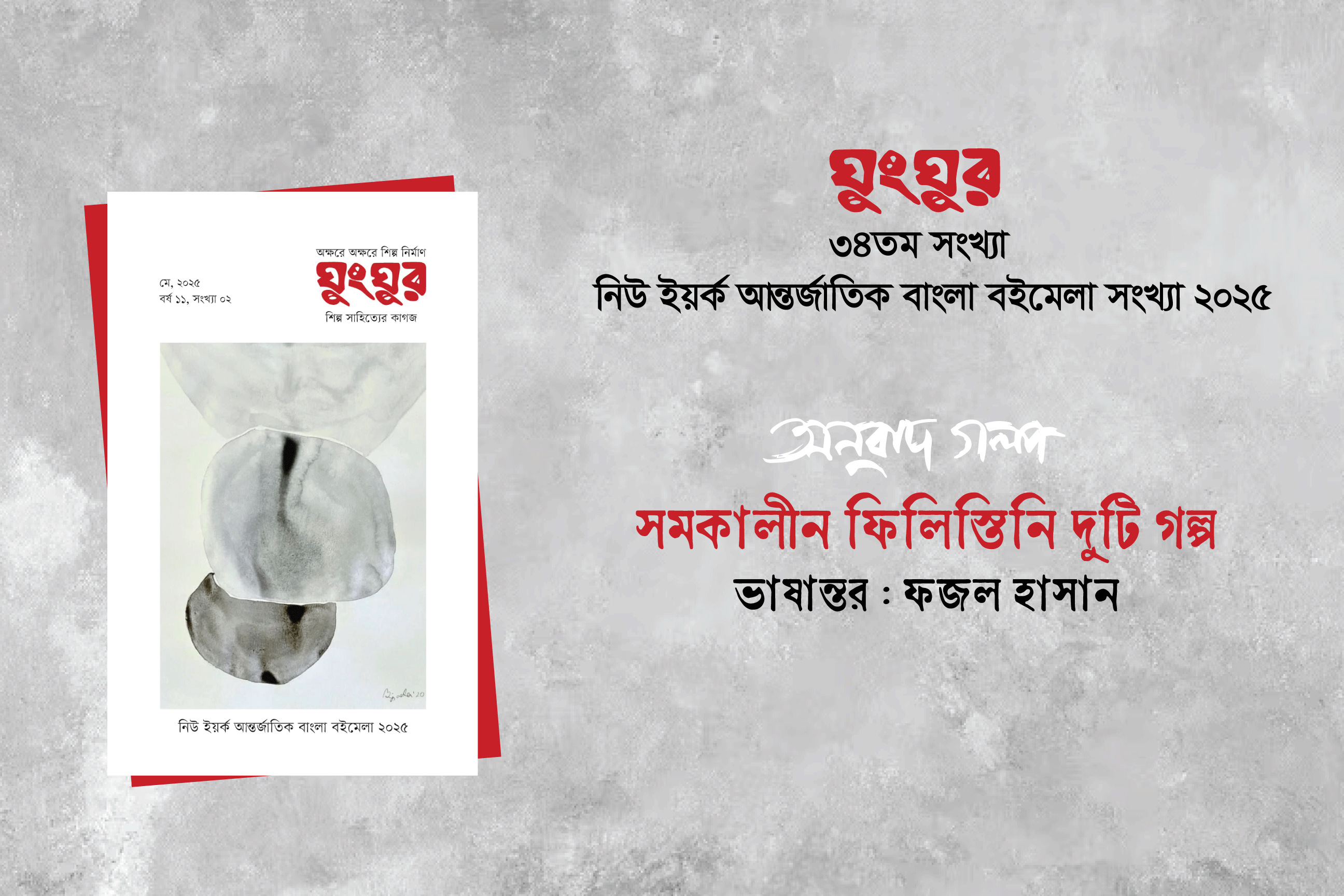আমার বাবা

[ইস্তাম্বুল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়েরই সীমান্তবর্তী নগরী। শতবর্ষ আগে ফরমান জারি করে সেখানে চাপিয়ে দেয়া হয় ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুষঙ্গ। যদিও প্রাত্যহিক জীবনে ইসলাম ও প্রাচ্যের প্রভাব তখনো প্রবল। দুটো ভিন্ন তরঙ্গের অভিঘাত দোটানায় ফেলে দেয় নাগরিকদের। আশির দশকে উদভ্রান্তির ঘোর মৌসুমে বসফরাসের তীরবর্তী একটি অভিজাত অ্যাপার্টমেন্টে বসে নিজের শহরের কাহিনি লিখতে শুরু করলেন অরহান পামুক। স্থাপত্যবিদ্যার ডিগ্রি মাঝপথে ছেড়ে লেখক হওয়ার আশায় বিভোর এক যুবক। দেশের অস্থিরতার উৎস ও সমাধান যে খুঁজছিল কয়েক শতাব্দী ধরে ইস্তাম্বুলের ধারাবাহিক উত্থান ও অবক্ষয়, স্বতঃস্ফূর্ত উৎসব ও ভীষণ দাঙ্গার গল্পগুলোর মধ্যে। নাকি পামুক খুঁজছিলেন আপন যন্ত্রণার উপশম?
বহু পরে ইস্তাম্বুল : একটি নগরীর স্মৃতিগুচ্ছ (২০০৫) বইতে তিনি স্বীকার করবেন, ‘ইস্তাম্বুলের কাহিনি বলতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম এ তো আমার নিজের কথাই বলছি। আর আমার জীবনের ছবি আঁকার পর দেখলাম সেটা ইস্তাম্বুলের চেহারা।’
গল্প বোনার অপূর্ব মুনশিয়ানা তাকে দেশের জনপ্রিয়তম লেখক করে তুলল। একপর্যায়ে তো বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায় তুরস্কের মুখ। পামুকের আ স্ট্রেঞ্জনেস ইন মাই মাইন্ড, মাই নেম ইজ রেড, স্নো, হোয়াইট ক্যাসল ইত্যাদি উপন্যাস অনূদিত হয়েছে ৬৩টি ভাষায়। অর্জন করেছেন নোবেল পুরস্কার (২০০৬), সনিং পুরস্কার (২০১২) ও ডাবলিন সাহিত্য পুরস্কার (২০০৩)।
অরহান-অনুরাগী পাঠকের জন্য আনন্দের বিষয় হলো, তাদের প্রিয় লেখক সত্তর ছুঁয়েও কর্মব্যস্ত। এক সাক্ষাৎকারে অরহান পামুক বলেছেন, ‘আমি সবচেয়ে বেশি সুখী থাকি যখন ডেস্কে বসে লেখালেখিতে ডুব দিই।’]
সেই রাতে বাড়ি ফিরেছিলাম দেরি করে। ওরা বলল, আব্বা মারা গেছেন। শোকের প্রাথমিক আঘাত সামলে নিতে না নিতে ছোটবেলার একটা দৃশ্য ভেসে উঠল : হাফপ্যান্ট পরা আব্বার সরু দুটো পা।
রাত দুটোর সময় শেষবারের মতো দেখার উদ্দেশ্যে আব্বার বাড়িতে গেলাম। লোকজন বলল, পেছনের রুমে রাখা হয়েছে। ভেতরে ঢুকলাম। কয়েক ঘণ্টা পর ভোরের ঠিক আগে আগে ভালিকোনাগি এভিনিউতে (ইস্তাম্বুলের জনপ্রিয় শপিং জোন) যখন ফিরে এলাম, নিসানতাসির (অভিজাত এলাকা) রাস্তাগুলো জনশূন্য ও শীতল থমথমে হয়ে আছে। টিমটিম করে আলো জ্বলছে দোকানগুলোর জানালায়। ৫০ বছর ধরে ওগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে পার হই। সেদিন বহুদূরের ও অচেনা ঠেকল।
নির্ঘুম রাতের পর সকালবেলা ফোনে আলাপ সারলাম, দর্শনার্থীদের স্বাগত জানালাম এবং শেষকৃত্যের আয়োজনে ডুব দিলাম। যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে। নোট নিচ্ছি, অনুরোধ ও সান্ত্বনাবাণী শুনছি, ছোটখাটো ঝগড়াবিবাদ ফয়সালা করতে হচ্ছে এবং মৃত্যুসংবাদ লিখতে হচ্ছে, এরই মধ্যে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, সব মৃত্যুতেই কেন মৃতের চেয়ে আচার-অনুষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
সন্ধ্যাবেলা আমরা এদিরনেকাপি (ইস্তাম্বুলের সবচেয়ে বড়) কবরস্থানে গেলাম দাফনের প্রস্তুতি নিতে। আমার এক চাচাত ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বড় ভাই যখন কবরস্থানের ছোট্ট প্রশাসনিক ভবনে ঢুকলেন, আবিষ্কার করলাম ট্যাক্সিতে আমি ও ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই। ড্রাইভারটি বলে উঠলেন, তিনি আমাকে চিনতে পেরেছেন। আমি তাকে বললাম, আমার বাবা মারা গেছেন। আগপিছ কিছু না ভেবেই আমি আব্বার সম্পর্কে বলতে শুরু করলাম—আব্বা খুব ভালো মানুষ ছিলেন। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমি তাকে ভালোবাসতাম।
সূর্য একটু পরেই অস্তাচলে যাবে। গোরস্থান নির্জন শুনশান। গোরস্থানকে ঘিরে রাখা উচুঁ ধূসর ভবনগুলো প্রতিদিনকার বিমর্ষতা ঝেড়ে ফেলে অদ্ভুত আলো ছড়াচ্ছে। যখন কথাগুলো বলছিলাম, কোথা থেকে যেন হিম বাতাসের ঝাপটা এসে প্লেন ট্রি ও সাইপ্রাস গাছগুলোকে দোলাতে শুরু করল। আব্বার সরু পা দুটোর মতো এই দৃশ্যটাও আমার স্মৃতিতে গেঁথে গেল।
যখন আমরা নিশ্চিত হলাম যে আমাদের আরও খানিকটা সময় অপেক্ষা করতে হবে, ড্রাইভার আমার পিঠে ও বামপাশে দুটো জোরালো তবে সহানুভূতিমাখা চাপড় দিল। সে এর মধ্যে জানিয়েছে যে, আমাদের দুজনের নামে মিল আছে। আমি সেদিন তাকে যে কথাগুলো বলেছিলাম, আর কাউকে বলিনি। কিন্তু এক সপ্তাহ পর আমার স্মৃতি ও শোকের সঙ্গে ঘটনাটা আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেল। যদি আমি লিখে না ফেলতাম, এটা ক্রমশ বাড়ত এবং আমাকে তীব্র যন্ত্রণা দিত।
আব্বা একবারের জন্যেও কোনোদিন আমার দিকে চোখ রাঙাননি, কখনো বকা দেননি, কখনো গায়ে হাত তোলেননি—ড্রাইভারকে কথাগুলো বলার সময় খুব একটা ভাবনাচিন্তা করিনি। তাই বাদ পড়ে গিয়েছিল আব্বার দয়ালু হৃদয়ের সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণগুলো। যখন ছোট ছিলাম, আমার আঁকা প্রত্যেকটি ছবি খুব দরদ নিয়ে তিনি দেখতেন। হাবিজাবি প্রতিটি লেখা এমন খুঁটিয়ে দেখতেন যে মনে হতো ওটা একটা মাস্টারপিস। আমার সবচেয়ে ফালতু রদ্দিমার্কা কৌতুক শুনেও অট্টহাসিতে ফেটে পড়তেন। তিনি আমাকে যে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছেন, সেটা না পেলে লেখক হওয়া ও লেখালেখিকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়া আমার জন্যে আরও অনেক কঠিন হতো। আমরা দুই ভাই-ই যে অত্যন্ত ব্রিলিয়ান্ট ও অনন্য সেটা যে তিনি অবলীলায় আমাদের বোঝাতে পারতেন এবং আমাদের ওপর ভরসা করতেন, তার কারণ নিজের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। শিশুসুলভ সরলতার সঙ্গে তিনি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতেন যে কেবল তার পুত্র হওয়ার বদৌলেতে আমরাও তার মতো ব্রিলিয়ান্ট, পরিপক্ব ও উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন হবো।
আব্বা দারুণ সপ্রতিভ ছিলেন। মুহূর্তের অনুরোধে তিনি সেনাপ শাহাবুদ্দিনের (তুরস্কের নামকরা কবি ও কথাসাহিত্যিক) কবিতা আবৃত্তি করতে পারতেন, ১৫ ঘর পর্যন্ত পাইয়ের মান বের করতে পারতেন এবং মুভি দেখতে বসে শেষে কী ঘটতে পারে তা অনুমান করে তাক লাগিয়ে দিতেন। তিনি খুব একটা বিনয়ী ছিলেন না। নিজের সেয়ানাগিরির কাহিনি রসিয়ে রসিয়ে বলতে ভালোবাসতেন। তার প্রিয় গল্পগুলোর একটা ছিল, তিনি মাত্র হাইস্কুলে উঠেছেন, হাফ প্যান্ট তখনো ছাড়েননি। একদিন গণিত শিক্ষক সবচেয়ে বড় ক্লাসের ছাত্রদের রুমে তাকে ডেকে পাঠালেন। যে অঙ্কটা নিয়ে তার চেয়ে তিন ক্লাস ওপরের ছাত্ররা হিমশিম খাচ্ছিল, ব্ল্যাকবোর্ডে তিনি সেটার সমাধান বের করে ফেললেন। শিক্ষক সাবাস বলে উঠলেন আর আব্বা তখন বুক ফুলিয়ে বড় ভাইদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। তার এসব কীর্তি শুনে আমি একইসঙ্গে ঈর্ষা ও তার মতো হওয়ার আকাঙ্ক্ষার দোটানায় পড়ে খাবি খেতাম।
তার নজরকাড়া চেহারার ব্যাপারেও আমি সমানভাবে বলে যেতে পারব। সবাই বলত তার সঙ্গে নাকি আমার চেহারার মিল আছে। তবে তিনি আরও বেশি সুপুরুষ ছিলেন। একের পর এক ব্যবসায় ভরাডুবির পরও নিঃশেষ করতে না পারা পৈতৃক সম্পদ আর নজরকাড়া রূপের জোরে তার জীবনটা ছিল ভাবনাহীন আনন্দে ভরপুর। তাই প্রবল দুঃসময়েও তিনি বোকার মতো আশাবাদী হতে পারতেন, নিজের সামর্থ্য নিয়ে অটল থাকতে পারতেন। তার কাছে জীবনটা হাসিল করার বিষয় ছিল না, ছিল উপভোগের। পৃথিবীটা রণক্ষেত্র নয়, বরং খেলার মাঠ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা বিরক্ত হতেন এটা ভেবে, যৌবনে তার রূপ, বুদ্ধি ও সম্পদের যে জোয়ার ছিল সেই তুলনায় তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তির পাল্লা ততটা ভারি হয়নি। তবে অন্য সমস্ত ব্যাপারের মতোই এটা নিয়েও তিনি বেশিক্ষণ মাথা ঘামাতেন না। যেকোনো সমস্যা শিশুসুলভ ভঙ্গিতে যেভাবে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতেন তেমনি এই হতাশাও কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঝেড়ে ফেলতে পারতেন। তাই ত্রিশের পর তার জীবন থেকে লক্ষ্মীর বিদায়ে আশাভঙ্গের মিছিল ক্রমশ দীর্ঘ হতে শুরু করলেও তাকে কোনোদিন নালিশ করতে শুনিনি।
তার বৃদ্ধ বয়সের ঘটনা। নামকরা এক সমালোচক ও তিনি একত্রে ডিনার করেছিলেন। সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরে যখন দেখা হলো তিনি বেশ বিরক্তির সুরে আমাকে বলেছিলেন, আপনার বাবার জীবনে তো কোনো কমপ্লেক্স নেই দেখছি!
পিটার প্যানসুলভ আশাবাদ তাকে ক্রোধ ও মোহাচ্ছন্ন হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। তিনি প্রচুর বই পড়েছেন, কবি হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন, এমনকি বয়সকালে ভ্যালেরির কিছু কবিতাও অনুবাদ করেছেন; তারপরও আমার বিশ্বাস, তিনি নিজস্ব আরামবলয়ে বড্ড সেঁধিয়ে গিয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতের ব্যাপারে এতটাই নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, সাহিত্যিক সৃজনশীলতার জন্যে প্রয়োজনীয় তীব্র আবেগ তাকে কব্জা করতে পারেনি। যৌবনে তার সমৃদ্ধ একটা লাইব্রেরি ছিল। পরবর্তী সময়ে সেখানে আমার তাণ্ডব দেখে তিনি খুশিই হতেন। কিন্তু আমার মতো গোগ্রাসে ও উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা হয়ে তিনি বই পড়তেন না। তিনি পড়তেন তৃপ্তির জন্যে, চিন্তাভাবনার মোড় ঘোরানোর উপায় হিসেবে এবং বেশিরভাগ বই অর্ধেক বাকি রেখে দিতেন। অন্যদের বাবারা গলার স্বর নিচু করে জেনারেল ও ইমামদের গল্প শোনাতেন, আর আমার বাবা পায়ে হেঁটে প্যারিস আবিষ্কার কিংবা (জ্যঁ পল) সার্ত্রে ও (আলবেয়ার) কামুর সঙ্গে সাক্ষাতের গল্প করতেন। এই গল্পগুলো আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।
অনেক বছর পরে, একটি গ্যালারির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এরদাল ইনোনুর (লেখকের বাবার শৈশবের বন্ধু ও তুরস্কের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ইসমত পাশার ছেলে) সঙ্গে দেখা হলো। তিনি স্মিত হেসে আঙ্কারার রাষ্ট্রপতি ভবনে এক নৈশভোজের স্মৃতি রোমন্থন করলেন। আব্বার বয়স তখন ২০। প্রেসিডেন্ট সাহিত্য সম্পর্কে আলাপ শুরু করতেই আব্বা প্রশ্ন করে বসলেন, ‘আমাদের দেশে বিশ্বখ্যাত কোনো লেখক নেই কেন?’ আমার প্রথম উপন্যাস বের হওয়ার ১৮ বছর পর, আব্বা একদিন কিছুটা সলজ্জ ভঙ্গিতে আমাকে একটা ছোট্ট স্যুটকেস দিলেন। ওটার ভেতরে তার জার্নাল, কবিতা, নোট ও সৃজনশীল রচনা খুঁজে পাওয়ার পর অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলাম। অস্বস্তির কারণটা আমি ভালো করেই জানি। স্যুটকেসটা ছিল একটা অন্তর্গত জীবনের (inner life) প্রমাণ। বাবা পরিচয়ের বাইরে তার যে নিজস্ব একটা ব্যক্তিসত্তা থাকবে তা আমরা সন্তানরা মেনে নিতে পারি না। আমরা তাকে আমাদের প্রত্যাশার মাপেই দেখতে চাই।
আব্বা যখন আমাকে সিনেমা দেখতে নিয়ে যেতেন খুব ভালো লাগত। আর সেই সিনেমাগুলো নিয়ে অন্যদের সঙ্গে তার আলাপ শুনতেও খুব ভালো লাগত। নির্বোধ দুষ্টু ও আত্মা বিকিয়ে দেয়া লোকজনকে নিয়ে যে রসিকতাগুলো করতেন সেগুলোও আমার প্রিয় ছিল। একইভাবে ভালোবাসতাম যখন নতুন কোনো ফল, নতুন দেখা কোনো শহর বা নতুন কোনো বই নিয়ে আলাপ করতেন। সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতাম যখন তিনি আমাকে আদর করতেন। আর ভালো লাগত যখন কোথাও বেড়াতে নিয়ে যেতেন। কেননা গাড়িতে বসে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও মনে হতো, আব্বা হারিয়ে যাবেন না। গাড়ি চালানোর সময় পরস্পরের দিকে তাকিয়ে যেহেতু কথা বলা যায় না, তিনি আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো আলাপ করতেন, অত্যন্ত জটিল ও স্পর্শকাতর সব বিষয়ে। কখনো তিনি হয়তো থামতেন চুটকি বলার জন্যে, রেডিওটা ঘুটুরঘুটুর করার জন্যে কিংবা রেডিওতে যে গান বাজছিল সেটার সম্পর্কে বলার জন্যে।
তবে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেতাম এটা ভেবে যে, আমি আব্বার কাছাকাছি আছি, তাকে স্পর্শ করছি ও তার পাশে বসে কোথাও যাচ্ছি। আমি যখন কলেজে পড়ি, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরুর দিকেও জীবনের কঠিনতম ডিপ্রেশনের দিনগুলোতে মনে মনে চাইতাম, আব্বা যেন বাড়ি এসে আমার এবং আম্মার পাশে বসবেন ও আমাদের মন চাঙা হয় এমন কিছু বলবেন।
শৈশবে তার কোলে উঠতে বা পাশে শুয়ে তার গায়ের গন্ধ শুঁকতে ও ছুঁয়ে দেখতে ভালোবাসতাম। আমার মনে আছে, তখন আমি খুব ছোট, হেবেলিআদায় (মর্মর সাগরের একটি বড় দ্বীপ) তিনি আমাকে কীভাবে সাঁতার শিখিয়েছিলেন। পানির নিচে ডুবে যাচ্ছি, পাগলের মতো হাত-পা ছুড়ছি, হঠাৎ তিনি আমাকে ধরে ফেললেন, আমার উচ্ছ্বাস তখন দেখে কে! আবার শ্বাস নিতে পারছি সেজন্যে নয়, দুহাতে আব্বাকে যে জড়িয়ে ধরতে পেরেছি সেই আনন্দে এত উচ্ছ্বাস। পানির তলে ডুব দেয়া এড়াতে চিৎকার করে বলতে লাগলাম, ‘আব্বা, আমাকে ছেড়ে যেও না।’
কিন্তু তিনি আমাদের ছেড়ে গেলেন। তিনি পাড়ি দেবেন বহুদূরে, ভিনদেশে, অন্য কোথাও, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অজানা প্রান্তরে। সোফায় সটান হয়ে বই পড়ার সময় মাঝেমধ্যে পৃষ্ঠা থেকে চোখ তুলে তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে ভাবনায় ডুবে যেতেন। সেই মুহূর্তগুলোতে টের পেতাম, আব্বা বলে আমি যাকে চিনি তার ভেতরে আছে আরেক মানুষ, যে আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে। তিনি অন্য কোনো জীবনের খেয়ালছবি আঁকছেন আন্দাজ করে অস্বস্তি হতো আমার। তিনি কখনোসখনো বলতেন, নিজেকে আমার মনে হয় অকারণে ছোড়া কোনো বুলেট।
হাতেগোনা কিছু বিষয়ে আমার রাগ উঠত। আব্বার এই কথাটা ছিল তার একটি। আমি জানি না সেদিন কে সঠিক ছিল। ততদিনে আমিও সম্ভবত পালানোর জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম। তারপরও মুগ্ধ হতাম যখন তিনি ব্রাহমের (জার্মান সুরকার) প্রথম সিম্ফোনির টেপ ছেড়ে দিয়ে অদৃশ্য ব্যাটন হাতে অর্কেস্ট্রার নির্দেশনা দিতে শুরু করতেন।
সারাজীবন আনন্দের সন্ধানে ও ঝুটঝামেলা থেকে তিনি পালিয়ে বেড়িয়েছেন। তাই যখন ইন্দ্রিয়সুখ অর্থহীন বলে তিনি বিলাপ করতেন এবং অপরের ওপর দোষ চাপাতেন, আমার খুব বিরক্ত লাগত। প্রথম তারুণ্যে কখনো নিজেকে বলতাম, দয়া করে উনার মতো হয়ো না। আবার কখনো তার মতো সুখী, আয়েশি, নিরুদ্বেগ ও হ্যান্ডসাম হতে না পারার ব্যর্থতা আমাকে পীড়া দিত।
বহু পরে সমস্যাগুলো যখন ঝেড়ে ফেললাম, যে বাবা কোনোদিন আমাকে বকেননি বা দুমরেমুচড়ে দেয়ার চেষ্টা করেননি, ক্ষোভ ও ঈর্ষার পর্দা সরে গেলে তার চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। একসময় আমি বুঝতে পারলাম ও মেনে নিলাম যে, আমাদের দুজনের মধ্যে এমন অনেক মিল আছে যা এড়ানো অসম্ভব।
হালফিল কোনো আহাম্মকের ব্যাপারে যখন গজগজ করি, যখন ওয়েটারের কাছে অনুযোগ করি, যখন ওপরের ঠোঁট কামড়ে ধরি, যখন কোনো অর্ধসমাপ্ত বই এককোনায় ছুঁড়ে ফেলে দিই, যখন আমার শিশুকন্যাকে চুমু দিই, যখন পকেটে হাত দিয়ে টাকা বের করি কিংবা হালকা রসিকতায় কাউকে স্বাগত জানাই, তখন খেয়াল হয় যে আমি তাকে অনুকরণ করছি। কেবল এজন্যে নয় যে, আমার হাত, পা, কব্জির আদল অথবা পিঠের তিলটা তার সাথে মিলে গেছে। তার সাথে মিল আমাকে ভয় পাইয়ে দেয়, আতঙ্কিত করে এবং মনে পড়ে যায় ছোটবেলায় তার মতো হতে চাইতাম। আসলে প্রত্যেকের মৃত্যুযাত্রা শুরু হয় তার বাবার মৃত্যু-মুহূর্ত থেকে।
(*বন্ধনী-যুক্ত শব্দগুলো অনুবাদকের।)
রেজওয়ানুর রহমান কৌশিক প্রাবন্ধিক। বর্তমানে গবেষণা কাজে নিযুক্ত আছেন। ঔপনিবেশিকতা ও বিশ্বায়নের প্রভাবে সমাজ, অর্থনীতি ও ভূ-রাজনীতির পালাবদল সম্পর্কে তার আগ্রহ রয়েছে। তিনি ঢাকায় থাকেন।