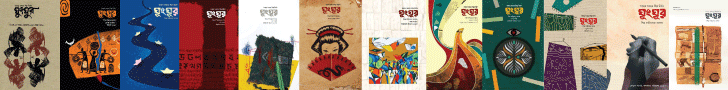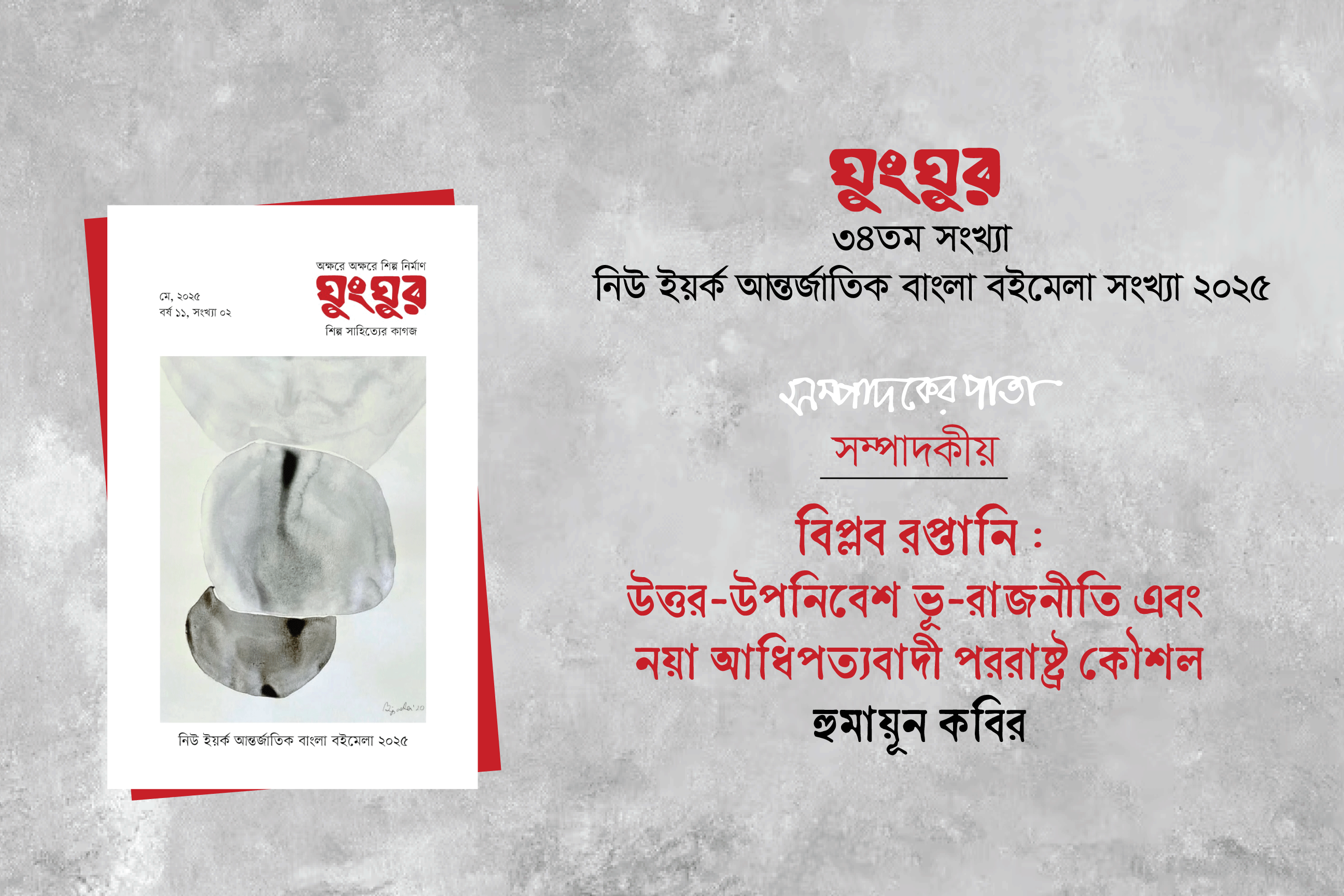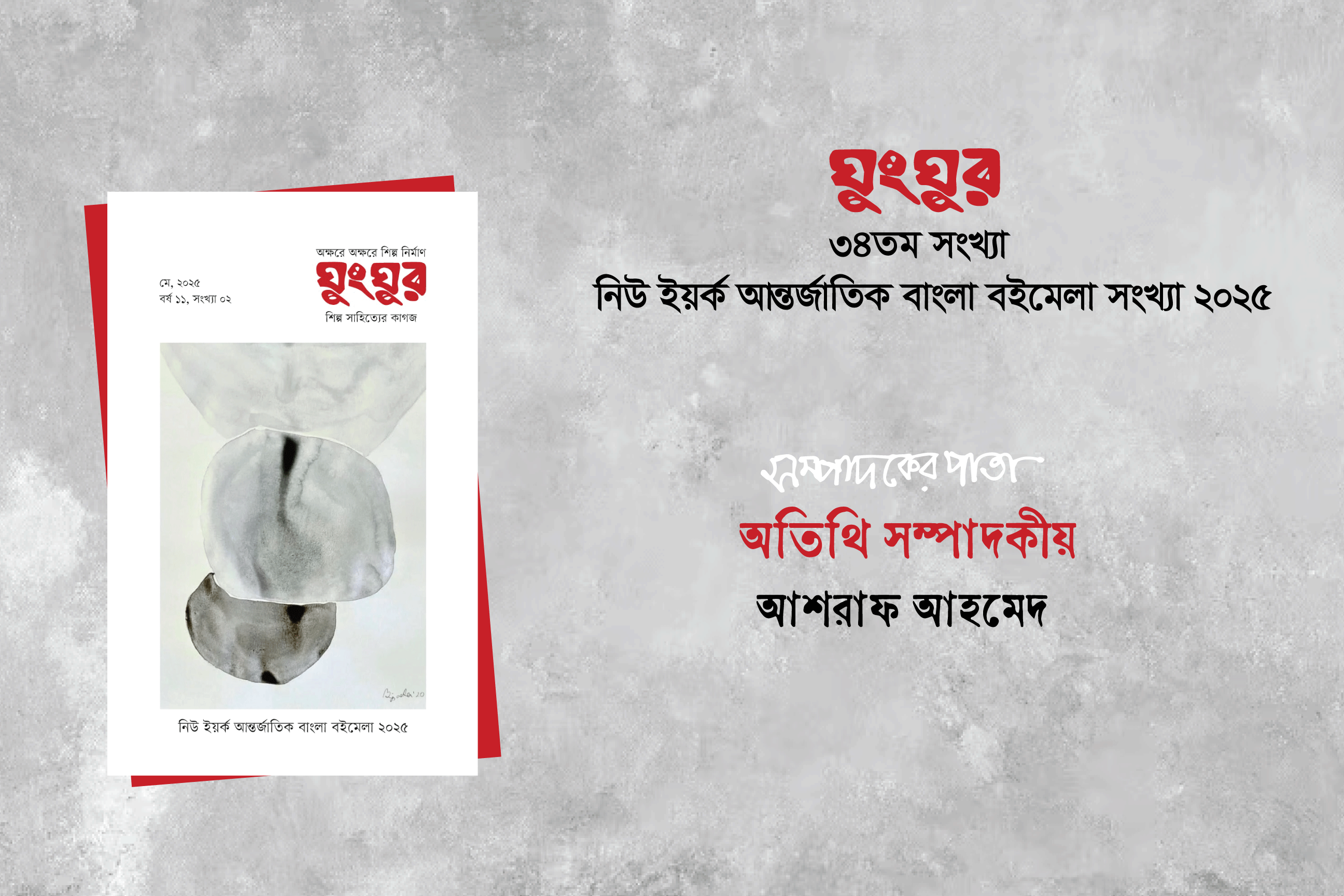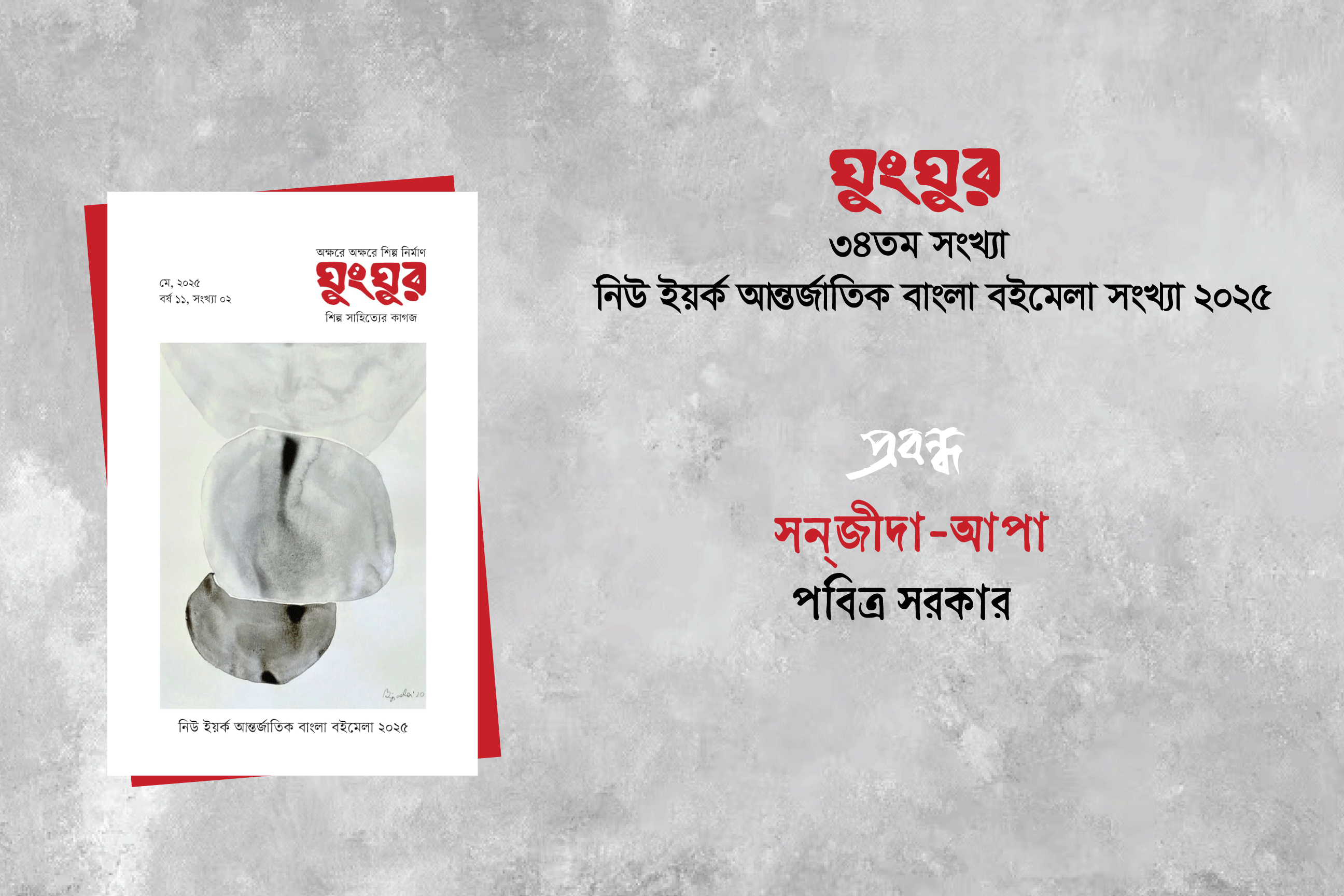বিপ্লব রপ্তানি : উত্তর-উপনিবেশ ভূ-রাজনীতি এবং নয়া আধিপত্যবাদী পররাষ্ট্র কৌশল
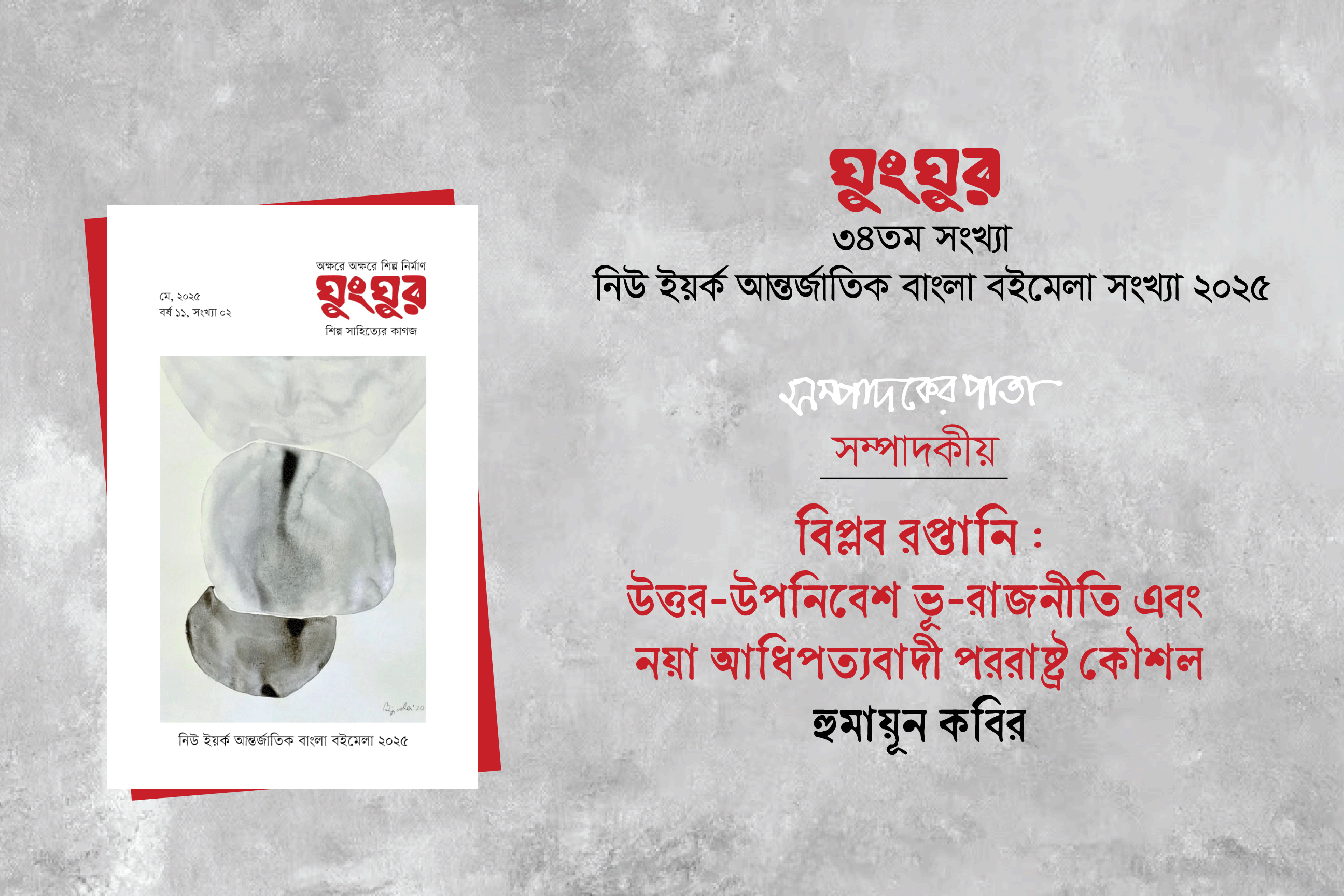
ভূমিকা
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, নানা কারণে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পৃথিবীর ভূ-রাজনৈতিক অবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসে। একের পর এক উপনিবেশগুলো হাতছাড়া হয়ে যেতে থাকলে পুঁজিবাদী বিশ্বের উপনিবেশ-নির্ভর বাজার অর্থনীতি মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ে। একই সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ দ্রুত ছড়াতে থাকলে পুঁজিবাদের তত্ত্বটিই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। শুধু তৃতীয় বিশ্ব নয়, খোদ ইউরোপেও শিক্ষিত তরুণ সমাজ ও শ্রমজীবীদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রচার প্রসার বাড়তে থাকে উল্লেখযোগ্য হারে। ইউরোপের প্রায় প্রতিটি বড় শহরে কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট পার্টির কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। এর পেছনে ছিল সাম্যবাদী দর্শনের আদর্শগত গ্রহণযোগ্যতা এবং একই সঙ্গে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের কার্যকরী প্রচার কৌশল।
বস্তুত সোভিয়েত ইউনিয়নের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার বিষয়টিতে রাখঢাক ছিল না মোটেও। ‘কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল’ (কোমিন্টার্ন) নামক সংগঠনটির মাধ্যমে দুনিয়াব্যাপী বিপ্লব করার কলাকৌশল ও রণনীতি নির্ধারণ করা হতো। ছিল নানাবিধ গোপন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রচারের জন্য বেতার কেন্দ্র, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।
এর জবাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমা বিশ্বেরও ছিল নিজস্ব প্রচেষ্টা। গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে পুঁজিবাদ ও মুক্তবাণিজ্যের প্রচার চলতে থাকে জোরেশোরে। ‘রেডিও ফ্রি ইউরোপ’-এর মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক জোটভুক্ত দেশগুলোর ভিতরে প্রপাগান্ডা কর্মসূচি চালু করা হয়। প্রথাগত রাজনীতির বাইরে শিল্প সাহিত্যের মাধ্যমগুলোকেও কাজে লাগানো শুরু হয় রাজনৈতিক প্রচারণার উদ্দেশ্যে। যেমন, এনিমেল ওয়ার্ল্ড-এর মতো রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন বিরোধী সাহিত্য প্রচার করা হয় ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার প্রণোদনায়। ভিন্নমতাবলম্বী রুশ সাহিত্যিকদের বই গোপনে বাইরে এনে ইউরোপে প্রকাশ করা হয় এবং দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে দেয়া হয় সিআইএ’র গোপন উদ্যোগে। এইসব প্রচারণার পাশাপাশি সাম্যবাদী দর্শনের বিস্তৃতি রোধে রাষ্ট্রীয় দমন নীতির আশ্রয় নেয়া হয়। খোদ যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানকে উপেক্ষা করে ‘লাল সন্ত্রাস’ এর জুজুর ভয় দেখিয়ে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রকাশ্যে হেনস্তা করা শুরু হয় সরকারি উদ্যোগে। সিনেটর ম্যাকআর্থার এবং এফবিআই প্রধান এডগার হোভার-এর মারমুখী দমন নীতিতে শুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি কিংবা শিল্প-সাহিত্যের সাধারণ চর্চা করাটাও একসময় সন্দেহজনক অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়। সরকারি নজরদারির আওতায় মার্কিন টিভি অনুষ্ঠানগুলোতে সোভিয়েত বা কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচারণা তুঙ্গে ওঠে।
ইউরোপে সোভিয়েত প্রভাব বিস্তার বন্ধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমা দেশগুলো একরোখা হয়ে ওঠে। কমিউনিজম রুখতে পুঁজিবাদী দেশগুলোর নানাবিধ অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গড়ে তোলা হয় ‘উত্তর আটলান্টিক চুক্তি’ বা ন্যাটো নামক সামরিক প্রতিবন্ধক। মহাযুদ্ধ শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্ত ঘেঁষা প্রায় সবগুলো ইউরোপীয় দেশে সোভিয়েতপন্থী কমিউনিস্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয় এবং সমাজতন্ত্রের ওপর সম্মিলিত পশ্চিমা সামরিক আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য ‘ওয়ারশ’ নামক সামরিক জোটে ঐক্যবদ্ধ হয়। এর মাধ্যমেই সূত্রপাত ঘটে দীর্ঘস্থায়ী এক স্নায়ু যুদ্ধের, শুরু হয় ন্যাটো এবং ওয়ারশ জোটভুক্ত দেশগুলোর মুখোমুখি অবস্থান।
ততদিনে, বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায়, উপনিবেশের পতন হয়েছে বিশ্বব্যাপী। শৃঙ্খলমুক্ত, সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর গণমানসে স্বভাবতই পশ্চিম-বিরোধী একটা মনোভাব বিরাজমান। যে কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী অবস্থান তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে আকর্ষণ করে প্রচণ্ডভাবে। আদর্শিক দিক থেকেও এই দেশগুলোর পশ্চাদপদ অর্থনীতি এবং ভয়াবহ দারিদ্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। দেখা যায়, মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, একের পর এক রাজতন্ত্র উৎখাত করে বামপন্থী সরকারগুলো ক্ষমতায় আসতে থাকে তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে। বাজার অর্থনীতির নানাবিধ পুঁজিবাদি কৌশল কাজে লাগিয়ে খোদ ইউরোপে সমাজতন্ত্রকে ঠেকানো সম্ভব হয়েছে, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের এই সমাজতন্ত্রমুখী প্রবণতা মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা শক্তির জন্য অতিরিক্ত হুমকি হিসেবে উপস্থিত হয়। এই হুমকির মোকাবেলায়, প্রকাশ্য সামরিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি নানাবিধ চোরাগোপ্তা কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। শুরু হয় সোভিয়েত ঘেঁষা দেশগুলোতে সরকার পরিবর্তনের গোপন কার্যক্রম। এই প্রেক্ষাপটে সিআইএ’র পরিকল্পনা এবং তত্ত্বাবধানে পশ্চিমা কর্তৃত্ব বিরোধী দেশগুলোতে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ডানপন্থী সরকার প্রতিস্থাপন একটা নৈমিত্তিক কাজ হয়ে দাঁড়ায়। মার্কিন এবং ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কর্মসূচির আওতায় সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে, প্রকাশ্য অগণতান্ত্রিক পন্থায়, সরকার পরিবর্তনের বিষয়টি এত ঘনঘন ঘটতে থাকে যে তা দেশ দুটির গণতান্ত্রিক আদর্শের ভাবধারাটিকে সরাসরি প্রশ্নবিদ্ধ করে। বিশ্বব্যাপী বুদ্ধিজীবী মহল এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়।
অবশেষে সারা বিশ্বকে জিম্মি করে রাখা শীতল স্নায়ু যুদ্ধের সমাপ্তি আসে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তি এবং কমিউনিস্ট শাসনের অবসানের মাধ্যমে। অচিরেই এই বিশাল দেশের ১৪টি রাজ্য ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে। ওয়ারশ জোট ভেঙে দেয়া হয়। এই অবস্থা পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি আকস্মিক শূন্যতা তৈরি করে, যার সুযোগ নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো। কমিউনিজম বিস্তারের লক্ষ্যে সোভিয়েত জোট কর্তৃক ইউরোপ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রহিত হওয়া সত্ত্বেও, এবং ওয়ারশ জোটের বিলুপ্তি ঘোষণা করা সত্ত্বেও ন্যাটো জোটকে অটুট রাখা হয় উদ্দেশ্যমূলকভাবে, এমনকি এর ক্রমাগত বিস্তৃতিও ঘটানো হয় দ্রুত গতিতে।
সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর যখন কমিউজমের সংঘবদ্ধ বিস্তারের প্রশ্ন কোনোভাবেই আর আলোচনার প্রসঙ্গ নয়, তখন পুঁজিবাদ ও বাজার অর্থনীতির প্রচার-প্রসারের জন্য সামনে নিয়ে আসা হলো গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়নের কনসেপ্ট। তৃতীয় বিশ্বে পশ্চিমা আধিপত্য বিস্তারের কৌশলেও পরিবর্তন এলো। বিশ্বজুড়ে এখন ‘অবাধ গণতন্ত্র’ প্রতিস্থাপনের এজেন্ডা, এমতাবস্থায় সামরিক ক্যু এর মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন দৃশ্যতই ‘অগণতান্ত্রিক’। তৃতীয় বিশ্বকে আয়ত্তে রাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কার্যপ্রণালীতে এবার কৌশলগত পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। অগণতান্ত্রিক সামরিক অভ্যুত্থানের নয়, বরং গণজাগরণ এবং গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করা গেলে একে ‘গণবিপ্লব’-এর আওতায় বৈধতা দেয়ার উপায় থাকে। এছাড়াও এতে অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের বিষয়টি প্রচারে আনা যায়। গত দশকে আমরা এই পদ্ধতির প্রয়োগ দেখেছি দেশে দেশে। উল্লেখ্য, এইসব দেশগুলোর প্রায় প্রতিটিতেই ছিল স্বৈরাচারী শাসক কিংবা নিপীড়নকামী গণতান্ত্রিক সরকার যার বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণের প্রচুর অভিযোগ এবং অনাস্থা। কিন্তু সাধারণ পর্যবেক্ষণেও একটি বিষয় উঠে আসে যে এই সবগুলো দেশই কোনো-না-কোনো ভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্ব তথা মার্কিন কর্তৃত্বকে অস্বীকার কিংবা অবহেলা করার সাহস দেখিয়েছিল।
যুগস্লাভিয়ার উদাহরণ
সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর সোভিয়েত বলয়ভুক্ত পূর্ব ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথ ধরে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই পরিবর্তনের কোনো কোনোটি ছিল শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন আবার কোন কোনটি জন্ম দেয় রক্তক্ষয়ী সংঘাতের। যুগস্লাভিয়ার উদাহরণটি একটি সংঘাতপূর্ণ পরিবর্তনের উদাহরণ। এই দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত ছয়টি রাজ্যকে প্রেসিডেন্ট টিটো তাঁর দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের কমিউনিস্ট শাসনকালে সার্থকভাবেই একত্রে রাখতে পেরেছিলেন, মূলত আদর্শগত ঐক্যবদ্ধতার কারণে। খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজমের পতনের পর এই ঐক্যবদ্ধতায় ফাটল ধরে এবং শুরু হয় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। ছয়টি রাজ্যের ভেতরে একে একে চারটি রাজ্যই স্বাধীনতা ঘোষণা করে আলাদা হয়ে যায়। বাকি দুইটি রাজ্য, সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রো, একত্রে টিকে থাকে যুগস্লাভিয়া নামে (পরবর্তীকালে অবশ্য মন্টেনিগ্রোও আলাদা হয়ে যায়)। সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচ রাজ্যগুলোর এইভাবে আলাদা হওয়াকে মেনে নেননি এবং নানাভাবে একে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করেন, শেষমেষ সেনাবাহিনী পাঠিয়ে বলপূর্বক দমন করার চেষ্টা করেন। এতে করে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংঘাত। বিশেষ করে ক্রোয়েশিয়া ও বসনিয়ায় সঙ্গে সংঘাতে সার্বিয়ার সেনাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ ওঠে। ইউরোপীয় দেশগুলো একযোগে সার্বিয়ার বিপক্ষে অবস্থান নেয়।
এই বিরোধকালীন সময়টিতে মিলোসেভিচ শক্ত হাতে বিরোধী দলগুলোকে দমন করেন, গণমাধ্যমের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করেন। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপকে রুশ প্রভাবমুক্ত করার অন্যতম প্রক্রিয়া ছিল ওয়ারশভুক্ত দেশগুলোতে কমিউনিস্ট বিরোধী, গণতন্ত্রমনা শক্তির ক্ষমতা দখল। পূর্ব ইউরোপীয় এবং বলকান দেশগুলোতে একের পর এক কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতাচ্যুত হতে থাকলেও মিলসেভিচ সার্বিয়াতে ‘সোশ্যালিস্ট পার্টি অফ সার্বিয়া’ নামে নতুন দল গঠন করেন। তাঁর রুশ ঘেষা অবস্থান এবং বাজার অর্থনীতির জন্য প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচিতে ধীরে চলা নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যথেষ্ট মাথাব্যথার কারণ ছিল। ১৯৯৬ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারে আবারো ক্ষমতায় আসে সোসালিস্ট পার্টি অফ সার্বিয়া। কিন্তু নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনে বিরোধী দলগুলো আন্দোলন শুরু করে। কিছুদিন পর ছাত্ররাও এই আন্দোলনে শরিক হয়। তুমুল আন্দোলনের মুখে মেলোসেভিচ বিরোধীদের কিছু দাবি মেনে নিয়ে কয়েকটি স্থানীয় সরকারে বিরোধীদের নির্বাচিত ঘোষণা করলে আন্দোলন থিতিয়ে পড়ে, একসময় আন্দোলনের যৌথ কাঠামো ভেঙে যায় এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেলোসেভিচ ক্ষমতায় টিকে থাকেন।
ইতোমধ্যে সার্বিয়ার অভ্যন্তরে কসভো নামক একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল স্বাধীনতার দাবি নিয়ে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। ‘কসভো লিবারেশন আর্মি’-কে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অপর দিকে সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে এই সশস্ত্র আন্দোলন শক্ত হাতে দমন করতে থাকেন। মেলোসেভিচ এমনিতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুনজরে ছিলেন না। এবার তাকে উৎখাত এবং শায়েস্তা করার একটা মোক্ষম সুযোগ হাতে এলো।
এই গৃহযুদ্ধে সার্বিয়ার সেনাদলের বিরুদ্ধে মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়া গেলে ন্যাটোর নেতৃত্বে বোমা বর্ষণ শুরু হয় সার্বিয়ার বিরুদ্ধে। একটানা আটাত্তর দিন বোমা হামলার পর অবশেষে মিলোসেভিচ হার মানেন এবং কসভো থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। কিন্তু যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশটির অর্থনীতিতে মারাত্মক ধ্বস নামে, জনমনে অসন্তোষ নেমে আসে এবং ক্রমাগত নিপীড়নের কারণে বিরোধী দলের অস্থিরতা বাড়তে থাকে। এমনি এক প্রেক্ষাপটে, মূলত বিপ্লবী ছাত্রদের একটি ছোট গ্রুপ মিলোসেভিচকে উৎখাতের জন্য সন্তর্পণে কাজে নামে। এবার তারা একা নয়, সঙ্গে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সক্রিয় সহায়তা।
সার্বিয়ার ‘বুলডোজার’ বিপ্লব
১৯৯৮ সালের ১০ অক্টোবর সার্বিয়ার বেলগ্রেড শহরে অটোপর (OTOPOR) নামক একটি সংগঠনের জন্ম হয়। ১৯৯৬ সালের ব্যর্থ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হাতে গোনা কয়েকজন ছাত্র মিলে গড়ে তোলা এই সংগঠনটি অচিরেই প্রায় সত্তর হাজার সদস্য সংগ্রহে সমর্থ্য হয়। এর পেছনে ছিল সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার বিষয়। এদের প্রতীক ছিল সাদা-কালো মুষ্টিবদ্ধ হাত। কমিউনিস্টদের ব্যবহার করা লাল রঙের মুষ্টিবদ্ধ হাতের বিপরীতে এই সাদা-কালো রঙের হাত। সংগঠনটির একক নেতৃত্ব ছিল না, ছিল সমন্বয়ক, যারা ভাগ ভাগ করে দায়িত্ব পালন করতেন। যেমন সদস্য সংগ্রহ, গণসংযোগ, বৈদেশিক যোগাযোগ, পত্র পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি।
আর্থিক অনুদান আসতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। সরাসরি সরকারি সূত্র থেকে নয়, আসতো বিভিন্ন ‘এনজিও’র মাধ্যমে। ঘটনার বহু বছর পর এখন নানাবিধ সংবাদ মাধ্যম এবং অন্যান্য সূত্র থেকে এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে সহজেই। ওয়াশিংটনে অবস্থিত ‘ন্যাশনাল এনডাওমেন্ট ফর ডেমক্রেসি’ (National Endowment for Democracy) এর কর্মকর্তা পল ম্যাকআর্থি বলেন ১৯৯৮ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত তার সংগঠন থেকে প্রায় তিন মিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছেন সার্বিয়ার সরকার উৎখাতের আন্দোলনকারীদের কাছে। ম্যাকার্থি নিজেও আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন সার্বিয়ার প্রতিবেশী দেশ হাঙ্গেরি এবং মন্টেনেগ্রোর বিভিন্ন শহরে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মেডেলিন আলব্রাইটের সঙ্গে বার্লিনে এক গোপন বৈঠক হয় আন্দোলনের নেতা হোমেন এর। ক্রোয়েশিয়ায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম মন্টেগোমারিও আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।
ইউএসএইড নামক সংস্থাটির থেকে পাঠানো হয় অনুদান। ইন্টারনেশনাল রিপাব্লিকান ইনস্টিটিউট নামক অন্য একটি সংস্থা থেকে শুধু আর্থিক অনুদান নয় বরং অটপর এর সদস্যদের ট্রেনিং এর জন্য লোক পাঠানো হয় বেলগ্রেডে। ডেনিয়েল কেলিনগার্ট নামক এক মার্কিন কর্মকর্তা অটোপর সদস্যদের সঙ্গে প্রায় ১০টি বৈঠক করেন পার্শ্ববর্তী দেশ হাঙ্গেরি এবং মন্টেনিগ্রোতে। কেলিনগার্টের সহায়তায় বুদাপেস্টের হিলটন হোটেলে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয় মার্চ মাসের ৩১ তারিখ থেকে এপ্রিলের ৩ তারিখ পর্যন্ত, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রর একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা, কর্নেল (অব.) রবার্ট হেলভেই, ২০ জন অটোপর সদস্যকে আন্দোলনের কলাকৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।
এই তথ্যগুলো এখন আর গোপন কিছু নয়, বরং খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী পত্রিকাগুলোতেই এই নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। (সূত্র : ১) প্রায় দুই বছরের প্রস্তুতির পর অভ্যুত্থানের সুযোগ আসে ২০০০ সালের জুলাই মাসে, যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়। আগে শুধু এক মেয়াদের জন্যই প্রেসিডেন্ট হওয়া যেতো। মিলোসেভিচ সরকার সংবিধানের নির্বাচনী বিধিমালা সংশোধন করে একই ব্যক্তির পরপর দুইবার প্রেসিডেন্ট হওয়াকে বৈধতা দেন। এছাড়াও নির্বাচনের নির্দিষ্ট দিনটিকে এগিয়ে আনেন। নিজেকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্যই এই পরিবর্তন বলে ধারণা করে সবাই। নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে লোক সমাগম ছিল খুবই কম, কিন্তু ফলাফলে দেখা যায় মিলোসেভিচ অনেক ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, বিরোধীপক্ষ ভোট জালিয়াতির অভিযোগ এনে রাস্তায় নামে। অন্যদিকে অটোপরের সমন্বয়কগণ গণঅভ্যুত্থানের পূর্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু করে, যার জন্য তারা গত দুই বছর প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি নিয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক জোট মাঠে থাকলেও, মূলত অটপোরের দক্ষ পরিচালনায়ই পুরো গণআন্দোলনটি বেগবান হয় এবং একসময় অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে, অক্টোবরের ৪ তারিখে, লুভিসাভ ডকিচ জো (Ljubisav Đokić Džo) নামের একজন বুলডোজার চালক তার বুলডোজার (প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল একটি এক্সকেভেটর) চালিয়ে পুলিশের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙে সার্বিয়ার সরকারি টিভি স্টেশনে ঢুকে পড়েন, এবং ছাত্ররা কেন্দ্রটি দখল করে ফেলে। এই খবর প্রচারিত হওয়ার পরপরই পুলিশ পিছু হটতে থাকে, পরের দিন মিলোসেভিচ পদত্যাগ করেন। সফল এই গণঅভ্যুত্থানটি এখন ‘বুলডোজার বিপ্লব’ নামে পরিচিত।
অতীতে ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সরকার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে, বৃহৎ শক্তির সরাসরি প্রণোদনায় পরিকল্পিতভাবে এই ধরনের গণঅভ্যুত্থানের প্রটোটাইপ হচ্ছে সার্বিয়ার স্বৈরশাসক মিলসেভিচকে উৎখাতের উদাহরণটি। সার্বিয়ার এই সফল গণঅভ্যুত্থান এতই নিখুঁতভাবে পরিকল্পিত ও এতটা দক্ষতার সঙ্গে কার্যকর করা হয়েছিল যে এটিকে স্বৈরাচার বিরোধী গণআন্দোলনের জন্য বিশেষ মডেল হিসেবে গণ্য করা হয় এখন, যা বিশ্বব্যাপী ‘বিপ্লব রপ্তানি’র পরবর্তী কর্মসূচিগুলোর জন্য একটি ছাঁচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।
‘বিপ্লব রপ্তানি’র কর্মশালা
সার্বিয়ার বুলডোজার বিপ্লবের চমকপ্রদ সাফল্যের পর উদার-গণতন্ত্র প্রচারকামী পশ্চিমা সংস্থাগুলো এর নিবিড় বিশ্লেষণ শুরু করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কট্টর কর্তৃত্ববাদী নীতিনির্ধারকেরা একে তৃতীয় বিশ্বের স্বৈরাচারী সরকার পতনের একটি উপযুক্ত কর্মসূচি হিসেবে চিহ্নিত করেন। এদের উৎসাহ ও প্রণোদনায় অটপোর দুইজন সমন্বয়ক, সারডা পপভিচ (Srdja Popovic) এবং স্লোবাডান জিনোভিচ (Slobodan Djinovic)-এর উদ্যোগে ২০০৫ সালে সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে প্রতিষ্ঠা করা হয় ক্যানভাস নামের (CANVAS, Center for Applied Non-Violent Action and Strategies) একটি রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যার মূল কাজ হচ্ছে বিশ্বব্যাপী স্বৈরাচার বিরোধী গণআন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া। এই সংস্থাটির প্রভাব বিশ্বব্যাপী এবং এর সহযোগিতায় গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছে নানা দেশে। প্রায় বছর দশেক আগে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে কেনভাসের কর্মকর্তারা প্রকাশ্যেই বলেন যে তখন পর্যন্ত তারা প্রায় ৩৭ দেশে গণঅভ্যুত্থান ঘটানোর প্রক্রিয়ায় সাহায্য করেছেন, এর মাঝে ৬টি সফল হয়েছে, যে তালিকায় রয়েছে জর্জিয়া (২০০৩), লেবানন (২০০৫), মালদ্বীপ (২০০৮), মিশর (২০১১) এবং ইউক্রেইন (২০১৪)। (সূত্র : ১২, ১৩)
তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে কীভাবে ছাত্রজনতার গণ অভ্যুত্থান ঘটাতে হবে এই নিয়ে কেনভাসের একটি ছক তৈরি করা আছে। সংস্থাটি প্রকাশ্যে অহিংস আন্দোলনের কথা প্রচার করে, নামকরণেও এর প্রতিফলন আছে, প্রাথমিক প্রশিক্ষণেও এই ব্যাপারটার ওপর জোর দেওয়া হয়। এদের গাইডবুকে থাকে কীভাবে গোপনে সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটাতে হবে; নিয়মানুবর্তিতা, ঐক্যবদ্ধতা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। এরপরে আসে কীভাবে নিষ্ক্রিয় ও ভীতু সমর্থকদের সাহসী ও প্রতিবাদী কর্মী হিসেবে রাস্তায় নামানো যায়, কীভাবে গণ অসন্তোষকে উজ্জীবিত করে জনরোষে পরিণত করা যায়। লক্ষ্য রাখা হয় মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, দুর্নীতি, গুম হত্যা, রাজনৈতিক নির্যাতন—এইসব বিষয়গুলোর ওপর, যা যেকোনো স্বৈরাচারী সরকারের শাসনকালে ঘটতেই থাকে নিয়মিত। শেখানো হয় কীভাবে এই ইস্যুগুলোকে কার্যকরীভাবে সামনে এনে গণমানসকে বিক্ষুব্ধ করে তুলতে হয়, কীভাবে সরকার পরিবর্তনের কথা না বলেও সরকারের স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের বিরোধীতার দাবি নিয়ে আন্দোলনটিকে তুঙ্গে নিতে হয়। শেখানো হয় কীভাবে নিজেরা অহিংস থেকেও পুলিশ সদস্যদের মারমুখী করে তুলতে হয়। কেনভাস প্রশিক্ষক ইভান মারোভিচ এর মতে, ‘আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বিপ্লবটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই হয়েছে। দেখে মনে হয় লোকজন দলে দলে রাস্তায় নেমে এসেছে। কিন্তু এর পেছনে থাকে মাসের পর মাস, এমনকি বছরের প্রস্তুতি… অত্যন্ত সুচারুভাবে এর পরিকল্পনা করা হয়, যাতে মূল আন্দোলন শুরু হওয়ার কয়েক সপ্তাহের ভেতরেই সরকারের পতন ঘটে’ (‘Revolutions are often seen as spontaneous... It looks as if people just went into the street. But it’s the result of months or years of preparation. It is very boring until you reach a certain point where you can organize mass demonstrations or strikes. If it is carefully planned, by the time they start, everything is over in a matter of weeks’). (সূত্র : ৫)
কেনভাসের প্রশিক্ষণকালে একটা ম্যানুয়াল ব্যবহার করা হয়, যা অটোপরের ট্রেনিংয়ে অবশ্য পাঠ্য ছিল। বইটির রচয়িতা জিন শার্প নামক এক ভদ্রলোক, বোস্টনে থাকেন, একসময় হার্ভাডে পড়াতেন। বইটির নাম, From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation, এতে আন্দোলনের ১৯৮ টি ধারার উল্লেখ আছে। শার্পের মতে, ‘My key principle is not ethical. It has nothing to do with pacifism. It is based on an analysis of power in a dictatorship and how to break it by withdrawing the obedience of citizens and the key institutions of society.’ (সূত্র : ১৬)
সার্বিয়ার গণঅভ্যুত্থানের প্রস্তুতিপর্বে অটপোরের কর্মীদের বইটি প্রায় মুখস্থ করানো হতো। পরবর্তী সময়ে কেনভাসের তত্ত্বাবধায়নে যে সব দেশে গণজাগরণ হয়, সেখানেও বইটি স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করে, এমনকি ফটোকপি করে, আন্দোলনের সমন্বয়কদের কাছে ছড়িয়ে দেয়া হতো।
কেনভাস এর ট্রেনিং কারিকুলামে পুরো বিপ্লবের কাঠামোকে ধাপে ধাপে সাজানো হয়। এর ভেতরে আছে অডিও ভিস্যুয়াল বক্তৃতা, ওয়ার্কশপ, পাঠ্য পুস্তক, ইত্যাদি। এই পুস্তিকাগুলোর কিছু কেনভাস-এর নিজের প্রকাশিত, তবে গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্যপাঠ্য হচ্ছে জিন শার্পের লেখা বইটি । কেনভাস-এর একটি শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রের নাম Bringing Down a Dictator যা প্রশিক্ষণার্থীদের দেখানো হয়। একটি ভিডিও গেইমও আছে যেখানে আন্দোলন এবং অভ্যুত্থানের নানা সম্ভাব্য চিত্র তুলে ধরে শিক্ষা দেয়া হয়।
গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার নামে পশ্চিমা বিশ্ব কেনভাসের কর্মকাণ্ডকে নানাভাবে স্পন্সর করে। অর্থনৈতিক সাহায্য আসে বেসরকারি সংস্থা এবং এনজিওদের মাধ্যমে। পুরো বিষয়টাই করা হয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অহিংস এবং অসহযোগ আন্দোলনকে উৎসাহ দেয়া এবং এই সম্পর্কিত কলা কৌশলের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে। একাডেমিক সাপোর্ট আসে নানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বেলগ্রেড বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিকাল সায়েন্স বিভাগ কেনভাস-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে একটি স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করেছে। কেনভাস-এর প্রশিক্ষকরা ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে হার্ভার্ড, জনস হপকিনস, কলাম্বিয়া, জর্জটাউন-এর মতো বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বক্তৃতা দিচ্ছেন। কেনভাসের কর্মকর্তা ও প্রধান প্রশিক্ষক পপভিচকে বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সেখানে তিনি মিসরের অভ্যুত্থান সম্পর্কে বলেন, ‘This was not a spontaneous 19 day revolution, forget about the illusion… this is a very shallow understanding of what we were doing for a long time’. (Journeyman.tv)
নানা দেশে গণবিপ্লব ঘটানোর প্রক্রিয়ায় কেনভাসের কার্যক্রম নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকায়। এই নিয়ে গবেষণাও করছেন অনেক শিক্ষাবিদ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম এঙ্গডাল (William Engdahl) বহির্বিশ্বে নানামুখী মার্কিন আধিপত্যবাদ নিয়ে গবেষণা করছেন। জার্নিম্যান টিভিকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে বলেন :
‘The key actors in OTPOR went on to create CANVAS, … and operate in some 50 countries. They are simply following an agenda given to them by people in Washington for regime change. They are using this deniability that they are simply idealistic young people from Serbia who did it successfully and is so happy about it that they want to show it to the rest of the world. That is hardly a plausible explanation in my view they are financed by American intelligence services and the target countries they target, like the Egypt most recently, are precisely the countries that are in the Pentagon list for destabilization and regime change’. (Documentary: Does the USA Sponsor Revolution? Journeyman tv
উপসংহার
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ হস্তক্ষেপে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বলপূর্বক সরকার পরিবর্তনের ইতিহাস নতুন নয়। মহাযুদ্ধোত্তর কালে এর শুরু ১৯৪৯ সালে সিরিয়ার নির্বাচিত শোকরি সরকারকে উৎখাতের মাধ্যমে। এর কিছুদিন পরেই ইরানের নির্বাচিত মোসাদ্দেক সরকারকে উৎখাত করা হয়। অন্তরালে জ্বালানী ও বাণিজ্য স্বার্থ থাকলেও প্রকাশ্য উদ্দেশ্য হিসেবে কমিউনিজম রোখার বিষয়টিকেই ফোকাস করা হতো পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমে। গণতন্ত্রায়ণের প্রসঙ্গটি ততোটা জোর দিয়ে বলা হতো না, অন্তত প্রথম দিকে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে, এক হিসেবে দেখা যায় যে বিশ্বযুদ্ধের পরে এখন পর্যন্ত আফ্রিকা, এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার প্রায় পঞ্চাশটি দেশে এই ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টা এখন আর গোপন নয়, সামান্য ঘাঁটাঘাটি করলেই এর বিস্তর তথ্য উঠে আসে পশ্চিমা মাধ্যমগুলো থেকেই। কিন্তু সাম্প্রতিককালে, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, এই বলপূর্বক সরকার উৎখাতের কারণ হিসেবে কম্যুনিজম রোখা নয়, বরং ফ্যাসিবাদ রোখা এবং গণতন্ত্র কায়েম করার কথাই তুলে ধরা হচ্ছে। এবং নতুন কর্মকৌশল অনুযায়ী সামরিক অভ্যুত্থান নয় বরং ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমেই এই কর্মটি সমাধা করার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে।
একথা সর্বজনবিদিত যে তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে প্রকৃত গণতন্ত্রের চর্চা হচ্ছে না, বরং গণতন্ত্রের ছাঁচে স্বেচ্ছাচারী কর্তৃত্ব চলছে যথেচ্ছ। ক্ষমতার অপব্যবহার, ব্যাপক দুর্নীতি, বিরুদ্ধ মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করা—এসবই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পরিচিত বিষয়। কিন্তু সাম্প্রতিক উদাহরণগুলো খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, বেছে বেছে সেইসব দেশেই স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থান হয়েছে যেখানে মার্কিন এবং পশ্চিমা স্বার্থ হুমকির মুখে ছিল। আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে সামরিক অভিযান (ইরাক), সামরিক ক্যুদেতা (মিশর) কিংবা ‘বিপ্লব রপ্তানি’র (লিবিয়া) মাধ্যমে পট পরিবর্তনের পর সেইসব দেশগুলোতে এখনো প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বৈরতন্ত্র নতুন রূপে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।
এসব কারণে, পুঁজিবাদি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উত্তরণ পর্বে নব্য-উদারনীতির (Neo-liberalism) প্রচার এবং গণতন্ত্রের বিশ্বায়ন নিয়ে নিবিড় আলোচনায় ক্রমশ উঠে আসছে ভিন্নমত—উদার গণতন্ত্রের নিখাদ আকাঙ্ক্ষা নয় বরং উপনিবেশ-উত্তর বিশ্বের নতুন ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নব্য উপনিবেশিক পররাষ্ট্র নীতির কর্তৃত্ববাদী মনস্তত্ত্বই এই মিশনের মূল কারণ।
তৃতীয় বিশ্বের ভাবুকদের জন্য এ বিষয়টি চিন্তার উপকরণ হতে পারে। তেমনি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট নিয়ে ভবিষ্যৎ গবেষণাকারীদের কাছেও বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হতে পারে।
হুমায়ূন কবির
১১৫, কবির লেন, জেলিকো, টেনিসি, যুক্তরাষ্ট্র।
এপ্রিল ৩০, ২০২৫।
References:
1. Cohen, Roger, Who Really Brought Down Milosevic, The New York Times Magazine, Nov. 26, 2000
2. From Resistance to Revolution and Back Again: What Egyptian Youth Can Learn from OTPOR When Its Activists Leave Tahrir Square. By Mladen Joksic and Marlene Spoerri. Carnegie Council for Ethics in International Affairs. Feb 18, 2011.
3. Hallas, Duncan. The Comintern: The History of the Third International. (London: Bookmarks, 1985).
4. McDermott, Kevin, and J. Agnew. The Comintern: a History of International Communism from Lenin to Stalin. (Basingstoke, 1996).
5. Rosenberg, Tina. Revolution U-What Egypt Learned from The Students Who Overthrew Milosovic. Foreign Policy, Feb 2, 2011
6. Gelvin, James. The Arab Uprisings: What Everyone Needs to Know. New York: Oxford University Press. (2012) P. 54
7. Katchanovski, I. (2023). The Maidan Massacre Trial and Investigation Revelations: Implications for the Ukraine-Russia War and Relations. Russian Politics, 8(2), 181-205 Online Publication Date: 21 Jun 2023
8. John F. Kennedy School of Government. "Nonviolent Struggle: Lessons from Serbia Applied in the Middle East and Africa". Harvard University. Archived from the original on 17 October 2011.
9. Bernhard, N. (1999) ‘U.S Television News and Cold War Propaganda, 1947-1960’. Cambridge: The Press Syndicate of the University of Cambridge.
10. Urban,G. (1997) ‘Radio Free Europe and the Pursuit of Democracy: My War Within the Cold War’. New York: Vail-Ballou Press.
11. Di Giovanni, Janine. Blueprint for a revolution, Financial Times. 18 March 2011.
12. Mohammed Adel, Interview with Al Jazeera English, 9 February 2011
13. Wikipedia, Center for Applied Nonviolent Action Strategies (Retrieved on 4/28/2025)
14. Leibovitz, Liel (March 2012). "The Revolutionist". The Atlantic. March 2012 issue.
15. Kerry Raymond Bolton, Are American Interests Behind The “Spontaneous” Revolts In North Africa? World Affairs: The Journal of International Issues, 2011
16. Gene Sharp. From Dictatorship to Democracy. The New Press, 2012.