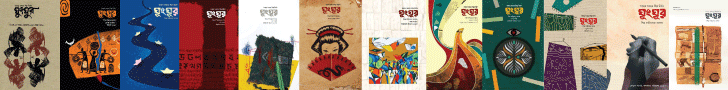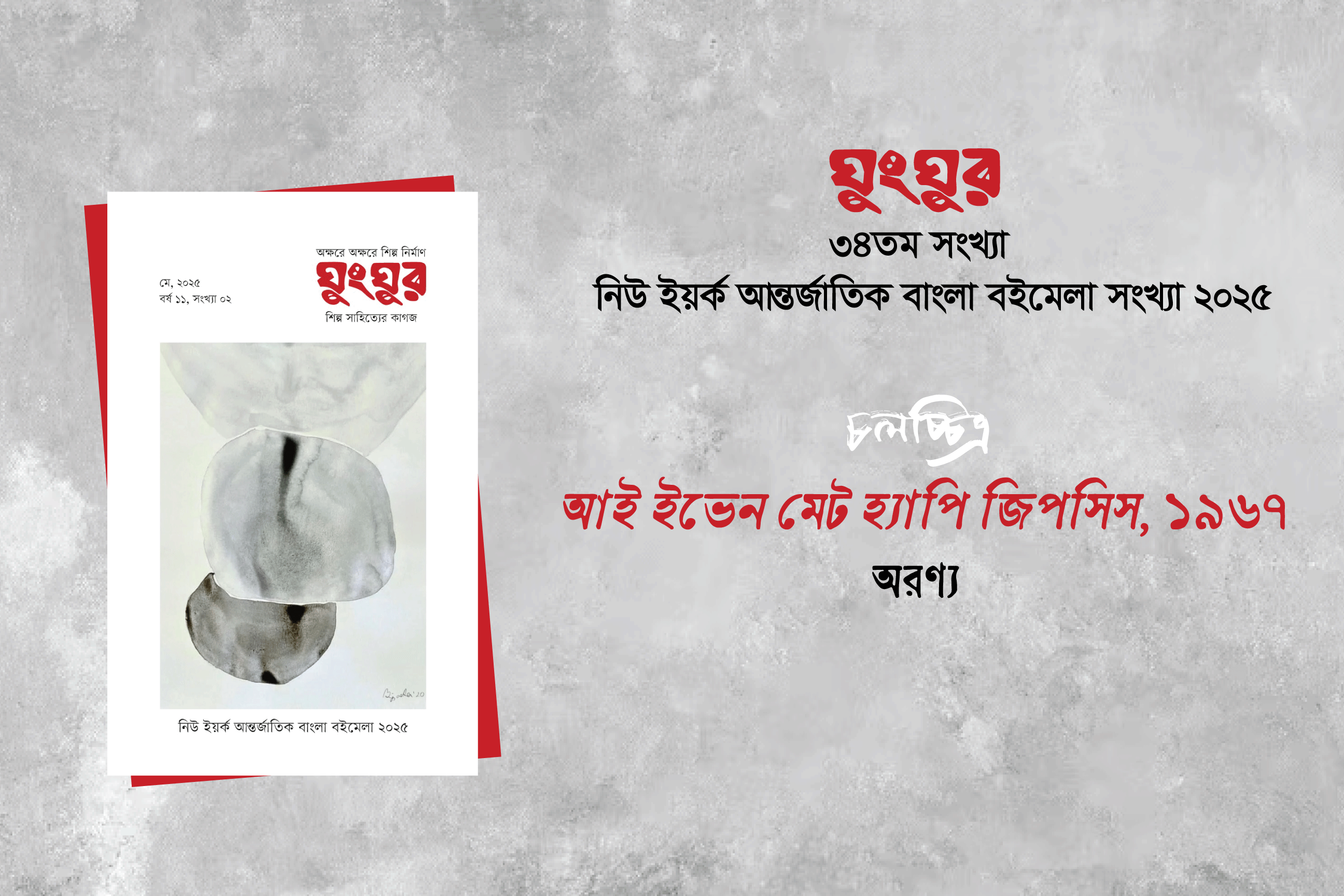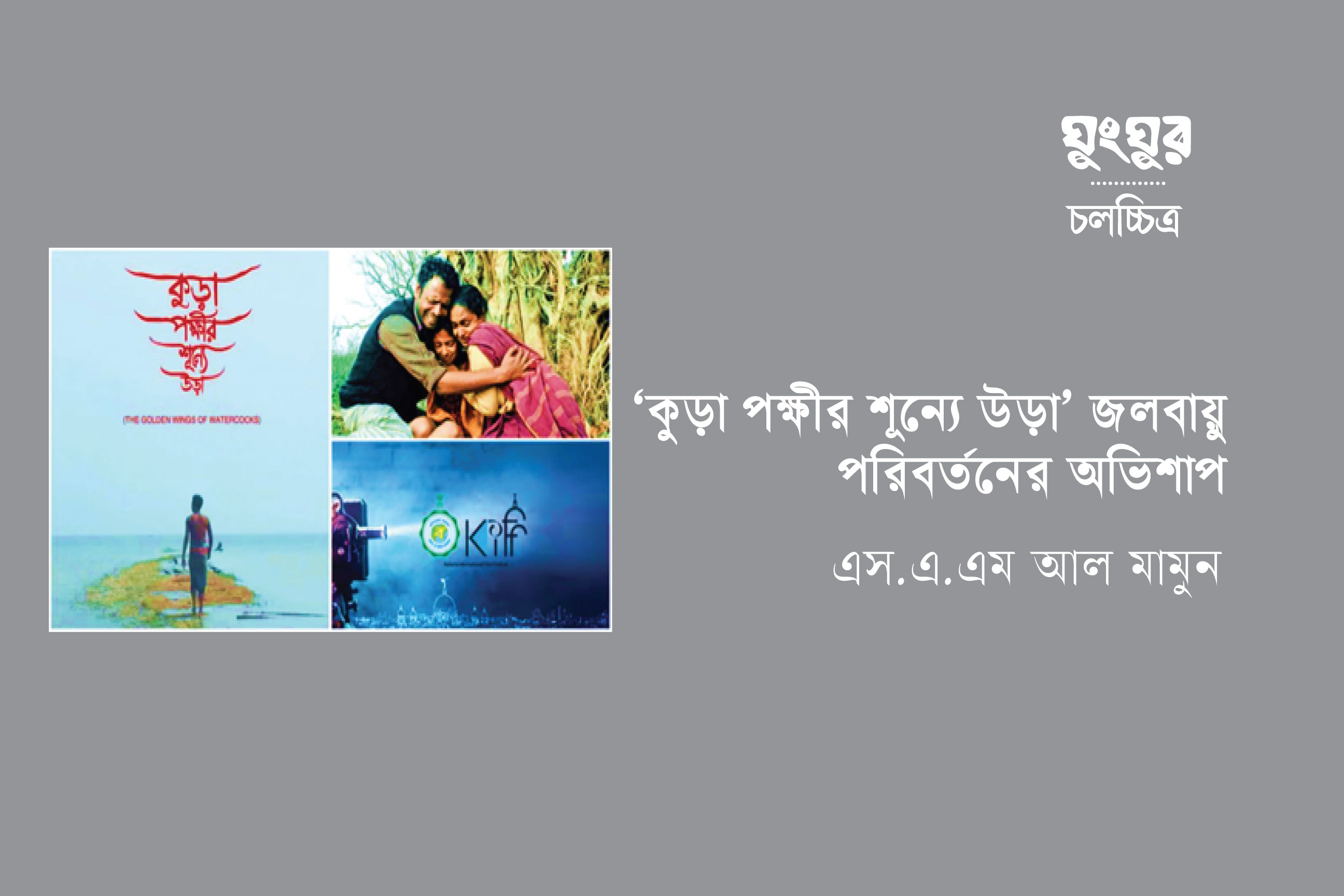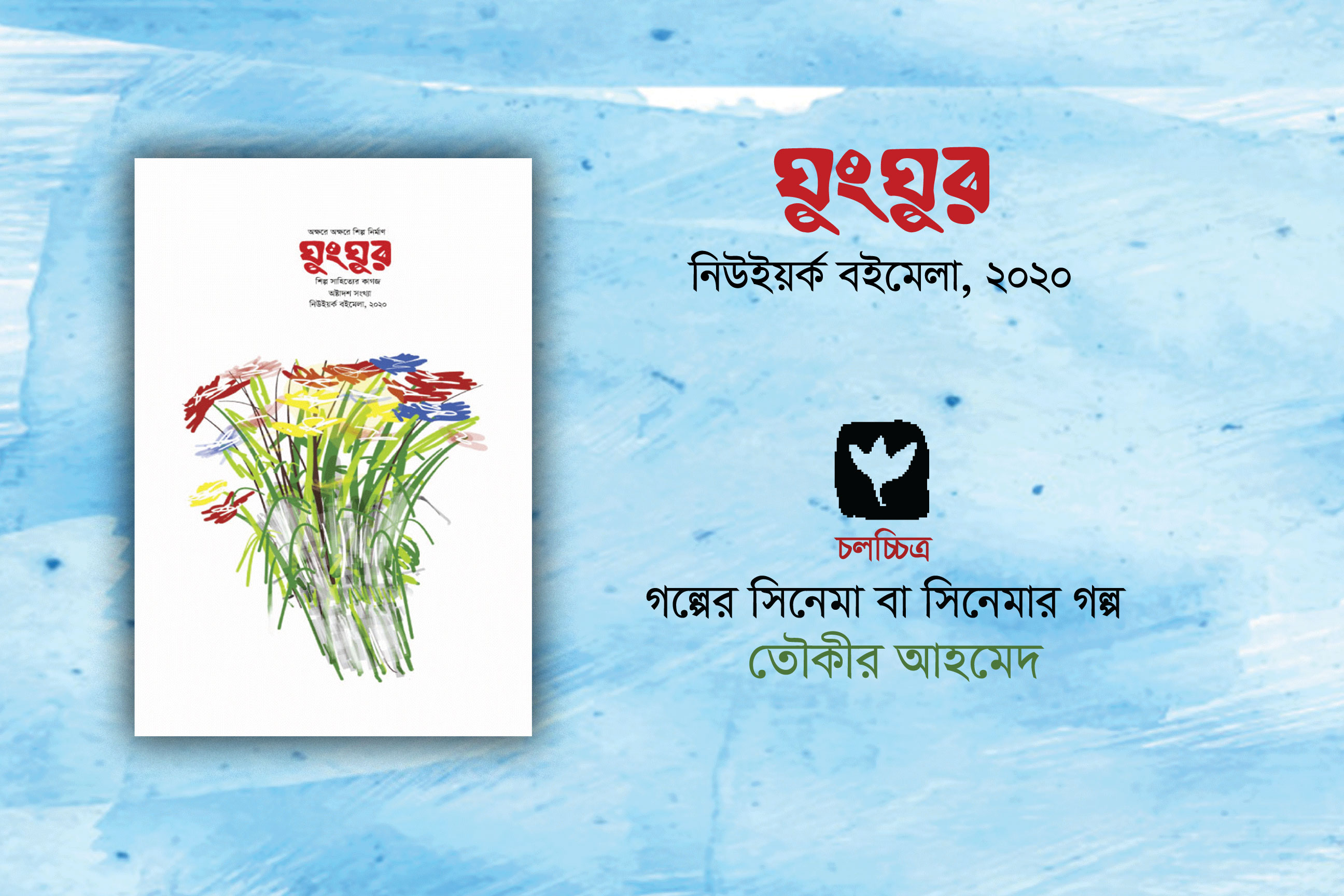রোম যখন পুড়ছিল, নিরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছিল!
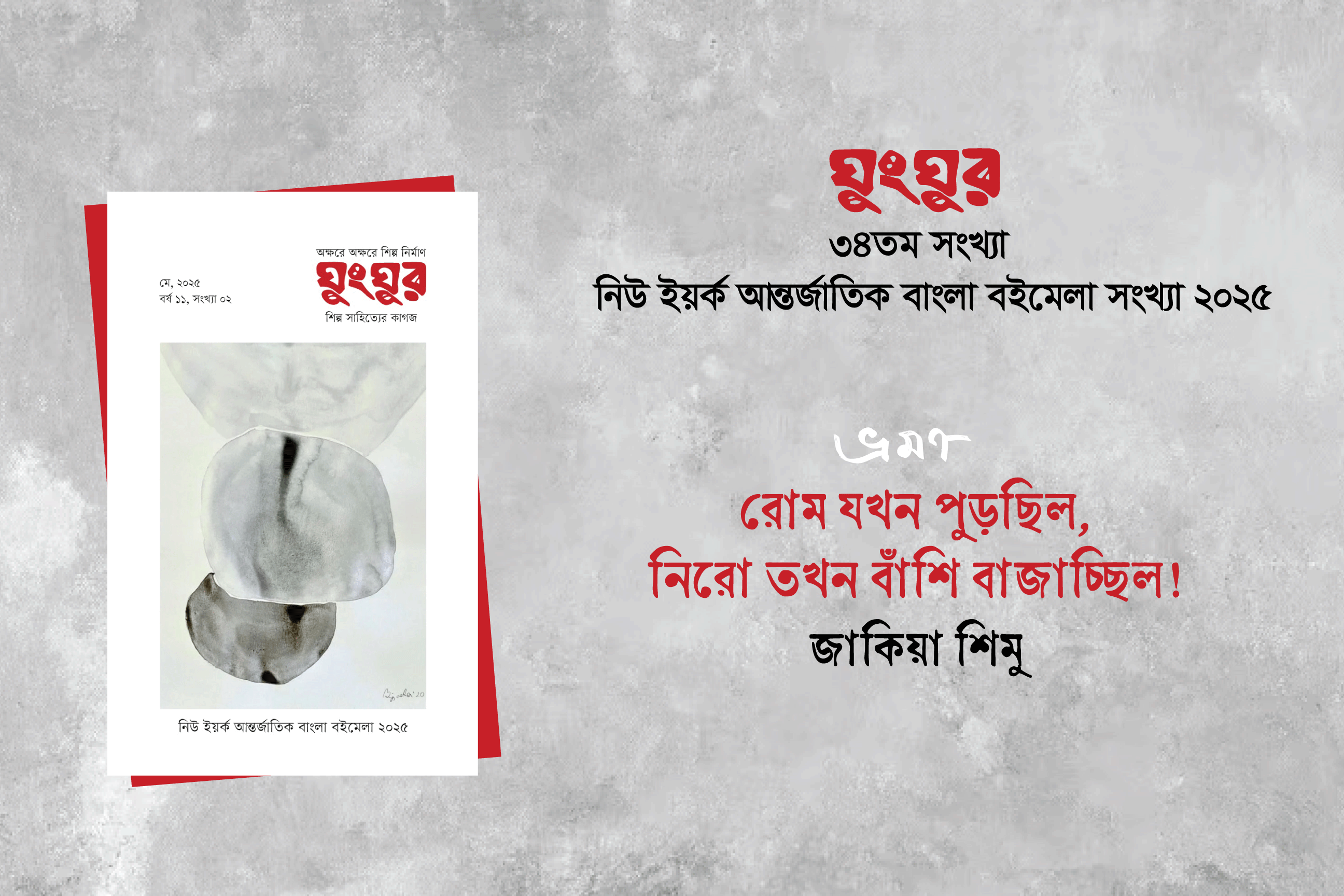
রোমের আকাশে আজ মিহি কুয়াশা জমেছে তারসঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জমেছে শীতকালীন-মেঘের। ওদিকে ভরাযৌবনের চাঁদ তার দেহের জৌলুস বিলোতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ক্রমেই কুয়াশা-মেঘের ফাঁকফোকর দিয়ে রূপজৌলুসের খানিকটা মোলায়েম আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে রোম শহরের আনাচে কানাচে। অমনতর চনমনে আলোর ঝিলিকের সঙ্গে কলোসিয়ামের বিশেষ শ্রেণির কৃত্রিম আলোকচ্ছতা পুরোশহরকে প্রায় দু’হাজার বছর পেছনের ঝলমলে ইতিহাসে টেনে নিতে পাঁয়তারায় ফেঁদেছে। আমার মতো ইতিহাস গিলে খাওয়া হাজার হাজার পর্যটকের মেলা মিলেছে সেখানে। আমি কলোসিয়ামের সীমানা ঘেঁষে নির্বাক দাঁড়িয়ে আছি অনেকটা দলছুট হয়ে। এমন চমৎকার একটি পরিবেশে, ছেলে আমার একটি যুতসই ফটো তুলবে বলে মুখিয়ে আছে কিন্তু কিছুতেই মায়ের মুখের সেই পরিচিত আদলটা সে খুঁজে পাচ্ছে না! মায়ের মুখে আকাশের সমস্ত মেঘেরা ভর করেছে। চোখের কোণে জমা-জলে চাঁদের কোমল আলো চিকচিক করছে। কারণ আমি ফিরে গেছি কলোসিয়ামের শুরুর দিকের ইতিহাসে! 
সম্রাট ভেসপাজিয়ান জনসভা এবং নাট্যউৎসবের জন্যে এমফি-থিয়েটারিয়াম ফেভিয়াম নামে এটি শুরু করলেও তার মৃত্যুর সুযোগে তার পুত্র টাইটাস যিনি পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম সম্রাটদের একজন হিসেবে পরিচিত, মূল নকশা কেটেছেঁটে নতুন করে কলোসিয়াম নামে এবং বিশেষ খেলার স্থান হিসেবে এটিকে ঘোষণা করেন। কলোসিয়ামের গ্যালারিতে একসঙ্গে পঞ্চাশ হাজার দর্শক বসতে পারত। এরপর বিশেষ খেলার নামে শুরু হয় পশু লড়াই—লড়াই চলে পশুগুলোর করুণ মৃত্যু না-হওয়া পর্যন্ত। ইতিহাস বলে সম্রাট টাইটাস দীর্ঘদিন পশুর লড়াই এবং এসব পশুর করুণ মৃত্যু দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে মানুষে মানুষে মৃত্যু লড়াইয়ের আয়োজনের নির্দেশ দেন! এবার পশুর বদলে জড়ো করা হয় রাজবন্দী, যুদ্ধবন্দী, ক্রিতদাস এবং মৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের। লড়াইকারীদের বলা হত গ্ল্যাডিয়েটর। শুরু হয় মানুষের রক্তের হোলি খেলা এবং সেই খেলার বলি হয় হাজার হাজার নিরীহ মানুষ। এমন বীভৎস সে কাহিনি যে একসময় স্বয়ং সম্রাট টাইটাস এসব খেলা দেখে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যান। এরপর মানুষের এমনতর মরণখেলা সাময়িক বন্ধ হলেও পরবর্তী সময়ে আবার চালু হয়! এবং রোমের দুর্ধর্ষশাসক জুলিয়াস সিজার, ট্রাজানসহ ইতিহাসে অমর হয়ে থাকা এসব সম্রাটগণ এবং তাদের পরিবার দেশের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং বিদেশি কূটনৈতিকগণ মানুষের মৃত্যু লড়াই দেখে বিকৃত আনন্দ পেতেন! চারতলা বিশিষ্ট উপবৃত্তাকার রোমান সভ্যতার অপূর্ব নির্মাণশৈলীতে পরিপূর্ণ এবং বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য আমাকে টানতে পারেনি মোটেও বরং যতক্ষণ ওখানে ছিলাম অদ্ভুত কাঠামোটির প্রতিটি ইট কাঠ পাথরে মিশে থাকা নিহতদের অন্তিম নিঃশ্বাস আমাকে অবিরত দগ্ধ করেছে।
কলোসিয়াম থেকে তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়তে চোখের জলের সঙ্গে এবার এসে সখ্য করে বৃষ্টিজল। ঝুরঝুরিয়ে বৃষ্টি নামে। রাস্তার পাশে মেট্রোস্টেশনে ঢুকে পড়ি। এ ফাঁকে জমাটবাঁধা অন্ধকার হাতড়ে বেরিয়ে আসা জুনিপোকাদের মতো দল দলে বেরিয়ে আসে আমাদের বাংলাদেশীয় শত শত গ্ল্যাডিয়েটর! কারও হাতে ফুল, কারও হাতে মোড়কে বাঁধা ছাতা। এরা বৃষ্টিতে ভিজে এসব বিক্রি করছে। এগিয়ে যাই। ফুল কিংবা ছাতা কোনটারই দরকার নেই তারপরও হাত বাড়িয়ে ফুল নিই। কৌশলে ভাব জমাতে এগিয়ে যাই কিন্তু তাদের মেজাজমর্জি ভালো নেই। এদের কারও কাগজ নেই, ইতালিয়ান ভাষা জানা নেই। পেটের দায়ে এবং পরিবারের আহ্লাদ মেটাতে জীবন বাজি রেখে সাগর নদী সাঁতরে স্বপ্নের ইউরোপে ঢুকেছে কিন্তু এখানে কাজ নেই! ভিখারির আদলে কোনমতে বেঁচে থাকার একটা পথ খুঁজছে! আমি স্থিরচোখে তাকিয়ে দেখি, আহা! কোন মায়ের আদরের ধন! কেউ কেউ বিশেষ কৌশলে অভিনয় করে চলেছে, যেমন পেটে হাত ডলে পর্যটকদের ক্ষুধার জ্বালা বুঝাতে, কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্নপ্রান্তের এসব পর্যটক বিব্রত হলেও কেউ কেউ দু’ এক ইউরো হাতে ধরিয়ে দিয়ে সরে পড়ছে! বাংলাদেশি হিসেবে এ লজ্জা আমরা রাখতো কোথায়! আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, বিলিয়ন-ট্রিলিয়ন চুরি করা আধুনিক যুগের আমার দেশের জুলিয়াস সিজার, নিরোদের চেহারা!
প্রাচীন রোম পৃথিবীর সমৃদ্ধতম প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে অন্যতম। শহরটির আনাচেকানাচে প্রাচীন স্থাপত্যের হাজারো নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আমরা গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কলোসিয়াম ছুঁয়ে যাওয়া রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করি। আমাদের মতো হাজারো পর্যটক হেঁটে হেঁটে রোমান সভ্যতার সেই সোনালি কালে ফিরে যায়। ততক্ষণে আকাশের মেঘ কেটে সরু কুয়াশাকে তোয়াক্কা না-করে চাঁদের আলো শহরটিকে ভাসিয়ে দেয় যেন। ইতালি পর্যটন নির্ভর দেশ। রাস্তাঘাট কোণাকাঞ্চি সর্বত্র কৃত্রিম আলোর ফোয়ারায় ঝলমল করছে। পিয়াজা ভেনেজিয়া থেকে কলোসিয়ামের দিকে যেতে রোমান ফোরাম, ট্রাজানের ফোরাম বামদিকে চোখে পড়ে কনস্ট্যানটিনের চার্চ এবং প্যালাটিন হিল। তারও একটু যেতে ফ্লাভিয়ান প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে দেখতে আরও এগিয়ে যাই। আমাদের পা দুটি ঘোড়ার খুরের মতো শক্ত সমর্থ্য হয়ে ওঠেছে বোধকরি কারণ দিন-রাত হাঁটছি। যেন কোনো ক্লান্তি নেই। আমাদের ইউরোপের সঙ্গে সময়ের ব্যবধানে ঘুচাতে দিন-রাত উলটপালট হতে চোখের ঘুমও যা আসে সেই বাসে-ট্রামে, গভীর রাতে হোটেলে ফিরে ভোরে আবার বেরিয়ে পড়ার তাড়া। কলোসিয়াম ফেলে একটু এগিয়ে যেতে, ওপিও পার্ক! সেখানে দেখা মিলল সম্রাট নিরোর (বাবার কাছে গল্পে তাঁকে বাঁশিবাদক সম্রাট বলে জানতাম) গোল্ডেন হাউস, বিস্ময়কর ভূগর্ভস্থ কমপ্লেক্স যা হয়তো খুঁড়াখুঁড়ি হচ্ছে কিন্তু অর্ধেকটা দেখে তার বিশালত্ব আন্দাজ করতে সময় লাগে না।
রাত বাড়ে তার সঙ্গে পাল্লা ধরে পর্যটক নামে রোম শহরে! ট্রেভি ফাউন্টেন বা ঝর্ণা, ১৬০০ সালের দিকে যে শৈল্পিক রেনেসাঁ শুরু হয় তখনকার সময়ে পুননির্মিত হয় এবং দুনিয়ার বিখ্যাত ঝর্ণাগুলোর একটি! এই ঝর্ণাটির একটি চমৎকার ইতিহাস আছে। ইতিহাসটি এর গায়ে খুদাই করা বারোক শৈলির ভাস্কর্যগুলোতে কী অপূর্বভাবেই না ফুটে উঠেছে। ট্রেভি ফাউন্টেন-এর স্থাপত্যকলা এককথায় বিস্ময়কর এবং রাতে এর সৌন্দর্য যেন প্রকৃত সরব হয়ে ধরা দেয়। অনেকেই এক সেন্ট ইউরো ঝর্ণার পানিতে ছুঁড়ে দিয়ে আবার এখানে ফিরতে প্রার্থনা করে। আমাদের কাছ কয়েক নাই তবে আবার নয় বহুবার এখানে ফিরে আসার প্রতিজ্ঞা করে সেদিনের মতো হোটেলে ফিরি। 
রোমের পেটের ভেতর একশো একুশ একর জায়গা নিয়ে দুনিয়ার ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র ভ্যাটিকান সিটি। ভ্যাটিকান পাহাড়ের ওপর একটি ত্রিভুজাকৃতি জায়গা নিয়ে এর অবস্থান। দক্ষিণ-পশ্চিমের সেন্ট পিটার চত্বর বাদে বাকি সবদিক দিয়ে এ শহর মধ্যযুগ এবং রেনেসাঁর সময়ে নির্মিত সুউচ্চ প্রাচীর দিয়ে রোম শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। খ্রিষ্টধর্ম প্রবর্তনের আগে থেকে এই স্থানটিকে বিশেষ পবিত্র মনে করা হতো। কালক্রমে প্রথমে পাহাড় কেটে উদ্যান এরপর সম্রাট ক্যালিগুলা একটি সার্কাস তৈরির পরিকল্পনা করলেও শেষ করে যেতে না পারলে, সম্পূর্ণ করেন সম্রাট নিরো। ধারণা করা হয় এই সার্কাসের প্রান্তরেই সেন্ট পিটারকে মাথা নিচে পা ওপরে তুলে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। তবে বর্তমানে সেই ভ্যাটিকানের একমাত্র ধ্বংসাবশেষ হল ভ্যাটিকান ওবেলিস্ক! প্রাচীন দালান কোঠা, বিশাল চত্বর আর উদ্যানে ঢেকে আছে একশো একুশ একরের এই ক্ষুদ্র দেশ।
প্রাচীন কারুকাজে ঢাকা সবচেয়ে বড় দালানটি সেন্ট পিটারের ব্যাসিলিকা, যা বর্তমানে রোমান ক্যাথলিকদের প্রধান গির্জা। ঢুকেই চোখে পড়ে সুসজ্জিত সুইস গার্ডদের, এরা পিঁপড়ের সারি বাঁধা দলের মতো কুচকাওয়াজে এগিয়ে যাচ্ছে। এদের নিয়ে সবার মতো আমারও আকর্ষণ কম নয়। এরা সুদর্শন, বয়স আঠার থেকে ত্রিশের কোঠায়। সুইজারল্যান্ডের এই গার্ডদের কাজের প্রধান শর্ত এরা বিয়ে করতে পারবে না! এরা ভ্যাটিকান সিটির পাহারাদার, তাজ্জব আইনকানুন! চারদিকে এত মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যে ভরা যে মনে হয় চোখের যেন পলক না পড়ে। সেন্ট পিটারস ব্যাসিলিকা এবং সিসটিন চ্যাপেলের দৃষ্টিনন্দন স্থাপনায় যারপরান বুঁদ হয়ে রই কতক্ষণ কে জানে! প্রথম দেখলাম বলে নয়, সঙ্গের বন্ধু পরিবার বহুবছর ধরে এদেশে বাস করছে তাদেরও দেখলাম প্রথম দেখার মতো মুগ্ধ ডুবে আছে।
সিসটিন চ্যাপেলের ছাদ থেকে শুরু করে চার দেয়ালজুরে সর্বকালের বিখ্যাত শিল্পীদের অন্যতম মাইকেলেঞ্জেলো ফ্রেস্কোগুলো দেখে কানাও যেন জ্ঞান হারাবে। এছাড়াও রাফায়েল, কেরাভারজিও, বামান্তের মতো এমন প্রথিতযথা শিল্পীদের শিল্পকর্মে পুরো ভ্যাটিকান সিটি যেন এক বিশাল জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। ১৯৮৪ সালে বিশ্বের মধ্যে একমাত্র পুরো ভ্যাটিকান সিটিকে ইউনেস্কো হেরিটেজ সাইটের অন্তর্বর্তী করে নেয়। মনে মনে ভাবলাম, আরও আগে কেন করা হয়নি।
আপাতত রোম’কে অপেক্ষায় রেখে ছুটলাম আমার প্রিয় কবি দান্তে আলিঘেরি, গ্যালিলিও, বিখ্যাত স্থপতি ফিলিপ্পো ব্রুনেলেসচি, বুঁদ হয়ে থাকা সিস্টিন চ্যাপালের ছাঁদ আঁকিয়ে ভাস্কর মাইকেলেঞ্জেলো, আর মোনালিসা খ্যাত লিওনারদো দ্য ভিঞ্চি সহ সব বিখ্যাত মানুষজনের জন্মভিটা আরনো নদীর কূলঘেঁষা শহর ফ্লোরেন্সের দিকে। ভোর সকালে রওনা হয়ে সকাল সকাল পৌঁছে গেলাম আমার স্বপ্ন গুরুদের দেশে। ’৫৯ সালে ফুলিয়াস সিজারের রাজত্বকালে গড়ে ওঠা শহর শিল্প, স্থাপত্য ও ইতিহাসের ঠাঁসা বুননে আজও মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেড়শো বছরজুড়ে নির্মিত ক্যাথেড্রাল সান্তা মারিয়া দেল ফিয়োরে ফ্লোরেন্সের আইকনিক ল্যান্ডমার্ক। ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হলেও আমাদের পা এককদম নড়ে না। শেষমেশ ভেতরে প্রবেশ।
মজার একটা ইতিহাস আছে এর নকশা বিষয়ে। এটি নির্মাণে নকশা’র খোঁজ করা হলে হাজার হাজার নকশাবিদ বিভিন্ন নকশা নিয়ে হাজির হয় কিন্তু শেষমেশ কিনা ফিলিপ্পো ব্রুনেলেস্কি নামের এক স্বর্ণকারের নকশায় নির্মিত হয় এই ক্যাথেড্রালটি। এবং এর সুবিশাল লাল গম্বুজটি কোনরকম আধুনিক প্রযুক্তি ছাড়া এবং সেসময়ে বড় গম্বুজ তৈরির কোনো পদ্ধতি কারও জানা ছিল না, দীর্ঘ ষোল বছর নিজ প্রচেষ্টায় তিনি তা নির্মাণ করেন। ব্রুনেলেস্কি তাঁর কাজের কোনো স্কেচ কিংবা ব্লুপ্রিন্ট রেখে যাননি। এর ভেতর দশটি ব্রোঞ্জের প্যানেলে ওল্ড টেস্টামেন্টের কাহিনি খোদাই করা আছে। এর অনবদ্য শিল্পভাবনায় মুগ্ধ হয়ে মিকেলেঞ্জেলো’র গলায় সুর মিলিয়ে নিজেও স্বর্ণদ্বার যথার্থ নাম বলে গুনগুনিয়ে ওঠলাম। এর চত্বরে রয়েছে বেল টাওয়ার এবং ব্যাপ্টিস্ট্রি নামের আরও দুটি অপরূপ স্থাপত্য।
মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে ষোড়শ শতাব্দীতে মিকেলেঞ্জেলো অসাধারণ সৃষ্টি ডেভিড-এর মর্মর মূর্তিটির আকর্ষণে গ্যালারিয়া ডেল জাদুঘরে ঢুকে পড়ি। এটি পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম ধরা হয়। আমার মতো বাকিসবার অবস্থা। বিস্ময়মাখা চোখে হা করে দেখছি। ডেভিড ছাড়াও মিকেলেঞ্জেলো’র আরও কিছু অসমাপ্ত ভাস্কর্য এখানে রয়েছে যা থেকে চোখ সরানো সত্যিই দায় হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া রেনেসাঁ শিল্পী জ্যোত্তোর শিল্পকর্মের এক বিশাল সংগ্রহ এই জাদুঘরে রয়েছে।
পিয়াজ্জা দেলা সিনোরিয়া ইতালির একটি বিখ্যাত ল্যান্ডমার্ক। চারপাশে দর্শনীয় সব স্থাপনায় ভরা। মেডিসিদের বিখ্যাত প্রাসাদ পালাতজো ভেক্কিও তার পাশে ওপেন আয়ার মিউজিয়াম। প্রাসাদের ভেতরে কক্ষগুলোতে রেনেসাঁ যুগের অসামান্য সব শিল্পীর ফ্রেসকো’র কাজ দেখার মতো! ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত আর্ট গ্যালারি এবং পৃথিবীর বিখ্যাত মিউজিয়ামগুলোর অন্যতম উফিজি গ্যালারি-রেনেসাঁ যুগের প্রায় সব বিখ্যাত শিল্পীদের প্রায় দেড় হাজারের মতো শিল্পকর্ম রয়েছে। আমরা সকাল থেকে হাঁটছি একমনে, যেন ফিরে গেছি সেই রেনেসাঁ যুগে! একসময় পেট সংগ্রাম করে ওঠে। তবে রোম-এ সুন্দরবন রেস্টুরেন্ট’র কাচ্চি আমাদের পেটের চাহিদা পুরোটাই কড়ায়গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়েছিল তা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। সেই স্বাদ কখনো ভুলা যাবে না। ফ্লোরেন্সে অবশ্য পিজ্জা-পাস্তা খেয়ে আপাতত চালিয়ে নিতে হল।
ফ্লোরেন্স শহরেও বাঙালি এবং দেশীয় খাবারের কমতি নেই। চায়ের বিরতি নিতে সেরকম এক রেস্টুরেন্টে ঢুকি। আমার বিশেষ উদ্দেশ্য অবশ্য প্রবাসীদের খোঁজখবর করা। যেখানে বাঙালি দেখেছি, উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে গিয়ে তাদের কথা জেনেছি। কারও দুঃখে মন কেঁদেছে কেউ কেউ অবশ্য সুখের বার্তাও দিয়েছে। তবে মোটের ওপর পরদেশে আমাদের এই রেমিটেন্স যোদ্ধারা ভালো নেই! তা অবশ্য হাড়েগুঁড়ে টের পেয়েছি ইতালির রোম, ভেনিস এবং মিলানের বাঙালিদের খুব কাছ থেকে দেখে। রোমের পার্ক কিংবা রাস্তাঘাটে বৃষ্টিভেজা শীতের রাতে কাগজপত্রহীন সহায়সম্বলহীন বাঙালিদের দশা দেখে চোখ ভিজে ওঠেছে। ভেনিসের ব্যস্ততম রাস্তায় কাঁথাকম্বলে শরীর মুড়িয়ে একজন বাঙালিকে পড়ে থাকতে দেখে এগিয়ে গেছি, লজ্জায় শামুকের মতো নিজের মুখটাকে কাঁথার ভাঁজে লুকিয়ে ফেলেছে! যদিও এ লজ্জার দায়ভার তার নয়, আমাদের আমাদের শাসকশ্রেণির! এ কষ্ট বলে বুঝাবার নয়।
একশো আঠারটি ছোট দ্বীপ নিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত শহর ভেনিস। শিল্প সাহিত্য বিশেষ করে স্থাপত্যশিল্পে ভেনিস নগরীর তুলনা সে নিজেই। পুরো নগরজুড়ে জালের মতো বিছিয়ে আছে অসংখ্য খাল, শহরটিকে দ্বিখণ্ডিত করেছে গ্র্যান্ড ক্যানেল নামে বড়ো খাল। নৌকা চেপে ওঠতে দু’পাশে চোখে পড়ে নগরের চোখ ধাঁধানো রং, নকশা ও স্থাপত্যশৈলীতে। খালের ওপর রয়েছে অসাধারণ কারুকাজ খচিত অসংখ্য সেতু। তবে সবচেয়ে মনকাড়া সেতু হিসেবে রিয়াল্টো’র নাম বলতেই হয়। এই সেতুর কারুকাজ অসম্ভব সুন্দর। ভেনিসের বাসিন্দাদের ঘরবাড়িগুলো যেন এক একটি নান্দনিক রূপ, প্রত্যেক বাড়ির ঘাটে নৌকো বাঁধা। নৌকোতে বসে অপলক চোখে তাকিয়ে দেখি—সেন্ট মার্কস ব্যাসিলিকা, ডোজের প্রাসাদ ভৌজ প্যালেস, মনোমুগ্ধকর অসংখ্য প্রাচীন স্থাপত্য, প্রাসাদ, অপেরা রয়েছে হাউজ,ক্যাফে, বুটিক, রেস্তোরাঁ। সেন্ট মার্কোর বিখ্যাত স্থাপত্য ‘ক্যাথেড্রাল’ এর চারদিকের দেয়ালে কারুকার্যে সুসজ্জিত এবং অক্ষরে লিপিবদ্ধ নানান কাহিনি মুগ্ধ বিমোহিত করে।
নৌকোতে ভেসে চলে গেছি মুরানো এবং বুরানো দ্বীপে। মুরানো দ্বীপ কাচশিল্পের জন্যে বিখ্যাত। বুরানো দ্বীপের নানান রঙের বাড়িঘরের সৌন্দর্যে থমকে দাঁড়াতে হয়। এই রঙিন বাড়িঘরগুলো নিয়ে স্থানীয় একটি গল্প চালু আছে—এই দ্বীপে জেলেরা প্রথম বসতি স্থাপন করে। ভোরবেলা এরা দলবেঁধে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেত এবং ফিরতো বেশ রাত করে। রাতের আঁধারে নিজ নিজ বাড়ি ঠাহর করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং এ সমস্যা কাটাতে এদের মাথায় এক বুদ্ধি ভর করে। সেমতে যে যার পছন্দের রঙে বাড়িঘর রং করে। তাতে করে পুরো এলাকা রঙিন হয়ে ওঠে এবং এদের নিজ নিজ বাড়ি চিনতেও সুবিধা হয়। এখন সেসব বাড়িঘর নেই কিন্তু আধুনিক বাড়িগুলোতেও সেই রঙের ঐতিহ্য বজায় রয়েছে, বহু পর্যটক ছুটে আসে মুরানো’তে।
এরা লেসের কাজের জন্যেও বিখ্যাত। বাড়ির আঙিনায় বুটিক দোকানগুলো লেস ছাড়াও হাতের কাজের জিনিসপাতি, ঘুরে ঘুরে দেখার লোভ সামলানো দায় হয়ে দাঁড়ায়। ভেনিস এর নাম সোনালি দ্বীপ। এই সোনালি দ্বীপের সৈকতে বসে গোধূলিলগ্নের সূর্যাস্তের শোভায় মুগ্ধ হয়ে প্রাচীন নগরের অপার বিস্ময়ে ডুবে রই। দূর থেকে রাতের ভেনিসকে গভীর অরণ্যে ছুটে চলা দলছুট জুনিপোকার মতো মনে হয়। হারিয়ে যাই আমার বাড়ির পাশের ইছামতী নদীতে। একসময় এই মরা নদীর বুকে যৌবনের দুর্দান্ত তেজ দেখেছি আমি। সে নদীর জলের ছাদে দলবেঁধে বেদে-নৌকো ভাসত। রাতের আঁধারে কুপি বাতি টিমটিম করে জ্বলতো, আমাদের বাড়ির উঠোন থেকে দূরের সেই বাতিগুলোকে দেখে আমার কাছে জুনিপোকা মনে হতো।
খুব ভোরে ভেনিসের ঘুমভাঙা মুখ দেখতে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। বেশি রাত করে হোটেলে ফেরা পর্যটকদের শেষরাতের ঘুম তখনো ভাঙেনি। এই সুযোগে রাস্তাঘাট পুল সাকো সব ফাঁকা ফাঁকা। নির্দ্বিধায় হেঁটে চললাম ভ্যানিসের আনাচে কানাচে। রাতের আঁধার কিংবা দিনের আলোতে অথবা ভোরের নীল আভায় ভিন্ন ভিন্ন সৌন্দর্যে ভরপুর এই ভেনিসকে দেখা দু’চারদিনের কাজ নয়। ‘আবার আসিবো ফিরে’ এমন আশ্বাসে জড়িয়ে ভেনিসকে পেছনে রেখে, চললাম মিলানের পথে।
মিলান বিশ্বের ফ্যাশন এবং ডিজাইনের রাজধানীগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে বিবেচিত। মিলান ইতালির শিল্প বাণিজ্যের প্রধানতম শহরও বটে। ফ্যাশনে ইতালিয়ানরা দুনিয়াজোড়া বিখ্যাত। ইতালিয়ানদের নিয়ে প্রচলিত আছে এরা বাঁচে স্টাইলের সঙ্গে, মৃত্যুটাও নাকি স্টাইলের সঙ্গেই হয়। আসলে এরা ফ্যাশন সচেতন বলেই এমন কথা বলা হয়। ভুবনসেরা ব্রান্ডের বেশিরভাগ জন্ম এই শহরে এবং শহরের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে পৃথিবীর বিখ্যাতসব ব্রান্ডের শোরুমগুলো। বৃষ্টিভেজা শীতের রাতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ফ্যাশনসচেতন মানুষের আনাগোনায় জমে ওঠা বিশ্বের প্রাচীন শপিংমলগুলো দেখে তা কড়ায়গণ্ডায় টের পেলাম।
মোটের ওপর ফ্যাশন নিয়ে আমার মোটেও আগ্রহ নেই, তারপরও কিছুটা সময় সেখানে ব্যয় করে, বেরিয়ে গেলাম প্রাচীনসব দালানকোঠা, স্তম্ভ, ভাস্কর্য দেখতে। আমি দুনিয়ার যেখানে যাই সবার আগে শিল্প সাহিত্য এবং স্থাপত্যকলার খোঁজখবর করি। ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে। ছাতা মাথায় দলবেঁধে নেমে পড়লাম মিলান শহরের কেন্দ্রস্থলে। মিলানের শৈল্পিক উপস্থাপনা বেশ উচ্চমানের, যা প্রতি মাসে পালাজ্জো রিয়েল এবং ট্রিয়েনালে দি মিলান দ্বারা আয়োজিত বৈচিত্রময় প্রদর্শনী দ্বারা প্রমাণিত হয়। দাঁড়ালাম মিলানের কেন্দ্রীয় স্মৃতিস্তম্ভ, ডুওমো’র উঠোনে! বৃষ্টিদানার ওপর চারদিকের বৈদ্যুতিক আলো ডুওমো’কে বেহেশতি প্রাসাদের মতো জ্বলজ্বলে করে রেখেছে। এর সুউচ্চ চূড়াগুলো দেখার মতো এবং শীর্ষচূড়ায় খচিত স্বর্ণের ম্যাডোনিনা মূর্তি অলৌকিক আলোর বিচ্ছুরণ ঢালছে যা চোখ ধাঁধিয়ে যায়। এটি ইতালির বৃহত্তম গির্জা এবং বিশ্বের পঞ্চতম বৃহৎ এটি। গির্জাটির শিল্পকর্ম এতটাই দৃষ্টিনন্দন যে এটা নিজেই একটি বৃহৎ শিল্পকর্ম। এর চারপাশে অসংখ্য ছোট বড় চিত্রকর্ম এবং প্রায় তিন হাজারের মতো ভাস্কর্য রয়েছে যা মিলানের প্রধান আকর্ষণ বলে মনে করা হয়।
রাতের মিলানে চোখজুড়িয়ে, বেশি রাতে হোটেলে ফিরে এলেও কারও চোখে ঘুম নেই। বন্ধু স্বজন সবার আতিথেয়তায় ডুবে থেকে ঘুম কোথায় ছুটে গেছে জানা নেই। প্রায় সারারাত ধরে আড্ডা শেষে ভোরের আলোতে মিলানের পথে বেরিয়ে গেলাম। মিলান আজকের শহর নয়। খ্রিষ্টপূর্ব চারশো অব্দে এ শহরের পত্তন ঘটে। এরপর বিভিন্ন চড়াইউৎরাই পেরিয়ে আজও সে সুপ্রাচীনকালের বিভিন্ন স্থাপনা, ভবন স্মৃতিস্তম্ভ, প্রাসাদ, গির্জা ধরে রেখে বিশ্বে নিজের প্রাচীন ইতিহাস ঐতিহ্যে নিজেদের স্থান আগলে রেখেছে। রেনেসাঁর আঁতুড়ঘর বলে খ্যাত এই শহরের যাদুঘরে দেখা হল লিওনারদো দ্য ভিঞ্চির দেয়াল চিত্র দ্য লাস্ট সাফার, মাইকেলেঞ্জেলোর পিটা রোন্ডানিনির মতো শিল্পগুলো। এছাড়াও রয়েছে রেনেসাঁ যুগের বিখ্যাতসব শিল্পীদের করা ফ্রেস্টো ভাস্কর্য। বিখ্যাত অপেরা ভবন লা স্কালা। এতকিছুর পরও বিংশ শতকের কুখ্যাত শাসক মুসোলিনী কথা মনে পড়তে মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল! এই শহর থেকে তিনি তার শাসন শুরু করেন এবং তার পতনও ঘটে এই মিলান শহরেই। পরক্ষণে মনে হল মিলান সেসব কলঙ্ক হাঁসের পাখা ঝাড়ার মতো করে ঝেড়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করেছে তার প্রাচুর্যময় ইতিহাস ঐতিহ্য আর নিজস্ব সংস্কৃতির বিনিময়ে।
হাতে আরও দু’তিন দিন সময় আছে এই ফুসরতে মিলান শহরকে আপাতত অপেক্ষায় রেখে ছুটলাম রোমের কাছাকাছি আরেক শহর তেরনি’র উদ্দেশ্যে। ট্রেন ছুটছে দুর্দান্ত গতিতে,বাইরে শীতের রাত জমেছে জুতমতো। চোখে আধো ঘুম লেগে থাকলেও বারবার আঁধার বেধ করে দূর বহুদূর থেকে জুনিপোকার মতো আলো ছুটে আসতে অন্য ভাবনায় এসে মাথায় ভীড় করে। রোম থেকে দিনে যখন একই পথ ধরে দিনের আলোতে ছুটে গেছি, চোখে পড়েছে উঁচু নিচু টিলার ধার ঘেঁষে দিগন্ত ছুঁয়া খোলামাঠ। কোথাও ফসলী জমি,কাজ করছেন আমাদের প্রিয়দেশ ছেড়ে আসা প্রবাসী ভাইয়েরা। তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। এই শীতের রাতে হয়তো কোনমতে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে, ফেলে আসা স্বদেশ, দেশের প্রিয়জনদের স্মৃতি হাতড়ে নির্ঘুমে জেগে আছেন! বিধাতা বড়ো অভাগা দেশে জন্ম দিয়েছেন আমাদের। বুকের ভেতর প্রিয়দেশটাকে গুঁজে রেখে অন্যদেশের জন্যে দিনরাত খেঁটে যাই।
আকাশ পরিষ্কার এবং ঝকঝকে নীল। শীতল হাওয়া বইছে। শীতকাল যেন মনেই হলো না। কিন্তু গত দুই দিনে আগে শীত উপলক্ষ্যে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মানবসৃষ্ট মারমোর’ জলপ্রপাত অর্থাৎ Cascata delie Marmore বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এমনতর খবরে হতাশ হলেও আশা ছাড়লাম না। ছুটলাম নদী পাহাড় ছাড়িয়ে বড় পাহাড়ের পেট চিরে আরও ওপরের দিকে মারমো’র জলপ্রপাতের খোঁজে। জনমানবহীন এক পাহাড়ি অরণ্য। আমদের গাড়ি চলছে দু’পাশের সৌন্দর্যে বুঁদ হয়ে আছি, হঠাৎ সাথের মানুষগুলোর সমস্বরে চিৎকার ধ্যান ভাঙে এবং গাড়ির কাচের ওপাশে চোখ পড়ে! মারমোর’ জলপ্রপাত! রোমানরা ২৭১ খ্রিষ্ট্রাব্দে এটি তৈরি করে! বন্ধ হওয়ার সুযোগে চারপাশে মধ্যরাতের নিস্তব্ধতা ভর করেছে। অল্প কয়েক গাড়ি একেবেঁকে পাহাড়ের গা বেঁয়ে চূড়ার দিকে চলছে। পাহাড়ের আনাচে কানাচে বাবুই পাখির বাসার আদলে দু’ চারটে ঘর বাড়ি চোখে পড়ল, ঝুলে আছে পাহাড়ের গা ধরে। জলপ্রপাতের প্রবেশস্থলে নাকি হাজার হাজার মানুষ টিকিট কাটতে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে আজ সেখানে একজন মানুষও নেই। একজন পাহারাদারের দেখাও পেলাম না। গেইটের পাশে বন্ধ’ কথাটা স্পষ্ট চোখে পড়লেও চিপা দিয়ে কোনমতে গা এলিয়ে ঢুকে পড়লাম! বিস্তর খোলা প্রান্তর, চারপাশে আব্রুবেড়া হয়ে পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়গুলোকে এখনো ঠান্ডা কাবু করতে পারেনি। পাহাড়ের গায়ের-বরণ ধূসর টিয়েরঙটা। সবুজে ঢাকা পাহাড়ের গা চুয়ে মৃদুধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে খালের জলে, কিংবা জলের ধারা খাল বয়ে নিয়ে চলেছে। চমৎকার প্রকৃতি, পাহাড়-ঝর্ণা-আকাশ এবং চারপাশের শুনশান নীরবতা যেন পৃথিবী নয়, ভিন্ন জগত!
জাকিয়া শিমু গল্পকার, ভ্রামণিক ও শিক্ষক। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় বসবাস করেন।