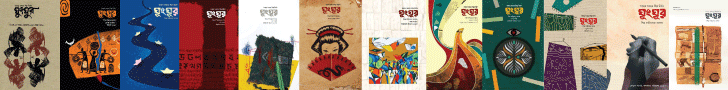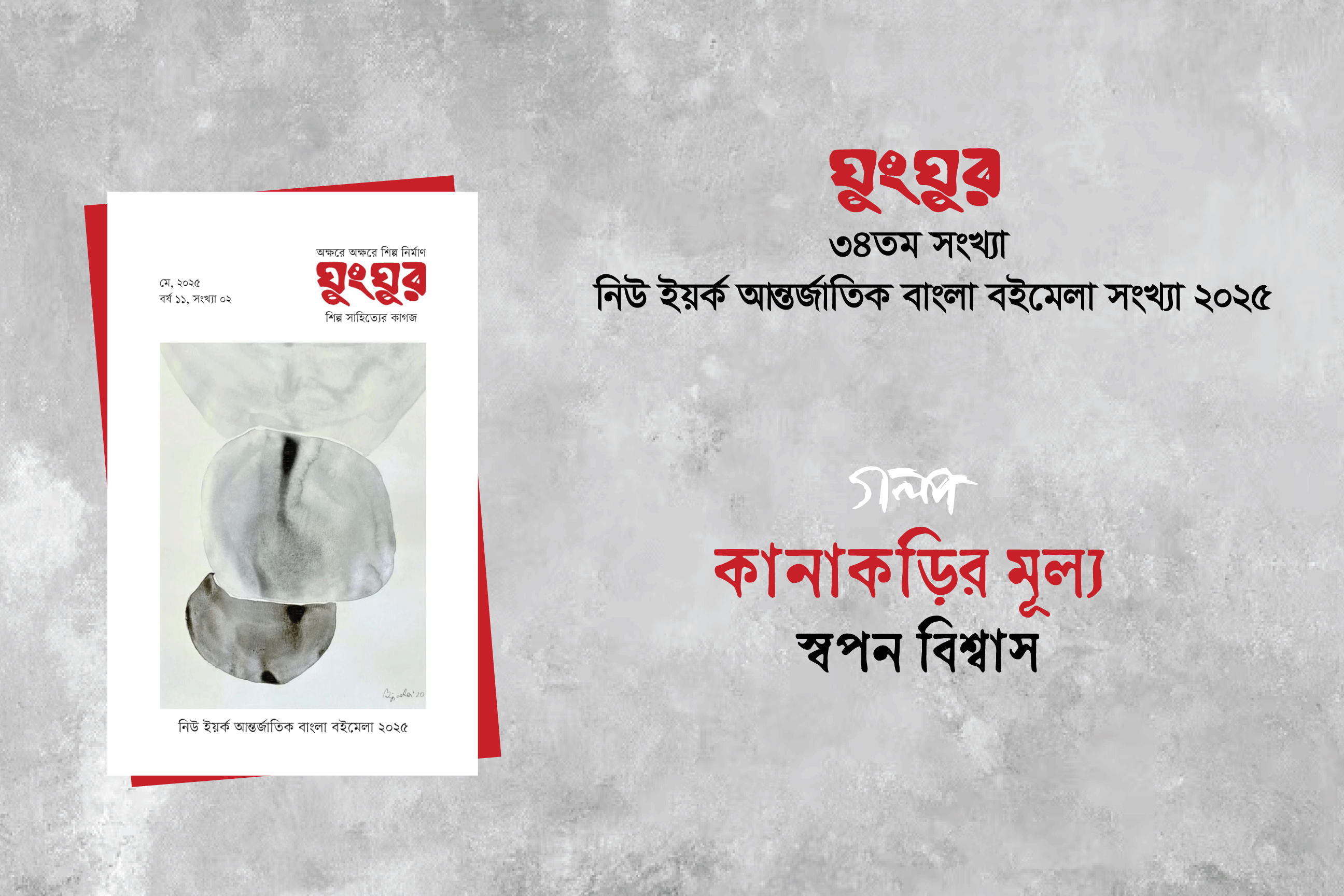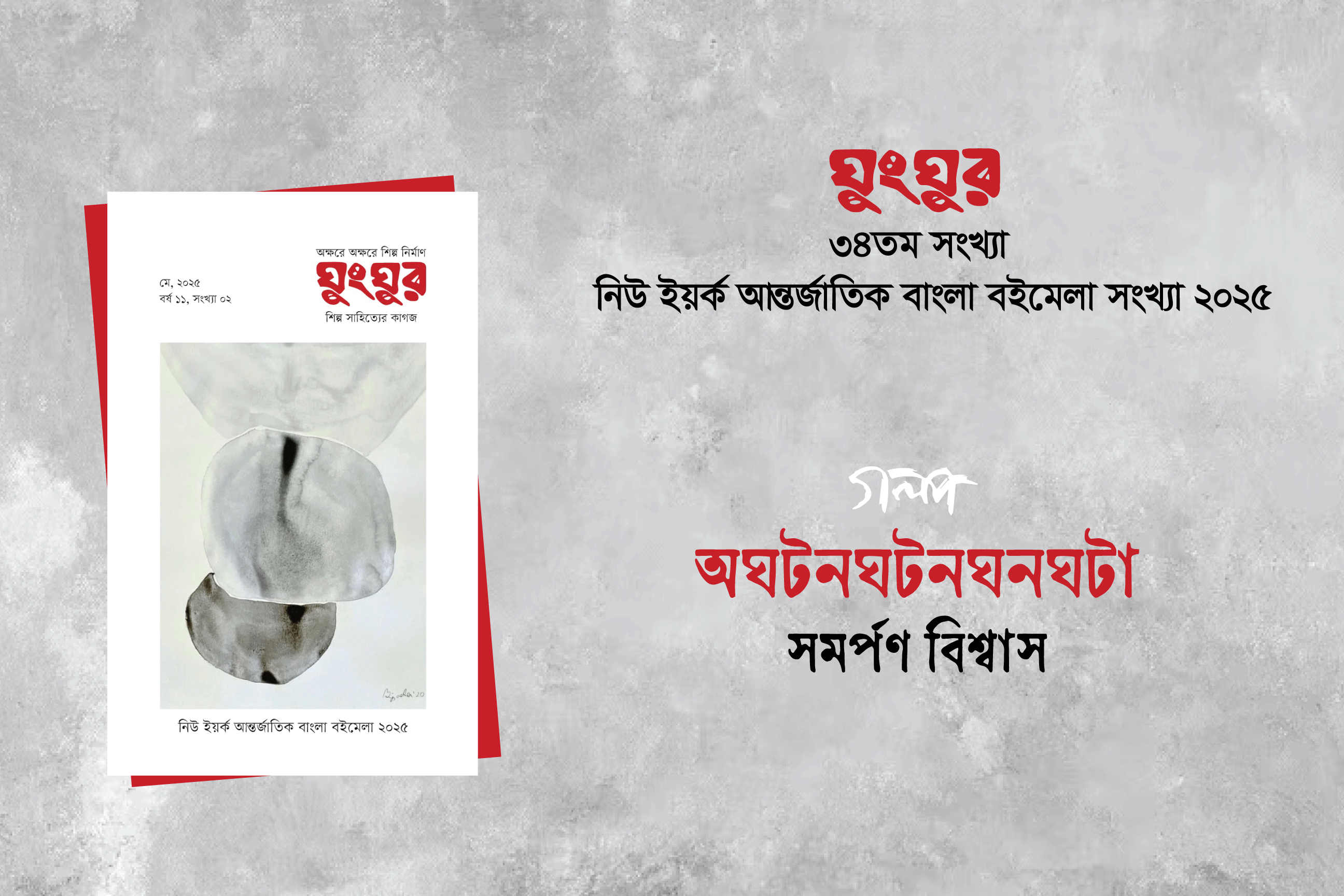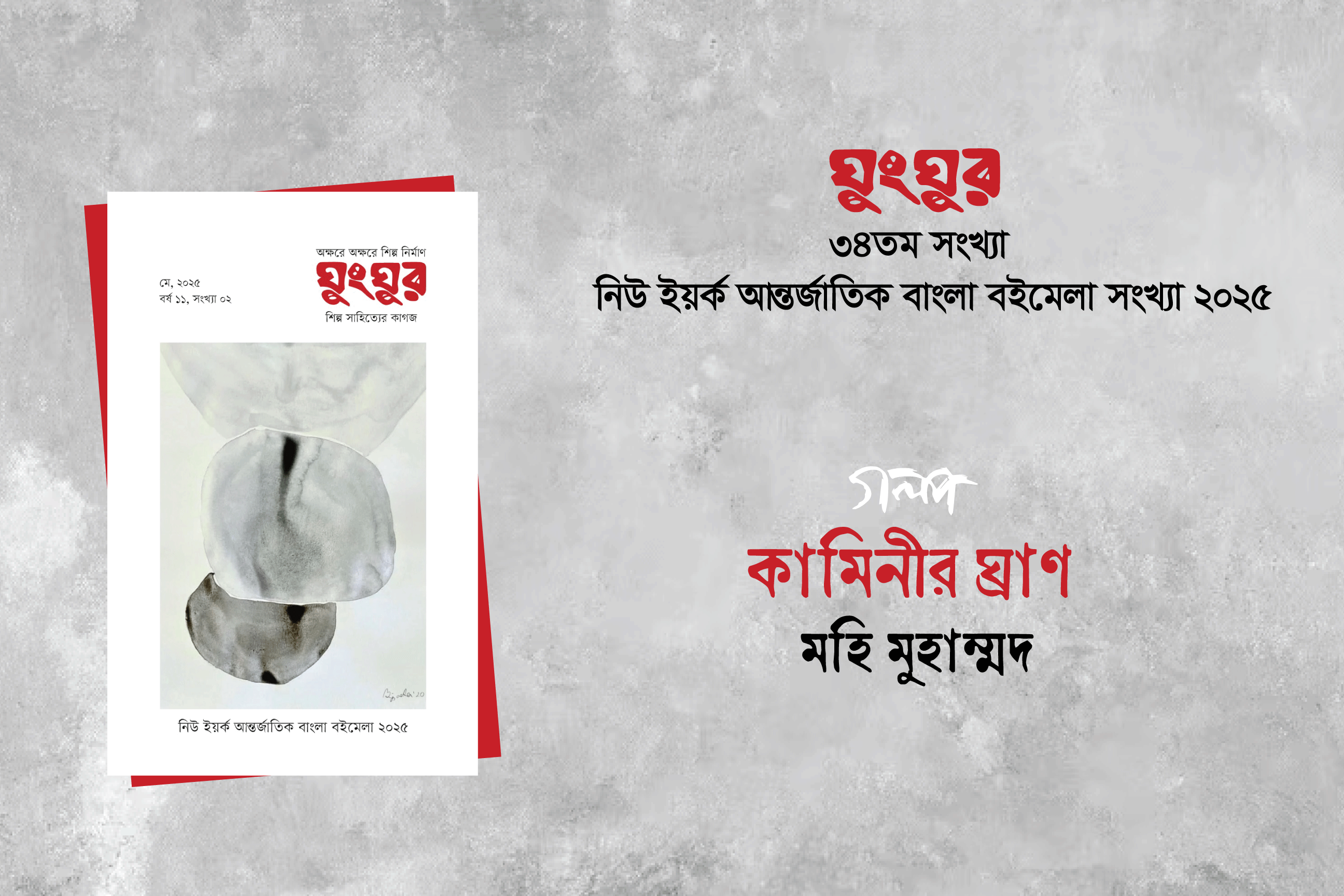বন্ধুতার চতুর্ভুজে আমরা চারটি বাহু

একটি থোকায় যেমন কখনো থাকে কুড়ি বাইশটা আঙুর আবার কখনো থাকে মাত্র ডজনখানেক, তেমনি স্কুল কলেজে বন্ধুর আড্ডায় কখনো দেখা যায় দশ পনেরোজনের হল্লা আবার কখনো শুধুই দুই কি তিনজনের গলাগলি। হলাহলি আর গলাগলির পাল্লা ভারী করে ছাত্রছাত্রীর মহল্লায় যুক্ত হয় নতুন সদস্য। আবার পুরনোদের অনেকেই ক্ষয়ে ভেঙে পড়ে এখানে ওখানে। ভাঙা টুকরোগুলো যুক্ত হয়ে তৈরি করে আরেকটা দল। ইউনিকর্ন কিংবা ট্রায়াঙ্গেল শেইপ।
কথাটি যখন মনে পড়েছে আমার তখন কিন্তু আমি জ্যামিতির শেইপ নিয়ে ভাবছিলাম না। তখন আমি শেষ সকালের অবসরে আলমারির এলোমেলো তাকগুলো গোছাতে বসেছি। আলমারির পুরনো কাগজপত্রের মাঝ থেকে বের হলো বেশ পুরনো কয়েকটি ছবি। যে ছবিগুলোতে আটকে আছে অনেক বছর আগের আমি ও আমার বান্ধবীদের দুর্দান্ত আড্ডাবাজির মূল্যবান কিছু মুহূর্ত, যেন ছবির পাতায় লেগে আছে কয়েকটি মরে যাওয়া প্রজাপতির ডানার বিবর্ণ নীলাভ আলো।
ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে মুহূর্তেই আমি চলে গেলাম আমাদের সেইসব দিনগুলোতে। যখন আমি আর আমার সখীরা সবাই তরুণী ছিলাম। যখন আমরা যুবতী ছিলাম। যখন আমাদের চোখে এই পৃথিবীটা ছিল জাদুকরের অত্যাশ্চর্য ঝালরের রং, রূপ আর রসের ছোঁয়া। পৃথিবীর ঘূর্ণন এমনিতে টের পাওয়া না গেলেও তখন আমরা প্রতিটি পদক্ষেপে অনুভব করতাম বেঁচে থাকার উল্লাস। তখন আমরা চারটি বান্ধবী ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির রৈখিক অবয়বে তৈরি করেছিলাম বন্ধুতার এক অদৃশ্য চতুর্ভুজ। যে চতুর্ভুজের আয়তন এখনো আমার কাছে গোটা পৃথিবীর সমান।
বিএ পাস করার পর একটা সরকারি কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম আমি। ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স আর মাস্টার্স করার উদ্দেশ্যে আমরা একেকজন দেশের একেক জায়গা থেকে এসে পৌঁছেছিলাম একই স্থানে। মহাকাশের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত ছুটে ছুটে অবশেষে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হবার মতো ছিল আমাদের এই সম্মিলন।
সেই সরকারি কলেজে ইংরেজিতে অনার্স পড়তে গিয়ে আমার পরিচয় হয়েছিল রত্নার সঙ্গে। আমাদের দুজনের বয়স একই সমান হলেও রত্নার তখন ছিল একজন বিশালদেহী স্বামী আর তিন বছরের একটি কন্যাসন্তান। আমার তখনো বিবাহ সম্পর্কের কাছাকাছি যেতে আরও অনেকগুলো বছর বাকি ছিল। তবু সাক্ষাতের প্রথম সপ্তাহেই রত্নার সঙ্গে আমার একটা অদ্ভুত রকমের বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল। রত্না ছিল আমাদের চতুর্ভুজ বন্ধুতার প্রথম সরলরেখা। দুই যুগেরও বেশি সময়ের আগের কথা মনে করতে গিয়ে এখন যেটুকু মনে পড়ছে, তাতে বলতে পারি, প্রথমত রত্নার প্রতি আমার আগ্রহ জন্মেছিল ওর মুখের মিষ্টি হাসি আর কৌতুকপূর্ণ কথা শোনে।
কানের কাছে যখন আমি সুদূর অতীত থেকে ভেসে আসা রত্নার হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, ঠিক তখন সেই রিনিঝিনি হাসির শব্দকে উস্কে দিয়ে রাস্তার একটা রিকশাওয়ালা টিংটিংটিং করে ঘণ্টি বাজালো বেশ কয়েকবার। পর্দা সরিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা এক-পাওয়ালা লোক ক্রাচে ভর দিয়ে ধীর গতিতে রাস্তা পার হচ্ছে। তাই রিকশাওয়ালার বিরক্তির ঘণ্টি এই মধুর টিংটিংটিং। পথ পরিষ্কার হতেই রিকশাটি দূরে চলে গেল। মুহূর্তে গলির একেবারে শেষ মাথায়। আমি ফিরে তাকালাম আমার হাতের দিকে। আমার বান্ধবীদের একটা গ্ৰুপ ফটোর দিকে।
আমাদের চারজনের আরেকজনের নাম ছিল সীমা। রাঙামাটির মেয়ে। ঢাকায় মামার বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করছিল। সীমার সঙ্গে প্রথম যেদিন কথা হলো ক্লাসরুমে, সেদিন ওর নামটি শোনে আমার মনে পড়ে গিয়েছিল সৈয়দ শামসুল হকের সীমানা ছাড়িয়ে উপন্যাসের নাম। সামনের বেঞ্চিতে বসেছিলাম আমি। পেছন থেকে কয়েকটি মেয়ের সরস কলকল হাস্যধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম বেশ পরিষ্কার। ওরা কথা বলছিল নিউমার্কেট আর চাঁদনি চকে শপিং করতে গেলে ভিড়ের মাঝে মিশে থাকা পুরুষ লোকগুলোর মেয়েদের শরীর হাতড়ানোর ব্যাপারে। ক্লাসের মেয়েদেরকে নিজের হাতের আঙ্গুলগুলো দেখিয়ে সীমা বলেছিল, ‘এই জন্য আমি ঐদিকে যাওয়ার আগে আঙুলের দশটা নখ ধার দিয়ে নেই খুব ভালো করে। একবার মার্কেটে ঢোকার সময় টের পেলাম আমার শরীরের পশ্চাৎদেশে একটা হাত সেঁটে আছে শক্ত করে, অনেকক্ষণ ধরে। আমি তখন আস্তে করে আমার এই চোখা নখের থাবায় সেই হাতটিকে এমন খামচি মেরে ধরে রেখেছিলাম যে বেচারা অনেকক্ষণ খুব কসরত করার পর ছোটাতে পেরেছিল নিজের হাত।’
সামনের বেঞ্চে বসে আমি পেছনের মেয়েগুলোর কথার ভেতর থেকে সীমার কথা শুনছিলাম মন দিয়ে। আসলে কথা নয়, শুনছিলাম ওর উচ্চারণ আর কথার অন্যরকম টান। পাহাড়ি ঝরনার শব্দ খুঁজে পাচ্ছিলাম যেন আমি ওর কথায়। অশুদ্ধ প্রমিত উচ্চারণ, তবু কী মিষ্টি! পেছনে ঘুরে বললাম, ‘এই তুমি তো খুব সুন্দর করে কথা বলো।’
সপ্রতিভ হেসে সীমা বলেছিল, ‘আমি জানি। আর আমি দারুণ মজার মজার কথাও জানি।’ ‘তোমার নাম কী?’ জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি। উত্তরে বলেছিল, ‘সীমা। আমি এক সীমাহীন ভালোবাসার সীমারেখা।’
শরীর বাঁকিয়ে পেছন ফিরে আমি একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম ওর দিকে হ্যান্ডশেক করার জন্য। সীমা আমার হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রশ্ন করেছিল, ‘তোমার নাম কী বন্ধু?’
চতুর্ভুজ বন্ধুতার দ্বিতীয় সরলরেখাটির প্রতি আমার মুগ্ধতার সেটি ছিল প্রথম প্রহর।
পায়ের কাছে গা ঘষছে পুসি বিড়ালটা। এই সময় ওর একটুখানি দুধ খাওয়ার অভ্যাস। যদিও পুসি আমার নিজের পোষা বিড়াল নয়, তবু পাশের বাড়ির বিড়ালটি রোজ এই সময়টাতে আমার কাছে এসে আহ্লাদ করে একবাটি দুধের জন্য। পুসিকে দুধের বাটি এগিয়ে দিয়ে আমি খাটের ওপর পা তুলে বসলাম। বাইরে থেকে চড়া রোদ এসে পড়ছে আমার মুখের ওপর। গরমে অস্থির লাগলেও আমি রোদে গা মেলে দিলাম। মনে মনে চাইছি রোদে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাক আমার বর্তমান জীবনের সকল দীনতা।
হাতের ছবিতে আর কলেজে আমার অন্য বান্ধবীটির নাম ছিল জবা। রক্তজবার মতো সব সময় লাল টুকটুক হয়ে থাকত ওর ফর্সা গালদুটি। জবা ছিল পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়ার মেয়ে। পাঁচ ভাইয়ের একমাত্র বোন। পঞ্চ পাণ্ডবের দল জবাকে আদরের চেয়ে শাসন করত অনেক বেশি। তাছাড়া জবা অত্যাধিক সুন্দরী হওয়ায় ছেলেদের খপ্পর থেকে বোনকে সরিয়ে রাখার চেষ্টায় পাঁচ ভাইয়ের একজন না একজন প্রহরীর মতো জবার আশেপাশে লেগে থাকত প্রায় সর্বক্ষণ।
বিছানা থেকে নেমে আমি আবার গেলাম আলমারির সেই তাকটির কাছে যেখানে আমাদের পুরনো ছবিগুলো পেয়েছিলাম একটু আগে। মনে হচ্ছিল আরও কিছু ছবি থাকার কথা ওখানে। খাঁজে ভাঁজে আটকে থাকা কিছু গোপন জহর-রত্নকে খুঁজে পাবার জন্য তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম আমি সাগরের জল সেচে সাতরাজার ধন খুঁজে পাবার বাসনায়। কিন্তু তাকের অবশিষ্ট সব কাপড় মেঝেতে ফেলে দিয়েও আর কোনো ছবি পেলাম না। তাই হাতের ছবিগুলোকে শক্ত করে অথচ সতর্কতার সঙ্গে বুকে চেপে ধরে রাখলাম কিছুক্ষণ। তারপর ঠান্ডা মেঝের ওপর পা মুড়ে বসে পড়লাম। দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে কোলের ওপর বিছিয়ে রাখলাম স্মৃতির মণিমাণিক্য, চারটি ছবি।
আমাদের চতুর্ভুজ বন্ধুতার তৃতীয় সরলরেখা ছিল সীমা আর চতুর্থ রেখাটি ছিলাম আমি। তিনজনের পরিচয়ের পর এবার আমার পরিচয় দেবার পালা। আমি রোকসানা। ঢাকার কাছাকাছি নারায়ণগঞ্জের মেয়ে। মাস্টার্স পাস না করা পর্যন্ত ঢাকায় একটা মহিলা হোস্টেলে সিট নিয়েছিলাম। তবে প্রতি মাসে একবার করে নারায়ণগঞ্জে যেতাম বাবা আর মাকে দেখতে। মেট্রিক আর ইন্টারমিডিয়েটে খুব ভালো রেজাল্ট করার পর আমার ইচ্ছে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব। কিন্তু চান্স পাইনি বলে সরকারি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে পড়তে যাওয়া। আর একই কলেজে একই সাবজেক্টে পড়তে আসা উপলক্ষে আমরা চারজন খুব ভালো বন্ধু হয়েছিলাম সেই কয়েকটি বছর। তবে শুধুই কয়েকটি বছরের জন্য! অবশ্য যদিও আমরা চারজনের কেউই শেষ পর্যন্ত অনার্স পাস করতে পারিনি। সে গল্প একটু পরেই বলছি।
আমাদের চার বান্ধবীর মধ্যে একমাত্র রত্নাই তখন বিবাহিতা ছিল। আমরা বাকি তিনজন নিজেরা অবিবাহিতা হয়েও একটি বিবাহিতা বান্ধবী পাওয়ার ব্যাপারটিতে বেশ উত্তেজিত হয়েছিলাম প্রথমে। কিন্তু ধীরে ধীরে টের পেলাম ব্যাপারটাকে আমরা যতটা চমকপ্রদ হবে বলে মনে করেছিলাম, ব্যাপারটি আসলে তার চেয়েও বেশি চমকপ্রদ ছিল। জুন জুলাই মাসের প্রচণ্ড গরমে আমরা তিন বান্ধবী রোদে কিংবা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে রত্নার সোবহানবাগের বাড়ির চার তলায় উঠতাম সিঁড়ি বেয়ে। সিঁড়ির নিচতলা থেকে আরম্ভ হওয়া আমাদের কলকল হাস্যধ্বনি শোনা যেত চার তলার বন্ধ দরজার ভেতর থেকেও। কারণ আমাদেরকে কখনো দরজার কলিংবেল বাজাতে হয়নি। দরজার সামনে দাঁড়াতেই দরজা আপনাআপনি খুলে যেত আলিবাবার চিচিংফাঁক মন্ত্রের মতো। আমাদের ক্ষুধার্ত পেটে হাঙরের মতো হাঁ করে থাকা খাবারের চাহিদার জোগান দিতে সেগুনকাঠের বিশাল টেবিলের পিঠে থরে থরে সাজানো থাকত হরেক রকম লোভনীয় খাবার। যদিও তখন আমাদের একটুখানি গরম ভাত আর লেবু ডাল হলেই বেশ দৌড়াত, কিন্তু রাজভোগের মতো মোহনীয় খাবারে আমরা তিনজনই মনে করতাম আমাদের অনেক সৌভাগ্য যে রত্নাকে আমরা বন্ধু হিসেবে পেয়েছি।
আনন্দের সময় লাগামহীন ঘোড়ার মতো দ্রুতগতিতে ছোটে। আমাদের চারজনের সেই ঝালমুড়ি খাওয়া, মরিচের গুঁড়ো আর বিটলবণ মেখে টক মিষ্টি আমড়া খাওয়া, ফার্মগেটের ভিড়ের রাস্তায় গলা ফাটিয়ে গান গাওয়া, একই প্রিন্টের কাপড় কিনে জামা বানানো, একটা ফিল্মের রিল কিনে ছবি তোলা, এমন অজস্র আনন্দের দিনের মধ্যে আমরা একে একে হারাতে আরম্ভ করেছিলাম পরস্পরকে। হারানো সেই দিনগুলোর কথা মনে করতেই বাড়ির পেছন থেকে অনেকগুলো কাকের ডাক শোনা গেল। কাকের ডাক শোনা মানে অমঙ্গল। তবু যখন তখন আশেপাশে কর্কশ স্বরে ডেকে ওঠে মরার কাক। বাড়ির উঠান থেকে কাক তাড়ানোর মতো অত্যন্ত জরুরি কাজটিকে গ্রাহ্য করলাম না আজ। যেমন ছিলাম তেমন বসেই রইলাম। দেয়ালের সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করে ভাবতে থাকি আমি।
অনার্স তৃতীয় বর্ষের ক্লাস করছিলাম আমরা তখন। সকাল দশটায় ক্লাসে আসতে দেরি হয়েছিল সেদিন রত্নার। ওর দেরি দেখে আমরা তিনজন নিচুগলায় গালমন্দ করছিলাম রত্নার নাম ধরে। কিন্তু রত্না যখন ক্লাসে এসে ঢুকল, তখন আমরা তিনজনই কথা বন্ধ করে চুপচাপ তাকিয়ে ছিলাম ওর দিকে। কারণ, রত্নার গায়ে সেদিন বোরখা ছিল না। রত্না কেমন কাচুমাচু আর অস্বস্তিবোধ নিয়ে ক্লাসে ঢুকে একদম পেছনে গিয়ে বসেছিল। শেকসপিয়রের মেকব্যাথের ‘ফেয়ার ইজ ফাউল, অ্যান্ড ফাউল ইজ ফেয়ার,’ লাইনটির পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা করে টিচার যখন ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন, আমরা তিনজন দৌড়ে গিয়েছিলাম রত্নার কাছে। জানতে চাইলাম, ‘ব্যাপারটা কী? আজ বোরখা ছাড়া কেন?’
রত্না যেন আমাদের চোখের দিকে তাকাতেই পারছিল না। হতাশা, রাগ, ক্ষোভ, নাকি মুক্তির উল্লাস, কোনোটারই অবস্থান নির্ণয় করতে পারিনি আমরা ওর চোখে সেই মুহূর্তে। বাইরের আকাশে উজ্জ্বল সূর্যটাকেও মেঘ ঢেকে দিয়ে গিয়েছিল তখন কয়েক সেকেন্ডের জন্য। আমাদের মনে হয়েছিল, বৃষ্টি নামবে বুঝি!
সেদিন আমরা জেনেছিলাম রত্নার বিশালদেহের স্বামীর সঙ্গে গৃহপরিচারিকার কামজ সম্পর্কের কথা। একটা ছোট্ট ভয়েস রেকর্ডারে গৃহপরিচারিকার জবানবন্দি রেকর্ড করে নিয়েছিল রত্না মেয়েটিকে কিছু অর্থলোভ দেখিয়ে। স্বামীকে সেই রেকর্ড শুনিয়ে কৈফিয়ত দাবি করেছিল চড়াইখোলার খুব সাদাসিধা মেয়েটা। উত্তরে স্বামী বলেছে, তার জীবনেও তো কিছু সাধ আহ্লাদ আছে, সেগুলোকে তিনি কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবেন না। স্ত্রীর মর্যাদা পেতে হলে রত্নাকে মেনে নিতে হবে স্বামীর এইটুকু সামান্য চরিত্র দোষ! এবং মেনেও নিয়েছিল রত্না, স্বামীর অনাচারের বদলা নিতে নিজে বোরখা ছাড়া বাইরে এসেছিল কিছুদিন। চেষ্টা করেছিল নিজেকে বদলে নিতে। তবে সেই ঘটনার অল্প কয়েকদিন পর রত্নার কলেজে আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল পুরোপুরি।
দুধ খাওয়া শেষ করে পুসি এসে আমার কোলে জায়গা করে নিয়েছে। এমনিতে সে পায়ে পায়ে ঘুরলেও কোলে ওঠার সাহস করে না সহজে। অবোধ প্রাণী, হয়তো টের পেয়েছে আজ আমার মন আর্দ্র হয়ে আছে। ওর মতো আজ আমারও একটুখানি স্নেহের প্রয়োজন আছে।
ঝুম বৃষ্টির এক বিকেলে আমি গিয়েছিলাম রত্নার কাছে। কেমন আছে, কী করছে এইসব সাধারণ কথা জানতে। বাইরের কালো আকাশ আর দামাল বৃষ্টিকে হার মানিয়ে সেদিন কেঁদে আকুল হয়েছিল আমার বান্ধবী রত্না। বলেছিল, ‘আমি শুধু ওকে বলেছিলাম যা করার বাইরে করো, বাড়িতে করো না এসব। কাজের মেয়েটা আমার সঙ্গে কেমন সতীনের মতো ব্যবহার করে। তাও মানতে রাজি হয়নি।’ লোকটা বলেছে, ‘বাইরে যাবার খরচা কে দেবে শুনি!’ চড়াইখোলার মেয়ে রত্না এর কিছুদিন পরে ঢাকা শহর ছেড়ে গ্রামে চলে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে তার প্রাণের তিন বান্ধবীকেও মুছে ফেলেছিল জীবন থেকে এক লহমায়। হয়তো ওর আঘাতপ্রাপ্ত ঢাকা-জীবনের স্মৃতির সঙ্গে আমাদের উপস্থিতি মিশে ছিল বলে শাস্তি পেতে হয়েছিল আমাদেরকেও। আর বিনা দোষে আমার বন্ধু হারানোর দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগের সেই ছিল শুরু। সেই ছিল আমাদের বন্ধুতার চতুর্ভুজে বাহু বিসর্জনের প্রারম্ভকাল।
পাহাড়ি ঝরনার মতো উদ্দাম আর চঞ্চলা মেয়ে সীমা, ঢাকায় পড়তে আসার আগে রাঙামাটির একটা কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিল সে। উপজাতি অধিবাসীদের সামাজিক সমঅধিকার এবং রাজনীতিতে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের সমান অধিকারের জন্য উচ্চস্বরে কথা বলার সাহস রাখত আমাদের সীমা রানী দাস। অনার্স প্রথম বর্ষের শুরু থেকেই কলেজের ছাত্র-রাজনীতির সঙ্গে ভীষণভাবে জুড়ে গিয়েছিল সীমা। সভা, সেমিনারে বক্তব্য রাখত প্রায়ই। অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্রনেতাদের কারও কারও সঙ্গে বিবাদেও জড়িয়ে পড়েছিল, জানতাম আমরা। বুঝতে পারছিলাম, দলীয় কোন্দল, নেতৃত্বের মারামারি, চাঁদার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে তৈরি সংকটে নিজের মতামত জানাতে গিয়ে ক্ষমতাসীন নেতানেত্রীদের চক্ষুশূল হয়ে উঠছিল সীমা। তবে সীমার প্রাণের জন্য হুমকি হয়ে এসেছিল ওর নারী স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান আর মুসলিম দেশে একটি অমুসলিম মেয়ের রাজনীতিতে জড়ানোর প্রচেষ্টা। শারীরিকভাবে নির্যাতন করে মেরে ফেলা সীমার মরদেহটি পুলিশ উদ্ধার করেছিল কাঁচপুর ব্রিজের নিচ থেকে বস্তাবন্দি অবস্থায়। অনেকের কাছে কানাঘুষায় জেনেছিলাম আমরা, কয়েকজন শিবির ছাত্রনেতার রোষানলে পড়ে প্রাণ হারাতে হয়েছে আমাদের সাহসী বান্ধবী, সীমা দাসকে। পত্রিকার পাতায় বস্তাবন্দি সীমার উদ্ধারকৃত লাশের ছবি দেখেছিলাম আমি। ছবিতে বস্তার ভেতরেও সীমাকে সরলরেখার মতোই সোজা লাগছিল আমার চোখে।
আমার কোলের ওপর বলের মতো গোল হয়ে থাকা পুসি আর হাতের আঙুলে কাঁপতে থাকা ছবিটির দিকে তাকিয়ে আমার বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে সীমার সেই প্রথম কথা, ‘আমি এক সীমাহীন ভালোবাসার সীমারেখা!’ ঝাপসা হয়ে আসছে আমার চোখের দৃষ্টি। ঘাড় উঁচু করে আমি জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকালাম। শোবার ঘরের জানালায় আকাশের অংশটুকু কী ভীষণ বৈচিত্র্যহীন! আশ্চর্য, মানুষের কষ্টে আকাশের বুকে একটিও দাগ পড়ে না! শুধু রাস্তার গ্রিলের সঙ্গে গা লাগিয়ে ঢলতে থাকা নারকেলের চিরিচিরি পাতাগুলোকে কাঁপতে দেখলাম তিরতির করে।
আমাদের চারবান্ধবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর আর পুরো কলেজের সেরা সুন্দরী মেয়ে ছিল জবা। জবার খুব কাছের বান্ধবী ছিলাম বলে আমরা কলেজের সব ছেলেদের কাছে দারুণ সম্মান পেতাম। ক্যান্টিনে খাবার কিনতে গেলে, মুড়িমাখা মামার কাছে কিংবা কলেজের বেতন দেয়ার সময় রেজিস্ট্রার অফিসে আমাদেরকে কখনো লাইনে দাঁড়াতে হয়নি, শুধুমাত্র আমরা জবার বান্ধবী ছিলাম বলে। দুপুরে ক্যান্টিনে খেতে বসলে প্রতিদিনই কোনো-না- কোনো ছেলে আমাদের টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াত। তারা সবাই জবার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চায়। একটা ছেলে প্রতিদিন হাতে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে এসে একটা কথাই বলত, ‘জবা, তুমি শুধু একবার বলো তুমি আমাকে ভালোবাসো?’
জবা এইসব ছেলেদের কারও কথারই কোনো উত্তর দিত না। কেবল ভয়ে চুপসে যেত খুব। মাথা নিচু করে টেবিলের দিকে মুখ করে থাকত যতক্ষণ না ছেলেগুলো আমাদের টেবিলের কাছ থেকে সরে দাঁড়াত। তবু সিগারেট হাতে আসা ছেলেটি প্রতিদিন জবার পাশে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে নিরুত্তাপ জবাকে অপলক দেখত, আর সিগারেটের আগুন দিয়ে নিজের বাহুতে প্রতিদিন একটা করে হার্ট শেইপ আঁকত।
জবা কোনো ছেলেকে ভালোবাসত না। অথবা বাসত হয়তো। কিন্তু আমাদেরকে কখনো বলেনি সেসব কথা। রত্নার চড়াইখোলা চলে যাওয়া আর সীমার মৃত্যুর পর কলেজে তখন আমার একমাত্র বান্ধবী ছিল জবা। কিন্তু হঠাৎ করে একদিন জবাও কলেজে আসা বন্ধ করে দিল। আমি ওদের মণিপুরীপাড়ার বাড়িতে গিয়েছিলাম দেখা করতে। খোঁজ নিতে। হারাধনের পড়ে থাকা একটি মাত্র ছেলের মতো আমার তখন সেই একটি মাত্র প্রাণের বন্ধু সে। তাই জবা কোথায় হারিয়ে গেল, সে কথা না জেনে আমি থাকতে পারতাম কেমন করে! আমি ওর সংবাদ নিতে ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। বাড়ি গিয়ে আমি ওর সংবাদ জেনেছি। আর সেই সঙ্গে নিজের চোখে দেখেও এসেছি।
শব্দের অত্যাচার থেকে বাঁচতে মোবাইলের রিংটোন আমি সব সময় কমিয়ে রাখি। পরিচিত সবাইকে বলা আছে খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া আমাকে ফোন না করতে। পৃথিবীতে খুব অল্প মানুষের সঙ্গেই আমার বিস্তর যোগাযোগ বজায় আছে এখনো পর্যন্ত। তবুও বেশ অনেকক্ষণ ধরে বিপবিপ করে যাচ্ছে আমার মোবাইল নামের যন্ত্রটা। শব্দটা মাথায় যন্ত্রণা করছে খুব। বিরক্তি নিয়ে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মোবাইলের কাছে গেলাম। মোবাইলটার গলা টিপে, মানে সুইচ টিপে বন্ধ করে দিলাম যন্ত্রের সকল যন্ত্রণা। সেই সঙ্গে হয়তো আমারও। জানালার গ্রিলের সঙ্গে প্রেম করতে থাকা নারকেল পাতারগুলোকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে আমি কপাল ঠেকালাম গ্রিলের গায়ে। মরচে পড়া গ্রিলের কয়েকটা ক্ষত আমার কপালে দাঁত বসিয়ে দিল নিশ্চিন্তে। আমার চোখের দৃষ্টি বাইরে রাস্তার ওপর। কিন্তু আমার মনের দৃষ্টি পলকহীন তাকিয়ে আছে প্রায় দুই যুগ আগের একটি দৃশ্যে।
শান্ত আর লাজুক জবাকে পায়ে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল একটা অন্ধকার ঘরে। দিনের বেলা ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ দেখে প্রশ্ন করেছিলাম আমি। জবার মা বলেছিলেন, ‘জবা আলো সহ্য করতে পারে না। আলো দেখলে চিৎকার করে।’ বললাম, ওর শরীরের এই হাল কেন? আন্টির কথা থেকে বুঝেছিলাম অবিবাহিতা জবার প্রেগন্যান্ট হওয়ার খবর পেয়ে ওর পঞ্চপাণ্ডব ভাইয়েরা খুব ক্ষেপে গিয়েছিল। পাঁচভাই মিলে আদরের বোনকে এমন মেরেছে, যে বাড়িতেই গর্ভপাত হয় জবার। আর সেই সঙ্গে জবার স্বাভাবিক জীবনেরও ইতি ঘটে। কাউকে চিনতে পারে না। হয়তো ইচ্ছে করেই চিনতে চায় না আর। অবিকল সিনেমায় দেখা পাগলির চরিত্রে অভিনয় করা মেয়েগুলোর মতো দেখাচ্ছিল সেদিন জবাকে। আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেনি। অভিমান নিয়ে ফিরে এসেছিলাম আমি জবার বাড়ি থেকে। আর কোনোদিন যাইনি ওর কাছে। মনে মনে আশা করে থেকেছি, জবা নিশ্চয়ই আবার সেই আগের রক্তজবার মতো জেগে উঠবে একদিন, বিকশিত হবে সুস্থ আর স্বাভাবিক জীবনের পুষ্পিত কাননে। কিন্তু শুভকামনা আর অন্তর নিংড়ানো প্রার্থনার পরেও আমি বুঝে গিয়েছিলাম আমাদের কলেজ জীবনের বন্ধুতার চতুর্ভুজের তৃতীয় বাহুটিও আমাকে পরিত্যাগ করেছে। মহাবিশ্বের একরৈখিক তির্যক আলোকরেখার মতো আমিও হাহাকার করে জ্বলতে থাকলাম আমার সীমাহীন একাকিত্ব নিয়ে। আমি হয়ে পড়লাম একটি একক সরলরেখা। আবর্তনহীন, পরিধিবিহীন, গন্তব্য না জানা এক স্থবির কালো কালির দাগ!
জবার রক্তিম গালদুটির মতো জানালার কার্নিশে রাখা লাল টুকটুকে অর্কিড ফুলের দিকে চোখ যায় আমার। বেখেয়ালে আঙুল ছোঁয়াতেই কয়েকটা কাঁটা ফুটে গেল আমার আঙুলে। দুটি লাল রক্তবিন্দু জমে উঠেছে তর্জনীর মাথায়। ঠিক যেন শীতের সকালে ঘাসের ডগায় জমে থাকা শিশির বিন্দু।
জানালার গ্লাসে ভিন্ন ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি ক্লান্ত অপস্রিয়মাণ নারী ছায়ার দিকে চোখ গেল আমার। আমি অবসন্ন চোখে তাকিয়ে থাকি ছায়াটির দিকে। আমার ডান হাতে ধরা আছে একটা পুরনো রঙিন ছবি। ছবিতে আমরা চারটি বান্ধবী। প্রাণবন্ত হাসিখুশি চারটি মুখ। একটি সুখী বন্ধুময় চতুর্ভুজের চারটি বাহু। আমাদের চারজনের চারটি চমৎকার জীবন হবার কথা ছিল। রত্না, সীমা, জবা, তিনজনের জীবনের স্বপ্ন নিভে যাবার গল্প তো বললাম এতক্ষণ। এরপর আসে চতুর্থবাহু রোকসানার কথা। মানে, আমার কথা।
জবাকে শেষবার দেখে আসার পরেও কয়েক মাস কলেজ করেছিলাম আমি। ইচ্ছে ছিল ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স কমপ্লিট করতে পারলে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেব। ছাত্রছাত্রীদেরকে একদিন শেকসপিয়রের ট্রাজেডি পড়াব আর আমার তিন বান্ধবীর জীবনের সত্যিকার ট্রাজেডি গল্প শোনাব। কিন্তু সহসা আমাকেও কলেজ ছেড়ে নারায়ণগঞ্জে ছুটতে হয়েছিল আমার বাবার এক জরুরি তলবে। নারায়ণগঞ্জে পৌঁছানোর একদিন পর এক সন্ধ্যায় আমার বিয়ে হয়ে গেল পরিবারের পছন্দ করে রাখা পাত্রের সঙ্গে। বিনা পরিচয়ে, বিনা ঘোষণায়, বিনা ভালোবাসায় আমি সংসার আরম্ভ করেছিলাম আমার স্বামীর সঙ্গে। বিশ্বাসের স্তর গভীর হবার আগেই স্বামীর সঙ্গে আমি চলে এসেছিলাম বগুড়ায়, শ্বশুরবাড়িতে। সেই থেকে এখনো আমি বগুড়াতেই আছি। আমার স্বামীও আছেন আমার সঙ্গে। বিয়ের পর আমাদের দুজনের মোটেও বনিবনা হচ্ছিল না। চুম্বকের সমমেরু যেমন পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, আমাদের মধ্যেও তেমন সোহাগের বিমুখ আয়োজন সাজছিল। কিন্তু পাশাপাশি থাকতে থাকতে একসময় আমরা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে থাকি। একসময় আমাদের মধ্যে প্রেম হয়। আমাদের মনে ভালোবাসা জাগ্রত হয়। বছর তিন পর আমাদের একটি সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু আমাকে মৃতবৎসা উপাধিতে ভূষিত করে সন্তানটি আঁতুড়ঘরেই মারা গেল। সন্তান হারানোর ব্যথা বুকে নিয়ে যখন আমরা স্বামীস্ত্রী পরস্পরের হৃদয়ের নিকটবর্তী হলাম, ঠিক তখন আচমকা আমার স্বামী স্ট্রোক করেন। আর আচমকা সেই মুহূর্তটি থেকেই তিনি স্থায়ীভাবে লম্বাসন নিয়ে নিয়েছেন বিছানায়। তিনি কথা বলার চেষ্টা করেন খুব, কিন্তু সেসব কথার কোনো অর্থ হয় না।
কথায় বলে, বিকলাঙ্গ মানুষের পাশে যদি আপনি দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করেন, তাহলে আপনার ভেতরটাও বিকলাঙ্গ হয়ে যেতে সময় লাগবে না। নিজেকে আমার বিকলাঙ্গ মনে হয় অনেক আগে থেকেই। আমি চাইলে আমার স্বামীকে ফেলে রেখে চলে যেতে পারতাম। যেমন করে চলে গিয়েছিল আমার বান্ধবী রত্না। চরিত্রহীন স্বামীর সঙ্গে নির্দ্বিধায় আমাদের তিনজনকেও ফেলে দিয়েছিল জীবন থেকে। যোগাযোগের একটা সামান্য উপায় পর্যন্ত রেখে যায়নি। কিন্তু আমি পারি না। আমাদের পারিবারিক আর সামাজিক ব্যবস্থা আমাকে তা করতে উৎসাহিত করে না। উৎসাহ দেয়া তো অনেক দূরের কথা, সংসারের এমন সব পরিস্থিতিতে বাবা মা ভাই বোনসহ মামা চাচা আরও মুরুব্বি পদে যারা থাকেন, তারা সবাই মেয়েদেরকে হাত পা শক্ত করে বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে আটকে রাখে স্বামী নামের মানুষটির পাশে। সেই মানুষটি পঙ্গু হোক, বিকলাঙ্গ হোক, অক্ষম আর নাম কাওয়াস্তের একটা ভগ্ন অথর্বই হোক না কেন, স্বামী তো! জন্মের সময় একটি শিশ্ন নিয়ে জন্মেছিল যে এই পৃথিবীতে, তাই মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কোনো-না-কোনো শিশ্নহীনের মমতা আর শুশ্রূষা পেয়ে যাবার অধিকার তার জন্মগত। তাই আমি স্বামীকে ছেড়ে যাবার চেষ্টা করিনি কখনো। আমি মানুষটা এমনই, একটু কেমন যেন। মেনে নিয়েছি, এটাই আমার জীবন।
পাশের ঘর থেকে গোঙানির আওয়াজ আসছে। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি আমি। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো আমার বুক ভেঙে। কাছে না গিয়েও আমি জানি, আমার স্বামী এখন বিছানা ময়লা করেছেন। তার এখন সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু আমি ছুটে যাবার জন্য খুব একটা তাড়া অনুভব করছি না। আমার ডান হাতে ধরে থাকা ছবিটিতে বন্দি হয়ে আছে যে মুহূর্তের আনন্দ উচ্ছ্বলতার গল্প, সেই গল্পে আমি বিচরণ করতে চাই আরও কিছুক্ষণ। আমাদের চলে যাওয়া যৌবনের উচ্ছ্বতায় আন্দোলিত হোক আমার এই বিকলাঙ্গ মনের আঙিনা । ক্যাকটাসের কামড়, নারকেল পাতার আদর, পাশের ঘরের চাপা গোঙানি সব কিছুকে ছাপিয়ে আমার মনে পড়তে থাকে আমার তিনজন বন্ধুর কথা। প্রাঙ্গণ আমাদের বন্ধুতার চতুৰ্ভুজীয় পরমানন্দময় দিনগুলোর কথা। আমার মনে পড়ছে, রত্নাকে আমি ভালোবাসতাম। সীমাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। জবাকে আমি ঈর্ষা করতাম। আমার আমি রোকসানাকে, আমি সৌভাগ্যবতী মনে করতাম। আর এখন আমি আমাকে অনুকম্পা করি। প্রতিনিয়ত ক্ষমা করে দেয়ার চেষ্টা করি। আমি আমাদের চারজনের বন্ধুতাকে ভীষণ মিস করি।
লুনা রাহনুমা গল্পকার। দেশের জাতীয় দৈনিক, বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকা, মুদ্রিত লিটল ম্যাগাজিন ও ওয়েবজিনে নিয়মিত লিখছেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : ভালোবেসে এঁকে দিলাম অবহেলার মানচিত্র, এবং ফুঁ প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ : নারীবৃক্ষ। অনুবাদ গল্পগ্রন্থ : দিগন্তের দিকে হেঁটে যাওয়া মেয়েটি। তিনি বর্তমানে ইংল্যান্ডে বসবাস করছেন।