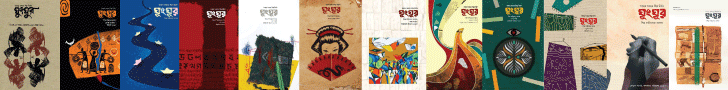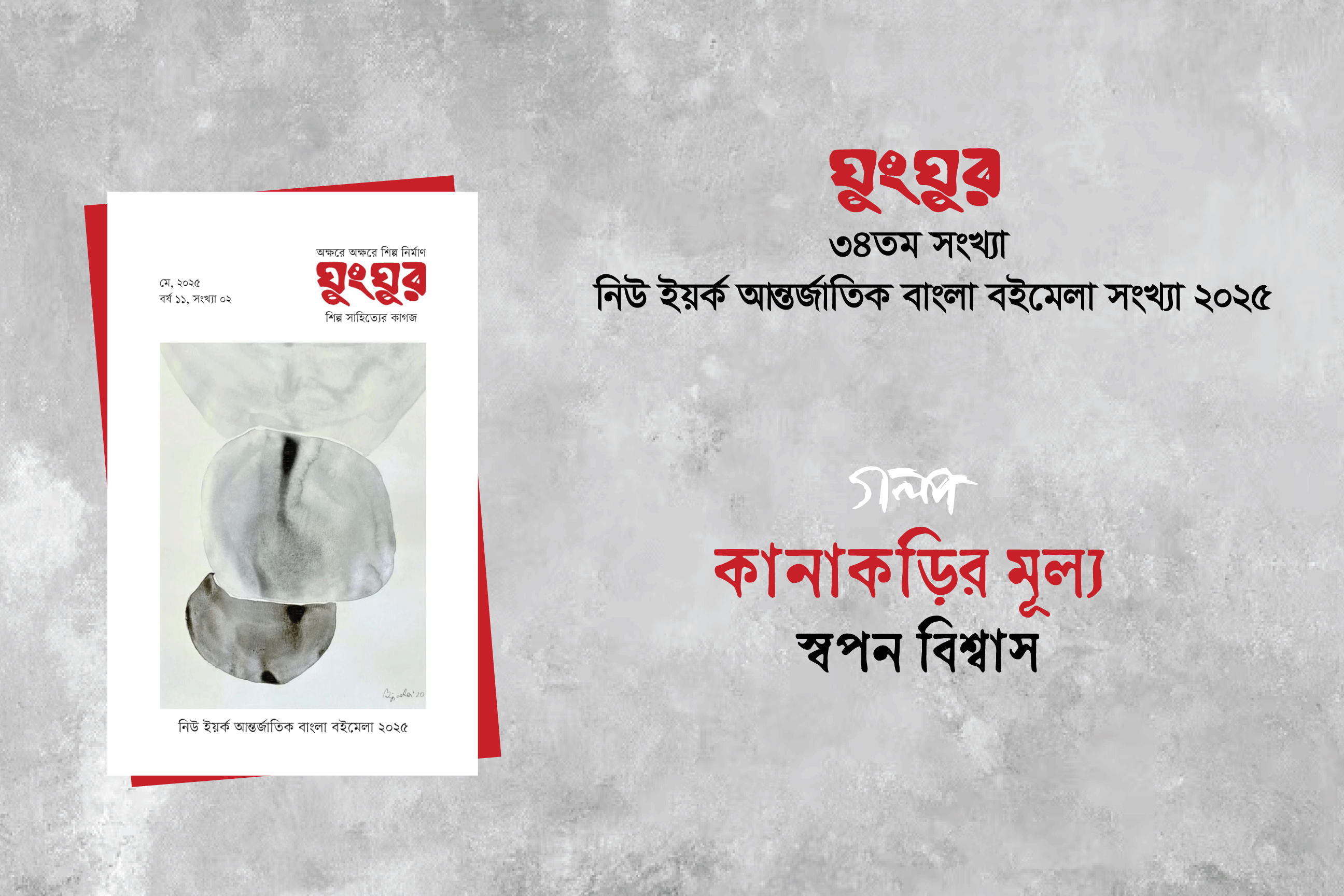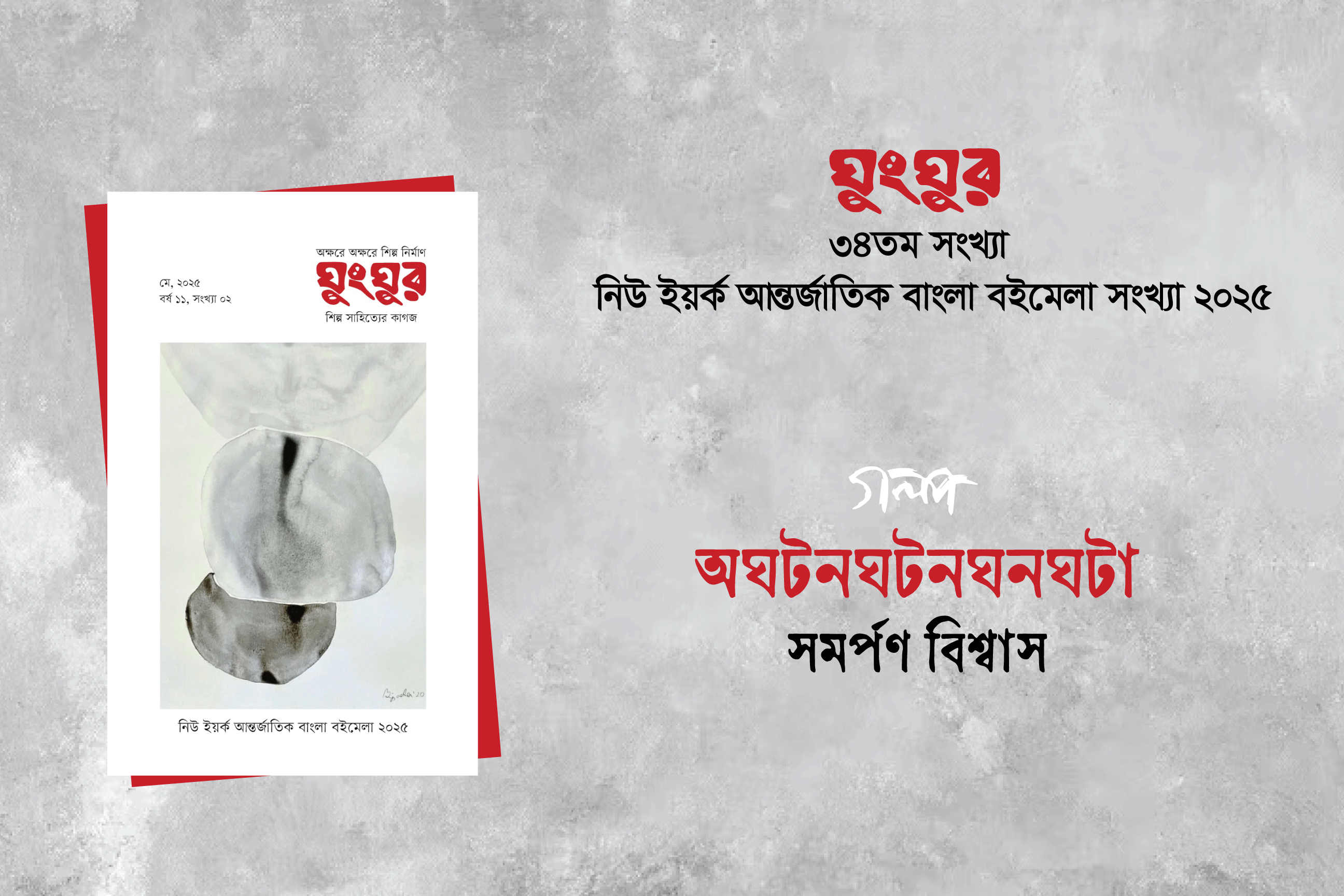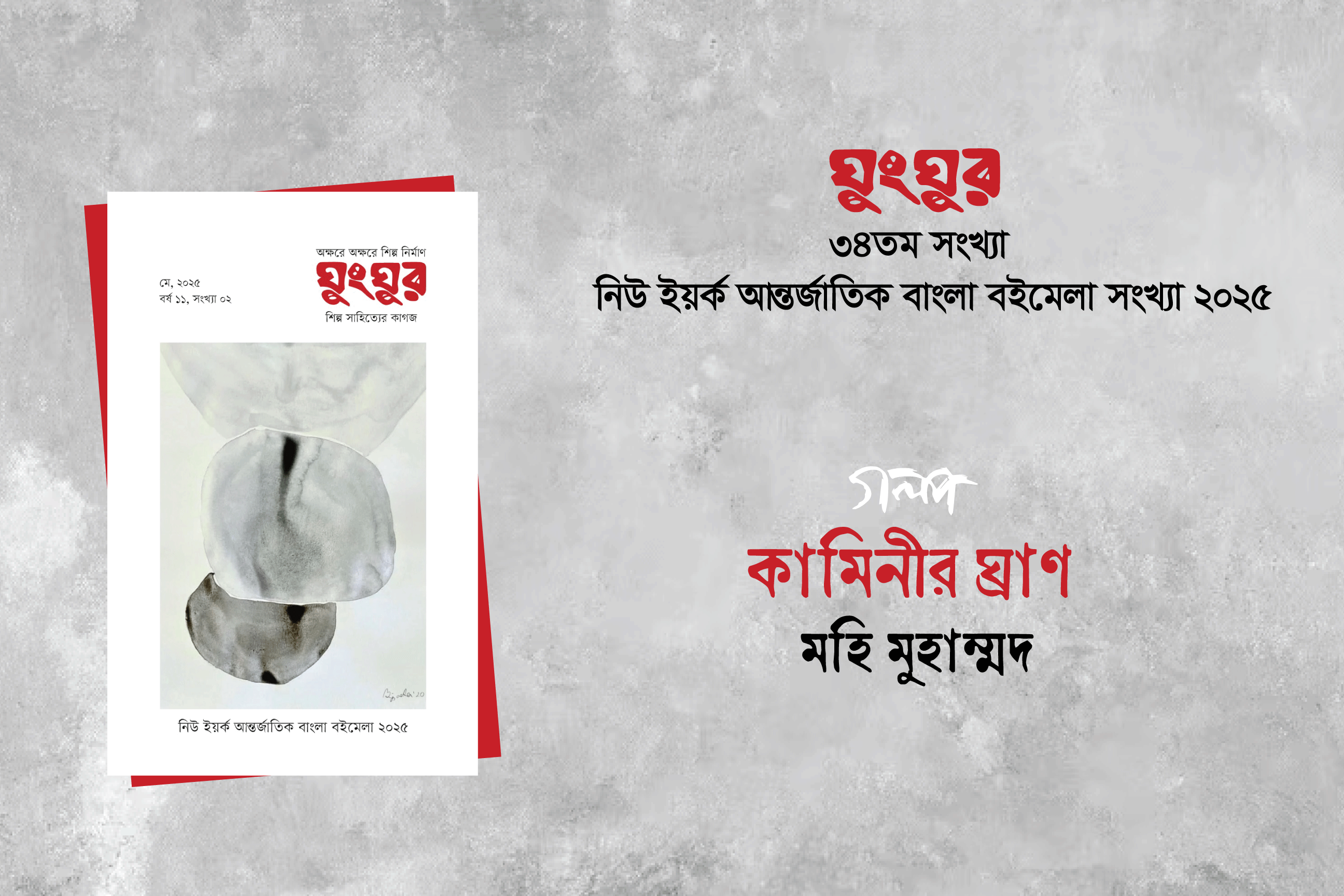আকাশ দেখার অসুখ

প্রতিদিনের মতো প্রত্যুষে ঘুম ভেঙে ঝটপট তৈরি হয়ে নিচ্ছিলাম। সময়মতো অফিসে পৌঁছানো আমার পুরোনো স্বভাব। সাত মিনিটে সকালের নাস্তা সেরে দৌড়ে গাড়ি স্টার্ট দিতে হবে। মা নাস্তা নিয়ে বসে থাকেন দিন শুরুর এই সময়টায়। এই সময় আমাদের মা-মেয়ে'র টুকটাক প্রয়োজনীয় কথা হয়। কাজ শেষে ফেরার পথে কী কী বাজারসদাই আনতে হবে, মা সেইসব আওড়াতে থাকেন পর্যায়ক্রমে। দেশে কোনো আত্মীয়ের টাকার অভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না, কারও মেয়ের বিয়ে পাকাপোক্ত হয়েছে, কিন্তু অর্থের অভাবে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার রাতের ঘুম হারাম, সেইসব। দেশের সঙ্গে মা-ই যোগাযোগটা চলমান রেখেছে। মায়ের এতেই আনন্দ। এর বাইরে তার অন্য কোনো চাহিদা নেই। নিজের জন্যে জগতের কোনো কিছুই যেন তার প্রয়োজন নেই। শারীরিক অসুস্থতার দিনগুলোতেও বলবে ও কিছু নয়, সেরে যাবে। পাছে আবার আমার রুদ্ধশ্বাস ছুটে চলা জীবন ব্যাহত করে হাসপাতালে দৌড়াতে হয়! আজও ব্যতিক্রম নয়। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে চেয়ার ঠেলে ওঠে দাঁড়াব, ঠিক সেই মুহূর্তে ফোন বেজে উঠল।
—হ্যালো, অরিত্রি আহমেদকে চাচ্ছি।
—বলছি
—আপনি কি একটু হাসপাতালে আসতে পারবেন?
—কেন, কী হয়েছে?
—একজন পেসেন্ট শেষরাতের দিকে মারা গেছেন। তিনি আপনার ফোন নাম্বারটি দিয়ে রেখেছিলেন। তার মৃত্যুর পর যেন আপনাকে সংবাদটি জানানো হয়।
—কী নাম তার?
—মাহতাব আহমেদ
—ঠিক আছে, আসছি।
কথা শেষ হতেই মায়ের উৎসুক অবয়বের দিকে তাকাই। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। সে দৃষ্টির নীরব জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর না দিয়েই বেরিয়ে পড়ি বাড়ির সামনে পার্ক করা গাড়ির দিকে। পিতার মৃত্যু সংবাদে পৃথিবীর যেকোনো কন্যারই গোটা পৃথিবী দুলে উঠার কথা। পিতা-কন্যা সম্পর্কটাই এমন। জগতের সবচে শক্তিশালী এক সম্পর্ক। কিন্তু আমার ভেতরে তেমন কোনো সুনামি বয়ে গেল না। যেন বহুকাল পূর্বে জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া স্বল্প পরিচিত কোনো আগন্তুকের মৃত্যু সংবাদে সামাজিকতা রক্ষার্থে নয়ত মানবিকতার অজুহাতে উপস্থিতি জানান দিতে হাসপাতালে ছুটে যাওয়া! অফিসে ফিরতে আজ ক্ষণিক দেরি হবে বলে কপালে বিরক্তি উদ্রেককারী ভাঁজ। ত্রিশ মিনিটের পথ। বড়জোর সব মিলিয়ে অফিস যেতে দুই ঘণ্টা দেরি হবে আজ।
গাড়ি হাইওয়ে ধরে ছুটে চলছে। সকালের এই সময়টা হাইওয়েতে স্লো ট্রাফিক লেগে থাকে। শাঁ শাঁ করে ছুটে যাওয়ার উপায় নেই। জিপিএস দেখাচ্ছে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে পৌঁছাতে। সামনে দৃষ্টিসীমায় যতদূর চোখ যায় শুধুই অফিসগামী গাড়ির সারি। মাথার উপরে শরতের ঝকঝকে নীলাকাশ। দলছুট মেঘ। সড়কের দুইধারে প্রকাণ্ড সব গাছের মগডালে সকালের নিরুত্তাপ সূর্যের কিরণ। দূরে বহুতল ভবনের গায়ে ঝুলে আছে ছোপ ছোপ রূপালি রোদ।
বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্কটি কেমন ছিল? খুব কষ্ট করে মনে করার প্রয়োজন পড়ে না। এখনো চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। মনে হচ্ছে যেন গতদিনের ঘটনা। ছোটবেলায় আমার জগত জুড়ে ভীষণ মজবুত এক আশ্রয়ের নাম ছিল বাবা। গলির মোড়ে এসে দূরের সরু রাস্তা যেমন করে বড় সড়কের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, আমি ঠিক তেমন করে বাবার বুকে লেপ্টে থাকা বাবা অন্তঃপ্রাণ কন্যা ছিলাম। আমার শহরের পাশ দিয়ে বহমান পদ্মা-মেঘনা-ডাকাতিয়ার সংযোগস্থলের সেই ঘূর্ণনে কালের বিবর্তনে অনেক কিছুই তলিয়ে গেছে। কিন্তু বাবার সঙ্গে আমার স্মৃতিগুলো আজও বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়নি। বাবা ছিলেন মেঘনাচরে বাতাসে হেলে থাকা শরতের শুভ্র কাশফুলের মতোই সাদামাটা। তাই বলে আমার জীবনটা কিন্তু বৈচিত্র্যহীন ছিল না মোটেও। কিন্তু সময়ের উত্তাল স্রোত মানুষকে কখন কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কেউ জানে না। নানু বলতেন, আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না। তবে কি আকাশের ওই পাড়ে যিনি বসে আছেন, তাঁর আঙ্গুলি হেলনেই আমার জীবনটা একদিনের নোটিশে উল্টে গেল?
সেদিন ছিল তুমুল বর্ষণের দিন। রাতে বাইরে রাতভর কালবৈশাখীর তাণ্ডব চলেছে। ঘুমোতে যাওয়ার আগে বাবার সঙ্গে মার কথা কাটাকাটি হতে শুনেছি। বিষয়টি কী নিয়ে, সেইদিকে মনোযোগ দেয়ার বিষয়টি আমার ছোট মস্তিষ্কে সাড়া দেয়নি। ওইটুকুন বয়সে এইসব পারিবারিক কলহ আমাকে তেমন ভাবনায় ফেলত না। কেননা, দিনশেষে বাবার বুকের ভেতর গুটিসুটি মেরে গল্প শোনাতেই আমার লোভ ও আগ্রহ ছিল। আর এ কাজটি করতে বাবা শত প্রলয়েও অনিয়ম করেননি। সুতরাং বড়দের অনেক কিছুতেই আমার মনোসংযোগ ছিল না। ভোরে বেলা করে ঘুম ভাঙলে দেখি ছোট খালামনি, নানু আমাদের বাসায়। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলছে না, জড়িয়ে ধরছে না, হাসছে না, স্কুলের সময় পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তৈরি করে দিচ্ছে না। আমি থমথমে ঘরে একাকি হেঁটে বেড়াই। বাবাকে খুঁজি। মাকে খুঁজি। নানু জায়নামাজে বসে দোয়া-দরুদ পড়ছেন। আঁচলের কোণে অশ্রুসজল চোখ মুছছেন। ছোটখালার মুখ ভর্তি শতাব্দীর কালো অন্ধকার ছেয়ে আছে। যেন আদিম কোনো আকাশ চোখ মেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বেলা গড়িয়ে সুনসান নীরব দুপুর। আচমকা কলিংবেলের শব্দে দৌড়ে যাই। চেয়ার টেনে যথারীতি তাতে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে দেই। পশ্চিমাকাশে মেঘের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার মতো করে ছোটখালা ভেতরের রুমে চলে যায়। আমার স্পষ্ট স্মরণে আছে, বাবা অন্যদিনের মতো বাইরে থেকে ফিরে আমায় জড়িয়ে ধরে আদর করেননি সেদিন। বাবাকে ভীষণ ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল। মুখটা ল্যাম্পপোস্টের ম্যাড়মেড়ে আলোর মতন আলোছায়াময়। আমি কাছ ঘেঁসে বসে মায়ের কথা জানতে চাইতেই আমায় আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে ধরেন। অনেকটা প্রাচীন দালানের স্যাঁতস্যাঁতে দেয়াল আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চাওয়ার মতো। আমি বাবার হৃদস্পন্দনের শব্দ শুনতে পাই। যেন তুমুল হাতুড়িপেটা আওয়াজ। ভেতরটা নিংড়ে জল এসে গিয়েছিল বাবার দু'চোখে। আমি আমার ছোট্ট ঘাড়ে ফোঁটা ফোঁটা জলের উষ্ণতা অনুভব করি। দুইদিন বাদে মাকে হাসপাতাল থেকে বাসায় আনা হয়। আমি নিয়মিত স্কুলে যাওয়া শুরু করি। বাবা আমায় ঘুমের সময় নিয়ম করে গল্প শোনায়। নানু, ছোটখালা গ্রামে ফিরে যায়। সবকিছু আগের মতো মনে হলেও কিছুই আর আগের মতো হয়ে উঠেনি। একরাতেই আচমকা আমাদের জীবনটা পদ্মফুল থেকে পদ্মপাতার জল হয়ে গেল। মা জানালার পাশে একমনে দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রকৃতির সঙ্গে মায়ের নীরব মানসিক আদান-প্রদান চলে। মায়ের আকাশ দেখার অসুখ হয়। দিনের ঝলমলে আলোয়, রাতের গহীন অন্ধকারে। কী জানি, ঘন অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে চেয়ে থাকলে সে-ও হয়তো একসময় সয়ে যায় চোখে! আমাদের জীবনে অদ্ভুত উদাসীন দিনের শুরু। মাকে আর কখনোই বাবার সঙ্গে কথা বলতে দেখিনি। নির্লিপ্ত মনে মা রেঁধে বেঁড়ে রাখেন। বাবা বাড়ি ফিরে একাকী নিজের মতো করে খেয়ে ড্রইং রুমে পত্রিকায় ডুবে থাকেন। আগের মতো অফিসে কী ঘটেছে, মায়ের সঙ্গে সেইসব গল্পে মেতে উঠেন না। আগাগোড়া রসিক বাবা বাকরুদ্ধ হয়ে থাকেন। রাত বাড়লে আমায় রোজকার নিয়মে গল্প শোনান। কিন্তু গল্পচ্ছলে আর কোনোদিনই বাবাকে আগের মতো বাড়ি কাঁপিয়ে বিকট শব্দে হা হা করে হাসতে দেখিনি। কিংবা অফিস ফেরত ঘর্মাক্ত বাবা আমায় জড়িয়ে ধরে 'মা, মা, মা... অরিত্রি মা আমার' বলে চুমু খায়নি। ড্রইং রুমেই ঘুমিয়ে পড়েন রোজ রাতে। আমি তাদের দৈনন্দিন গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথনের একমাত্র বাহক হয়ে ওঠি। বিষয়টি অনেকটা কোনো এক চেনা নদীর তীরে জলের কলতান থেমে যাবার মতন।
বড় হতে হতে পাড়া-প্রতিবেশী ও স্বজনদের কাছ থেকে যতটুকু জেনেছি, তার সারমর্ম করলে দাঁড়ায়, ছোট খালা ছিলেন অসম্ভব রূপবতী। এ নিয়ে মায়ের মনে একরকম হীনমন্যতা কাজ করত। নানাবাড়ির আর্থিক অবস্থা মোটেও ভালো ছিল না, বিধায় ছোটখালা স্কুলের গণ্ডি না পেরোতেই বিবাহের জন্যে নানাভাই পাত্রের সন্ধান করছিলেন। কিন্তু তুমুল মেধাবী ছোটখালার অনুরোধে বাবা তাকে শহরের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। স্কুল, কলেজ কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করে ছোটখালা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন বাবার আশ্রয়-প্রশ্রয়ে। সব খরচ বহন করছিলেন বাবা। বিষয়টি মায়ের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। মা উদ্ভ্রান্ত আচরণ শুরু করেন। বাবার সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হন। মায়ের মনে একরকম নিশ্চিত ধারণা জন্মে, বাবার সঙ্গে ছোটখালার মন-দেয়া নেয়া চলছে। অভিমানের ভারী পাথর মায়ের বুকে চেপে বসে। সেই রাতে এক গাদা ঘুমের ওষুধ খেয়ে মরতে বসেছিল মা। মধ্যরাতে গোঙানির শব্দে ঘুম ভেঙে আলো জ্বালান বাবা। দেখেন, মা মেঝেতে পড়ে আছেন। প্রতিবেশী ঝুমা আন্টিকে আমার দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে মাকে কোলে নিয়ে রাতের অন্ধকারে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে ছোটেন। ভাগ্যিস সময়মতো হাসপাতালে নেয়া হয়েছিল!
ঘটনাটি আমার মনে দারুণভাবে রেখাপাত করে। আমার বিচারালয়ে আমি বাবাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাই। যখন একটু একটু করে বুঝতে শিখি, আমার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মায়, যাহা রটে, তাহা কিছুটা তো বটে! কোনো কারণ ছাড়া নিশ্চয়ই একজন স্ত্রী তার স্বামীকে সন্দেহ করে না। নিশ্চয়ই বাবা ছোটখালার সঙ্গে বিশেষ কোনো সম্পর্কে জড়িয়েছেন। নইলে মায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আগ বাড়িয়ে এত আদিখ্যেতা কেনই-বা করতেন? বাবার প্রতি পাহাড়সম ঘৃণা জমতে থাকে মনের আকাশে। মনের অজান্তেই ধিরে ধিরে বাবার সঙ্গে আমার মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়। বাবা সন্ধ্যায় বাসায় ফিরলে আমি পড়ার ব্যস্ততা দেখাই, নয়তো ক্লান্তির অজুহাতে শোয়ে পড়ি। জানালা দিয়ে ঢোকা চাঁদের আলো মুখে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি প্রায়ই। কোনোদিন আচমকা সামনে পড়ে গেলে বাবা দশটা প্রশ্ন করলে একটার জবাব দেই। অধিকাংশ সময়ে দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে হুম হা উত্তর দেই। আমাদের তিন সদস্যের পরিবারে বাবা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো একলা হয়ে পড়েন। এ সময়ে মায়ের সঙ্গে আমার সখ্যতা বাড়ে। মা-ই হয়ে উঠে আমার বন্ধু, আমার পৃথিবী।
ডিসেম্বরের এক শীতল সকাল। বাইরে ফেরিওয়ালাদের হাঁকডাক। এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। বাবা একটি খাম হাতে ধরিয়ে দিয়ে খুলে দেখতে বলেন। দেখলাম বাবা ডিভি লটারি জিতেছেন। অফিসের অন্য কলিগদের দেখাদেখি ফরম ফিলাপ করেছিলেন। বাবাই একমাত্র অভিনন্দন বার্তা পেয়েছেন। নানাবিধ ডকুমেন্টস জমা দেয়া, ভিসার জন্যে ইন্টার্ভিউ দেয়া, সবকিছু কেমন যেন দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন হয়ে গেল। সকলে বলাবলি করছিল, আমরা নাকি তুমুল ভাগ্যবান! কত সহজে আমেরিকা যাওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলাম। সত্যিই এক বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় আকাশযানে চেপে স্বপ্নের মতো বিশ্বের রাজধানী নিউইয়র্কে চলে এলাম। ভোরের ঘুমন্ত জনপদের আচমকা জেগে উঠার মতন। আসলে জীবন এক বহমান নদী। কোথা থেকে কোথায় যে তার গন্তব্য, আমরা কেউই তা জানি না। আমরা শুধু নদীর ঢেউয়ের ন্যায় ভেসে চলি একূল থেকে ওকূলে।
বিদেশ বিভূঁইয়ে শুরুর দিকে আমরা একই বাড়িতে বসবাস করছিলাম। কিন্তু দিনের পর দিন আমাদের মা-মেয়ের জগতে বাবা নিজেকে একলা পথিক হিসেবে আবিষ্কার করেন। বাবাকে ধু ধু নিঃসঙ্গতায় পেয়ে বসে বোধহয়। একদিন আমায় ডেকে বলেন, আমার মনে হয় এভাবে অপাংক্তেয় হয়ে এখানে থাকা ঠিক হচ্ছে না আমার। আমি দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে কোনো প্রতিউত্তর করিনি। এইসব অবান্তর অহেতুক ঘটনা আমার জীবনে না ঘটলেই কী নয়? কেনোই-বা অচিন এক আবর্ত আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে? সত্যিই এক অপরাহ্নবেলায় ছোট একটি ব্যাগে নিজের জামাকাপড় গুছিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। ধীরে ধীরে স্ট্রিট পেরিয়ে এভিনিউয়ের দিকে হেঁটে দৃষ্টিসীমায় মিলিয়ে গেলেন, একটি বিন্দুর মতো একা, একজন মানুষ। আমরা মা-মেয়ে জানালার শার্শির ভেতর দিয়ে ধূসর কুয়াশার ন্যায় তার চলে যাওয়া দেখলাম। কেউ বাঁধা হয়ে দাঁড়ালাম না। যেন এমনটিই হওয়ার কথা ছিল। কিংবা এমনটিই চেয়েছিলাম আমরা।
মাস শেষে বাবা আমাদের বাড়িভাড়া পাঠিয়ে দেন বাড়িওয়ালার একাউন্টে। প্রতি মাসের শুরুতে খাওয়া খরচের চেক পাঠান মেইলে। এইসব তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আমার চাকরিটা হয়ে যাওয়ার পর আমরা আর তার সাহায্য নেইনি। নিতে চাইনি আরও আগে থেকেই। কেননা আমাদের তো আত্মসম্মানবোধ বলে কিছু অন্তত শেষ হয়ে যায়নি। শেষ অব্দি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে চাকরিটা পেয়ে গেলাম। ঠিকানা বদলের পর আমাদের আর জানা হয়ে উঠেনি তার নতুন ঠিকানা। জানার প্রয়োজন বোধ করিনি। যে মানুষ এক নারীতে সন্তুষ্ট নয়, সে হয়তো নিজের সুবিধার্থে ঠিকানা বদলেছে। কাউকে বিয়ে করে নতুন সংসার পেতেছে। এই দূর দেশে তো আর স্বজন, সমাজ, সংসার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কারো এহেন কর্মে ছি ছি করবে, সেই সময় কই এই উন্নত দেশে? অতএব সুযোগের সদব্যবহার করাটা বিচিত্র নয়।...
ছায়া-শীতল স্নিগ্ধ এক পরিবেশে হাসপাতালের সামনে এসে থামি। গাড়ি পার্ক করে সামনে এগিয়ে যাই। পাঁচ/ছয় জন মানুষ হাসপাতালের আনুষ্ঠানিকতা সেরে লাশ গাড়িতে তুলছিল। তিনজন কৃষ্ণাঙ্গ আর দুইজন বাঙালি মিলে বাকি আনুষ্ঠানিকতায় সহযোগিতা করছিলেন। তারা সকলেই মাহতাব আহমেদের অতি কাছের জন। জানালো, ফিউনারেল হোমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবে। তারা বলাবলি করছিল, তীব্র শ্বাসকষ্ট আর বুকে ব্যথা নিয়ে মাহতাব আহমেদ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। আমি নিজের পরিচয় দেই। অরিত্রি আহমেদ। বাবার বয়েসী একজন এগিয়ে এলেন। বললেন, 'আমি তোমার বাবার কলিগ। এর আগেও বুকে ব্যথা নিয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কোনো এক দুর্বোধ্য কারণে বুঝে গিয়েছিলেন, এ যাত্রায় আর ফেরা হবে না তার। তাইতো তোমার ফোন নাম্বারটি দিয়ে রেখেছিলেন আমায়। আমিই সকালে ফোন করেছিলাম তোমায়'। মুঠোফোনে ফিউনারেল হোমের ঠিকানা টুকে নেই। গাড়িতে বসে জিপিএসসে তা সেট করি। আজ আর অফিসে যাওয়া হবে না, ফোন করে জানিয়ে দেই।
হাসপাতাল থেকে মাত্র দশ মিনিট দূরত্ব। গোসল শেষে কফিনে রাখা হলো বাবার নিথর দেহ। আমি কাছে এগিয়ে যাই। আমার ভয় ভয় লাগছে। মৃত মানুষের তো উঠে আসার ক্ষমতা নেই, তবু কেন তা দেখে ভয় পাচ্ছি? বছর পাঁচেক হবে, বাড়ি ছেড়ে গেছেন বাবা। অথচ শেষ কবে তার মুখ দেখেছি মনে করতে পারি না। কেননা বহুকাল মুখের দিকে না তাকিয়ে দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় কথা সেরেছি। কেউ একজন কাফনের কাপড় সরিয়ে মুখের অংশ উন্মুক্ত করে দেয় দেখার সুবিধার্থে। বিষাদে আচ্ছন্ন এক প্রবীণের নিষ্প্রাণ মুখ! যেন শতাব্দীর নীল অন্ধকার এসে জমা হয়েছে তার মুখাবয়বে। কবে এত বুড়িয়ে গেলেন মানুষটি? বহু কাল, মহাকাল আগে দেখা দূরের কোনো এক আবছা পরিচিত মানুষ অনন্ত ঘুমে তলিয়ে আছে যেন। একজন কৃষ্ণাঙ্গ ইংরেজিতে বলছেন, জানাজা দিয়ে তাড়াতাড়ি কবর দিতে হবে সন্ধ্যা ঘনাবার আগে। 'আমার নাম রহমত, তোমার আব্বার রুমমেট। তুমি আমারে রহমত চাচা বইলা ডাইক্যো', কারও এমন কথায় পিছনে ফিরে তাকাই। তিনি আবারো বলেন, 'জানাজা শেষ হইলে আমার লগে বাসাত অ্যাইয়ো মা। তোমার আব্বা কিছু জিনিস তোমারে বুঝায়া দিতে কইছে।'
কী জিনিস? আমাকেই বা কেন বুঝিয়ে দিতে বলেছে? আমার সঙ্গে তো কোনো যোগাযোগই ছিল না তার! তাছাড়া রুমমেট কেন? তার কি বিগত পাঁচ বছরে কোনো পরিবার হয়নি? এমন হাজারো প্রশ্ন ঘুরছে মাথার চারপাশে। আমি যখন রহমত চাচার সঙ্গে সেই বাড়ির বেইজমেন্টে যাই তখন দিনের আলো সেদিনের মতো রাত্রির অন্ধকার গহ্বরে মিলিয়ে গিয়েছে। চারপাশে নিয়নের কমলা আলোর রাজত্ব। রহমত চাচা চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলতেই ভ্যাঁপসা গন্ধ নাকে এসে লাগে। একটি মাঝারি মাপের রুম। দুইপাশে দেয়ালের দিকে দুটি বিছানা। মাঝে ছোট্ট একটি টেবিল, দুটি চেয়ার। আসবাব বলতে এই-ই। একটি বিছানার পাশের দেয়ালে বাবা, মা আর আমার, আমাদের তিনজনের হাস্যজ্জ্বল ছবি টানানো। যখন আমাদের তিন সদস্যের পরিবারের একটি সুখী গল্প ছিল। ছবিটি দেশ থেকে বয়ে নিয়ে এসেছেন বাবা, আমার জানা ছিল না। 'এইডা তোমার বাপের বিছানা। এই ছবি দেখায়া কত রাইত তোমাগো গল্প করছে,তার হিসাব নাই', রহমত চাচা বলতে বলতে কাছে এসে দাঁড়ান। তিনি দুইটি খাম আমার হাতে তুলে দেন। একটি পাতলা, অন্যটি ভারী। পাতলা খামটি খুলতেই বেরিয়ে আসে বাবার শরীরের স্নিগ্ধ সুবাসমাখা চিঠি। বিলম্ব না করে সেটি খুলে পড়তে শুরু করি—
মা অরিত্রি,
তোমাদের ছেড়ে এসেছি পাঁচ বছর হয়। অথচ মনে হয় অনন্তকাল আমি তোমাদের দেখি নাই। তোমাদের দেখার তৃষ্ণা বোধ করি মৃত্যুর পরও মিটবে না। আমি তোমাদের ছেড়ে আসতে চাইনি। চেয়েছিলাম তুমি অন্তত আমাকে সহানুভূতির সঙ্গে বুঝবে। কেন যেন ওই বাড়িতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। এক ছাদের নিচে থেকেও যোজন যোজন দূরত্ব। বেঁচে থেকেও মৃত মনে হচ্ছিল। জীবন্মৃত। তবুও পাশের রুমেই তোমরা আছো, এমন ভাবনা আমায় স্বস্তি দিতো। যে দোষে আমাকে তোমরা দোষী সাব্যস্ত করেছ, একজীবন শাস্তি দিয়েছ, আমার তা পাওনা ছিল না। আমি আজও বুকে হাত রেখে বলতে পারি, আমি কোনোদিন কোনো অপরাধের সঙ্গে, পাপের সঙ্গে জড়াইনি।
আমি সত্যিই তোমাদের সান্নিধ্যে এক জীবন পার করে দিতে চেয়েছিলাম। তোমাদের ছেড়ে আসবার দিনে, আমি মনে প্রাণে চেয়েছি কেউ আমায় যেতে না দিক। শুধু একবার বাঁধা দিক। আমি ব্যাগ গুছিয়ে দরজার পাশে এসে থমকে দাঁড়িয়েছি। পিছনে ফিরে তাকিয়েছি। কান পেতে রয়েছি কেউ ডাক দিবে বলে। কিন্তু কাউকে দেখিনি। কিচ্ছু শুনিনি। দরজা পার হয়ে হলওয়েতে দাঁড়িয়ে থেকেছি কিছুক্ষণ। লিফ্ট এসেছে, চলেও গিয়েছে। তবু আমি দাঁড়িয়ে থেকেছি কয়েক মুহূর্ত। সেই মুহূর্তটা আমার কাছে শতাব্দীর দীর্ঘতম সময় মনে হয়েছে। নিচে রাস্তা ধরে আস্তে ধিরে হেঁটেছি। যদি উপর থেকে জানালা দিয়ে কেউ ডাকে, সে আশায়। যেতে যেতে বহুদূর চলে গিয়েছি। বড় রাস্তায় বাঁক নিয়ে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গিয়েছি। দিন, মাস, বছর কেটে গেছে, তবু কোনো ডাক শুনিনি। সেই তো ডাক এলো। ওপারের ডাক। এবার বোধ হয় সত্যিই ওপারের ডাক এসেছে। খামে কিছু ডলার আছে। এছাড়া আর কিছুই তো রেখে যেতে পারিনি। তোমার মাকে দেখে রেখো। আমাকে ক্ষমা করো। মা, মা, মা... অরিত্রি মা আমার।
ইতি,
তোমার হতভাগা বাবা
এক নিঃশ্বাসে পড়া শেষ করি। ভেতরটা অস্থির, অশান্ত হয়ে ওঠে। জলকল্লোলের শব্দ টের পাই। জলের ঢেউ আছড়ে পড়ছে যেন বুকের ভেতর। হাউমাউ করে কেঁদে ওঠি। তীব্র এক কষ্ট দলা পাকিয়ে দুমড়ে মুচড়ে চুরমার করে ফেলছিল আমায়। পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে জীবনরহস্য বোঝার বয়স না হয় আমার হয়নি, কিন্তু কেউ তো আমার সে ধারণা শুধরে দেয়নি! এ দায়ভার কার? কোন অজ্ঞাত শক্তি আমার পরীক্ষা নিচ্ছে? আমি বাবার ব্যবহৃত বালিশ জড়িয়ে ধরে বাবার গায়ের সুবাস খুঁজে ফিরি। বাবা, বাবা, বাবা বলে চিৎকার করে কাঁদি। দম বন্ধ হয়ে আসে। বেইজমেন্ট থেকে বেরিয়ে বাইরের বাতাসে বুকভরে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করি। যেন পৃথিবীর কোথাও এক চিলতে বাতাস নেই। ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে উঠছে বাবার বুকে লেপ্টে থাকা দিনগুলো। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বাবা দরজার সামনে দুইহাত বাড়িয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন, আর ছোট্ট আমি ছুটে গিয়ে তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছি। আমার কর্ণকুহরে ক্রমাগত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, মা মা মা... অরিত্রি মা আমার!
একজন মানুষ একবুক অভিমান জমিয়ে, অসীম যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে পৃথিবী ছেড়ে গেছেন। তাতে এই পৃথিবীর কারও কোনো ক্ষতি হয়নি। এখানে প্রতিদিন ভোর হবে, পাখি ডাকবে, কর্মব্যস্ত মানুষ ছুটে চলবে যার যার গন্তব্যে। দিনশেষে সন্ধ্যা ঘনাবে, রাত্রির বুক চিরে আবার ভোরের আলো ফুটবে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে অজানা থেকে যাবে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের বিষাক্ত ধোঁয়া কেমন করে একটি জীবনকে পৃথিবীর বুকে হত্যা করেছে শত সহস্রবার। যে হত্যার বিচার হবে না কোনোদিন মানুষের তৈরি আদালতে।
রিমি রুম্মান গল্পকার, প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট। দেশ ও প্রবাসের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকায় নিয়মিত লিখছেন। স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে বর্তমানে নিউইয়র্কের কুইন্সে বসবাস করছেন ।