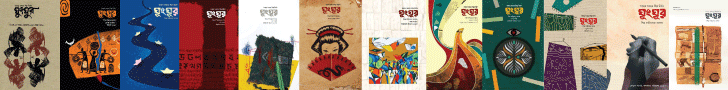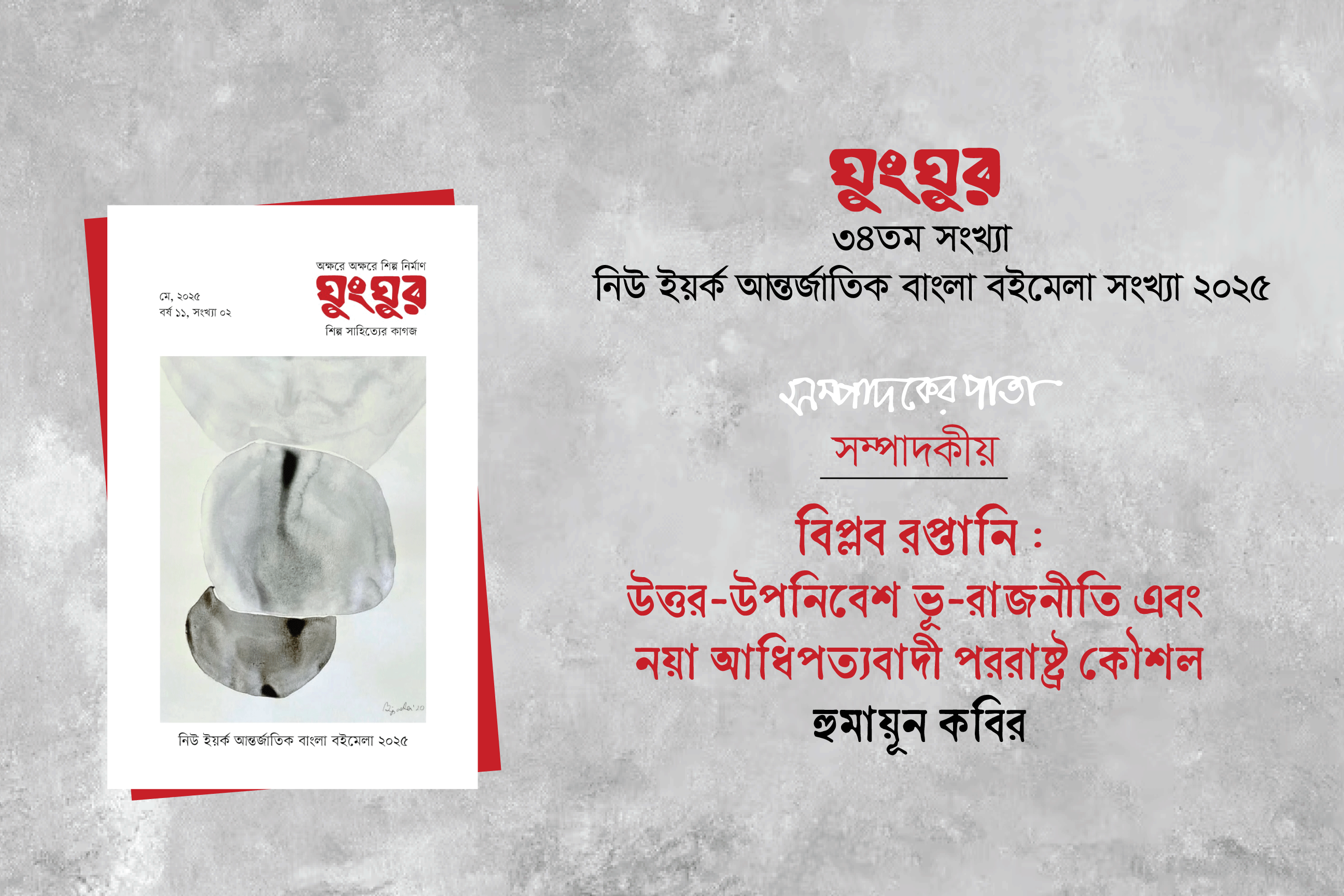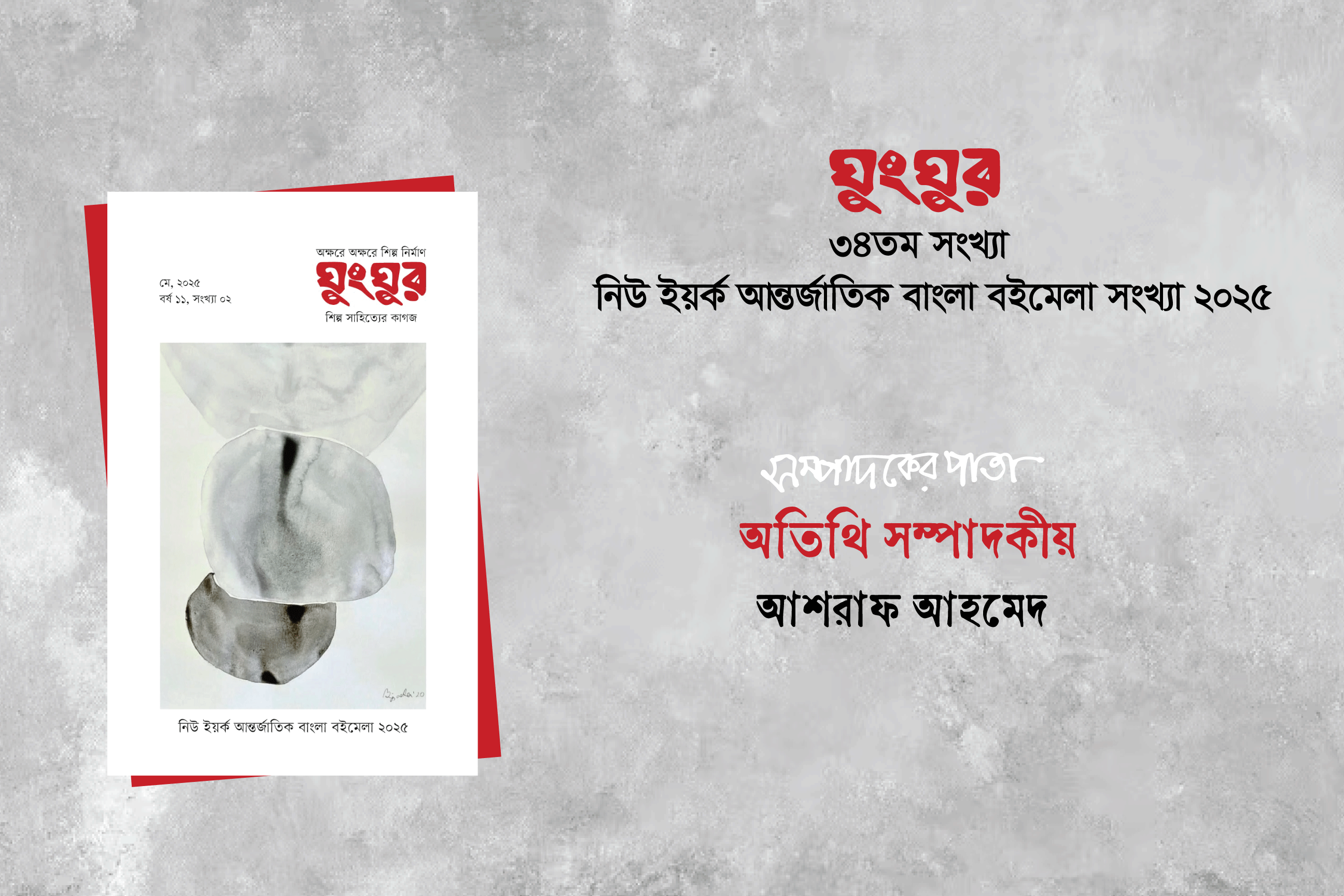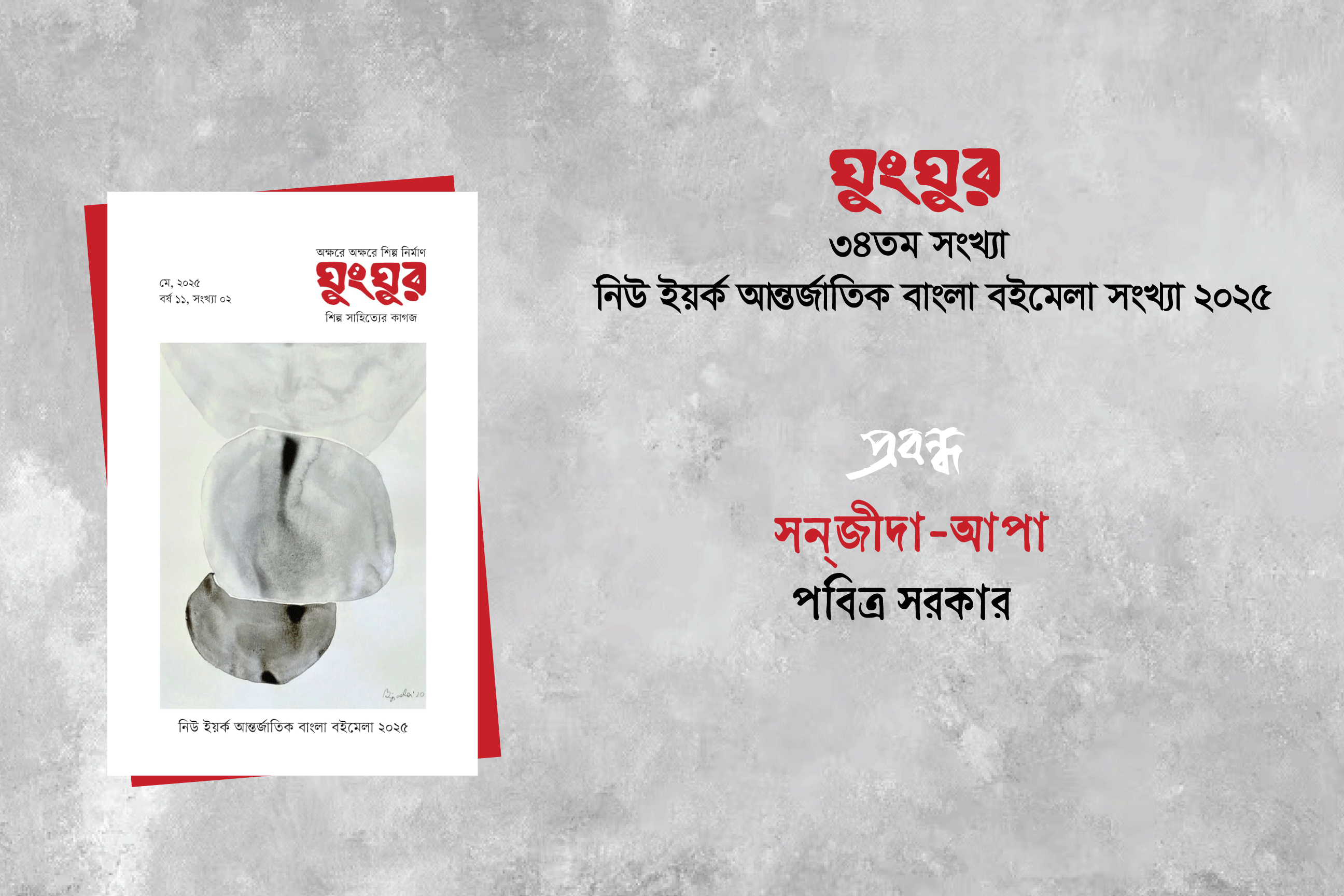সাহিত্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা : সৃজনশীলতার প্রতি চ্যালেঞ্জ
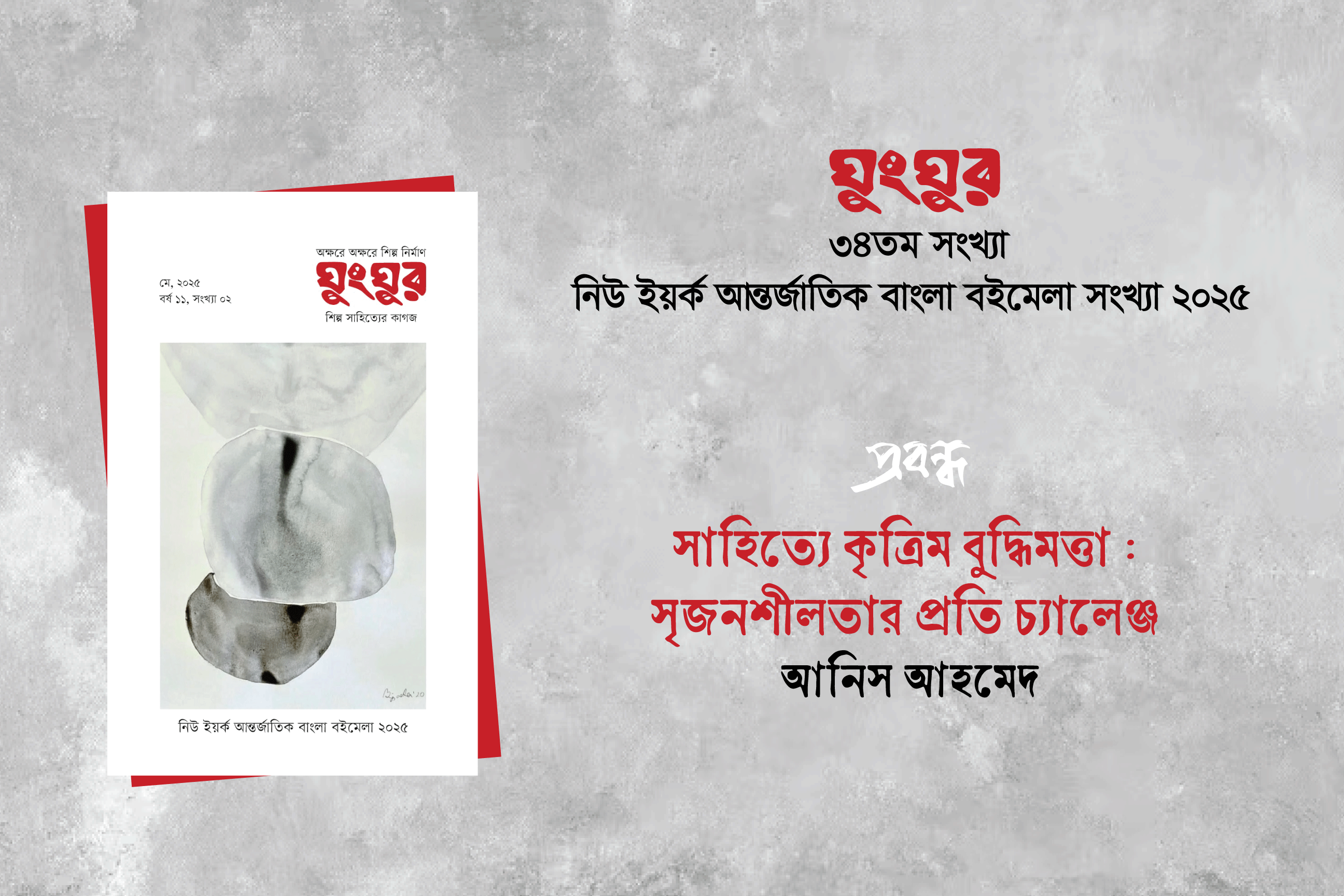
এখন প্রায় সর্বত্রই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) অর্থাত্ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জয়জয়কার শুনি। এখন হয়ে উঠেছে একটি একাডেমিক শিক্ষার ক্ষেত্র, যেখানে পড়ানো হয় কীভাবে কম্পিউটার এবং সফটওয়্যার তৈরি করতে হয় যা বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করবে। কম্পিউটারকে মিমিকস কগনেটিক এককে আনা হয়, যাতে করে কম্পিউটার মানুষের মতো ভাবতে পারে। যেমন, শিক্ষা গ্রহণ এবং সমস্যার সমাধান। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হলো মেশিন দ্বারা প্রদর্শিত বুদ্ধি। এই বুদ্ধিমত্তা সম্ভবত প্রাযৌক্তিক গবেষণাসহ বিভিন্ন রকমের কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলছে। আর এর ফলে মানুষের ওপর নানাবিধ বুদ্ধিবৃত্তিক চাপ অনেকটাই কমে আসছে। মানুষকে কেবল জানতে হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে পরিচালনা করতে হবে; তার করণীয় কাজটি তার ওপর হস্তান্তর করেই মানুষ অনেকটা নিশ্চিত হতে পারে। এটি কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি শাখা, যেখানে মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে কম্পিউটার দ্বারা অনুকরণ করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’ শব্দটি প্রয়োগ করা হয় তখন, যখন একটি মেশিন নির্দিষ্ট নির্দেশ অনুযায়ী নিজেকে কার্যকর করে, যেখানে অন্যান্য মানুষের মনের সঙ্গে মিল থাকে, যেমন, ‘শিক্ষা গ্রহণ’ এবং ‘সমস্যা সমাধান’। এটি একটি সিস্টেমের বহির্ভূত তথ্য সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারার ক্ষমতা, এমন তথ্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং ওই শিক্ষা ব্যবহার করে অভিযোজনের মাধ্যমে বিশেষ লক্ষ্য ঠিক করা।
তবে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কতটা সাফল্য অর্জন করতে পারবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন হয়েই থাকছে কারণ সাহিত্য তো কেবল বুদ্ধির বিষয় নয়, বোধি ও কল্পনার বিষয়ও, মন থেকে উত্সারিত অকৃত্রিম অনুভূতির কথা। মানুষের ভাবনা, তার নিজস্ব দৃষ্টিতে দেখা সত্যগুলো কিংবা তার সৃজনশীল কল্পনায় আঁকা চিত্রগুলোই সাহিত্য হয়ে ওঠে। সাহিত্যের নানাবিধ শাখার যে কাঠামোগত অবয়ব রয়েছে সে কথা যেমন সত্যি, তেমনি সত্যিই হচ্ছে এই কাঠামোর মধ্যের কিছু সৃষ্টিও। সত্য বটে সাহিত্যের অবকাঠামোতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অবদান রাখতে পারে কিংবা সাহিত্যিককে নতুন কোনো কাঠামো নির্দেশ করতে পারে কিন্তু সেই কাঠামোর ভেতরে সাহিত্যের যে একটা হৃদয় থাকে সেখানে কি এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সত্যিই কোন সৃজনশীল ভূমিকা রাখতে পারে!
২
বিশেষত সাহিত্যের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা, কবিতা লেখার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিক কৃত্রিমতা কি আদৌ সৃজনশীল ভূমিকা পালন করতে পারবে? ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের প্রখ্যাত কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডওয়ার্থ ও স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ যখন লিরিকাল ব্যাল্যাডস-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ওপর কাজ করছিলেন তখন ওয়ার্ডওয়ার্থ কাব্যতত্ত্ব বা পোয়েটিক্স-এর ওপর একটি নিবন্ধ লেখেন। সেই নতুন সংস্করণের মুখবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings: it takes its origin from emotion recollected in tranquility. কবি ওয়ার্ডওয়ার্থের এই সংজ্ঞাটি কবিতার ক্ষেত্রে আজও সমানভাবে প্রযোজ্য। কবিতাকে যখন তিনি একটি শক্তিশালী অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত অতি-প্লাবন বা বহিঃপ্রকাশ বলে অভিহিত করেন, তখন সেই অনুভূতি ও স্বতঃস্ফূর্ততা কোনটাই খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে। প্রথমত কৃত্রিম কোনো প্রক্রিয়াই স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে না এবং বুদ্ধিমত্তা ও অনুভবের মধ্যে কোনো রকম সমীকরণ সাধনও সম্ভব নয়। আর কেবল কবিতা কেন সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও, বিশেষত গল্প বা উপন্যাস যেখানে বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার সংযুক্তিতেই সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় সেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পাঠকদের কোনো নান্দনিক আনন্দ দিতে পারবে কি না সে নিয়ে প্রশ্ন আছে।
সে জন্য সম্ভবত এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ঢালাও প্রয়োগ নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাহিত্যের ক্ষেত্রে, বিশেষত গল্প উপন্যাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে সীমিত ভাবে বিষয় নির্বাচনে কিংবা কিছু ধারণা প্রদানে সহায়ক হতে পারে কিন্তু সেই বিষয় ও ধারণার সৃজনশীল প্রয়োগের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কোনো ভূমিকাই থাকতে পারে না কারণ সে ভূমিকা সৃজনশীল হবে না। সাহিত্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের আরেকটি বড় ঝুঁকি হচ্ছে এই যান্ত্রিক প্রক্রিয়া দু’জন ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিককে একই বিষয় এবং একই ধরণের ধারণা দিতে পারে যেখানে সাহিত্যিকের ব্যক্তিক বৈশিষ্ট সম্পূর্ণ নষ্ট হতে পারে। সাহিত্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের সবচাইতে নেতিবাচক দিক হচ্ছে যান্ত্রিক প্রয়োগে মানবিক শুদ্ধতা হারিয়ে ফেলা। আমরা সকলেই জানি যে—লেখা, এবং বিশেষত সাহিত্যের লেখা হচ্ছে একটি শিল্প যা মানবিকতা ও মৌলিকতার পরিমাপে মূল্যায়ন করা হয়, এআই সেই মৌলিক ও মানবিক মূল্যবোধকে পরিপূর্ণ ভাবে তুলে ধরতে পারে না। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বড়জোর কিছু পরামর্শ ও ধারণা দিতে পারে কিন্তু একজন লেখকের যে স্বতঃস্ফূর্ত মানবিক চেতনা কাজ করে তাতো এই যন্ত্র উপলব্ধ প্রয়োগের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যথার্থ ভাবে সাহিত্যের লেখার মধ্যে থাকে আবেগ, ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং পাঠকের সঙ্গে সম্পৃক্ততা, যার কোনটাই এই যান্ত্রিক উপায়ে সম্ভব না।
৩
তৈরি সাহিত্যের মধ্যে থাকতে পারে না। আর পাঠকের সঙ্গে সম্পৃক্ততার বিষয়টি সাহিত্যের আদি সংজ্ঞার সঙ্গেই সংযুক্ত যেখানে সাহিত্যের মানেই হচ্ছে ‘সহিতের ভাব’। লেখকের সঙ্গে পাঠকের এই ‘সহিতের ভাব’ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার তৈরি সাহিত্যের মধ্যে থাকে না বলে সংজ্ঞা অনুযায়ী তা কি সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে, এ জিজ্ঞাসাও জরুরি।
এখনকার যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ বড়জোর একটা উপায় হতে পারে কিন্তু কোনো ক্রমেই একজন লেখকের মানবিক দক্ষতা ও সৃজনশীল কল্পনার বিকল্প হতে পারে না। একজন সৃজনশীল লেখক যদি এআইয়ের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েন তা হলে তিনি যেভাবে লিখতে চান কিংবা সম্পাদনা করতে চান সেই দক্ষতাও হারাবেন। প্রযুক্তির ওপর অতি নির্ভরশীলতা আসলে লেখকের নিজের সমৃদ্ধিকে সংকুচিত করে আনে। লেখার ক্ষেত্রে যান্ত্রিক উপায় ব্যবহার করার আরেকটি অসুবিধা হলো এআই প্রায়শই অনুবাদ নির্ভর আর সেই অনুবাদ হয় যান্ত্রিক ও আক্ষরিক। আমরা ইতোমধ্যেই গুগল অনুবাদের কিছু দৃষ্টান্ত দেখছি যেখানে ভাষার প্রায়োগিক অর্থ আক্ষরিক অনুবাদের কাছে পরাস্ত হয়। তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু কোনো ক্রমেই সাহিত্যিকের স্বতঃস্ফূর্ততার বিকল্প হিসেবে নয়। সাহিত্যিকের নিজস্ব চিন্তা চেতনা কিংবা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে সত্য উপলব্ধ হয়, সেটিকেই একজন সাহিত্যিক তাঁর সৃজনশীল শিল্প দিয়ে গড়ে তোলেন। এখানে কৃত্রিমতা কিংবা বুদ্ধি প্রয়োগের অবকাশ নেই আর যেটুকু বুদ্ধি সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিক ব্যবহার করেন তা হয় তাঁর সৃজনশীলতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব যাঁরা সাহিত্যের মতো সৃজনশীল শিল্পের নান্দনিক প্রকাশ চান তাদের সকল প্রকার কৃত্রিম ও যান্ত্রিক বুদ্ধি প্রয়োগের চলমান প্রবণতা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে, নইলে সৃজনশীলতা কৃত্রিমতায় কাছে পরাস্ত হবে, সাহিত্য হারাবে তার সংজ্ঞায়িত সত্তা।
আনিস আহমেদ কবি ও প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দশ। পেশায় বেতার সাংবাদিক। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন।