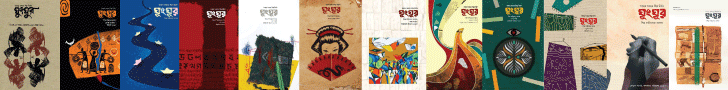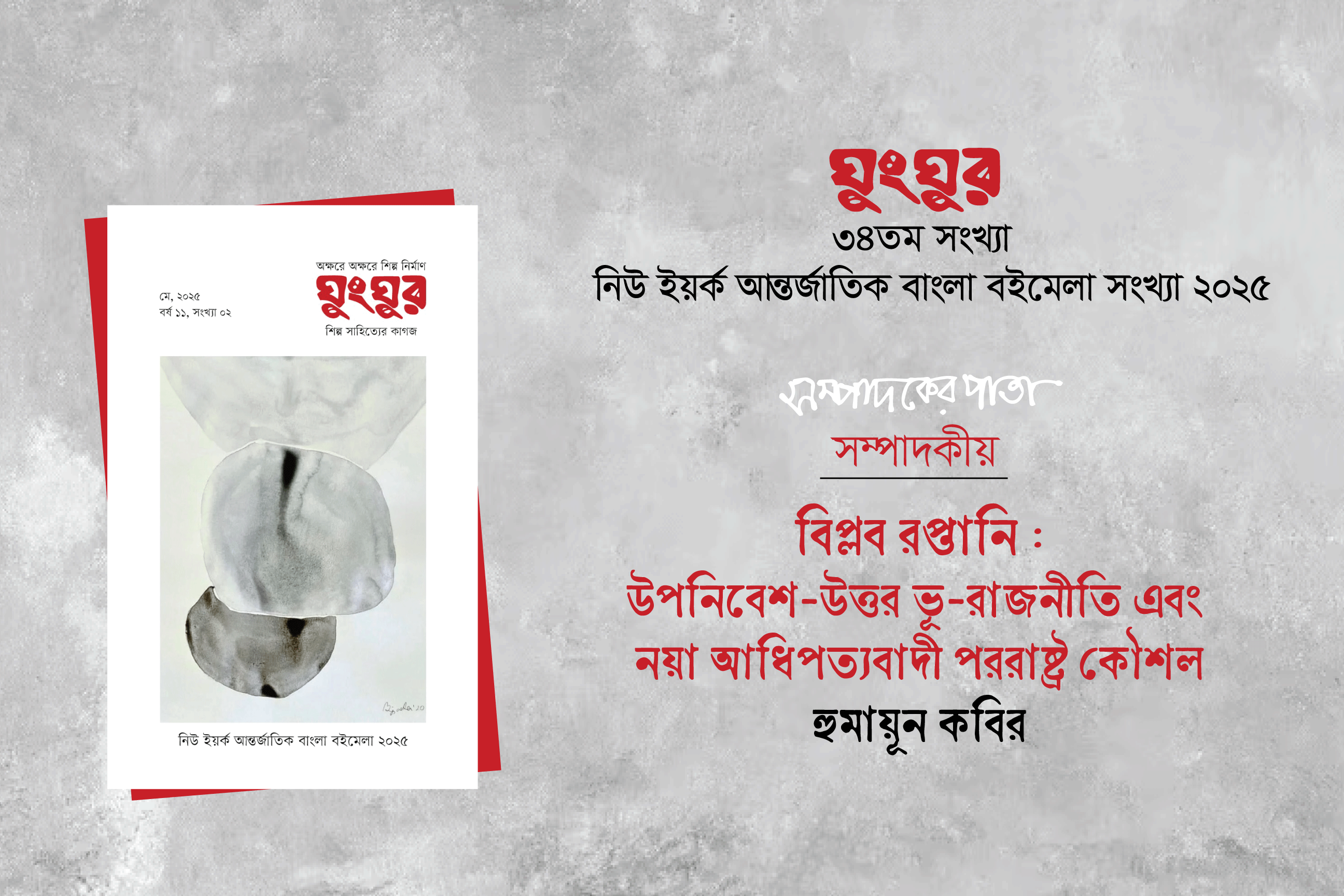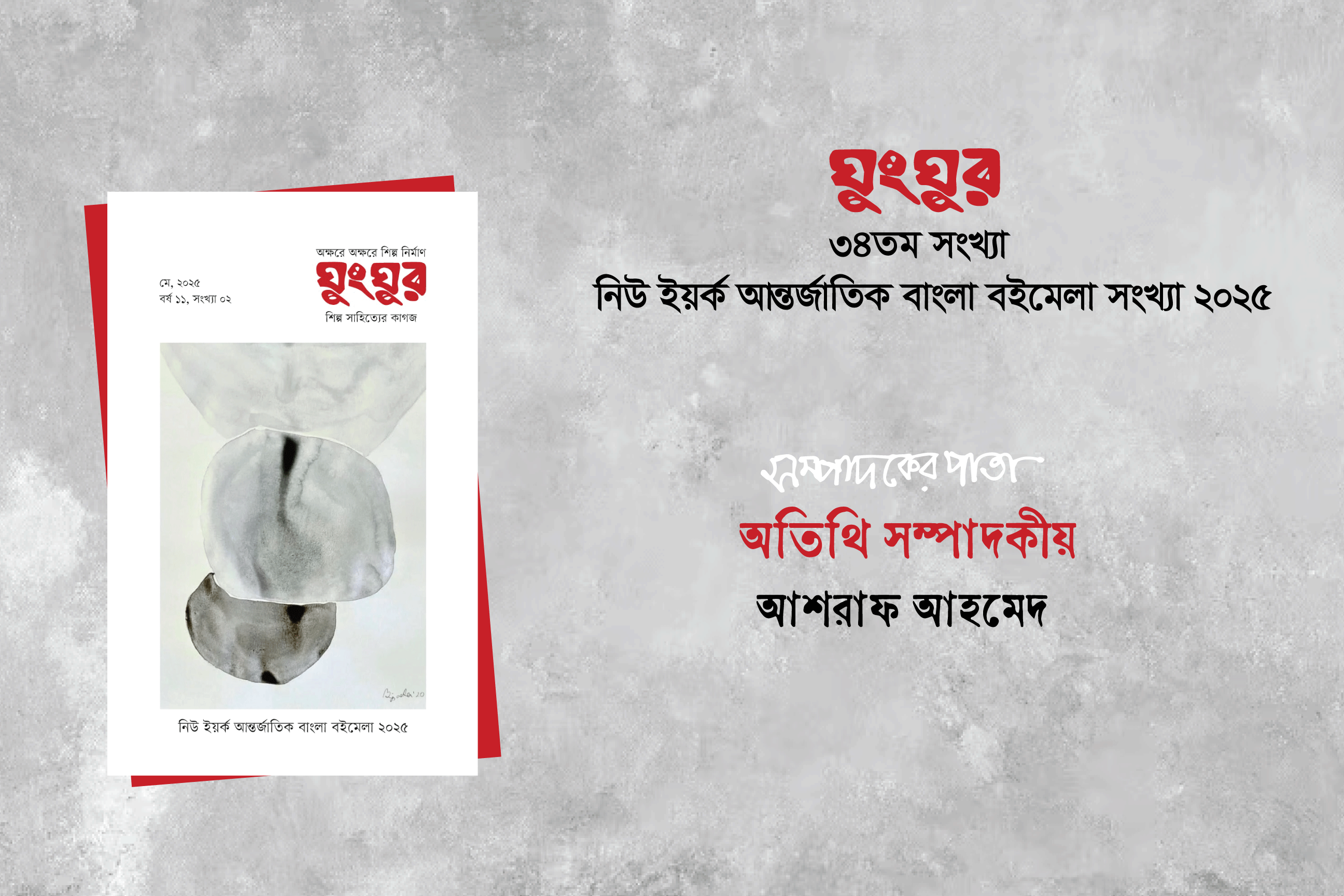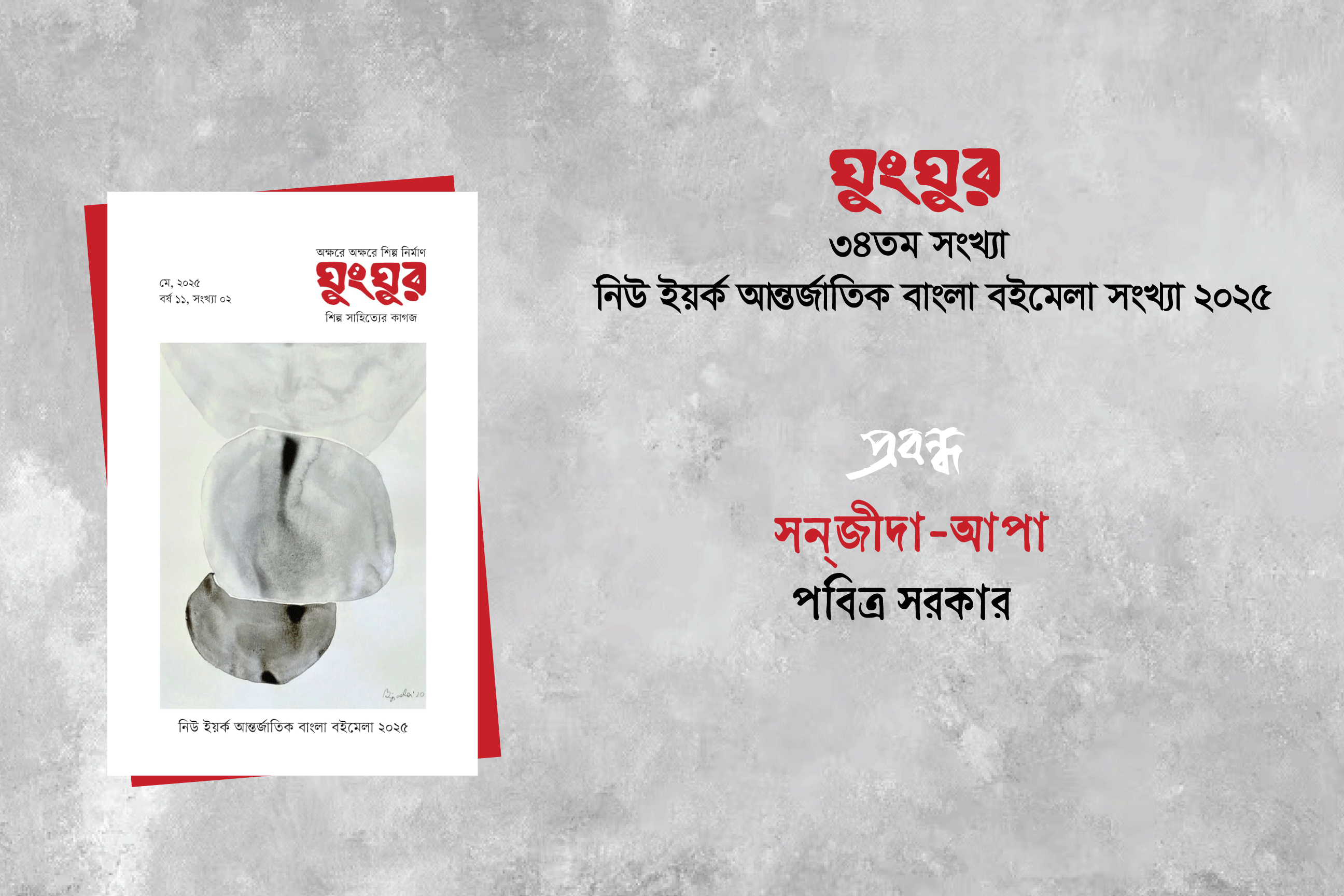রমাপদ চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের এক চিরসবুজ প্রতিভা
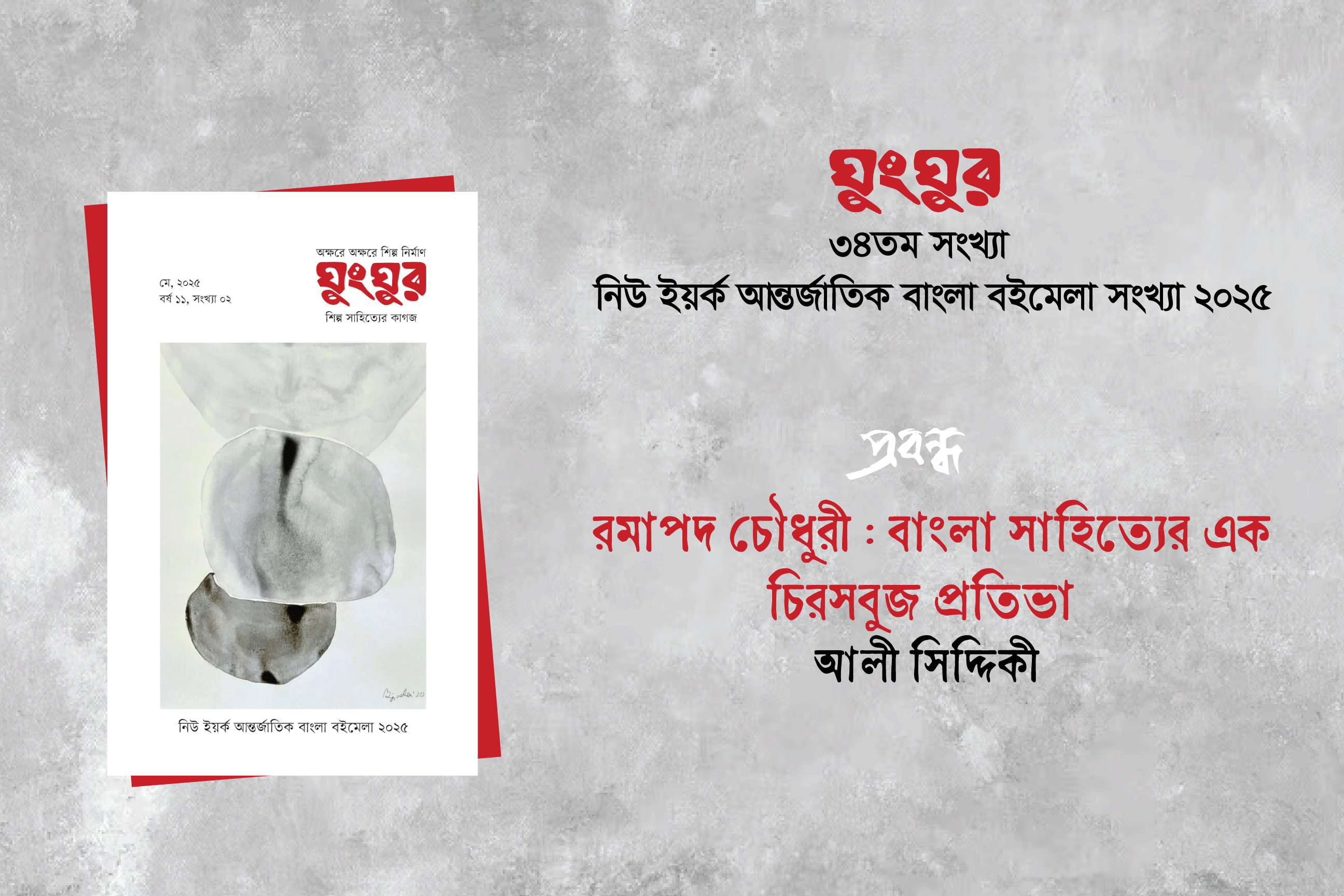
রমাপদ চৌধুরী (১৯২২-২০১৮) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রতিভাবান কথাসাহিত্যিক। তার সাহিত্যকর্মে স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতীয় সমাজ, মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংগ্রাম এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের জটিলতা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠেছে। সহজ-সরল ভাষায় জীবনের গভীর সত্য এবং বাস্তবতার প্রতিফলন তাঁর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এই প্রবন্ধে আমরা রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলোর মূল চরিত্র, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, এবং তাদের দর্শন নিয়ে গভীরতর আলোচনা করব।
বন্ধুদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে মাত্র ২৫ বছর বয়সে রমাপদ চৌধুরী প্রথম ছোটগল্প রচনা করেন। তার জীবনের প্রথম গল্প ‘উদয়াস্ত’ প্রকাশিত হয়েছিল যুগান্তর পত্রিকায়। এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এমএ পাস করে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দেন। কর্মজীবনে কালক্রমে তিনি ওই পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করেন এবং পত্রিকার রবিবার-র ক্রোড়পত্র ‘রবিবাসরীয়’ বিভাগের সম্পাদক হন। পাশাপাশি চলতে থাকে তাঁর নিজস্ব সাহিত্য চর্চা। ১৯৫৪ সালে প্রথম উপন্যাস প্রথম প্রহর প্রকাশ পায়। ষাটের দশকে দেশ পত্রিকায় তাঁর উপন্যাস বনপলাশীর পদাবলী পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়, যার ফলে তিনি পাঠক সমাজে পরিচিত মুখ হয়ে পড়েন। তিনি ১৯৬৩ সালে আনন্দ পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭১ সালে এখনই উপন্যাসের জন্য রমাপদ চৌধুরীকে রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বাড়ি বদলে যায় উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৮৮ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। দীর্ঘ সাহিত্য জীবনে তিনি পঞ্চাশটির ওপরে উপন্যাস রচনা করেন। এছাড়া দেশ পত্রিকার গল্প সংকলনও দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনা করেন। ২০১১ সালে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মারক আন্তর্জাতিক পুরস্কার চালু করলে প্রথম বছর বনপলাশী পদাবলী উপন্যাসের জন্য রমাপদ চৌধুরীকে ওই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।
তার রচনাবলীগুলো হলো : ১৯৫৫ প্রথম প্রহর (উপন্যাস সংগ্রহ-২), লালবাঈ (উ.স.-৫) ১৯৫৬, অন্বেষণ (দশটি উপন্যাস) ১৯৫৬, দ্বীপের নাম টিয়ারঙ (উ.স.-২) ১৯৫৭, অরণ্য আদিম (দশটি উপন্যাস) ১৯৫৮, এই পৃথিবীর পান্থনিবাস (উ.স.-৫) ১৯৬০, আলো আঁধার (দশটি উপন্যাস) ১৯৬০, বনপলাশীর পদাবলী (উ.স.-৪) ১৯৬২, আরো একজন (উ.স.-৩) ১৯৬২, পরাজিত সম্রাট (উ.স.-১) ১৯৬৬, এখনই (উ.স.-৩) ১৯৬৯, পিকনিক (উ.স.-২) ১৯৭০, যে যেখানে দাঁড়িয়ে (উ.স.-১) ১৯৭২, অ্যালবামে কয়েকটি ছবি (উ.স.-২) ১৯৭৩, খারিজ (উ.স.-১) ১৯৭৪, লজ্জা (উ.স.-১) ১৯৭৬, হৃদয় (উ.স.-১) ১৯৭৬, দ্বিতীয়া (দশটি উপন্যাস) ১৯৭৭, বীজ (উ.স.-১) ১৯৭৮, রূপ (উ.স.-৩) ১৯৮০, চড়াই (উ.স.-৩) [তিনটি উপন্যাস,দেজ] ১৯৮০, স্বজন (উ.স.-২) [তিনটি উপন্যাস,দেজ] ১৯৮১, অভিমন্যু (উ.স.-৩) ১৯৮২, বাহিরি (উ.স.-৪) ১৯৮৩, শেষ সীমানা (উ.স.-৩) ১৯৮৪, ছাদ (উ.স.-৪) ১৯৮৫, শেষের সীমানা (উ.স.-৩) ১৯৮৬,বাড়ি বদলে যায় (উ.স.-৬) ১৯৮৭, আকাশপ্রদীপ (উ.স.-৫) ১৯৮৭, দাগ (উ.স.-৪) ১৯৮৮, আশ্রয় (উ.স.-৪) ১৯৮৯, অহংকার (উ.স.-৬) ১৯৯০, স্বার্থ (উ.স.-৬) ১৯৯১, রাজস্ব (উ.স.-৫) ১৯৯২, ডুব সাঁতার (উ.স.-৫) ১৯৯৩, সাদা দেয়াল (উ.স.-৬) ১৯৯৪, পাওয়া (উ.স.-৬) ১৯৯৫, জৈব (উ.স.-৬) ১৯৯৫, অংশ (দশটি উপন্যাস) ১৯৯৭, তিনকাল (দশটি উপন্যাস) ১৯৯৮, আজীবন (দশটি উপন্যাস) ১৯৯৯, বেঁচে থাকা (দশটি উপন্যাস) ২০০০, একা একজীবন (দশটি উপন্যাস) ২০০০, মানুষের সংসার ২০০৩, সুখদুঃখ (সুখদুঃখ, ভবিষ্যৎ-এই উপন্যাস দুটি আছে) ২০০৪, পশ্চাৎপট (শেষ উপন্যাস) ২০০৫।
একজন সফল ঔপন্যাসিক হিসেবে রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসসসমূহ পর্যালোচনা করলে আমরা আবিষ্কার করি যে, উপন্যাসের আখ্যান নির্মাণে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি প্রচলিত উপন্যাস রীতির প্লট বা বৃত্তের অনুকরণ করে উপন্যাস রচনা করেছেন। তিনি মূলত সরল ও যৌগিক প্লট ব্যবহার করে তাঁর খারিজ, আরো একজন, লজ্জা, বীজ, পরাজিত সম্রাট, যে যেখানে দাঁড়িয়ে, ও হৃদয় উপন্যাস লিখেছেন। তিনি সরল প্লট ব্যবহার করে গুরু গম্ভীর উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন। উপন্যাসের বৈষয়িক সমৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে উন্নত শিল্পের কাতারে পৌঁছাতে পেরেছেন। তিনি পরম্পরাগত প্রবহমান বর্ণনারীতি পরিহার করে তাঁর উপন্যাসে একধরণের নতুনত্ব এনেছেন।
পাশাপাশি যৌগিক বৃত্তের ব্যবহার করেও তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর আকাশপ্রদীপ ও শেষের সীমানা উপন্যাসদ্বয় যৌগিক বৃত্তের প্লটের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রচলিত রীতিকে ছাপিয়ে আখ্যানভাগের মধ্যে দুটি স্তরকে আমরা বিদ্যমান থাকতে দেখি। তিনি সেটা বাড়ি বদলে যায় প্রসঙ্গকথায় এভাবে বিধৃত করেছেন—
‘এই চেনাজানা সমাজেরই কিছু চরিত্রকে কেন্দ্র করে যে-কাহিনি গড়ে ওঠে, তার মধ্যে কোথাও কোন ঘটনার ঘনঘটা থাকে না। যা ঘটে তাও আমাদের অচেনা নয়। এই সব চরিত্র কখনও নাটকীয় চরিত্র হয়ে ওঠে না, উচ্চরব আমার অপছন্দ, তাই কাহিনীর ক্ষেত্রেও কোন নাটকীয়তা থাকে না। একটি শান্তশিষ্ট গল্পের মধ্যেই আমার যা কিছু শিল্পকর্ম, যদি তা আদৌ থাকে, তা প্রায় অনুচ্চারিত ভাবে নিহিত থাকে। গল্প বলার সময় আমি শুধু গল্প বলারই চেষ্টা করি। তেমন কোনো জমজমাট গল্প তার মধ্যে না থাকা সত্ত্বেও আবিষ্কার করে অবাক হয়েছি যে, এইসব উপন্যাসের পাঠকও আছেন, এবং সংখ্যায় তারা নিতান্তই কম নয়… আমার গল্পের বা উপন্যাসের মধ্যে আরেকটি স্তর থাকে। সচেতন পাঠকের তা দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। তারা বুঝতে পারেন গল্পের বাইরেও কিছু বলার আছে, অন্য স্তরের কোন কথ।’
তাঁর বাড়ি বদলে যায়, লজ্জা ও বীজ উপন্যাসে দ্বিতীয় স্তরের ব্যবহার আমরা দেখি। বাড়ি বদলে যায় উপন্যাসে বাড়ি বদলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা মধ্যবিত্ত মানুষদের চরিত্র আমরা বদলে যেতে দেখি। তেমনি লজ্জা উপন্যাসে একটি চরিত্রের ভারসাম্য হারানোর কাহিনিকে চিত্রিত করতে গিয়ে পুরো মধ্যবিত্ত সমাজের অপ্রকৃতিস্থতাকে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা বীজ উপন্যাসের মূল স্তরে একজন মানুষের আকস্মিক নিরুদ্দেশ হবার কাহিনিকে রেখে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের মূল্যবোধ হারানো এবং বিবেক দংশনকে দ্বিতীয় স্তর হিসেবে ব্যবহার করে জাল টানার মতো করে ঘটনাকে তিনি টেনে তুলেছেন।
ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী ছিলেন আপাদমস্তক মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের রূপকার। তিনি একমাত্র বনপলাশির পদাবলী উপন্যাসটি রচনা করেছেন গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে। মধ্যবিত্তের নাগরিক জীবনের তিনি সফল কথাকার। তিনি বাঙালি সমাজের পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগী হলেও সমকালীন বাঙালি সমাজের জীবনদর্শনকেই মূলত রূপায়ণ করেছেন তাঁর উপন্যাসে। পরাজিত সম্রাট, চড়াই, অহঙ্কার, এখনই, অভিমন্যু, পিকনিক প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি সমকালীন মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনালেখ্য বিধৃত করেছেন। রমাপদ চৌধুরী উপন্যাস রচনায় মূলত ছোট ‘ক্যানভাস’ ব্যবহার করতেন। মধ্যবিত্ত সমাজের ভিন্ন ভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে তিনি এক একটি উপন্যাস রচনা করেছেন। তিনি স্বার্থ উপন্যাসে এঁকেছেন বিধবার আত্মমর্যাদাবোধ—স্বাতন্ত্র, আরো একজন উপন্যাসে নারী-পুরুষের পরকীয়া সম্পর্ক, অভিমন্যু উপন্যাসে এঁকেছেন বাঙালির বিবেকবোধের তাড়না, শেষের সীমানা মানুষের অসহায়ত্বের প্রতিবিম্ব, আর লজ্জা উপন্যাসে উঠে এসেছে মধ্যবিত্ত সমাজের লজ্জাবোধ।
রমাপদ চৌধুরী সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীকাল স্বাধীনতাত্তোর ভারতের মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন ধারা এবং পরিবর্তনশীল উপাদানসমূহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। মানুষের পরিবর্তিত জীবনের স্বরূপকে তিনি তার উপন্যাসে শিল্পের আধার হিসেবে আলোকিত করেছেন। তিনি প্রাচুর্যহীন ও ঘটনাবিরল উপন্যাসের প্রতি ছিলেন একনিষ্ঠ। ছোট্ট ক্যানভাসে ডিটেইলে যাবার পরিসর থাকে না তাই তাঁর উপন্যাসে খুঁটিনাটি পাওয়া যাওয়া না। বনপলাশীর পদাবলীর কাহিনি অর্ধ-শতাব্দীকাল বিস্তৃত হলেও ঘটনাকাল শুধু বছরখানেকের মতো। ঘটনার বিস্তার ঘটানোর চেয়ে গুটিয়ে ফেলাতেই যেন তার আনন্দ। দু’একটি উপন্যাস ছাড়া (দ্বিতীয়া, আজীবন) রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস সমূহে ঘটনাপ্রবাহ ও চরিত্রসমূহকে নাটকীয় হয়ে উঠতে দেখা যায় না। তার শিল্পকর্ম পরিকল্পিত ও নির্মোহ।
স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি আর্থ-সামাজিক চাপের মুখে পড়ে। এই পটভূমি রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর উপন্যাসে নগরায়নের প্রভাব, জীবনের অনিশ্চয়তা এবং সম্পর্কের সংকট বারবার উঠে এসেছে।
উদাহরণস্বরূপ, বাড়ি বদলে যায় (১৯৬৬) উপন্যাসে একটি পরিবারের বাসস্থান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সময়ের এবং মানুষের মানসিক পরিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসটি কেবল ভৌত স্থানান্তরের কাহিনি নয়, এটি সমাজ ও সম্পর্কের পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি।বাড়ি বদলে যায় রমাপদ চৌধুরীর অন্যতম আলোচিত উপন্যাস। উপন্যাসটি একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের ওপর ভিত্তি করে, যারা নতুন বাসায় চলে যাওয়ার পর মানসিক এবং পারিবারিক সংকটে পড়ে। পরিবারের কর্তা এবং গৃহিণী তাদের মতাদর্শগত অবস্থান ধরে রাখতে চাইলেও, সময়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এবং মূল্যবোধ বদলাতে শুরু করে। এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের মানসিক অবস্থার বিবর্তন মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্বন্দ্ব এবং জীবনের অনিশ্চয়তা চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছে।
খারিজ রমাপদ চৌধুরীর আরেকটি মাইলফলক সৃষ্টি। এটি তাঁর মিশ্র তরঙ্গ রীতিতে লেখা উপন্যাস। গৃহপরিচারক শিশুর মৃত্যু একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হরেন এবং তার স্ত্রীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই কাহিনি মধ্যবিত্ত সমাজের দায়বদ্ধতার অভাব এবং আত্মকেন্দ্রিকতার এক তীব্র সমালোচনা। হরেনের চরিত্রটি সমাজের নৈতিক অবক্ষয় এবং আত্মমুখীনতার প্রতীক।
একটি রাত নাগরিক জীবনের নিঃসঙ্গতা এবং জীবনের অর্থহীনতা তুলে ধরে। এক রাতের ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে লেখক চরিত্রগুলোর মানসিক টানাপোড়েন এবং দোলাচলকে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসটি অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের অসারতা এবং একাকীত্বের প্রতীক।
রাজনৈতিক পটভূমিতে রচিতবনপলাশীর পদাবলি উপন্যাসে ব্যক্তি, সমাজ এবং আদর্শের দ্বন্দ্ব উঠে এসেছে। এখানে ব্যক্তির নৈতিক দ্বিধা এবং সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সংঘর্ষে পড়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতলনাচের ইতিকথা কিংবা শহরবাসের ইতিকথার সঙ্গে এই উপন্যাসে কিছু ভাবগত সাদৃশ্য দেখা যায়। ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত বনপলাশীর পদাবলীর আদর্শবান গিরিজাপ্রসাদ শহুরে জীবন কাটিয়ে স্বল্প সঞ্চয়ে শহরে বসবাস অসম্ভব হওয়ায় অবসরের পর ফিরে গিয়েছিলেন বনপলাশি গ্রামে। কিন্তু শহুরে জীবনে অভ্যস্ত গিরিজাপ্রসাদ গ্রামজীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয় এবং হতাশ হয়ে গ্রাম ত্যাগ করতে হয়েছে। অন্যদিকে পুতুলনাচের ইতিকথার শশী গ্রামে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। গ্রাম ও শহুরে জীবনের বৈপরীত্য মানিকের পর পুনরায় রূপায়িত করেন রমাপদ চৌধুরী। মানিকের উপন্যাসের পটভূমি কলকাতা হলেও শহুরে মধ্যবিত্তের জীবন তাঁর লেখায় অনুপস্থিত। এখানে রমাপদ মানিক থেকে পৃথক।
আবার প্রকরণগত দিক থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাথেও রমাপদ’র বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি প্রধানত শোষিত, নিপীড়িত, নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের চালচিত্রকে উপজীব্য করে উপন্যাস লিখেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ক্রমবর্ধমান কলকাতার সমাজ বাস্তবতাকে চিত্রিত করেছেন এবং এক্ষেত্রে তিনি আধুনিক। তবে তাঁর লেখায় শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন তেমন রেখাপাত করেনি। তাঁর পাঁক বস্তি জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস, মিছিল উপন্যাসটি সমকালীন নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিচ্ছবি, যেখানে অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত মেসবাসী হতদরিদ্র দুই যুবকের লড়াইকে কেন্দ্র করে লেখা। তিনি ঘটনার পর ঘটনা গেঁথে গেঁথে লিখেছেন তাঁর উপন্যাস। অন্যদিকে রমাপদ চৌধুরী স্বাধীনতোত্তর নাগরিক মধ্যবিত্তদের জীবনধারাকে তার উপন্যাসে উপজীব্য করেছেন এবং প্রকরণগত দিক থেকে ঘটনার পর ঘটনা সাজানোর প্রক্রিয়াকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। এক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে তাঁর বিস্তর ব্যবধান। প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপনায়ন উপন্যাসটির সঙ্গে রমাপদ’র প্রথম প্রহর উপন্যাসটির চরিত্রগত সাদৃশ্য হলো দুই উপন্যাসের নায়কের ‘হয়ে ওঠা।’ কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র তার নায়কের ‘হয়ে ওঠা’র জন্য যতটুকু বিস্তার দেয়া প্রয়োজন ছিল তিনি দিলেন না। প্রথম প্রহর-এর নায়ককে সেটা দিয়ে রমাপদ অধিক সার্থকতা পেলেন।
রমাপদ লিখছেন, ‘লিখতে শুরু করেছি যখন, তখন আমাদের সামনে দুটি পথ—তারাশঙ্কর আর সুবোধ ঘোষ… সুবোধ ঘোষ আমাকে শুধু ভাষার আমন্ত্রণেই মুগ্ধ করেননি, আঞ্চলিক অভিজ্ঞতার মিলটাও বোধ হয় অন্যতম কারণ। কিংবা অভিজ্ঞতাই নয়, ওই বিচিত্র জগৎ আর বিচিত্র মানুষগুলোর প্রতি অবোধ্য এক আকর্ষণ ছিলো আমার মনে।’ (লেখালেখি)। সুবোধ ঘোষ ছিলেন তারাশঙ্কর ও রমাপদ’র আদর্শ। সুবোধ ঘোষের উপন্যাসে পরিবর্তিত কলকাতার মধ্যবিত্তদের জীবনচিত্র চিত্রিত হতো বিপুলভাবে। মানুষের খলচরিত্র, স্বার্থপরতা ও ভণ্ডামি সুবোধ ঘোষের লেখায় তীক্ষ্ণভাবে ফুটে উঠতো। তাই রমাপদ স্বল্প সময়েই সুবোধ ঘোষের গল্প রচনার কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। বত্রিশটি উপন্যাস লিখলেও তিন শতাধিক গল্প লিখে সুবোধ ঘোষ গল্পকার হিসেবেই জনপ্রিয় ও খ্যাতিমান হয়েছেন। তার গোত্রান্তর, অযান্ত্রিক, ফসিল প্রভৃতি গল্প সমকালীন পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে। তার সুজাতা উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের যে জীবনদর্শন তা রমাপদ চৌধুরীর অহঙ্কার উপন্যাসেও দেখা যায় যেখানে মধ্যবিত্ত সমাজ অর্থলোভের কারণে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়েছে। তবে রমাপদ চৌধুরীর বিশেষত্ব হলো জীবনে টাকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য হলেও এটা প্রমাণ করেছেন যে, টাকা জীবনের সব সমস্যার সমাধান করতে পারে না। প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত টাকা থাকা সত্ত্বেও একা একজীবন-এর চারুর জীবনের সমস্যা কিংবা সুখ দুঃখ উপন্যাসের আনন্দগোপালের দুঃখের অবসান হয়নি। একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন পুঁজিবাদী সমাজে প্রত্যক্ষ উপসর্গ। রমাপদ চৌধুরী এই ভাঙন পরবর্তী প্রতিক্রিয়াকেই তাঁর উপন্যাসে উপজীব্য করে তুলেছেন। এক্ষেত্রে সুবোধ ঘোষের জীবনাদর্শ অনুসরণ করেও রমাপদ স্বতন্ত্র। সুবোধ ঘোষের তিলাঞ্জলির (১৯৪৪) রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ তিনি গ্রহণ করেননি। তাছাড়া সুবোধ ঘোষ তার ত্রিযামা (১৯৫১), সুজাতা (১৯৫৩), ও শিউলিবাড়ি (১৯৬০) প্রভৃতিতে কলকাতা বাইরের হাজারীবাগ মাল্ভূমি এবং তৎসংলগ্ন সমতলভূমির গরিব মানুষদের উপন্যাসের উপজীব্য করেছেন কিন্তু রমাপদ তাঁর ছোটগল্পে নানা অঞ্চলের মানুষদের জীবনালেখ্য তুলে আনলেও উপন্যাসে তিনি কলকাতার মধ্যবিত্ত নাগরিকদের জীবনকেই রূপায়িত করেছেন।
আমরা আরও দেখি যে, স্বাধীনতোত্তর ভারতের বাংলা সাহিত্যে অন্যতম ঔপন্যাসিক হিসেবে উঠে আসে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নামও। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সময়ে বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজে প্রভূত পরিবর্তন ঘটে যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাসে স্থান করে নেয় সময়ের জারিত বাস্তব জীবনানুভূতির চালচিত্র। একইভাবে রমাপদ চৌধুরীও জীবনাভিজ্ঞতাকে তাঁর উপন্যাসে শিল্প হিসেবে তুলে ধরেছেন। তারা দু’জনই বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, সংঘাত, সংশয়, অবক্ষয়, লড়াই এবং আপোসকামিতার চিত্র অঙ্কন করেছেন শিল্পিত ভাবে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী’র সূর্যমুখী (১৯৫১) উপন্যাসে যেমন মধ্যবিত্ত সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আপোসকামিতাকে চিত্রিত করা হয়েছে ঠিক তেমনি রমাপদ চৌধুরী কলকাতার নাগরিক মাধ্যবিত্ত সমাজের চেতনাগত নিঃস্বতার চালচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর পরাজিত সম্রাট উপন্যাসে। মধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের সাদৃশ্য দৃশ্যমান যেমন তেমনি বৈসাদৃশ্যও আমরা দেখতে পাই। তাদের দু’জনের আবেদন এক নয়। জ্যোতরিন্দ্র নন্দীর সূর্যমুখী ও বারো ঘর এক উঠোন-এর মধ্যবিত্তদের প্রবণতা হলো কোনো-না-কোনোভাবে টিকে থাকা। অন্যদিকে রমাপদ চৌধুরী তাঁর চড়াই, বাহিরি কিংবা অভিমন্যু উপন্যাসে নবীন প্রজন্মের সফলতার লড়াইকে চিত্রিত করেছেন। আবার দেখি, জ্যোতিরিন্দ্রের চরিত্রগুলো তাদের অবদমিত যৌনকামনার ব্যাপারে যথেষ্ট খোলামেলা কিন্তু রমাপদ’র চরিত্রগুলো যৌনকামনা প্রকাশ করলেও তাকে বিকারের পর্যায়ে নিয়ে যায় না। রমাপদ যৌনতাকে জীবনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবেই তুলে ধরেছেন। এ ব্যাপারে আমরা তাঁর বক্তব্য পাই তার অ্যালবামে কয়েকটি ছবি উপন্যাসে শরীর ও মন-এর ব্যাখ্যায়। তিনি বলেছেন, ‘পাশাপাশি দুখানা ঘর। দ্যাখো, দ্যাখো, ঠিক আমাদের জীবনের মতোই, প্রেম ভালোবাসার মতোই। একটার নাম দাও শরীর, আরেকটা তোমার মন। মাঝখানে একটা দরোজা আছে, আছেই। তুমি যতোই খিল দিয়ে সেটা আটকে রাখো, তোমার চোখ বারবার সেদিকে যাবেই। আনাগোনার জন্যই তো এই মাঝের দরোজাটা। তুমি কোন ঘরে আছো, তাতে কিছু যায় আসে না, তোমাকে ওই দরোজাটার অন্য ঘরে পৌঁছে দিতে চাইছে।’ (অ্যালবামে কয়েকটি ছবি)। এতে প্রতীয়মান হয় যে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবং রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসে দুটি ভিন্ন আবেদন রচিত হয়েছে।
রমাপদ চৌধুরীর চরিত্রগুলো সাধারণত মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। তারা জীবনের বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে নৈতিকতার সঙ্গে আপস করতে বাধ্য হয়।খারিজ -র হরেন মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট এবং সামাজিক দায়িত্ব এড়ানোর প্রতিচ্ছবি। আরবাড়ী বদলে যায়-এর চরিত্ররা সমাজের পরিবর্তন এবং তাদের মানসিক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন।
রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্য আলবেয়ার কাম্যুর অস্তিত্ববাদ এবং আন্তন চেখভের বাস্তববাদের সঙ্গে তুলনীয়। কাম্যুর The Stranger এবং চৌধুরীর একটি রাত উভয়ই নিঃসঙ্গতা এবং জীবনের অর্থহীনতা অনুসন্ধান করে। উভয় ক্ষেত্রেই চরিত্রগুলো নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়। চেখভের ছোটগল্প এবং চৌধুরীর উপন্যাসে সাধারণ মানুষের জীবনের ক্ষুদ্র ঘটনাগুলো থেকে গভীর মানবিক সত্য উদ্ঘাটিত হয়। চেখভের The Lady with the Dog এবং চৌধুরীর খারিজ এর মধ্যে সাধারণ মানুষের জীবনের দুঃখ-কষ্ট এবং সামাজিক দায়িত্বের অভাবের দিক থেকে সাযুজ্য পাওয়া যায়।
রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্যে রাজনীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। বনপলাশীর পদাবলি-তে স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের রাজনৈতিক সংকট এবং ব্যক্তির সামাজিক দায়বদ্ধতা মূর্ত হয়েছে।
রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্য নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্যে মধ্যবিত্ত সমাজ তার কাজের সমাজতাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, খারিজ উপন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংকট এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা তুলে ধরা হয়েছে। (পৃ. ১৩-১৫)। মৃণাল সেনের পরিচালিত খারিজ চলচ্চিত্রটি তাঁর উপন্যাসের একটি সফল রূপান্তর এবং এটি কান চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছিল। গবেষক মিঠুন চক্রবর্তী তাঁর গবেষণাপত্রে বাড়ী বদলে যায় উপন্যাসে সমাজ ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরিবর্তন নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। (পৃ. ৭৮-৮৩)
রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্য আমাদের সময়, সমাজ এবং মানবিকতার গভীর অনুসন্ধান। তাঁর কাজ শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, বিশ্বসাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর উপন্যাস ও গল্পগুলো আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম আমাদের জীবনের বাস্তবতা, মানবিক সম্পর্ক এবং সামাজিক পরিবর্তনের একটি দর্পণ হিসেবে বিবেচিত হয়। তাঁর কাজ থেকে আমাদের সমাজ এবং সংস্কৃতির গভীরতর বোঝাপড়া লাভ করা যায়।
তথ্যসূত্র :
১। Chakrabarti, Kunal; Chakrabarti, Shubhra (22 August 2013), Historical Dictionary of the Bengalis. Scarecrow Press, P. 132. ISBN 978-0-8108-5334-8.
২। Dutt, Kartik Chandra (1999). Who's who of Indian writers: 1999 (End-century ed.). New Delhi: Sahitya Akademi. p. 239. ISBN 81-260-0873-3.
৩। লেখালেখি, গদ্য সংগ্রহ—রমাপদ চৌধুরী, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১। এবং মুশায়েরা। কল-৭৩। পৃষ্ঠা ১৭০- ‘৭১।
৪। অ্যালবামে কয়েকটি ছবি, উপন্যাস সমগ্র (২), রমাপদ চৌধুরী। তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ১৯৯৫। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ। কলকাতা- ৯। পৃ. ৪৫৫।
৫। বাড়ি বদলে যায়, প্রসঙ্গকথা, উপন্যাস সমগ্র (৬), রমাপদ চৌধুরী। প্রথম সংস্করণ ১৯৯৬, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ৪৯৯।
আলী সিদ্দিকী কবি, কথাসাহিত্যিক ও সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ ষোল। সম্পাদক : মনমানচিত্র। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পেনসেলভেনিয়া বসবাস করেন।