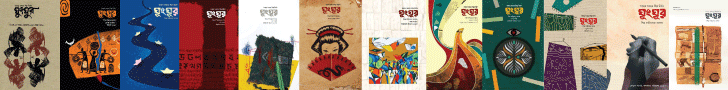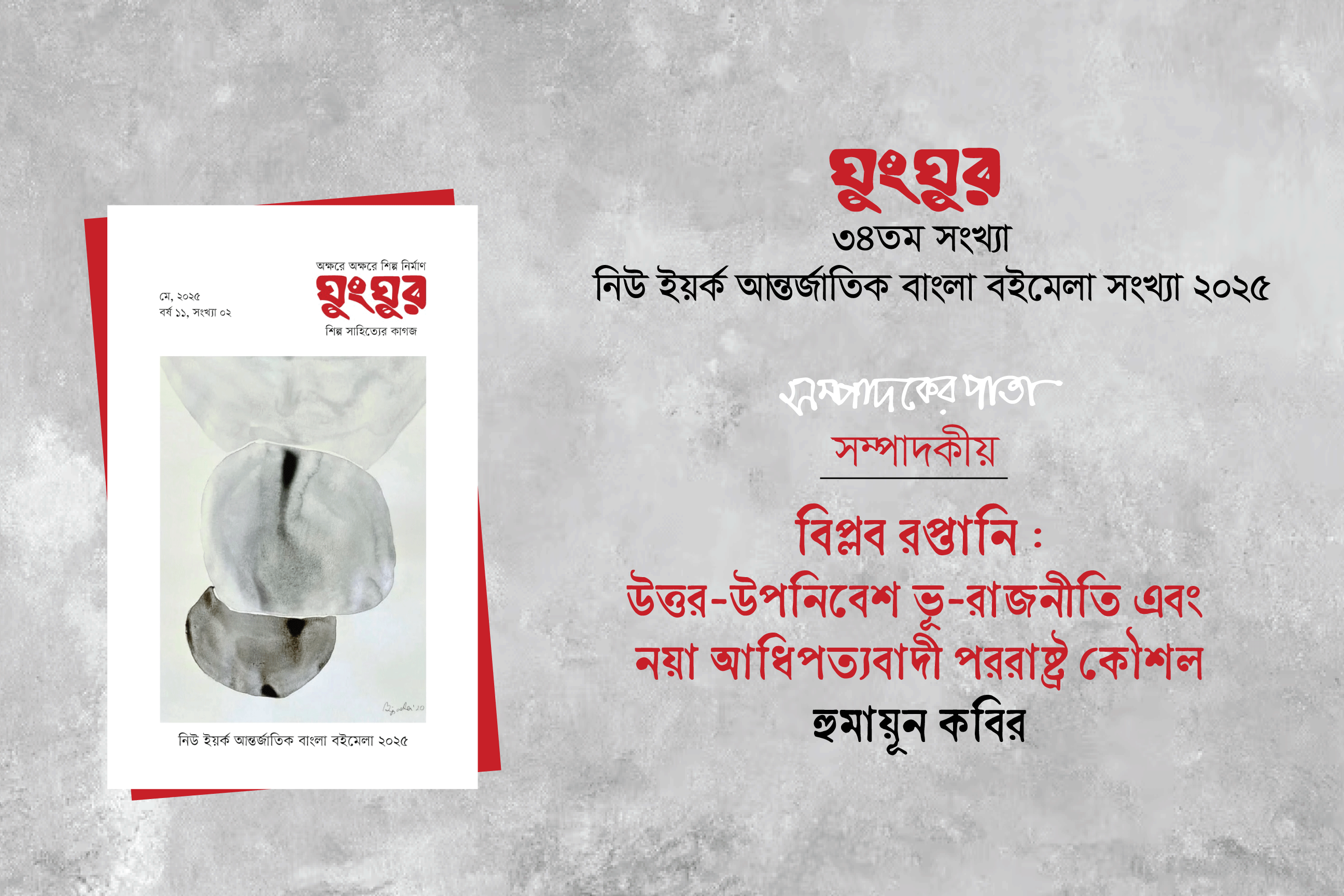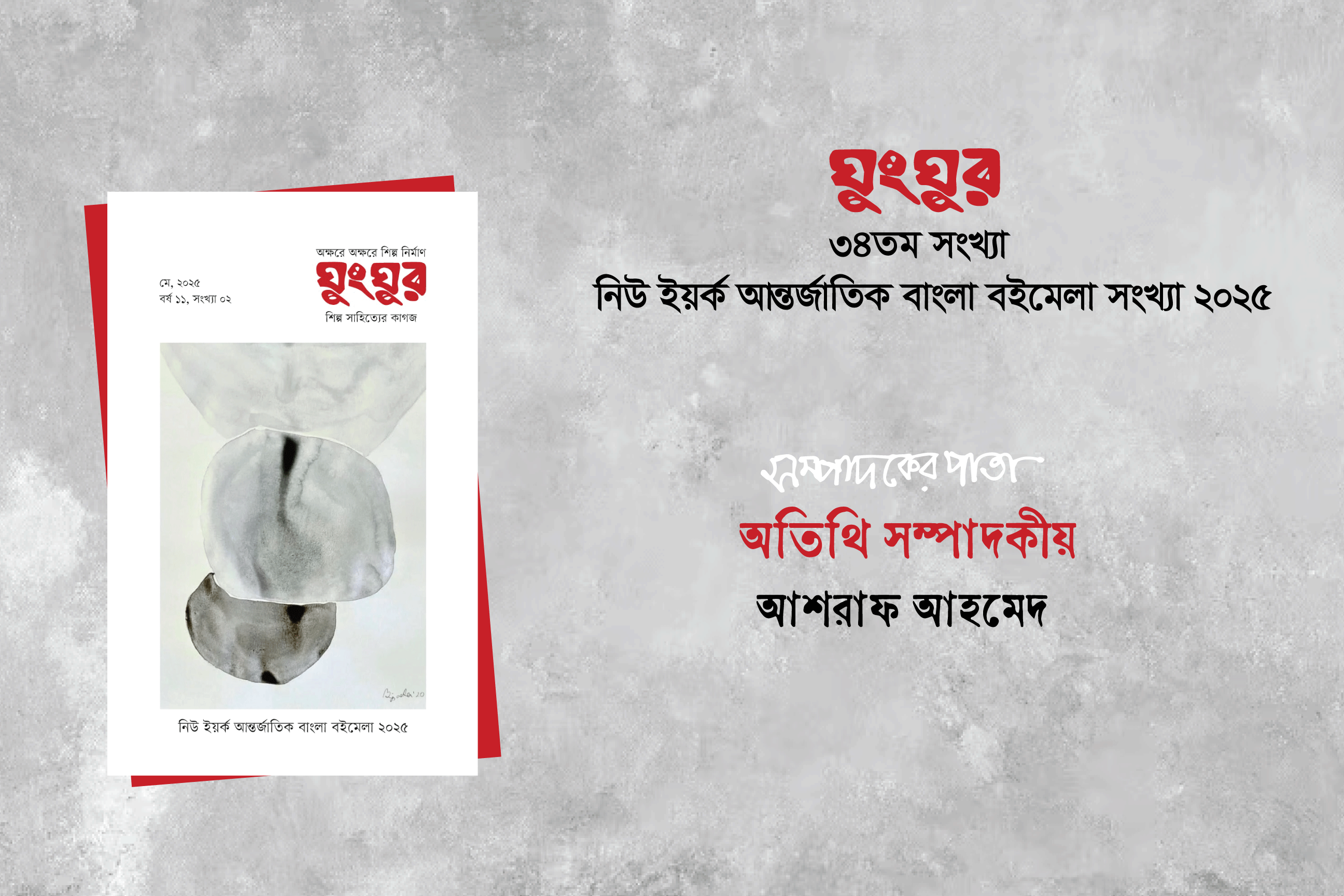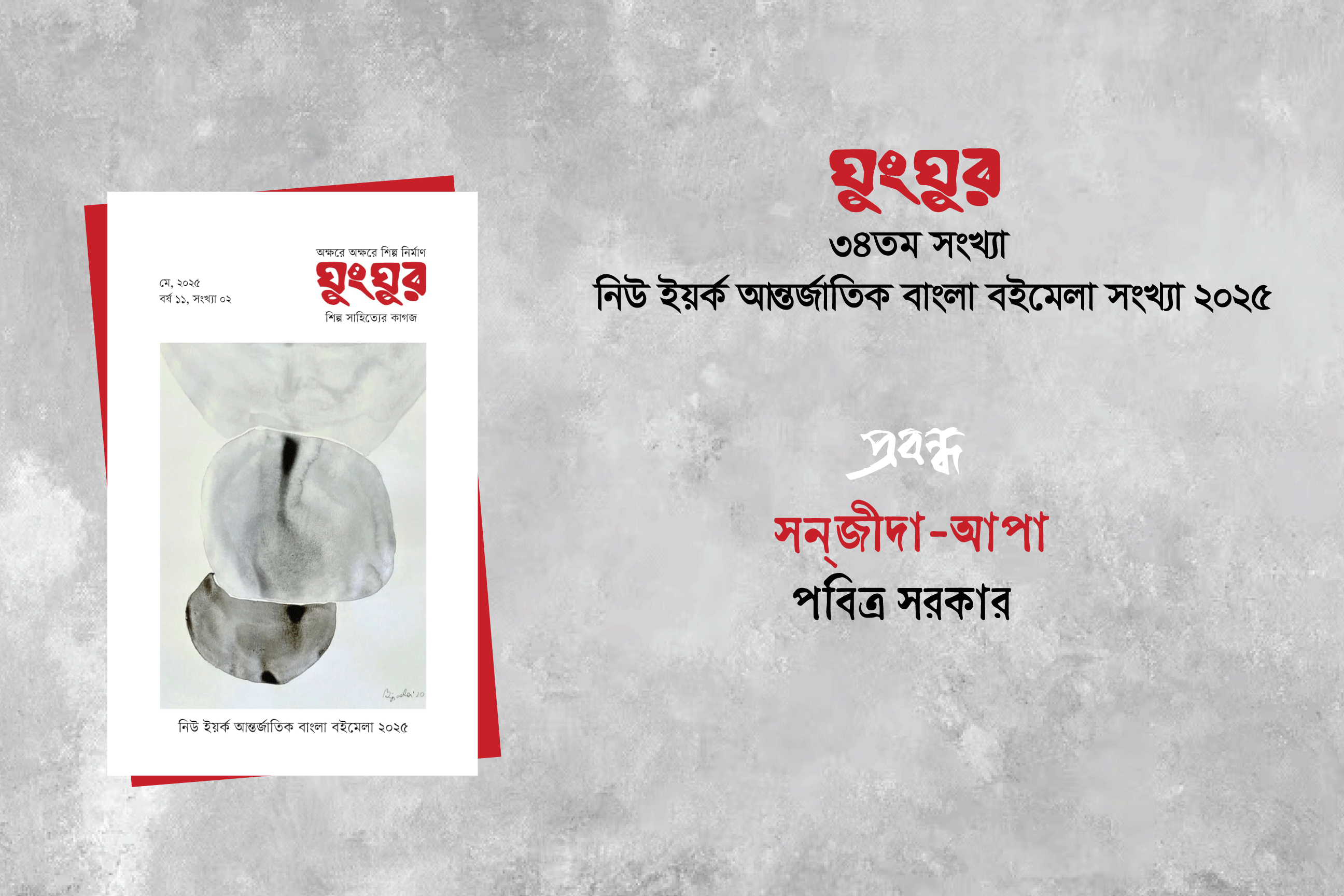অমূল্য যত পুরোনো
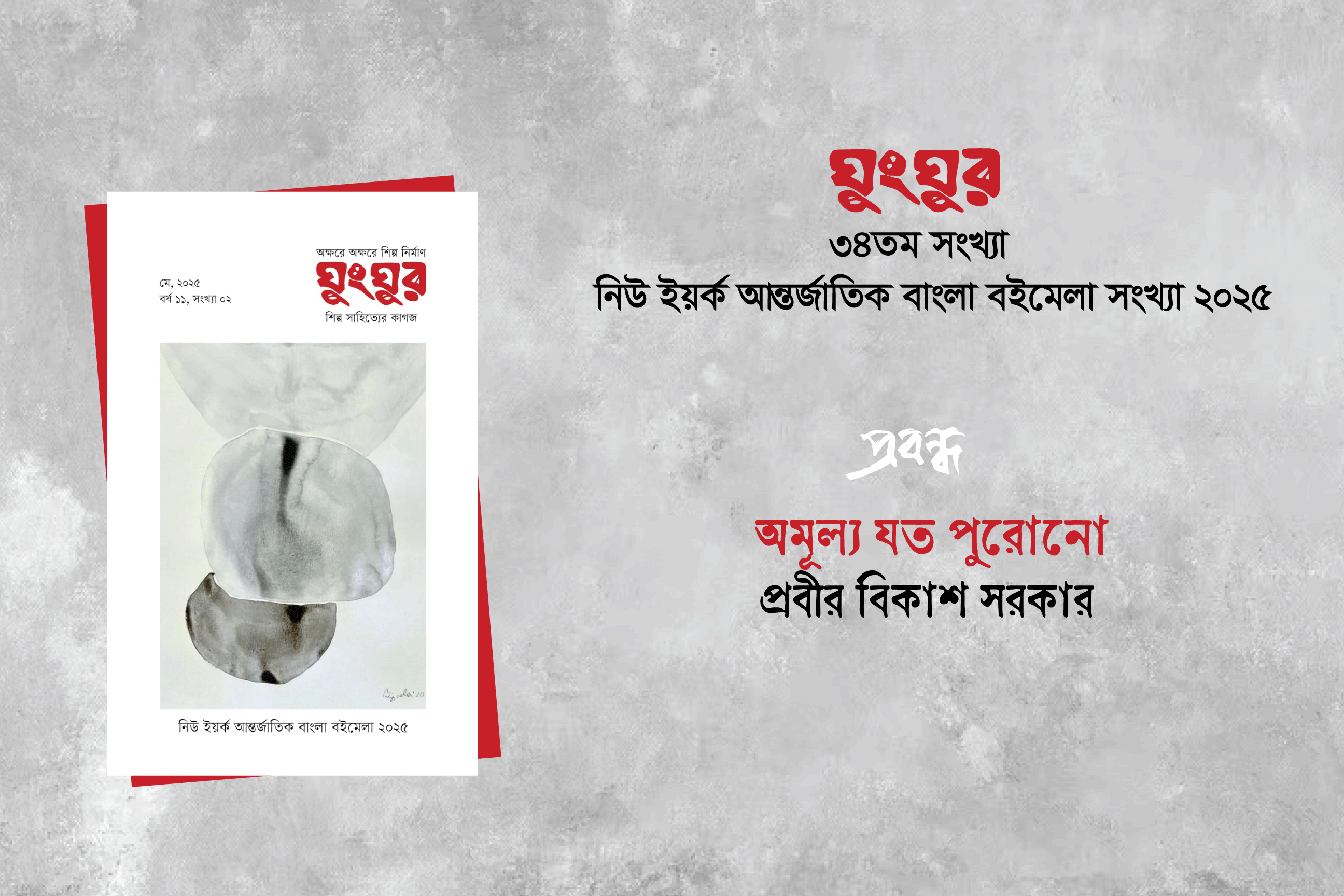
বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীতে—পুরোনো জেনেও আধেক চোখে না দেখার আহ্বান রয়েছে। শুধু নতুনকে দেখলে ‘একচক্ষু হরিণ’ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। তাই পুরোনো, প্রাচীন এবং নতুন মিলে একটি হীরকমালা। তাদের আলো দিকবিদিকে ছড়িয়ে থাকে। যেমন প্রকৃত শিক্ষকের মধ্যে দেখা যায় চতুর্দিকের জ্ঞানজ্যোতি।
ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম তাই হয়তো পুরোনো—প্রাচীনই আমার প্রকৃত শিক্ষক। পুরোনোর শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই নতুনদের মেধা জন্মলাভ করে। আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। পুরোনো কোনোকিছুকেই আমি অবহেলা করি না, এবার সে মানুষ হোক আর সামান্য জিনিসই হোক। কেননা তা থেকে কিছু না কিছু আমি জানতে পারি, শিখতে পারি, উৎসাহিত হই সর্বোপরি কাজে লাগাতে পারি। কেন যেন মনে হয়, পুরোনোটা ছিল বলেই সেটা আমার কাছে নতুন।
এই যে আমি বিগত ২৫-৩০ বছরের বেশি সময় ধরে জাপানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এতসব পুরোনো দলিলপত্র সংগ্রহ করেছি, যা সবই নতুন আলোকে আলোকিত মহামূল্যবান জিনিস বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা রবীন্দ্রনাথ একজন বিশ্বমাপের মনীষী—তাঁর মনস্বিতার গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং অপরিহার্যতাই আলাদা এবং অনন্যসাধারণ। আজও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনেক দেশেই তিনি নবীন—প্রবীণের পঠিত বিষয়, গবেষণার বিষয়, আদর্শ শিক্ষা এবং অনুপ্রেরণার উৎস। তা না হলে দেশ-বিদেশের তরুণ-তরুণীরা রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনস্থ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে অধ্যয়ন করত না। বিশ্বখ্যাত অনেক বিদ্বানের পা পড়েছে শান্তিনিকেতনের মাটিতে।
বেশ কয়েক বছর আগে জাপানশীর্ষ রবীন্দ্রগবেষক, বাংলা ভাষার পণ্ডিত এবং বাঙালিপ্রেমী প্রয়াত অধ্যাপক কাজুও আজুমার বাড়ির পরিত্যক্ত কাগজপত্রের স্তূপ থেকে তিনটি পুরোনো বই সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু পড়া হয়ে ওঠেনি ব্যস্ততার কারণে। এবার পড়ে ফেললাম। বলাই বাহুল্য, অজানা অনেক তথ্য ও ইতিহাস অবগত হলাম।
যষ্টি-মধু.কলকাত্তাই সংখ্যা
প্রথম বইটি একটি সাহিত্যভিত্তিক সাময়িকী বা ম্যাগাজিন তাতে রঙ্গ-ব্যঙ্গই মূল বিষয়াদি। কাগজটি মাসিক, নাম, যষ্টি-মধু.কলকাত্তাই সংখ্যা এবং সরকারিভাবে নিবন্ধনভুক্ত। জানি না এখন সেটা আর প্রকাশমান কি না? আশ্বিন ’৭৭ এবং অক্টোবর ’৭০, শারদীয় কলকাত্তাই সংখ্যা এটা। সাদাকালো, ১৩৬ পৃষ্ঠা প্রচ্ছদসহ। সম্পাদক কুমারেশ ঘোষ।
একদা ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী কলকাতা নিয়ে কত যে অম্লমধুর ছড়া, কবিতা, গল্প, নিবন্ধ, ফিচার, রম্যরচনা, প্রবন্ধ এবং ইতিহাসবিষয়ক তথ্যাদি রয়েছে এই ম্যাগাজিনটিতে সেসব না পড়লে জানতামই না! সুতরাং অনেক বিষয়ই নতুন হিসেবে উন্মোচিত হয়েছে আমার দৃষ্টিতে। তিলোত্তমা কলকাতা মহানগরী যে কত বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছিল প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ভারত স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত তার একটি অনন্য দীর্ঘ রোমান্টিক ভ্রমণ বলা যায় এই সাময়িকীটি।
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগের কতিপয় কবি ও সাহিত্যিকের লেখা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, যেমন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম প্যাঁচা, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর) প্রমুখ। পরের যুগের রয়েছেন যথাক্রমে, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বনফুল, আনন্দ বাগচী, আবু আতাহার, মন্মথ রায়, আশাপূর্ণ দেবীসহ আরও অনেক কবি ও সাহিত্যিক। কিংবদন্তিতুল্য ব্যঙ্গচিত্রী (কার্টুনিস্ট) চণ্ডি লাহিড়ীর চিত্রও মুদ্রিত হয়েছে একাধিক।
যে রচনাটি পাঠ করে দারুণ ঋদ্ধ হয়ছি সেটা হলো, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের কলিকাতা——সেকালের ও একালের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ কলকাতার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর জরিপকৃত তথ্য-উপাত্ত (ডেটা) এই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। বিষয়গুলো যথাক্রমে দুর্ভিক্ষ ও লোকের মৃত্যু, ইট ও চুনের দর, কলিকাতায় প্রথম ডাক, প্রতি শুক্রবারে বেত্রাঘাত, ধোপা-নাপিত ও দর্জির মেহনত—আনা, সেকালের ডাকঘরের কথা, হিন্দু পর্ব ও উৎসব—দিনের তালিকা, সেকালের বাংলা সংবাদপত্রের নাম, বাগবাজার চিত্রেশ্বরী মন্দিরে নরবলি, কয়েকটি মজাদার বিজ্ঞাপন, সহরের পথে কুকুরের উৎপাত, সেকালের ঔষধ ও ডাক্তারের ভিজিট, আপিসে কড়ির ব্যবহার, ইউরোপীয় ভবঘুরের দল বৃদ্ধি এবং সতীদাহের একটি দৃশ্য। এ যুগের আমাদের কাছে এসবই নতুন জ্ঞান ছাড়া আর কী! যদিও বা পুরোনো। কিন্তু এইসব পুরোনোকে না জানলে কতকিছু যে অজানা থেকে যায় এই সাময়িকীটি তার জ্বলন্ত উদাহরণ বলাই শ্রেয়।
ত্রিশের সশস্ত্র অভ্যুত্থান
দ্বিতীয় গ্রন্থটি অসামান্য একটি গ্রন্থ এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অমূল্য ইতিহাস। ত্রিশের সশস্ত্র অভ্যুত্থান শীর্ষক গ্রন্থটি লিখেছেন গ্রিফিথ স্মৃতি— পুরস্কারপ্রাপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের অধ্যাপিকা ড. আশা দাশ। ১৩২ পৃষ্ঠার গবেষণাকৃত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে চট্টগ্রাম সশস্ত্র অভ্যুত্থান সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে ১৯৮০ সালে। গ্রন্থটি গ্রন্থকার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক কাজুও আজুমাকে স্বহস্তে লিখে উপহার দিয়েছিলেন।
লেখিকা গ্রন্থের ‘নিবেদন’ সূচনায় প্রথমেই লিখেছেন, ‘১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল সর্বাধিনায়ক সূর্যসেনের নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখা অভিযানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে এবং ভারত ভূখণ্ডে প্রথম অস্থায়ী স্বাধীন সরকার ঘোষণা করে। এই বিপ্লবী অভিযাত্রা পরবর্তীকালে শৌর্যময় এক আবহ সৃষ্টি করে পরাধীন জাতির ইতিহাসে জ্যোর্তিময় নবযুগের আবির্ভাব ঘটায়। ব্রিট্রিশের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ কারাগারের লৌহ-কপাট এর পর থেকে ক্রমশ ভাঙতে শুরু করে। অবশেষে স্বাধীনতার ঊষার আলো যা উনিশ শ’ ত্রিশের ১৮ই এপ্রিল ভারতের পূর্ব দিগন্তকে প্রথম স্পর্শ করেছিল তার মহাভাস্বর গৌরব দীপ্তি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতভূমিকে উদ্ভাসিত করে দেয়।
কিন্তু সর্বাধিনায়ক সূর্যসেন কেবল একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নিয়ন্তাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিপ্লববাদের উত্তুঙ্গ প্রাণপুরুষ। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৭ সাল, এই সপ্তদশবর্ষ এবং তার পরে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সূর্য সেন বিপ্লববাদের প্রাণসামগ্রীর ধারক ও বাহক। রামমোহন থেকে আরম্ভ হয় ভারত-জাগরণের সূচনা পর্ব। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে তিনি বিপ্লবের সূচনা করেন। পরবর্তীকালে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ প্রমুখ মহা-মনস্বিগণ স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন, আর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের জন্য ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল-চাকী-কানাই-সত্যেন-বাঘাযতীন প্রমুখ যাঁরা রক্তমূল্য দিয়ে গেছেন সূর্যসেন সেই বিপ্লবী তপস্বীদের পরিপূর্ণ উত্তরাধিকার বহন করে ভারত-বিপ্লবের ইতিহাসকে স্তর থেকে স্তরান্তরে উত্তরণ করে দিয়েছেন। এ যুগেও আমরা যখনই কোন বিপ্লবী চরিত্রের প্রতিরূপ খুঁজি তখনই আমাদের মানস-চক্ষে ভেসে ওঠে বিপ্লব—প্রকর্ষের পুরোধা সূর্যসেনের জ্যোতিষ্মান আলেখ্য—যে আলেখ্যে তপস্বীর নিস্পৃহতা, সুদূরের স্বপ্নালুতা এবং বজ্রের কাঠিন্য এই ত্রয়ী সত্তার প্রতিফলন ঘটেছে।’
বলা বাহুল্য, এই তথ্যই বা এখনকার প্রজন্ম ক’জন জানে! জানে কি কোনো রাজনীতিক? বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক?
সূচিপত্রের তালিকায় যে পর্বগুলো বর্ণিত তা এ রকম :
১. বিপ্লবের তত্ত্বচিন্তা ও অনুষঙ্গ
২. ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি : আদর্শ ও সংগঠন
৩. ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি : কর্মপরিচিতি
৪. বিদ্রোহ ও গণচেতনা
৫. বিদ্রোহের ত্রুটিবিচ্যুতি
৬. বিদ্রোহের সময়
৭. বিদ্রোহের ফলশ্রুতি
৮. বিপ্লবী সূর্যসেনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা
৯. জীবনালেখ্য : বিপ্লবীর জীবন নির্দেশিকা
১০.জাতীয় শিক্ষক সূর্যসেন
১১. সূর্যসেনের রচনাবলী প্রসঙ্গে
১২. সব্যসাচী ও সূর্যসেন সমীক্ষা
১৩. গ্রন্থপঞ্জী
১৪. নির্ঘণ্ট
ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন বা সংগ্রাম বিষয়ে এমন আকর্ষণীয়, রোমান্টিক এবং তথ্যবহুল গ্রন্থ খুব কমই রচিত হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। লেখিকা কী মমতা আর মর্যাদার সঙ্গে সেই সময়কার অগ্নিখেলার দুঃসাহসী বাঙালিদের নিয়ে আলোচনা করেছেন, পাঠ না করলে তাঁদের স্বদেশচিন্তা সম্পর্কে অনুভব করা সম্ভব হতো না। তাঁদের মূল্যবান জীবনের বিনিময়ে ভারত স্বাধীন হয়েছে, ঘটনাক্রমে পূর্ব বাংলাও স্বাধীনতা অর্জন করে বাংলাদেশ হয়েছে, সেই বাংলাদেশে সূর্যবিপ্লবী সূর্যসেনের স্বাধীনতাবিষয়ক চিন্তাকে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্বদেশকে ভালোবাসার শিক্ষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি বিগত ৫৪ বছরেও! সুতরাং স্বাধীনতার অর্থ ও মূল্যকে অনুধাবন করতেই শেখেনি স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রজন্মগুলো ভুল-ভ্রান্তিভরা রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারণে। সূর্যসেনের নেতৃত্বে কোনো ধর্মেরই দিকনির্দেশ ছিল না, অথচ তাঁরই উত্তরসূরি রাজনৈতিক নেতারা স্বাধীনতার পরপরই ধর্মকে টেনে এনেছেন সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে, তোষামোদী করেছেন এবং এই ধারা আজকে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবসা, সংগঠন ও সমিতি পর্যন্ত। একতরফা সাম্প্রদায়িক আক্রমণ, হত্যা, ধর্ষণ, বাড়ি—জমি লুটপাট, মন্দির ও বাড়িঘর জ্বালাও—পোড়াও, জাতীয় সম্পদ ধ্বংস, স্বাধীনতার ম্যুরাল গুঁড়িয়ে দেয়া, মুক্তিযুদ্ধের স্মারকস্তম্ভ বিধ্বস্তকরণ ইত্যাদি অপকর্ম গণমাধ্যমের প্রথম পৃষ্ঠা দখল করছে প্রতিদিনই। আর সরকার ও রাজনীতিকরা একেবারেই প্রতিবাদহীন নীরব দর্শক। কোথায় আজ বাঙালির আত্মগৌরব, রাজনৈতিক শিক্ষা ও স্বদেশপ্রেম? সব হারিয়ে ফেলে উন্মাদে পরিণত হয়েছে এই জাতি। দুর্ভাগ্যজনক করুণ পরিণতিবরণই যেন ছিল মহান বিপ্লবীদের স্বাধীনতার আন্দোলনের ফলাফল!
আমার কুটিরের কথা
তৃতীয় গ্রন্থটি আমার অজানায় এক নতুন ইতিহাস। আমার কুটিরের কথা প্রচ্ছদসহ সব মিলিয়ে মাত্র ২০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকাবিশেষ। হালকা বটে, কিন্তু তথ্যের মাত্রায় ওজনবিশিষ্ট বলতেই হবে। লিখেছেন প্রফুল্ল কুমার গুপ্ত, ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ তারিখে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ থেকে।
পুস্তিকার প্রথমেই ‘লেখকের নিবেদন’-এ রচয়িতা লিখেছেন, ‘প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের পেছনে এক একটি ইতিহাস আছে। আমার কুটির গড়ে ওঠার পেছনেও একটা ইতিহাস আছে। কিন্তু বাইরের মানুষ বা দূরের মানুষের কাছে “আমার কুটির” যেমন ছিল অপরিচিত, তেমনি ছিল কতকটা যেন রহস্যাবৃত।’
এরপর লেখক ‘আমার কুটিরের কথা’ মূল রচনায় লিখেছেন, ‘সম্ভবত ১৯২৩ সাল—মহাত্মা গান্ধী এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির সেই মহামিলন দেখার জন্য বাইরে থেকে যাঁরা তখন বোলপুরে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে এক আদর্শপাগল যুবকও এসেছিলেন গান্ধী দর্শনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। কিন্তু সেদিন কে জানতো যে, বোলপুরের অলেখা ইতিহাসে তিনিও একটি অধ্যায় যোজনা করে রেখে যাবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, প্রকাশ্য দিনের আলোতে যে ইতিহাস রচিত হয়, লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্ধকার গহ্বরেই হয়তো তাঁর উদ্ভব হয়। ‘আমার কুটিরে’র উদ্ভব একদিন সেইভাবেই হয়েছিল এবং কতকটা লোকচক্ষুর অন্তরালেই হয়েছিল বলা চলে। তিনশো বিঘা পরিমিত এই ভুখণ্ডটি তখন ঊষর, কাঁকর ও জঙ্গলাকীর্ণ এবং মানুষের বাসের অযোগ্য। শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন পার হয়ে বল্লভপুর আসার যে পথ, সে পথও তখন কিছু সুগম ছিল না। কিন্তু দেখা যায় যে, কোন কিছু সৃষ্টির ডাক যখন আসে, তখন স্রষ্টা হয়তো নিজেরই অজান্তে পরিচালিত হন। গান্ধী দর্শনে এসে সুষেণ মুখোপাধ্যায় শ্রীনিকেতনের পথ ধরে এগিয়ে এলেন। চোখে তখন তাঁর মধ্যাহ্ন সূর্য্যরে দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস, কিন্তু রক্তে সৃষ্টির নেশা লেগেছে। তার কিছুদিন আগে একটি রাজনৈতিক মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে তিনি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, প্রকৃত প্রমাণ অভাবে ছাড়া পান। সুরুলের জমিদারবাবুদের কাছে তিনি প্রার্থনা জানালেন ওই জঙ্গলাকীর্ণ ভুখণ্ডের কিছুটা জমা—বন্দোবস্ত করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু কোপাই নদীর ধারে সিদ্ধেশ্বরীর মহাশ্মশানের সেই জঙ্গলের কি তখন কিছু দাম ছিল? জঙ্গল বন্দোবস্ত পেতে তাই কোনো বেগ পেতে হয়নি সেদিন, ঝড়ে উড়ে আসা বীজ যেমন সেখানে একদিন এক জঙ্গলের সৃষ্টি করেছিল, বাইরে থেকে উড়ে আসা একটি আদর্শপাগলের মানুষ তেমনি আর একদিন সেখানে ‘আমার কুটিরে’র পত্তন করেছিলেন।
‘আমার কুটির’ নামটির মধ্যেও একটা তাৎপর্য আছে। যে কেউ ওটিকে ‘আমার’ করে নিতে পারবে, সেটা তারও কুটির। সুষেণবাবু তাঁর কলকাতার অফিসের মধ্যে সোনার জ্বলজ্বলে অক্ষরে একটি কাচে বাঁধা কথা টাঙিয়ে রাখতেন ‘আমার দেশ’। আমাদের দেশ বলতে যে নৈর্ব্যক্তিকতা আসে, এ তার চেয়েও স্পষ্ট, আপন ও স্বকীয়। সবার দেশ মানে কারও দেশই নয়; এ আমার দেশ, আমার কর্তব্য, আমার প্রত্যক্ষ, নিজস্ব ও অপরিত্যাজ্য এক দায়িত্ব।
তাঁর ভবঘুরে ছন্নছাড়া জীবন, ছেলেবেলা থেকেই গতানুগতিক সাংসারিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ছিলেন উদাসীন; ফলে তথাকথিত উচ্চ শিক্ষালাভ করার সুযোগ তিনি পাননি। কিন্তু তা না পেলে কি হয়, জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন তার কোন তুলনা হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—‘আধুনিক বিদ্যালয় থেকে আদর্শ মানুষ বেরোয় না, সেখান থেকে বেরোয় কেরানি, হাকিম, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রিট। যে দু’চারজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়, তাঁরা সকলেই বাইরের বিশ্বে প্রস্তুত।’ সুষেণ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে হয়তো সেই কথা বলা চলে।
পরবর্তী সময়ে কর্মযোদ্ধা এই সুষেণ মুখোপাধ্যায় একটি বিন্দুতে স্থির থাকেননি, রামকৃষ্ণ মিশন থেকে শুরু করে একাধিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, বৈপ্লবিক আদর্শকে গ্রহণ করে স্বাধীনতার আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছেন, অনেক প্রভাবশালী বিপ্লবীর আশ্রয়কেন্দ্র করে তুলেছিলেন ‘আমার কুটির’কে। রাজনীতিবিদ সুভাষচন্দ্র বসুসহ অনেক খ্যাতিমান ‘আমার কুটিরে’ পদধুলি রেখেছেন। বহু অসহায় মানুষের জীবনের দায়দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন সুষেণবাবু। ‘অমর কুটির’কে জীবিকার মাধ্যম করার লক্ষ্যে প্রথমে কাপড় ছাপানোর কর্মস্থানে পরিণত করেন। তারপর হস্তশিল্প হিসেবে চর্মশিল্প, চাষাবাদসহ নানা ধরনের কর্মটপ্রকল্পে বিস্তৃত করতে সমর্থ হন। শান্তিনিকেতনসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে এমনকি একসময় জাপানেও ‘আমার কুটিরে’র পণ্যসামগ্রী বিক্রি হয়েছে। এখনো এই প্রতিষ্ঠান চামড়ার হাতব্যাগের জন্য সুবিখ্যাত।
বাঙালি চেষ্টা করলে কী না পারত এক সময়! কর্মপাগল, স্বদেশপ্রেমী এবং মানবতাবাদী অকৃতদার সুষেণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তেমনি একজন কর্মবীর বাঙালি। বলা যেতেই পারে, বাংলার আর্থিক মুক্তিযুদ্ধের একজন প্রথম সারির মহান মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তিনি। সেই খবর আমার প্রজন্মের বা নতুন প্রজন্মের ক’জনই বা জানি!
এইসব পুরোনো গ্রন্থাদি পড়ে নতুন কতকিছুর যে সন্ধান পাই তার কোনো হিসেব নেই, নেই আনন্দের পরিসীমা। কেবলই সঞ্জীবিত হই পুরোনোকে খুঁজে নিতে নতুন তথ্যভাণ্ডারকে আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করার জন্য। নিজে জেনে অন্যকে জানানোর মধ্যে মহৎ একটা লক্ষণ আছে বই কি!
প্রবীর বিকাশ সরকার শিশুসাহিত্যিক ও গবেষক। তাঁর ২৯টির ওপর গ্রন্থ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ : উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে, অবাক কাণ্ড, জানা অজানা জাপান (তিনখণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ও জাপান : শতবর্ষের সম্পর্ক, সূর্যোদয়ের দেশে সত্যজিৎ রায়। অধুনালুপ্ত মাসিক মানচিত্র ও মাসিক কিশোরচিত্র-এর সম্পাদক। তিনি জাপানের টোকিওতে বসবাস করেন।