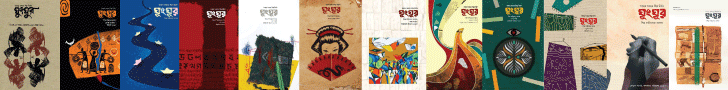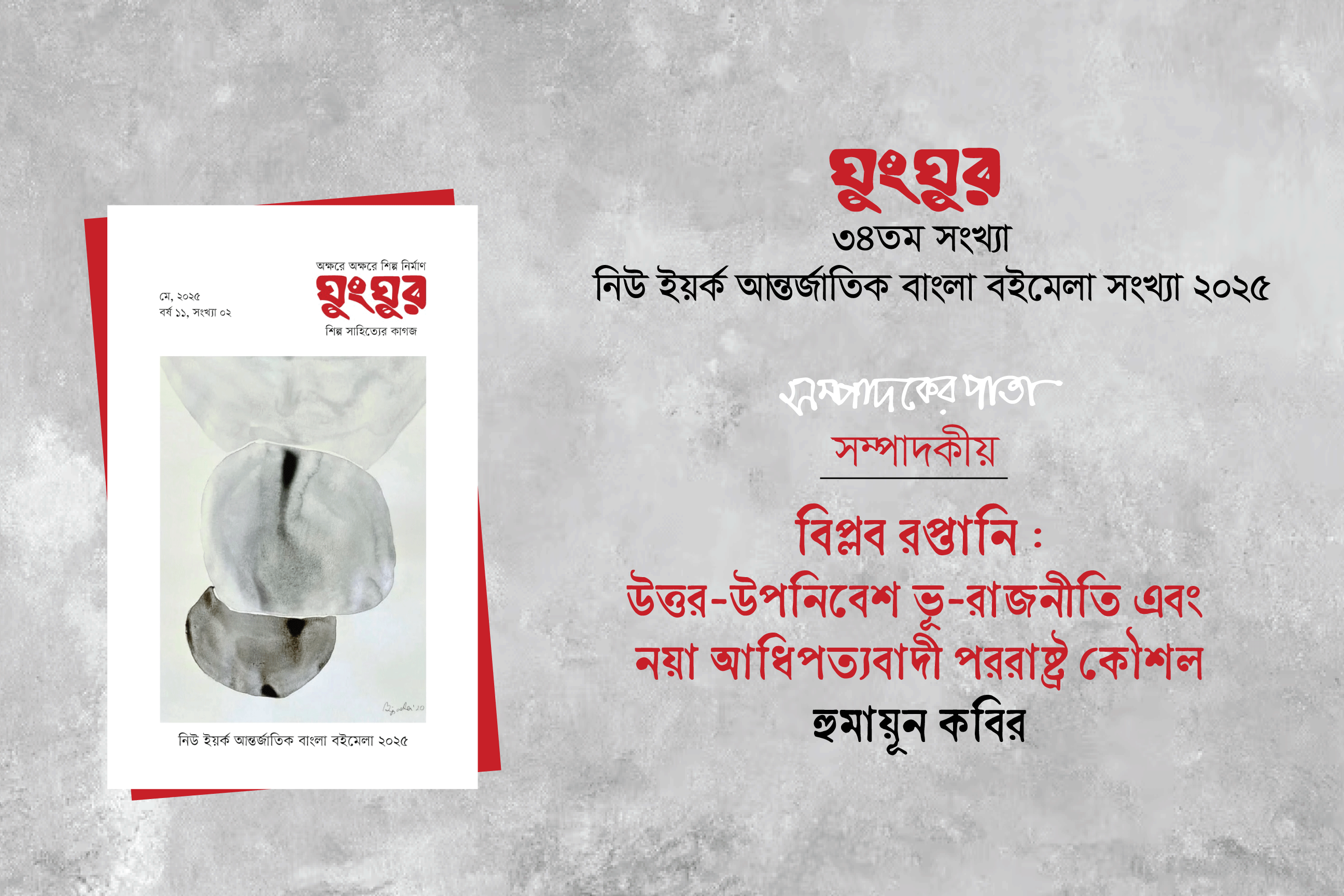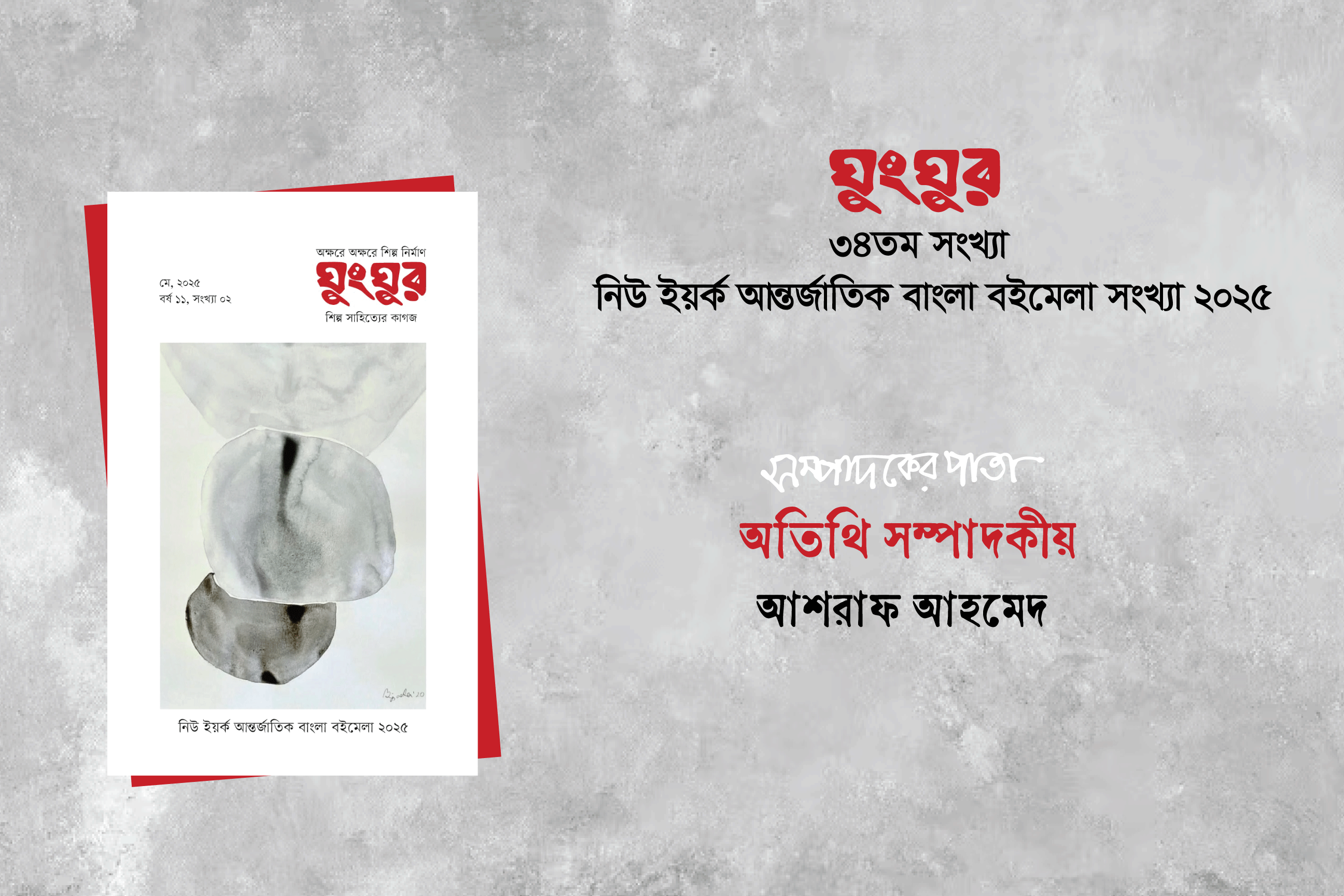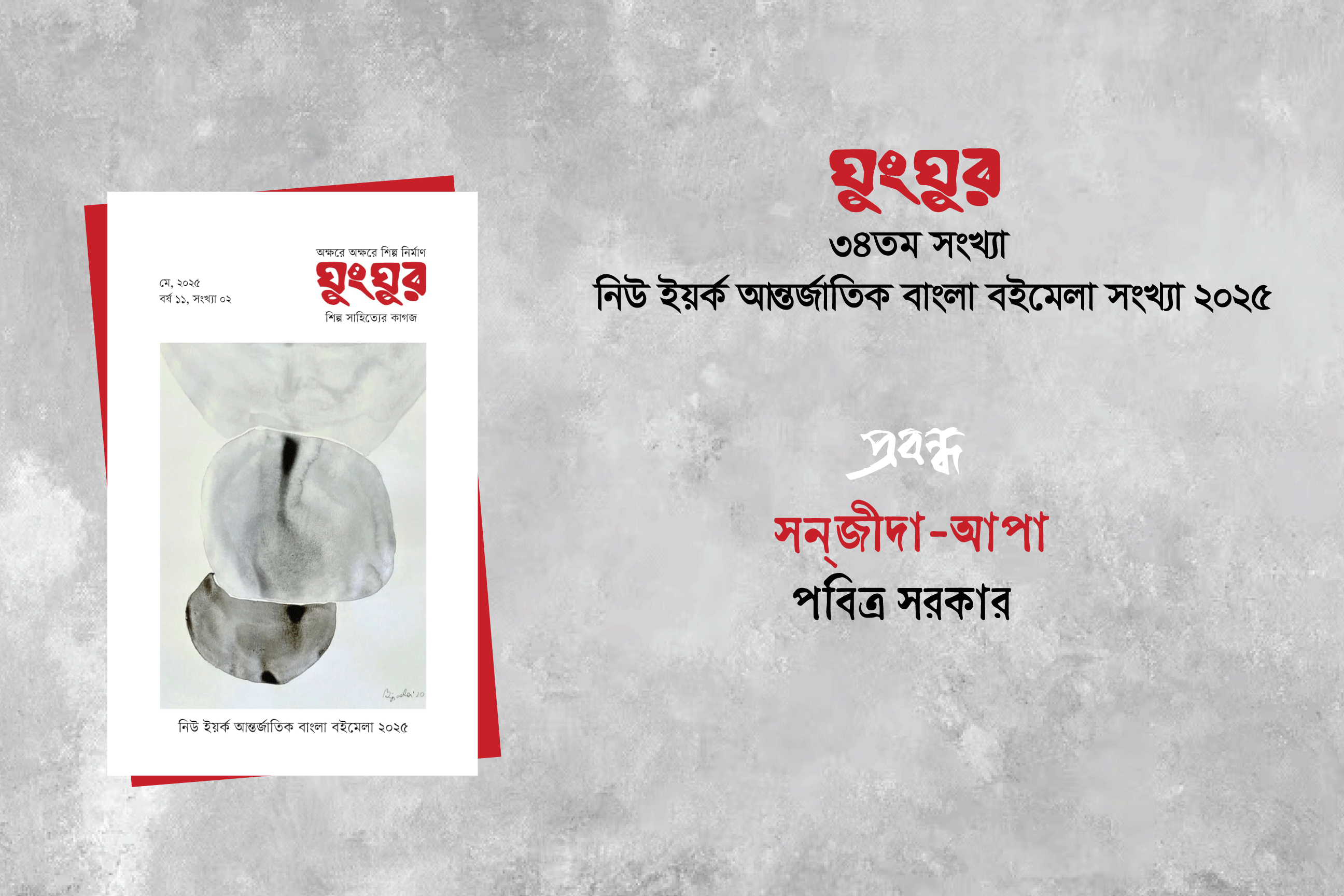প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতা : ভাষায়, ভাবনায়, ছন্দে ও বোধে
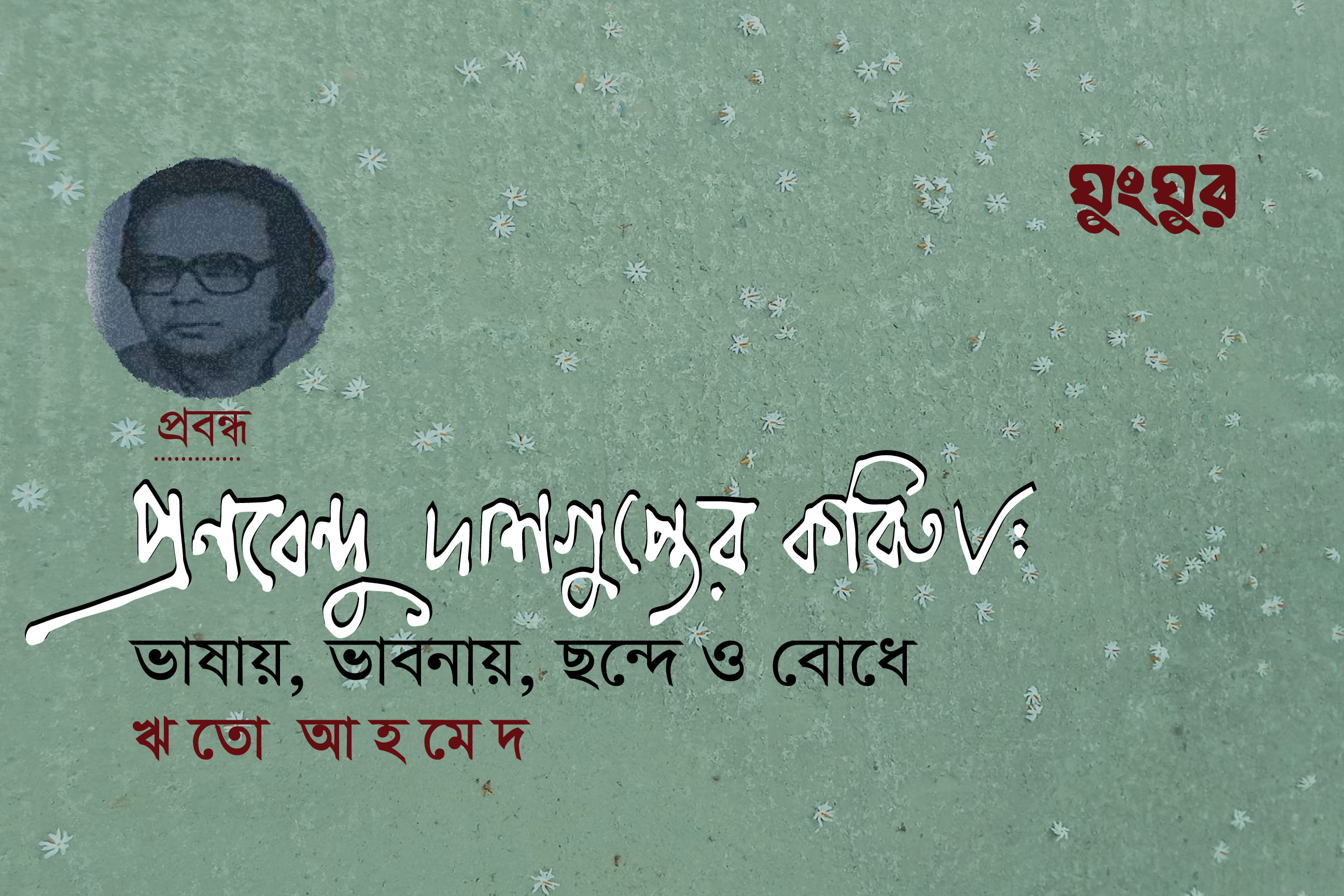
আমরা, দগ্ধ হতে হতে বুঝেছি, কোনো প্রেম পূর্ণ হয় না, সব বাসনা অসমাপ্ত থাকে, হঠাৎ মাটি ফেটে তলিয়ে যায় সম্পর্ক—
—জয় গোস্বামী
‘প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কোনো বই কখনো সংস্করণের মুখ দেখেনি! কোনো বই, কখনো না! তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা কতদিন হল উধাও। নির্বাচিত কবিতাও।’ কবিতা সমগ্র ১ এর ‘সম্পাদনা বিষয়ে ১’ প্রাককথনে এই কথাটাই বলছিলেন সুমন্ত মুখোপাধ্যায়। ২০১৬-র জানুয়ারিতে কবি, প্রকাশক সৌরভ মুখোপাধ্যায় তাঁর সপ্তর্ষি প্রকাশন থেকে যে বই দুটি প্রকাশ করেছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে সে’দুটো গত শুক্রবার তক্ষশিলা থেকে আমার হাতে এসে হাজির হয়েছে। কবিতা সমগ্র ১ ও ২। পৃষ্ঠা উল্টে পড়ে যাচ্ছিলাম ১। সুমন্ত মুখোপাধ্যায় সেখানে আরও লিখেছেন, ‘আমাকে প্রথম প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতা পড়িয়েছিলেন ভাস্কর চক্রবর্তী। কিন্তু যে যত্ন আর ভালোবাসায় তিনি নিজে পড়েছিলেন সে আন্দাজ আমার আছে। আর তাই তাঁর ভালোবাসা ভরা মন আমি খুঁজে বেড়াই। … আমার সমস্ত কাজ তাঁরই জন্য।’ সুমন্ত আমাদের আরও জানান যে কবি জয় গোস্বামী তাকে এই বইদুটি সম্পাদনা করতে বলেছিলেন। যিনি বাংলা কবিতার ভেতর দিকের অনেক ঘটনার সাথেই জড়িয়ে আছেন। প্রণবেন্দুর কবিতা সমগ্র প্রকাশের প্রাথমিক উদ্যোগ তাঁরই।
বোঝা গেল, তাহলে এইভাবেই, ২০২১-এর এই পাঠকের কাছে এসে পৌঁছুলেন কখনো-সংস্করণের-মুখ-না-দেখা প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত! না, শুধুই কি তাই? এর আগেও কি প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষ পরিচয় তো হয়েছিলই। আর সেখানেও ওই ভাস্কর চক্রবর্তী আর জয়ের নাম। ‘শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়’ গদ্যে ভাস্কর তাঁকে কীভাবে এনে পৌঁছালেন আমাদের কাছে! মনে পড়ছে, ‘আমরা প্রায় একটা ঝর্ণার কাছে এসে পৌঁছেছি, প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতা সম্পর্কে দু-চার কথা জানতে চাইছি যখন। চাপা যে সন্দেহ আর অবিশ্বাস, চাপা যে ঘৃণা আর ক্রোধ—অবহেলা, লাঞ্ছনা আর অপমান—চাপা যে ভয়, বিরক্তি আর মহানিঃসঙ্গতা—সেইসব বিষ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছেন।’ সেই থেকেই তো গূঢ় একটা আগ্রহ জন্মায় তাঁকে পড়ার। ‘তাঁর কবিতার মানুষ আর জীবন আর প্রকৃতির স্বাদ গ্রহণ করতে করতে, আমরা তাঁর সেই গতিপথটার কথা যেন না ভুলি। আমরা যেন না ভুলি—কী সরু, কী জমজমাট, কী কর্কশ একটা সময়কে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তিনি এসে পৌঁছালেন আমাদের কাছে।’ আমরা তাঁকে পড়ব বলেই তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তাঁর বইগুলো খুঁজতে থাকি। সেই ১৯৯০ এ বেরোয় তাঁর কবিতা সমগ্র ১। তারপর খুব সন্তর্পণে তাও বিলুপ্ত হয়ে যায়। নেই। বহুবছর বাজারে তাঁর বই আর পাওয়া গেল না। বিগত বিশ/পঁচিশ বছরে আমরা যারা বেড়ে উঠলাম তাদের কাছে প্রণবেন্দু কেবলই এক কবিনাম হয়ে রইলেন। ভাস্কর বলছিলেন, ‘প্রত্যেক দেশেই এমন কিছু কবিতা আছে, আমার মনে হয়, হাজার প্রচারিত হলেও সমসাময়িক তিনহাজার চারহাজার পাঠকের কাছে পৌঁছতে পারে না। ঠিকই ব্যাপারটা। কিন্তু ব্যাপারটা এই কথা কখনোই বলে না যে কবিতাগুলো ব্যর্থ হয়ে গেল।’… ‘দশকের পর দশক, ২০/২৫ জন পাঠকের হাতে সেসব কবিতা ঘুরতে ঘুরতে, আবার একদিন, আরও জ্যান্ত হয়ে ফিরে আসে। অহরহ আমরা দেখি, কত সফল কবির মৃতদেহের বুকে কত ব্যর্থ কবি পা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। … কবিতার ইতিহাস বোধহয় এইরকমই।’
কষ্ট হয়। দুঃখবোধে আচ্ছন্ন হই কথাগুলো পড়ে। মনে পড়ে বাংলা কবিতার ইতিহাসে, জীবদ্দশায় সবচেয়ে অবহেলিত কবি ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। তাঁর কলকাতার মেস জীবনের সেই কয়েকদিন না-খেয়ে-থাকা দুপুরের সেই মুহূর্ত গুলোর কথা একজন কমলালেবু উপন্যাসে কী নিষ্ঠুর মায়াময় লেখনীর মাধ্যমে শাহাদুজ্জামান বর্ণনা করেছেন আমাদের, পাশের বাড়ির বারান্দায় খাঁচার পাখিটারে খেতে দেয়া এক টুকরো বিস্কিট নিয়ে ক্ষুধা-পেটে জীবনানন্দ দাশের সেই গল্প রচনার ঘটনাটুকু। —এইরকমই হয়। আবার, প্রণবেন্দুও ফিরে আসছেন এবার। ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে আরও জ্যান্ত হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসছেন তিনি। তাঁর কবিতার প্রতি আজকের পাঠকের আগ্রহও আশাব্যঞ্জক। কারণ, সেই ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতেই তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন বাংলা কবিতার একটা নির্জন দিক। একটা নিশ্চুপ আন্দোলন। যার শুরুটা ছিল ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত ছড়ানো। এই সময়টাতেই পাল্টে গিয়েছিল তাঁর ভাষা ব্যবহার, কবিতা ধারণা, ছন্দ এবং জীবনদৃষ্টি।
আমরা পড়তে পড়তে একটু একটু করে এগিয়ে যাবো তাঁর কবিতার পাল্টে যাওয়া সেই পথে।
ভাষা ব্যবহার
দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৭ তে প্রণবেন্দুদা আমাদের জানিয়েছিলেন, ‘আমার প্রথম কবিতার বই এক ঋতু তে অনেক বাসনা-বিধৃত, প্রেমের কবিতা ছিল। তারপরেও আমি অনেক প্রেমের কবিতা লিখেছি (দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ সদর স্ট্রিটের বারান্দা-তে ‘প্রেমিকাকে’-এই সিরিজে অনেক কবিতা আছে), কিন্তু প্রথম বইটির প্রেমের কবিতায় আমি শুধু প্রথানুগ শব্দসম্ভার ব্যবহার করেছি, নিজস্ব diction বা কণ্ঠস্বর তখনো আবিষ্কার করতে পারিনি। ‘এক ঋতু’-র শেষের দিকের কয়েকটি কবিতা ও সদর স্ট্রিটের বারান্দা-র কবিতা থেকেই আমি নিজস্ব ভূমি খুঁজে পেয়েছি মনে হয়।’ আবার শতভিষা-র এক সাক্ষাৎকারে আমরা তাঁকে বলতে শুনি, ‘হ্যাঁ ১৩৬৩। তখনো আমি নিজের ভাষা খুঁজে পাইনি এবং সে বিষয়ে আমি অবহিত ছিলাম। তখনো আমি ভালো কবিতা লিখছিলাম কখনো কখনো, কিন্তু নিজের ভাষায় নয়, কোনো বিবেকবান এবং জেদী কবির মতো আমিও চাইছিলাম নিজের ভাষা খুঁজতে। এবং একসময় যেমন ‘এক ঋতু’-র দ্বিতীয় পর্বের কবিতা যা ‘পূর্বপট’ থেকে শুরু হয়েছে। … তারপরে আমি নিজের কণ্ঠস্বর এবং ভাষা দুটোই খুঁজে পেলাম। … সেটা হয়ে গেল হঠাৎ, একটা শিমুলের বীজ ফেটে তুলো বেরিয়ে আসে যেরকম। দেখলাম চোখের সামনে আমার ভাষাকে আবিষ্কার করলাম, আমার ভঙ্গিকে আবিষ্কার করলাম। কিন্তু তার পেছনে ছিল একটা তাগিদ, একটা সচেতন তাগিদ যে আমি নিজের ভাষা খুঁজে পাবো।’ শুরুতে প্রত্যেক বড়ো কবিরই বোধহয় এইরকম একটা তাগিদ থাকে নিজের ভেতর। আর সেই তাগিদ থেকেই জন্ম হয় নতুন কাব্যভাষার। শুরু হয় কবিতার নতুন গতিপথ। গত শতাব্দীর ৫০-এর দশকে (১৯৫৭) বেরোয় তাঁর প্রথম কবিতাবই এক ঋতু। প্রকাশক ছিলেন শতভিষা পত্রিকা ও প্রকাশনীর পক্ষে দীপঙ্কর দাশগুপ্ত। তখন শতভিষা পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক তরুণ মিত্র বইটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছিলেন, ‘প্রথম দিকের কবিতার গঠনের নৈয়ায়িক বিশদতা এবং পরবর্তী কবিতাগুলির সাঙ্কেতিক সংক্ষিপ্ততায় অনুষঙ্গের দ্যোতনা—এই উভয় ক্ষেত্রেই কাব্যের প্রসাদ্গুণ বর্তমান।’ অর্থাৎ বইটির কবিতাগুলো দুটি ভাগে বা ভাষাভঙ্গিতে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিজস্ব কণ্ঠস্বর নেই যদিও শেষ অংশে তার আভাস পাওয়া যায়। বইটির প্রথম কবিতাটি যদি পড়ি—
ভীরুচোখ লুব্ধ হল জীবনের পণ্যবিপণিতে;
দূরের দ্বীপের ঘ্রাণ কাছের গভীর গূঢ় টানে
ভেসে এল এ-হৃদয়ে। তীব্রবহা প্রগাঢ় শোণিতে
মাতাল মাল্লার মোহ ভাষা পেল পাল-ছেঁড়া গানে,
তবু যত অনিয়মী, তত যেন মনে হয় পরে
আরেক বন্দর আছে, বিচ্ছুরিত আঙুরের আভা
বিলাসী আঙুলে, ঠোঁটে, দেহতটে নিভৃত নারীর
ঢেলে দেবে পাথেয় প্রচুর। জীবনের হিংস্রতম থাবা
সহসা লুকাবে ভয়ে,—দাহদীপ্ত এ-তরবারির
উজ্জ্বল শরীরে তারি জরাজয়ী মন্ত্র ঝরে পড়ে।
(ভরা আঠারোর গান/ এক ঋতু)
নিঃসন্দেহে খুব ভালো এবং সার্থক একটি কবিতা। এবার নিচের কবিতাটি পড়ি—
সে এসে দাঁড়ায় বুঝি আকাশের মতো,
তবু স্থির, আলোয় আনত
শরীরে কোথাও আমি চামেলি কি জুঁই
রাখি না কিছুই;
সে যদি হাওয়ায় সরে, জলে ভেসে যায়,
দাবানলে পোড়ে—
তার মৃতদেহে, নাকি স্মৃতির শরীর
ভীরুহাতে, চুপিচুপি ছুঁই।।
(ভ্রষ্টপ্রেম/এক ঋতু)
শব্দ চয়ন ও তার ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ করা যায়। লুব্ধ, পণ্যবিপণী, তীব্রবহা, শোণিতে, মাল্লার, পাল-ছেঁড়া, বন্দর, দেহতট, দাহদীপ্ত, তরবারি, জরাজয়ী প্রভৃতি শব্দ সমূহের ব্যবহার প্রবণতা দেখা যেত ৩০-এর এমনকি ৫০-এর অনেক কবিদের কবিতায়। পরের কবিতাটিতে ভাষা অপেক্ষাকৃত অনেকটাই সহজ ও সাবলীল। সে এসে দাঁড়ায় বুঝি আকাশের মতো / তবু স্থির, আলোয় আনত। সহজ সাধারণ শব্দে বলা কবিতার লাইন। যে সব শব্দ আমরা দৈনন্দিন জীবনে হামেশাই ব্যবহার করে থাকি। সেই সব শব্দে গড়ে উঠেছে তাঁর কবিতার এই নতুন ভাষা। এখান থেকেই ৫০-এর শক্তি, সুনীল, শঙ্খ, প্রণব, শরৎ কিংবা তারাপদ রায়দের পাশাপাশি আমরা নতুন এক কবি প্রণবেন্দুকে দেখতে পাই কিছুটা। যদিও তাঁর নতুন কাব্যভাষার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ পাই আরও ৯ বছর পর, ১৯৬৬ তে। দ্বিতীয় কবিতাবই সদর স্ট্রিটের বারান্দা-য় এসে। এর কবিতাগুলো একেবারে অন্যরকম। বলা যায় এইখানেই প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের নতুন পথের শুরু। তিনি বলেন, ‘কোনো কবি যদি একই বিষয়ে সারাজীবন পুনরুক্তি করেন, তাঁর যদি কোনো উত্তরণ না হয়, তা যেমন দূষণীয়, কবি যদি ‘চরিত্রবান’ না হন, তাঁর যদি নিজস্ব কোনো পৃথিবী তৈরি না হয়ে ওঠে, তাঁর গলার স্বর যদি সহজে না চেনা যায়, তা-ও একইভাবে সমালোচনাযোগ্য। আমি কখনই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে চাইনি, আরও পাঁচজন অনুভূতিশীল মানুষের মতো আমিও বারবার কেঁপে উঠেছি, পাল্টে গেছি।’
সদর স্ট্রিটের বারান্দা কৃত্তিবাস প্রকাশনী থেকে বের কারেন স্বয়ং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁরসদর স্ট্রিটের বারান্দা-য় দেখা গেল তিনি ৫০-এর অন্য কবিদের থেকে একেবারে আলাদা। এক স্বগত কথনের চাল লক্ষ করা যায় কবিতাগুলোয়। যাকে তৎকালীন অনেকে ‘ব্যক্তিগত কবিতা’ ভেবে ভুল করেছেন।
ভাঙা-ঘরে, মস্ত একটা হাওয়ায়,
মানুষ কাঁপছে;
একটা হাত পাশের মানুষীকে
ধরে আছে, আরেকটা হাত
কোথায় রাখবে—বুঝতে পারছে না,
পায়রা এসে বসেছে নিমগাছে।
সামনে শুধু রুদ্র এক পাহাড়
সামনে এক প্রচণ্ড ঝামরানো
সমুদ্রের ক্লান্ত অন্ধকার।
আড়াল করে দেখে নেবার মতো
কোথাও আর গোপন দৃশ্য নেই;
মস্ত একটা হাওয়ায়, ভাঙ্গা-ঘরে,
মানুষ কাঁপছে।।
(মানুষ, ১৯৬১/সদর স্ট্রিটের বারান্দা)
বিষাদ, বিপন্নতা, বিষণ্নতা—প্রণবেন্দুদার কবিতার ভাষার সাথে সন্তর্পণে ওতোপ্রোতভাবে এগিয়েছে। তিনি পাঠকের সাথে কমিউনিকেট করছেন এক রকম বিপন্নতার ভেতর দিয়ে। মস্ত একটা হাওয়ায় মানুষ কাঁপছে। ভয়াবহ দাঁত খিঁচিয়ে আছে মানুষের অনিশ্চিত জীবন। সামনে রুদ্র পাহাড়, প্রচণ্ড ঝামরানো সমুদ্রের ক্লান্ত অন্ধকার। এমনই বিপন্নতায় সে তার পাশের মানুষীর দিকে মানে জীবনেরই দিকে বাড়িয়ে ধরে আছে হাত। জীবনের পায়রা জীবনের সুখ এসে বসে আছে নিম গাছে। সে দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু নাগালে আসছে না। ভাঙা ঘরে ঝড়ো বাতাস এসে এলোমেলো করে দিচ্ছে জীবন। সদর স্ট্রিটের বারান্দার প্রথম কবিতা। বিষণ্ণ মানুষের বিপন্নতার ছবি এঁকেছেন। মানুষ, ১৯৬১ কবিতার নাম। কিন্তু ১৯৬১ কেন? সময়কে, মহাকালকে যুক্ত করে দিলেন কবিতায়? পৃথিবীতে মানুষের ছবি জীবনের ছবি আবহমান কাল ধরে এই রকমই!
ভাষা, মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এক মানুষের সাথে আরেক মানুষের কমিউনিকেটের প্রধান মাধ্যম। আর এই জন্যই হয়তো কবিতা জরুরি, সাহিত্য জরুরি। একটা বিশেষ মাত্রায় লেখকরাই ভাষার অভিভাবক। কেননা, কবিতা, গল্প বা উপন্যাসই ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখে। সেইভাবে কবিতাকেও বাঁচিয়ে রাখে কবির নিজস্ব কাব্যভাষা। ভাষার ব্যবহার বৈচিত্র। আমরা জেনেছি, ইংরেজি ‘পোয়েম’ শব্দটি এসেছে গ্রিক ‘পোইন’ থেকে, যার মানে হচ্ছে ‘সৃষ্টি করা’। অর্থাৎ কবি হলেন স্রষ্টা। সেইসাথে দ্রষ্টাও। তিনি দেখেন এবং সৃষ্টি করেন। কবি, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত তাঁর আত্ম-আবিষ্কারের ভেতর দিয়ে কবিতায় ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে যান মানুষেরই কাছে।
খুব ভয়ে ভয়ে আমি
কবিতা লেখার দিকে চলে আসি।
এত ভীরু শিখা, তাকে
যে-কোনও জলের কাছে, যে-কোনও ঝড়ের কাছে
নিয়ে যেতে বড় দ্বিধা হয়,
যদি নিভে যায়, যদি তার
আঁধারে যাবার
কোনও অসুবিধা থাকে!
আমি কাকে যে বাঁচাবো, তাও
বুঝতে পারি না।
(আমি কবিতার দিকে/সদর স্ট্রিটের বারান্দা)
এই কবিতাটিতে ধীর লয়ে, লাইন ভেঙে ভেঙে এগিয়েছেন। প্রথমে, খুব ভয়ে ভয়ে আমি’তে এসেই ভেঙে দিয়েছেন। তারপর, শিখা’র পরে একটা কমা,—থামতে দিচ্ছেন পাঠককে। শিখাটাকে, তার ভীরুতাকে বুঝে নিতে দিচ্ছেন। কেমন ভীরু সে? যেকোনো জলের কাছে, যেকোনো ঝড়ের কাছে নিয়ে যেতে দ্বিধা হয় যদি নিভে যায় এমন। তাঁর ভেতরের আশঙ্কাকে, দ্বিধাকে, আত্ম-জিজ্ঞাসাকে দৃঢ়তার ভেতর কবিতায় স্থাপন করে দিলেন তিনি। আঁধারে যাবার’ পর লাইনটাকে আবারও ভেঙে আরও ডান দিকে সরে এলেন অসুবিধার আশঙ্কাটাকে নিয়ে। ঠিক তার পরপরই একটা সংশয়, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা। আমি কাকে বাঁচাবো, তাও বুঝতে পারছি না। কমার ব্যবহার, লাইন ভাঙা, স্পেস এই কবিতাটির ভাষাকে অনন্য করেছে। সদর স্ট্রিটের বারান্দা-র শেষ কবিতাটির নাম ‘সদর স্ট্রিটের বারান্দা’। আসুন কবিতাটি পড়ি—
বারান্দা, রেলিং সব কাছে ছিল;
আমি দাঁড়ালাম, আর
ভোর হয়ে এলো।
দেখলাম—
আর পাঁচজন বেশ সুস্থ, স্বাভাবিক,
চলার আদল যেন মূর্তিমান ছাঁচের আদল—
টান দিলে হাওয়ার ভেতর ভরে ওঠে।
শুনলাম—
মাতাল লোকটা নাকি মারধর করেনি মেয়েটিকে,
চটি উড়ে এসেছিল দৈবাৎ হাওয়ার জোরে
পাঁচিল ডিঙিয়ে,
আজ তার দু-নম্বর মেয়েটির কান্নার শ্রাবণ
এ পাড়ার সানাই।
বুঝলাম
যা কখনও ঠেকানো যাবে না,
তা এতোই একান্ত, সহজ,
তাকে নিয়ে জল্পনা করাও
যেন চোখ বেঁধে চলা।।
একটা কমার মাধ্যমে ‘বারান্দা’ আর ‘রেলিং’ ঘরের বাইরের একটা ছোট্ট ছবি মুহূর্তে চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা। তার বাইরে কী? সদর স্ট্রিট? এর পর হঠাৎ আছড়ে পড়ার মতোই ‘সব কাছে ছিল;’, একটা সেমিকোলন। একটা উন্মোচন। যা হয়তো খেয়াল করে দেখা হয়নি আগে। এখন এই যে এসে দাঁড়ালাম বারান্দায়, রেলিঙের গা ঘেঁষে, আর ভোর হয়ে এলো। সব পরিষ্কার হয়ে গেল। এতোক্ষণ যা অন্ধকারে ছিল, যা সম্পূর্ণ বুঝে ওঠার অপেক্ষায় ছিল, বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই, যেন সব রহস্যের সমাপ্তি হলো। বোধগম্যতায় চলে এলো সব। একটা করে লাইনের স্পেস রেখে তিনটা অংশে। দেখলাম। শুনলাম। এবং বুঝলাম। বুঝার শেষ পরিণতিটা আরও একটা লাইনের স্পেস দিয়ে এলো ‘যেন চোখ বেঁধে চলা’। কবিতা তো শুধু পড়ার বা শোনারই নয়। দেখারও। এই কবিতাটি সেটাই বলছে আমাদের। দেখতে দেখতেই জীবনের গূঢ় একটা সত্যতে এসে উপনীত হলাম আমরা। যা কখনো ঠেকানো যাবে না, তা এতই একান্ত, সহজ, তাকে নিয়ে জল্পনা করাও যেন চোখ বেঁধে চলা। দুটো দাঁড়ি দিয়ে কবিতাটি শেষ হচ্ছে। অবশ্য প্রণবেন্দুদার সব কবিতাই দুই দাঁড়িতে শেষ।
তুমি হও গহীন গাং, আমি ডুইব্যা মরি’’
মৈমনসিং গীতি থেকে সরে সরে হাওয়া কাছে আসে,
আর কোনও মৃত্যু যেন আমি আর ভাবতে পারি না—
কলকাতা শহর থেকে চোখ রাখি পাশের আকাশে।
প্রেম? না সমস্ত ঘৃণা? যা হয় তা হও, তুমি—তুমি,
অসমাপ্ত জল থামে অচ্ছোদ চোখের আড়াআড়ি;
আমি কি স্রোতের শ্যাওলা? কি বল হে গ্রাম বাংলাদেশ?
যদি ডাক দাও, তবে একবার ভেসে যেতে পারি।।
(বাংলাদেশ/ শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়)
নদীর টলমলে জলের মতোই তাঁর ভাষা। ওপরে কী স্নিগ্ধ! আর ঠিক তার অল্প নিচেই দৃঢ়, প্রত্যয়ী স্রোত। সন্তর্পণে এগিয়ে যায় মানুষের দিকে। পাঠকের মনে ও মননে জায়গা করে নেয় নিশ্চিত।
কবিতা ধারণা, কবিতা ভাবনা
শতভিষায় প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত বলছিলেন, ‘আমি কবিতা লেখার সময়ে সচেতন মনটাকে হারিয়ে ফেলি না, আধোঘোরের মধ্যে কবিতা লিখি। ঘোর শব্দটা সদর্থে ব্যবহার করতে হবে, আমি বলতে চাই তখন আমার নিবিষ্টতা এত বেশি তীব্র থাকে, কনসেনট্রেশন, যেকোনো কিছুই আমাকে তখন বিচলিত করে না। তখন আমার সচেতন মন আর অচেতন মন এর মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি কবিতা লিখি। যাতে আমার মনে হয় যে অনেকসময় অচেতনের অবচেতনের উদ্ভিদ উঠে আসে আমার কবিতায়।’ অনেকেই তাঁর লেখায় এক ধরনের দিব্য উদ্ভাসনের কথা বলেন। তিনিও স্বীকার করেন এক ধরনের আধ্যাত্মিক আয়তন আমাদের জীবনে আস্তীর্ণ হয়ে থাকে, যে বিষয়ে আমরা অনবহিত হবার ভান করি। গুরুগম্ভীর কোনো ব্যাপার নয়। খুব ছোট ছোট বিষয়েও এই আয়তন আকীর্ণ হয়ে থাকে। যেমন সন্ধ্বেবেলার কাক ছাদের কার্নিশে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে, তারপর নিস্তব্ধ নিরুদ্দেশের দিকে হঠাৎ ডানা মেলে দেয়; কিংবা শীতের দুপুরে একটা বিড়াল চকিতে পাঁচিল থেকে লাফ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, বিকেল-সন্ধের সন্ধিক্ষণে কাচের জানালার পর্দা সরাতেই অলৌকিক রঙে ভরে গেল ঘরের দেয়াল, পার্কে এক তরুণী তার প্রেমিকের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হেসে উঠল, রুমাল বিছিয়ে গাঢ়-সবুজ ঘাসের উপর বসে পড়ল, অথবা চলন্ত ট্রেন থেকে চোখে পড়ল, সাইকেলে চড়ে একদল যুবক উদাস রাস্তার আড়ালে হারিয়ে গেল;—এই ধরনের সমস্ত আপাত-তুচ্ছ, ছোট ছোট ঘটনায় কম্পমান হয়ে ওঠে অন্য একটি যবনিকা, আবরণ—যার আড়াল থেকে নির্গত হয় এক রকম রহস্যানুভূতি। এই অনিভূতিকেই কবি আধ্যাত্মিক বলছেন। এখান থেকেই তাঁর কবিতার উৎসার। কবিতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা তিনি খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর ‘কবিতা ও আমি’ গদ্যে। তাঁর মতে কবিতা ও সাহিত্য যত anthropocentric বা মানবমুখনী হবে ততই মঙ্গল। এই মানবমুখিনতার সাথে আধ্যাত্মিকতার বা ঈশ্বর বিশ্বাসের কোনো বিরোধিতা নেই। আধ্যাত্মিক অনুভূতি আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে। যেমন রবীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, আল মাহমুদ কিংবা ফ্রান্সের ক্লোদেল, ‘ফোর কোয়াট্রেটসের’ এলিয়ট। তবে, প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতার, আর এর ধারণার বদল বা পরিণতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর আমেরিকা প্রবাসের পর, যখন দেশে ফিরে আসেন, তারপর থেকেই তাঁর কবিতার এই বাঁকবদল। তিনি নিজেই বলেন, ‘আমার আগের কবিতার সাথে আমার সাম্প্রতিক কবিতার অমিল যেমন আছে তেমনই অনেক মিলও রয়েছে। বুদ্ধিগ্রাহ্য স্তরে বা আমার ভাবনাবলয়ে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে।’ সেই পরিবর্তনের ফল স্বরূপ তিনি কবিতা ভাবনার নতুন পথ তুলে ধরেন আমাদের সামনে। আবার ভাস্কর চক্রবর্তী বলেন, ‘—বিস্ময়ের ব্যাপার একটা, কোথা থেকে এলেন আমাদের প্রণবেন্দু? আমরা দেখি, রবীন্দ্রনাথ থেকে তিনি ততটাই দূরে যতদূরে তিনি বোদল্যের বা রিলকার। জীবনানন্দও তাঁকে ছুঁতে পারেননি কিছু। সমসাময়িক কৃত্তিবাসের তুমুল হৈ-হল্লা থেকেও তিনি দূরে। বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জন বেরিম্যান, এঁরা ছিলেন প্রণবেন্দুর মাষ্টার মশাই, তাঁদের উপস্থিতিও নজরে পড়ে না তাঁর কবিতায়। প্রায় সারা পৃথিবী জুড়ে যে অ্যান্টিপোয়েম প্রবলভাবে দাপিয়ে বেড়ালো, তাও তাঁকে স্পর্শ করলো না। তবে কি আমেরিকার রবার্ট ব্লাই, রবার্ট ক্রিলি, জেমস রাইটরা যেভাবে ভাবছিলেন একদিন কবিতাকে, তার একটা ছোঁয়া পেলেন তিনি?’ মনে হতে পারে, কিন্তু, ইশারাময় প্রণবেন্দু কোনো সঙ্কটাপন্ন কবি নন। তাঁর কবিতা মৃদু এবং স্পষ্ট। শান্ত আর অভিমানী। তিনি সঙ্কট পেরিয়ে যাওয়া মানুষ-নিসর্গে-মেশা পৃথিবীর দিকের কবি। কাছের জিনিসগুলো চিনিয়ে দিতে দিতে আমাদের বেশ খানিকটা দূরে নিয়ে যান। বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা এই দুই অনুভূতির পারস্পারিক টানাপড়েনে সৃষ্টি হয়েছে তাঁর অনেক কবিতা।
শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়, শুধু নয় ঘরের ভেতর পায়চারি,
কিন্তু যে বড়াব হাত সে আঙুল পুড়ে যাবে না তো?
কবিতা লেখার হাত আহার্য নেবার হাত প্রেম করবার গূঢ় হাত
সকল আঙুল যদি পুড়ে যায়, তা হলে কোথায়
অপ্রাপণীয়ের দাবি মেটাতে পারব এই কয়েক ঘণ্টার অবসরে!
(বিচ্ছিন্নতা/শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়)
পল ক্লে চিত্রকলা বিষয়ে মন্তব্য করতে যেয়ে বলেছেন, ‘it is a method of transforming quantity into quality’. প্রণবেন্দুর মতেও তাই। প্রত্যেক মুহূর্তে আমরা ঘটনা আর অভিজ্ঞতার দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছি। সেইসব অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নিচ্ছে কবিতা। কবি হচ্ছেন সমাজের সবচেয়ে সেনসিটিভ ইনস্ত্রুমেন্ট বা অনুভূতিশীল মানুষ। আপাততুচ্ছ ঘটনাতেও তিনি কেঁপে ওঠেন। কখনো বিচলিত হন, কখনো বা উদ্বুদ্ধ। তিনি বলেন, সর্বদাই একজন কবির অনুভূতি সক্রিয়। সবকিছুই অন্তহীন তরঙ্গাভিঘাতের মতো আছড়ে পড়ছে তার হৃদয়ে, অস্তিত্বে। কবি মানেই ‘হোল টাইম পোয়েট’ আর কবিতা লেখা তার ‘হোল টাইম জব’। তবে আরও দশ জনের মতো তাকেও জীবিকার জন্য অফিসে যেতে হয়, বাজার করতে হয়, তাকেও ডাক্তারের কাছে যেতে হয়, খেলাধুলা রাজনীতি প্রভৃতি নিয়ে আড্ডা দিতে হয়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে প্রায় গোপনে, অন্তঃশীল ফল্গুর মতো তার কবিতা চর্চার স্রোত প্রবাহিত হয় সবসময়। তার স্বরচিত মগ্নতায় তিনি আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন সর্বদা। আপ্লুত হয়ে থাকেন। তাই প্রণবেন্দুর মতে একজন কবি যখন জুতোর ফিতে বাঁধেন, তখনো তিনি কবি। তাঁর সুকুমার নিভৃত সত্তাটিকে তিনি যথাসাধ্য গোপন করে রাখেন, সমাজের ব্যবহারযোগ্য বা ব্যবহারোপোযোগী কোনো মুখোশ, তাকে পরে থাকতে হয় কখনো কখনো। হয়তো বা অধিকাংশ সময়।
তাঁর কাছে, কোনো কবিতার কবিতা হয়ে ওঠার প্রধানতম শর্ত তার অনুভূতিগ্রাহ্যতা। আবেগ, মনন, দক্ষতা, কোনো কিছুকেই তিনি অস্বীকার করেন না—কিন্তু শব্দপুঞ্জ যদি অনুভূতিগ্রাহ্য না হয়, তাকে তিনি কবিতা বলতে না রাজ। কবিতা নিঃসন্দেহে আবেগ ও মননের মিশ্রণ। মনন বেশি হলে কবিতা মননধর্মী হয়, আবেগের মাত্রা চড়লে তা হয় আবেগ-প্রধান কবিতা। কিন্তু তা যদি আমাদের অনুভূতিকে স্পর্শ করতে না পারে, তাকে সঞ্জীবিত করতে না পারে, তাহলে তা, আর যাই হোক, কবিতা নয়। অন্তত প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের এমনই ধারণা।
দীর্ঘ কবিতা বলতে গেলে তেমন লেখেননি তিনি। আবিষ্কার-উন্মুখ ফরাসি পাঠকের কাছে যিনি ‘শুদ্ধ করে দিয়েছিলেন গোষ্ঠীভাষা’, অর্থাৎ কবিতার বয়ান—বোদল্যের, মালারমে ও তাঁদের সতীর্থদের কাছে যাঁর থেকেই কবিতার পৃথিবীর শুরু, সেই এডগার অ্যালান পো একবার বলেছিলেন, ‘A long poem is flat contradiction in terms.' প্রণবেন্দুদাও এমনটাই ভাবতেন। মনে করতেন, দীর্ঘ কবিতায় একটা ছোট কবিতাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড়ো করে দেয়া হয় বা দীর্ঘ কবিতা কেবল কয়েকটি ছোট কবিতার যান্ত্রিক সংযোজন মাত্র। তিনি মিতকথনে বিশ্বাস করতেন। দীর্ঘ কবিতার চর্চা তাঁর ধাঁতে ছিল না। আবার তিনি এও মনে করতেন, কবিতা অঙ্কশাস্ত্র নয়, যে তার একটিই অমোঘ অর্থ হওয়া সম্ভব। কবিতায় অর্থ ও ব্যঞ্জনা নানাস্তরে বিস্তীর্ণ ও হিল্লোলিত হয়ে থাকে। তার শরীর থেকে একাধিক তাৎপর্যের অভিঘাত একই সঙ্গে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। তাছাড়া, কবিই যে তার কবিতার শ্রেষ্ঠ বোদ্ধা ও সমালোচক, তা-তো নয়।
ভেতরে ভেতরে জ্বলে যাচ্ছে, অথচ বাইরে ছাই জমছে না
এই আমার চুরুট—
একে তোমরা লক্ষ কর
(আমার চুরুট/হাওয়া স্পর্শ করো)
তবে, কবি মাত্রই কখনো কখনো কবিতার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তখন না লিখে তার উপায় থাকে না। অযথা বিরক্ত করে তার রচনা কিছু দিনের জন্য থামিয়ে দেখা যায় মাত্র। চারপাশে যদি তীব্র আলোড়ন চলতে থাকে, তখন অনেক সময়ই কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে না। কবিতা লেখা নিঃসঙ্গ মানুষের সামাজিক কাজ। প্রণবেন্দুদা বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা ও বেদনা অনুভব করেন এবং তাঁর কবিতার ভেতর দিয়ে এই বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেন। তিনি লাইট এন্ড শেড ইউজ করেন। আর একটা জিনিস হলো অ্যামবিভ্যালেন্স, কোথাও আলো পড়ছে, কোথাও অন্ধকার পড়ছে। তিনি এর ভেতর দিয়েই তাঁর চারপাশ নিয়ে কথা বলেন। কোনোটাই পুরোপুরি অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়, আবার বলা যায় না কোনোটা পুরোপুরি আলোকিত। হতে পারে, নাও হতে পারে। এই দোলাচলতায় এগিয়েছে তাঁর কবিতা।
এবং মুশায়েরা পত্রিকার কবি ও কবিতা সংখ্যায় (১৯৯৮) নিজের নতুন কবিতা নিয়ে কবিতা ভাবনা নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, ‘আমার কবিতা বিষয়ে পাঠকমহলে দুটো ধারণা আছে। এক মগ্ন অন্তর্মুখী; আর সাম্প্রতিক কবিতা থেকে আলাদা—অনেকাংশে সমাজমুখী। প্রথম দলের কথাই বহুলাংশে সত্য। মগ্নতা ও অমগ্নতার মধ্যে একটা সাযুজ্য আনার চেষ্টা করে চলেছি আমি। আমার সাম্প্রতিক কবিতা হয়তো ঈষৎ তির্যক যা আগের কবিতায় ছিল না।’ এই মগ্নতা আর তির্যকতা নিয়েই সবার অলক্ষ্যে আট বছর ধরে তৈরি হয়ে যাচ্ছিল তাঁর শেষ কবিতাবই ‘রৌদ্রের নখরে’।
এর কিছু কাল আগে ৯০ দশকের শুরুর দিকে লিখা হচ্ছিল তাঁর ‘বাধা পেরোনোর গান’-এর কবিতাগুলো। কবিতার বাইরে থেকে ঘনিয়ে আসা কতরকমের বাধা আর উদ্বেগ থেকেই একটা কোনো প্রতিরোধ, প্রতিবাদের কথা ভাবছিলেন প্রণবেন্দু। তাঁর ‘বাধা পেরোনোর গান’ হয়ে উঠল সেই নতুন রকম কবিতা ভাবনার দলিল। সেই সময়কার কবিতা পরিবেশ আর তাঁর কবিতা ভাবনা নিয়ে অলিন্দ পত্রিকায় লিখে যাচ্ছিলেন বেশ কিছু কবিতা-কথাও।
একজন কবি প্রচার যন্ত্রের আনুকূল্য পান তখনই যখন তিনি যা লিখেছেন তা বাজারে চলে।
(অলিন্দ/শারদ ১৩৯৬)
কবিতাকেই শুধু সমাজ সচেতন হতে হবে তাই নয়, সমাজকেও হতে হবে কবিতা সচেতন।
(অলিন্দ/ শরৎ ১৩৯৭)
...কিন্তু সাময়িকভাবে জনপ্রিয় হতে পারেন কেউ কেউ—যিনি দশ বছর আগে জনপ্রিয় ছিলেন তিনি এখন হয়তো জনপ্রিয় নেই, কিংবা যিনি এখন কবি হিসেবে জনপ্রিয় তিনি দশ বছর পরে হয়তো জনপ্রিয় থাকবেন না। যিনি সারা জীবন নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা, এবং মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের কামনা করে কবিতা লেখেন তিনি কখনোই জনপ্রিয় হতে পারবেন না—যদিও গুণগ্রাহীদের কাছে তিনি আদৃত হবেন, খ্যাতিও জুটতে পারে একটু আধটু, প্রভাব প্রতিপত্তিও কিছুটা হতে পারে। পাঠক বা সম্মেলনের শ্রোতাদেরও দোষ দেয়া যায় না—তাৎক্ষণিকভাবে কানের ভিতর দিয়া তাঁদের মরমে পশে না সেই কবিতা তাঁদের ভালো লাগবে কেন? তাহলে কবিতার প্রকৃতিই জনপ্রিয়তা বা অ-জনপ্রিয়তার নির্ধারক। পাশ্চাত্যের সব দেশেই কবিতা শোনার পরে কবি সম্মেলনে শ্রোতারা করতালি দেন (তাও একেবারে শেষে), তা পাঁচজন কবিই হোক আর দশজন কবিই হোক। কলকাতা শহরের কবি সম্মেলনে কবি হিসেবে যাবার সুবিধে অসুবিধে দুটোই আছে—সুবিধে এই যে, শ্রোতাদের কবিতা ভালো লাগলো বা লাগলো না, তা সঙ্গে সঙ্গে জানা যায়, অসুবিধে এই যে, কোনো বিখ্যাত কবিও যখন পাঠান্তে মৃদু করতালি পেয়ে চলে যান, তখন—আর কিছু নয়—ঈষৎ ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা হয়। শুধু কবি সম্মেলনে করতালি নয়, কবিতার বইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ও এই কবিতার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। ঈষৎ উত্তেজনা, একটা গল্প, উপচীয়মান আবেগ, নাটকীয়তা, এই সমস্ত গুণ কবিতায় থাকলে তা সঙ্গে সঙ্গে আদৃত হয়, এবং তার সঙ্গে যদি যুক্ত হয় সাংবাদিকতা। আরেকটি বিষয় আমি এখনো উল্লেখ করিনি—তা হলো রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ। যিনি মূলত একাকী এবং নিজেকে যোগাযোগ করতে চাইছেন সবার সাথে, তাঁর কবিতা প্রতিক্রিয়াশীল নাও হতে পারে। কিংবা একেবারেই তা নয়। একাকী মানে এই নয়, তিনি মানুষজনকে চেনেন না, বা তাঁর কোনো প্রভাব প্রতিপত্তি নেই, কিন্তু কবিতা লেখবার মুহূর্তে তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ, তাঁর সামাজিক মুখোশ তখন খসে গেছে, তিনি আবার যুক্ত হতে চাইছেন সেইসব মানুষের সঙ্গে যারা ভালোবাসায় ঘৃণায় তাঁর অনুভূতির অধীন হতে পারেন। তরুণ কবিরা অনেকে হয়তো জানেনও না ওপর থেকে কারা দড়ি নাচাচ্ছে, তাঁরা অনেকে ভালোবাসার যোগ্য, অনেকে ঘৃণার্হ।
আমাদের ক্ষণকালের জীবদ্দশায় খুব দ্রুত ঘটে যায় সব কিছু—কবিতা লেখা, জনপ্রিয় হওয়া বা না হওয়া, প্রচারিত হতে পারা বা না পারা, সব কিছুই। তবু একজন প্রবীণ কবির উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলব—কবিতা লেখাই কবির একমাত্র কাজ, অন্য কিছু নয়। কোনো বুদ্ধিমান কবি মাঝে মাঝে ভাবতে পারেন, তিনি একেবারে বোকা হয়ে গেছেন, কোনো সাদামাটা কবির সাফল্যেও অনেকে তাঁকে খুব বুদ্ধিমান ভাবতে পারেন।
পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার ক্রমিক হচ্ছে ৩১%, তার মধ্যে আমি কোথায় যেন পড়েছিলাম সাহিত্য পাঠকের ক্রমিক হলো ৫%, আর কবিতা পাঠকের ক্রমিক ১% বা তারও কম। এই ১% এর বাইরে যারা সাক্ষর বা শিক্ষিত অথচ কবিতার কিছুই বোঝেন না, তাঁরা যখন পদ্মবনে মত্ত হস্তীর মতো প্রবেশ করেন তখনই নানাবিধ অসুবিধা দেখা দেয়। পশ্চিমবঙ্গে অনেক তরুণ কবি এখন কবিতা লিখছেন, তাঁরা এ-বিষয়ে অবহিত হন।
(অলিন্দ/শীত ১৩৯৮)
বিখ্যাত কবি শ্রী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাথে আমি একমত যে “এখন কবিদের, আমাদের দেশে, টাকার দরকার—তোমার এই মোক্ষম কথাটা স্বীকার করতে আমার অনেকদিন লেগেছে (সামসুল কোথায় এবং কেন এই মোক্ষম কথাটা লিখেছেন, তা আমি আজও জানি না। নিশ্চয়ই কোথাও লিখেছেন বা বলেছেন, না হলে সুভাষদা লিখবেন কেন?) এমনকি নাজিম হিকমত আর পাবলো নেরুদা জোর দিয়ে এ কথা বলার পরেও।” হিকমত আমার ততটা পড়া নেই তবে নেরুদার সমস্ত লেখা পড়ে আমি আমার না-চোখে পড়া তাঁর এই উক্তিকে মিলিয়ে নিতে পারছি না। অবশ্য যে মার্ক্সবাদে সম্প্রতি লুকাচের সঙ্গে হোলৎসের কথোপকথন পড়ে (ইংরেজিতে নাম Conversations with Luka’cs—থিয়ো পিংকাসের সম্পাদিত, ইংরেজি সংস্করণ Merlin Press, ১৯৭৪) আমি বহুলাংশে আকৃষ্ট হলাম, তার একটি সূত্র হলো যেটুকু কাজ আমরা করি তার জন্যে পারিশ্রমিক দাবি করা অন্যায়? কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে “নক্ষত্রের রাত” এর মতো পত্রিকায় সুভাষদা যে চিঠি পাঠিয়েছেন ১৮.৬.৯২-তে, যার সম্পাদক আমার প্রিয় কবি সামসুল হক, তার পত্রিকাটিকে তো আমরা ছোট ম্যাগাজিনই বলব? তাঁরা কীভাবে টাকা দেবেন লেখকদের, আমার বুদ্ধিতে ঠিক আসছে না। ছোট ম্যাগাজিনেই নির্মিত হচ্ছে এমন সব কবিতা, যা আকারে ছোট হলেও (বা পত্রিকাটিকে আমরা অন্যান্য যে কোনো দেশের মতোই ‘লিটিল ম্যাগ’ বলি) গুণগতভাবে ছোট নয়—এ তো অপ্রতিষ্ঠানের এক প্রতিষ্ঠিত সত্য।
জনপ্রিয়তাও এক ধরনের মূল্যবান মূল্য, প্রচার যেমন, তার চেয়েও অনেক বেশি অমূল্য—কিন্তু আরেক ধরনের মূল্য তো সামসুলের মতো আরও অনেক অ-জনপ্রিয় কবিই পেয়ে থাকেন—হয়তো নগদ বিদায়, অন্তত “বিদায়” নয়, লেখা না থামানো পর্যন্ত।
(অলিন্দ/শীত ১৩৯৯)
কবিতামোচ্ছবে যারা দলে দলে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের নানা ধরনের মুখনিঃসৃত শব্দ কানে আসছে। ভালোই লাগছে। তবে সাধারণ শিক্ষিত বলে যে বাকবন্ধটি চালু আছে, তাঁরা কবিতা বোঝেন না বলে সরাসরি জানিয়ে দেন। বিষয়টি এখানেই শেষ হলে ভালো হোতো, কিন্তু তা যে হবার নয়। প্রতিটি মানুষেরই (শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সাধারণ বা অসাধারণ মানুষ, যেমনই হোন) কবি বলতে একটি ধারণা আছে, যা মার্কসীয় ধারণার সাথে ঠিক মেলে না। সাধারণ মার্ক্সবাদী বলে যদি কোনো কথা হয়, তাহলেই এই অভিধাযুক্ত ব্যক্তিও কবি বলতে পরশপাথর খোঁজা কোনো খ্যাপাকে বুঝবেন। কবির যে অন্য কোনো শ্রমিকের থেকে স্বতন্ত্র কোনো ভূমিকা নেই, এটা হয়তো তিনিও স্বীকার করবেন না। এক হিসেবে সত্যিই নেই, আরেক হিসেবে আছে। নেই এজন্য যে, কবিতা লিখতে হলেও কথঞ্চিৎ পরিশ্রম করতে হয় (লেখবার সময়টুকু বলছি না, পিকাসোর গারতুদ স্তাইনের মাথাটি আঁকবার গল্পের মতো। ‘মাথা আঁকতে আর কতক্ষণ লাগবে?’ এই বিখ্যাত উক্তির কথা ভাবতে পারি এ প্রসঙ্গে) আর কবির ভূমিকা ঈষৎ স্বতন্ত্র এইজন্যেই যে তিনি তাঁর শ্রমের মূল্য পান না সর্বদা, এবং তাছাড়াও তাঁর মনে হয় যে তিনি মানুষের মন বদলের একটা কিছু আবহাওয়া তৈরি করেছেন, যা অন্যেরা সহজে পারে না।
কবিতামহোৎসব বা মোচ্ছব একটি সামাজিক সংকীর্তন—তাতে একটু আধটু তো শব্দ হবেই। আমিও তো নিঃশব্দে এই কথাটা বলতে পারলাম না। ঈষৎ শব্দ হল কোথাও। তবে দলে দলে আমরা যোগ দেব কিনা, সেও জোর করে বলা যায় না।
(অলিন্দ/গ্রীষ্ম ১৪০০)
ছন্দ চেতনা, ছন্দ ব্যবহার
বাংলা ভাষা কানে না এলে আমার ভেতরের কবিতা লেখার যন্ত্রটা অকেজো হয়ে যায়। প্রণবেন্দুদা বলছিলেন। বাংলা ভাষার অন্তঃস্পন্দে বা rhythm যথেষ্ট পরিমাণ কানে না এলে আমি বাংলা ভাষায় কবিতা লিখতে পারি না। হ্যাঁ, তাই হয়েছিল। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত যখন তিনি আমেরিকা প্রবাসী ছিলেন তখন সেই চার বছরে মাত্র চার/পাঁচটি কবিতাই লিখতে পেরেছিলেন। তিনি মূলত পয়ারে ও গদ্যছন্দেই কবিতা লিখেছেন। পয়ারকে মাঝেমধ্যে ঈষৎ ভেঙে দিয়েছেন, এই পর্যন্ত। তাঁর কাছে মনে হয়েছিল তিনি যা বলতে চান, যেভাবে বলতে চান তার জন্য এই ছন্দবন্ধটিই সবচেয়ে স্বস্তির। তবে স্বরবৃত্তেও অনেক কবিতা লিখেছেন। মাত্রাবৃত্তেও।
সমস্ত ঝর্নার জলে
তুমি কিরকম যেন চাবি ঘুরিয়েছ,
মাঝে মাঝে থেমে যায়,
আবার ঝর্ঝরস্বরে পাথরে গড়ায়;
জল খসে পড়ে।
তুমি কি কিছুই আর
সহজ অঙ্ক দিয়ে
পারবে বোঝাতে। বুকের ভেতরে
কেন দাগ পড়ে। বুকের ভেতরে
কে রাধা, কে কৃষ্ণ হবে
এই নিয়ে গোলযোগ বাড়ে,
আমার ঝর্নার জলে, তোমার
হাতের বোনা তাঁত বেজে ওঠে।
(প্রেমিকাকে ৪/ সদর স্ট্রিটের বারান্দা)
‘আমি সব কবিতাই ছন্দে লিখি। গদ্যে মাত্র কয়েকটি কবিতা লিখেছি, ছন্দ বলতে যদি মাত্রাবৃত্ত বোঝাও বা অক্ষরবৃত্ত বোঝাও বা ছন্দ এবং মিল বোঝাও, তো আলাদা কথা।… তা যদি বলতে চাও, আমি একটা নিজস্ব ছন্দ, একাটা প্রবহমান পয়ার আবিষ্কার করেছিলাম। নিজের কণ্ঠস্বরের একটা অন্তঃস্পন্দময় প্রক্ষেপ ঘটে, এটা অনেক কবির ক্ষেত্রেই ঘটে। আমার ক্ষেত্রেও ঘটেছে বলেই আমার ধারণা। ছন্দটা আমি আমার নিজের গলার প্রকৃতি অনুযায়ী বানিয়ে নিয়েছি। এখনো মাঝে মাঝে পাঁচ মাত্রার কবিতা লিখি। আসলে ছন্দটা কখনো কখনো প্রকট, প্রত্যক্ষভাবে থাকে, কখনো প্রচ্ছন্ন, গোপনভাবে। আমি এই প্রচ্ছন্ন ছন্দে বেশি কবিতা লিখেছি।’ শতভিষায় তাঁর কবিতার ছন্দ নিয়ে এই কথাগুলোই বলছিলেন তিনি। আবার ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয় ‘তিনটি কাব্য নাটিকা’। এ নিয়ে এবং মুশায়েরা পত্রিকায় তিনি আমাদের জানান, ‘কাব্য নাটিকায় আমি ছন্দ নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা করেছি। ছন্দ শুধু নয়, ব্যঙ্গ, পরিহাস, বাক-ব্যবহার, নানা রকমের ইশারা-ইঙ্গিতে মনের এক অজানা ভাণ্ডার হয়ে আছে। কতরকমের উক্তি, শব্দ ব্যবহার রয়ে গেছে। যেখান থেকে খুলে যেতে পারে পরবর্তী কবিতায় পৌঁছানোর রাস্তা।’
অমিয়।। ফোটে ফোটে, ফোটে,
ওগো, পুকুরে ফুল ফোটে।
রক্ত তিলক পরে আছি
কেন যাব গোঠে?
শ্যামল।। এক পায়ে আমিও আছি খাড়া
সা—রা—রা—রা—রা—রা,
আমাদের দেবে এখন কারা পাহারা।
এক পায়ে আমিও আছি খাড়া।
ইন্দ্রাণী।। আমায় তবে হতে হবে স্বয়ংবরা নাকি
বলে দে না, কাকে নেব, অচিন দেশের পাখি।
ভেতর থেকে কী যেন আজ করছে ডাকাডাকি।
আমায় হতে হবে আবার স্বয়ংবরা নাকি।
ভবভূতি।। ফাঁকি, ফাঁকি, ফাঁকি।
বন্ধ করে দেব আমি
সমস্ত চালাকি।
(বীজ/কাব্য নাটিকা)
জীবনশৈলী, জীবনবোধ
With age, art and life blend into one. শেষ বইয়ের প্রবেশক হিসেবে তাঁর প্রিয় শিল্পী ব্রাক-এর এই উক্তিটি ব্যবহার করেছেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। বলেছেন, ‘আমার জীবনশৈলী আর জীবনবোধই আমার কবিতাকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করেছে সবসময়।’ তিনি সাধারণত চারপাশের জীবন থেকেই কবিতার উপকরণ, চিত্রকল্প, উপমা ইত্যাদি আহরণ করতেন। কেননা, কবিতা জীবন থেকেই সবকিছু নেয়, আবার জীবনকে ফিরিয়েও দেয় তার ফলশ্রুতি। কবিতার ভেতরদিকের ভূগোলে অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার আবিষ্কার ঘটে। এই অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা মানে আজগবি ঘটনা নয়—এমন কোনো অভিজ্ঞতা যা অনেক ভেতর থেকে উঠে এসে আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব সঞ্জীবিত করে। প্রত্যেক কবিরই নিজস্ব জগত থাকে, সাইকেল থাকে, ঘর গেরস্থালি থাকে, আরও অনেক কিছু থাকে, leitmotif থাকে। এর মধ্যে নিজস্ব পৃথিবীটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেটা জীবনবোধে পরিপূর্ণ থাকে। যে শিল্প বা কবিতা আমাদের জীবনবোধকে একই সঙ্গে আলোকিত ও বিস্তৃত করতে পারে না, তাকে মহৎ শিল্প বা মহৎ কবিতা বলা যায় না। রেক্সরথ বলেছিলেন, The greatest poetry cannot redeem an obnoxious creed and an unpleasant dispose. শিল্প বা সাহিত্যে বা মানুষের যেকোনো রূপময় অভিব্যক্তিরই মূল কেন্দ্র হলো মানুষ। আমরা কবিতা বা উপন্যাস রচনা অথবা যে ছবিই আঁকি না কেন আমাদের প্রধান দায়িত্ব হলো মানুষকে স্পর্শ করা, মানুষের চেতনার উন্মীলন ঘটানো। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত কখনো রাজনীতি করেননি। কারণ তাঁর ধারণা ছিল রাজনীতিবিদরা মানুষকে ‘thing’ বা ‘abstruction’ হিসেবে দেখেন। এবং সেটাই তিনি মানতে পারেননি। রেক্সরথের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, we react to things and we respond to persons, in the arts we respond to the living communication of a person, no matter how long gone the artist may be. তাই শিল্পের জন্যই শিল্প—এই তত্ত্বে এখন আর মন ভরে না। আপ্তবাক্যের মতো শোনাতে পারে যদিও, তবে এ কথাই ঠিক যে জীবনের জন্যেই শিল্পের অস্তিত্ব বা জীবনের জন্যেই শিল্প।
প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের প্রথম কবিতার বই “এক ঋতু” তে অনেক বাসনা-বিধৃত, প্রেমের কবিতা ছিল। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ সদর স্ট্রিটের বারান্দা-তে ‘প্রেমিকাকে’-এই সিরিজে অনেক কবিতা আছে। তবে হ্যাঁ, এই বই থেকেই তাঁর জীবনদৃষ্টি স্পষ্ট হতে থাকে পাঠকের কাছে। স্পষ্ট হতে থাকে তাঁর জীবনবোধ সরাসরি মানব-ভাবনার সাথে সম্পর্কিত। ভাস্কর চক্রবর্তী আমাদের মনে করিয়ে দেন, ‘আমাদের এই সময়টা আমাদের চারপাশে একটা ছাইয়ের পাহাড় ছড়িয়ে দিয়েছে। দেখা, পথ চলা, আমাদের কথা বলা পর্যন্ত প্রায় একটা অসম্ভাব্যতার কাছে এসে পৌঁছেছে। এই ছাই, এই অর্থহীনতার পাশে আমরা সকলেই কম বেশি কাত হয়ে আছি। তবু, এই ছাই-ই তো শেষ কথা নয়। প্রণবেন্দু দাশগুপ্তকে দেখি এই ছাই সরিয়ে-সরিয়ে, কী সাবলীলভাবে, কী ব্যস্ততাহীন, কী শান্ত, কী নিশ্চিতভাবে এগিয়ে চলেছেন, আর লিখে রাখছেন যা-কিছু, শেষ পর্যন্ত তা বোধহয় আমাদের বাংলা কবিতার চিরকালীন একটা গর্বের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো।’
কবিতার শিকড় যদি জীবনের আরও নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে লেখাই ভালো। তীব্র সময়, তীব্র স্বর আলোড়ন, না লেখার ইচ্ছে আর জীবনের নানা দিকে ছড়িয়ে পড়া কবিতা, শিকড়-বোধ আর কবিতা আক্রান্ত মনের আকাশ টানে লিখা হয়েছিল তাঁর পরবর্তী কবিতাবই নিজস্ব ঘুড়ির প্রতি এর কবিতাগুলো। ১৯৭৫ সালের মার্চে প্রকাশিত হয় এই বই। অবশ্য রচনাক্রমের দিকে খেয়াল করলে বুঝা যায় পরবর্তী বই ‘শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়’ এর কবিতাগুলো অপেক্ষাকৃত আগের। তবে, পত্রিকায় প্রকাশের সূত্র ধরে বলা যায় এই সময়টাতেই তাঁর তিনটি কবিতা বইয়ের কবিতা পাশাপাশি তৈরি হয়ে উঠছিল। তিন রকম উৎসারের ভেতর দিয়ে সাজিয়ে নেয়া হয়েছিল এদের। কারণ তাঁর কবিতাবইগুলো প্রত্যেকটি কোনো না কোনো থিমাটিক প্রি অকুপেশন থেকে গড়ে উঠত। ‘নিজস্ব ঘুড়ির প্রতি’ এর কবিতাগুলোয় ‘ঘুড়ি’, ‘নাটাই’, ‘সুতো’ শব্দগুলো বারবার এসেছে। তিনি এই বইয়ে প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব একটা জগতের কথা বলেছেন। ‘নিজস্ব’ কথাটির একটা মানে পাওয়া যায় এখানে।
লাল ঘুড়ি বুকের ওপরে ঠেকে যায়।
তুমি কোন দিক থেকে সুতো পাঠিয়েছ?
তোমার রঙিন ঘুড়ি, হে কিশোর,
আমি আজ ফেরত দেব না—
ছাতে গিয়ে ওড়াবো আকাশে।।
(রবিবার/ নিজস্ব ঘুড়ির প্রতি)
আমিই সব তদারকি করছি; আমার ঘুম এখন ভেঙে গেছে
আমি আজ স্বাধীন, নিশ্চিন্ত।
ডালপালার মতো, শিকড়ের মতো পৃথিবীর সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে যাবো এখন,
আমার উৎসর্জন তোমরা লক্ষ কর—লক্ষ কর
(তোমরা লক্ষ কর/ নিজস্ব ঘুড়ির প্রতি)
‘মানুষের পাশ থেকে সরে যায় সঠিক মানুষী,/ ভাষা না-শেখার জন্য, ভাষা না-জানার জন্য/ শুধু ভাসাভাসা’ (এই সেই জায়গা/ শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়)। ১৯৭৬ এর জুলাই মাসে প্রকাশিত হয় এই বই। যে অস্থির সময়ের ভেতর দিয়ে মানুষ যাচ্ছিল তখনকার সেই অস্থিরতার ভেতর দিয়েই যে বিচ্ছিন্নতাবোধ কাজ করছিল একের সাথে আরেকের সেই বিচ্ছিন্নতাটুকুই শেষ কথা নয়। তবে এই অস্থিরতার কথাটুকুও জোরেশোরে নয়, খুব শান্ত, নিস্তরঙ্গ ভঙ্গিতে এসেছে। প্রণবেন্দুদা নিঃসঙ্গতা প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা ও বেদনা আমি অনুভব করি, এবং আমার কাব্যচর্চার মাধ্যমে তা অতিক্রম করার চেষ্টা করি। আধুনিক মানুষ কেন বিচ্ছিন্ন বা এলিয়েনেটেড সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত আছে। একই সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবোধ, এবং তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা – এই দুই অনুভূতির পারস্পারিক টানাপোড়েনে তৈরি হয়েছে আমার অনেক কবিতা।’ শুধু বিচ্ছিন্নতা নয় বইটির মূল সূত্র ছিল সময় মানুষ আর সমস্ত দেশটার সঙ্গে শুধুমাত্র কবিতা দিয়েই একটা যোগাযোগ তৈরি করা। তিনি চেয়েছিলেন কোলাহলের মধ্য থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে আরও নিয়মিত জায়গায় পৌঁছে যাওয়া যায় কিনা। we live a long time, and God knows it is love we need.
সরে যেতে গিয়ে দেখি, এখনও আড়াল থেকে
আলো ঝরে গাছের ওপর,
(সরে যেতে গিয়ে/শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়)
শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়, শুধু নয় ঘরের ভেতর পায়চারি,
কিন্তু যে বাড়াবে হাত সে আঙুল পুড়ে যাবে না তো?
(বিচ্ছিন্নতা/শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়)
কে কাকে ফিরিয়ে দিলে?
আলো চলে এলে কিন্তু, তোমার নিজের আয়না তোমাকে তাড়াবে।।
(কে কাকে/শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়)
ধারাবাহিক অন্তরদহনের অনুভব নিয়ে ১৯৭৭ এর জুন মাসে এসে প্রকাশিত হলো ‘হাওয়া স্পর্শ করো’। অদৃশ্য, স্নিগ্ধ এক স্পর্শ প্রত্যাশার বই। জীবনের বা চারপাশের জটিলতাকে পরিশোধন করে, নিজস্ব অনুভূতির সমানুপাতিক নির্যাসটুকু ছেঁকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এই বইয়ের কবিতাগুলো। জটিলতাকে অস্বীকার না করেও, তার ভেতর দিয়ে গিয়ে তাকে অতিক্রম করার বোধ রয়েছে এখানে। মিনিমাল পেইন্টিং বলে একটা কথা আছে। মানে হচ্ছে সমস্ত বর্জন করে করে গড়ে ওঠা। সবকিছুর বাইরের আবরণ ছিঁড়ে ফেলে ভেতরের অন্তঃসারে পৌঁছানোর একটা চেষ্টা।
এত হইচই, এত আলো, রেস্তোরাঁয় এত ফুলঝুরি—
তবু মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ
ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসে।
(অর্থহীন/হাওয়া স্পর্শ করো)
মানুষ এসেছে, তার দুই চোখে স্বপ্ন নেই আজ,
তুমি লিখে যাও, তুমি স্পষ্ট লিখে যাও—
(তুমি লিখে যাও/হাওয়া স্পর্শ করো)
এর পরপরই ১৯৭৮ এর নভেম্বরে এলো ‘মানুষের দিকে’। প্রণবেন্দুর বইগুলো একেকটা জীবনদৃষ্টি নিয়েই যেন এগোয় কোনো অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে। তিনি তো বলেইছেন কবিতা যতো মানবমুখনী হবে ততোই মঙ্গল। এর সাথে কারো কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। এই মানুষ কোনো রাজনৈতিক মানুষ না। সাধারণ মানুষ। যে মানুষকে আমরা চিনি বা জানি। শুধু মানুষ বিষয়ে চিন্তা নয়, তাদেরকে ভালোবাসা ও বোঝার চেষ্টা নিয়ে বিশেষ মনন ও অনুভূতি থেকে উৎসারিত হয়েছে এই কবিতাগুলো।
ক্রমশ আমার সব মনে পড়ে যায়
ক্রমশ আমার বুকে ভাঙা-নৌকো এসে জোড়া লাগে,
মাতাল সমুদ্র এসে বুনে যায় বেটোফেন তীরের শরীরে,
তুমিই কি তুলেছিলে হাত? মনে পড়ে, সব মনে পড়ে…
মনে হয়, মানবজন্মে এসে ভালো হল, খুব
ভালো হল।।
(মনে পড়ে/মানুষের দিকে)
যাব, ঘরে যাব।
বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস সমস্ত অরণ্যে খেলা করে।
কোথাও কি আলো জ্বলে? কারা জ্বালে?
কে আছে ওখানে?
আছে কি মানুষ, যারা ভালোবাসে, ঘৃণা করে, বাঁচে?
(ঘরে যাব/মানুষের দিকে)
ভেতর এবং বাহির বলে আলাদা কিছু নেই। তবে, অন্য এক জমির কথা আছে পরের ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত ‘অন্ধপ্রাণ জাগো’ বইটিতে। ‘দ্যাখো, আমি সুখ দুঃখ দুহাতে সরিয়ে/ অন্য এক জমিতে এসেছি।’ (সুখ দুঃখের পর/অন্ধপ্রাণ জাগো)। এইখানে এসে কবি যে বোধের কথা বলছেন, তা হলো, সমকালের বোধ। সমকালের স্রোতোধারায় ভেসে ভেসে বেঁচে থাকা ছাড়া কোনো গত্যান্তর নেই আমাদের। ভালোবাসা আর চেতাবনির ভেতর থেকেই কথা বলেছেন বারবার তাঁর ‘অন্ধপ্রাণ জাগো’ বইতে।
এর পরের বিশ বছরে আরও চারটি মৌলিক কবিতাবই বেরোয়। আর শ্রেষ্ঠ কবিতা ১৯৮৭তে। তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ কথাটি আপেক্ষিক আর বিতর্কের। তাই তিনি একে নির্বাচিত কবিতা বলতেই আগ্রহী ছিলেন। গাছের ডালপালা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু কাণ্ড ও শিকড় একই থাকে, অথবা বলা যায় সমস্ত পরিবর্তন আর বিবর্তনের মধ্যেও একটা অবিচ্ছিন্ন সত্তা কোথাও থেকে যায়। যাকে চেনা যায় জীবনবোধ হিসেবে।
কে সরিয়ে নিচ্ছ মানুষকে
মানুষের কাছ থেকে?
তোমারও তো মানুষজন্ম হয়েছিল—
তবে কেন অন্যের জীবন নিয়ে
ছিনিমিনি খেলো?
(কে তুমি/অন্ধপ্রাণ জাগো)
আমরা গর্ত থেকে বিচ্যুত হয়েছি। আজ
পেছনে যাবার কোনও প্রয়োজন নেই।
(শুরু হয়ে গেছে/অন্ধপ্রাণ জাগো)
নিঃশব্দ শিকড়ের প্রথম কবিতাটিই চমকে দেয় আমাদের। ‘বিষ’। ‘আর কিছু না-ই থাক/ বিষ কিন্তু সবার ভেতর রয়ে গেছে!/ কেউ ব্যবহার করে কেউ তেমন করে না।/ তবু বিষ আছে।’ ভালোবাসা আর সাবধানবাণীর পর হঠাৎ করেই ‘বিষ’ চলে এলো। সর্বংসহা পৃথিবী ক্রমেই কুঁকড়ে ছোট হয়ে আসছে। বিষ থেকে বাষ্প উঠে চরাচর আচ্ছন্ন, ধুসর হয়ে গেছে। এমনই পৃথিবীর ছবি তুলে ধরছেন আমাদের সামনে।
মুখোশ, মুখোশ, শুধু মুখোশ লাফিয়ে ওঠে
মুখের ওপরে।
(অন্ধ নাচ/ নিঃশব্দ শিকড়)
জট খোলো।
কোথাও না কোথাও সুতো
জড়িয়ে গিয়েছে।
কোথাও না কোথাও সুতো
বারবার, জড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে।
জট খোলো।
(খোলো/নিঃশব্দ শিকড়)
যেভাবে আরম্ভ করি, শেষ ঠিক সেভাবে ঘটে না।
মাঝখান থেকে শুধু একটা জীবন পুড়ে যায়।
(আরম্ভ, শেষ/ নিঃশব্দ শিকড়)
প্রণবেন্দুদা ব্যক্তিগত সম্পর্ককে খুব গুরুত্ব দিতেন। একটু একটু করে জল দেন সেইসব সম্পর্কের শিকড়ে। আবার তাঁর এইসব কবিতায় গাছের পাতা গজানোর মতোই সহজ এবং স্বতঃস্ফূর্ততার অনুভূতি পাওয়া যায়। লক্ষ করা যায় ছোট ছোট কারুকাজ। জীবনবোধের পাশাপাশি চলতে থাকে এক ধরনের শান্ত শিকড় সন্ধানও। কেননা, প্রতিমুহূর্তে আমরা জীবন মৃত্যুর উন্মথিত আঘাত-প্রত্যাঘাতে জর্জরিত হই। আমাদের মনে প্রতিমুহূর্তে প্রশ্ন জাগে। সেইসব উৎরোল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার একটা প্রচেষ্টাও পাই আমরা এই নিঃশব্দ শিকড়ে। সেটা ১৯৮৬। এর ৫ বছর পর ১৯৯১ সালে ‘এখন গুজব নেই’। উৎসর্গপত্রে দেখতে পাই বোদল্যের-এর একটি লাইন, I do not have the life I deserved. কিন্তু কেন এই স্মরণ। ভেতরে ভেতরে তিনিও কি এমনই ভাবতেন নিজেকে? ‘মানুষ মানুষকে শুধু সন্দেহ করে। শুধু সমস্ত গুজব/ শুনে, ঠিক করে—কাকে ভালোবাসা দেবে, কাকে অবহেলা।’ আবার— ‘এখন গুজব নেই। নির্মেঘ আকাশ জেগে আছে।’ তবে কি সমস্ত গুজব সরিয়ে একটা প্রসারণের কথা বলতে চেয়েছেন তিনি? হ্যাঁ, এই সময় থেকেই সাহিত্য জগত নিয়ে একটা নতুন রকম ধারণা প্রকট হয়ে ওঠে তাঁর কবিতায়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর কবিতা জগত নিয়ে তাঁর ভাবনার কথা লিখতে থাকেন তিনি।
উড়ো ছাই, আমি আজও জীবন বুঝিনি, উড়ো ছাই
তুমি পুড়তে পুড়তে পুড়তে
শক্ত কিছু একটা থেকে ক্রমশ পাঁজরসার কংকালের মতো—
(উড়ো ছাই শোনো/ এখন গুজব নেই)
আমরা ততটা উঠতে পারি না, যতটা নক্ষত্রেরা ওঠে।
(উত্থান পতন/ এখন গুজব নেই)
কিন্তু কোনদিকে যাব?—আমি ভাগ হয়ে আছি,
কেম্পটি ফলস, আমিও তোমার মতো পাথরে পাথরে
ঝাঁপ দিয়ে, হয়ে গেছি আলাদা আলাদা
কে আমাকে ধরে নেবে?
(কেম্পটি ফলস, মুশৌরী/ বাধা পেরোনোর গান)
কোথাও তুমি যেয়ো না, তুমি গেলেই
বাধা দেবে তারাই, যারা তোমাকে কিনে নেবে
বলেই, নানা ছলে দ্যাখো বাঁধাল সব বাধা।
(বাধা পেরোনোর গান/ বাধা পেরোনোর গান)
সমকালীন কবিতা-পরিবেশ থেকে প্রতিনিয়ত পাওয়া কষ্টে এক ধরনের যন্ত্রণাবোধ আর তীব্র প্রতিরোধ নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত এই বইয়ে। কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৯১ থেকে ১৯৯৩। আর ১৯৯৪ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় বই আকারে। সমস্ত রকম বাধা আর উদ্বেগ থেকে এক রকম প্রতিবাদ, প্রতিরোধের কথা ভাবছিলেন তিনি। আর তাই হয়তো এই বইয়ের ভাষা কিছুটা তির্যক, কিঞ্চিৎ কটু ও ব্যঙ্গাত্মক।
কবিতা লিখি, সেই তো প্রতিবাদ।
কে পড়ে কারা পড়ে?
তবুও লিখি সেই তো প্রতিবাদ
(প্রতিবাদ করো/ বাধা পেরোনোর গান)
যদি কোথাও অস্পষ্ট কিছু নেই, তা হলে তো দিব্যি বেঁচেআছি।
(স্পষ্ট কথার সময়/ বাধা পেরোনোর গান)
কোথাও কিছু নেই তবু এক ঝলক হাওয়া এলেই বুক কেঁপে ওঠে।
(আকস্মিক/ বাধা পেরোনোর গান)
এখন অনেক শব্দ হয় কিছু শব্দ ভোমরার মতো
(শব্দ, নীরবতা/ বাধা পেরোনোর গান)
বড়ো বড়ো চোখ, কেমন অদ্ভুত চাউনি, মেরে ফেলবে না তো!
(বড়ো বড়ো চোখ/ বাধা পেরোনোর গান)
পরের এবং তাঁর শেষ বই ‘রৌদ্রের নখরে’ তেও এমনই তির্যকতা আর সেই প্রণবেন্দুও মগ্নতা পাই আমরা। এই সময়েই একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা, সাহিত্যিক সমাজ ব্যাপী নৈঃশব্দ্য আর অসুখের তীব্র প্রকোপে আক্রান্ত কবি তাঁর কর্মক্ষেত্র থেকে স্বেচ্ছা অবসরে যান। এতোদিনের সঙ্গীসাথি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সব ফেলে একা সময় কাটাচ্ছিলেন অনেকটা দূরে। আর হৃদয়ে রৌদ্রের তেজে একটু একটু করে পুড়ছিলেন। সেই আট বছরের তৈরি হয়ে ওঠা কবিতাগুলো নিয়ে ২০০২ সালে বেরোলো তাঁর শেষ কবিতাবই। উৎসর্গে আছেন ক বি শামসুর রাহমান আর বেলাল চৌধুরী।
ভয় নয়, অন্য কিছু জন্ম নেয় শহরে শহরে,
হাতল পিতলে তৈরি, ঘুরিয়ে দিলেই সব খোলে।
(যন্ত্র/রৌদ্রের নখরে)
এখন যে ভেতরে ভেতরে সব কেঁপে ওঠে, এখন যে ভেতরে ভেতরে
শিকড় ছড়িয়ে যায়, তারও দীর্ঘ ইতিহাস আছে। তুমি শোনো
(ভেতরে শিকড় কেঁপে ওঠে/রৌদ্রের নখরে)
হাত থেকে ফসকে গেছে যে-টুকু রাত্রি, তার অন্ধকার
এখন বাইরে, ঘিরে আছে আগুনকুণ্ডের পাশে ভীল যুবকেরা।
(মৃত্যু/রৌদ্রের নখরে)
প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কাছে একবার জানতে চাওয়া হয়েছিল, কে বড়? কবিতা, নাকি জীবন? তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে তারপর বললেন, ‘জীবন’। এখন দু’হাত পেতে অপেক্ষায় থাকো,/ অন্তত একটিবার জীবন, তোমার হাত স্পর্শ করে যাবে।
অলংকরণে কথাসাহিত্যিক মনি হায়দারের আলোকচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে।
ঋতো আহমেদ কবি, গদ্যকার এবং অনুবাদক। কর্মজীবনে বর্তমানে একটি টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত। ঢাকায় বসবাস করছেন। তার প্রকাশিত মৌলিক কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে—ভাঙনের মুখ (২০১৮), উন্নয়নের গণতন্ত্র (২০১৮), হে অনন্ত অগ্নি (২০১৯), জলের পাতাল (২০১৯)। প্রকাশিত অনুবাদকাব্যগ্রন্থ—ওয়াকিং টু মার্থাস ভিনিয়ার্ড (২০২০), আদিরসাত্মক সংস্কৃত কবিতা (২০২১)।