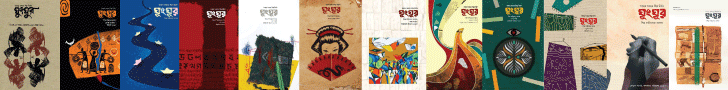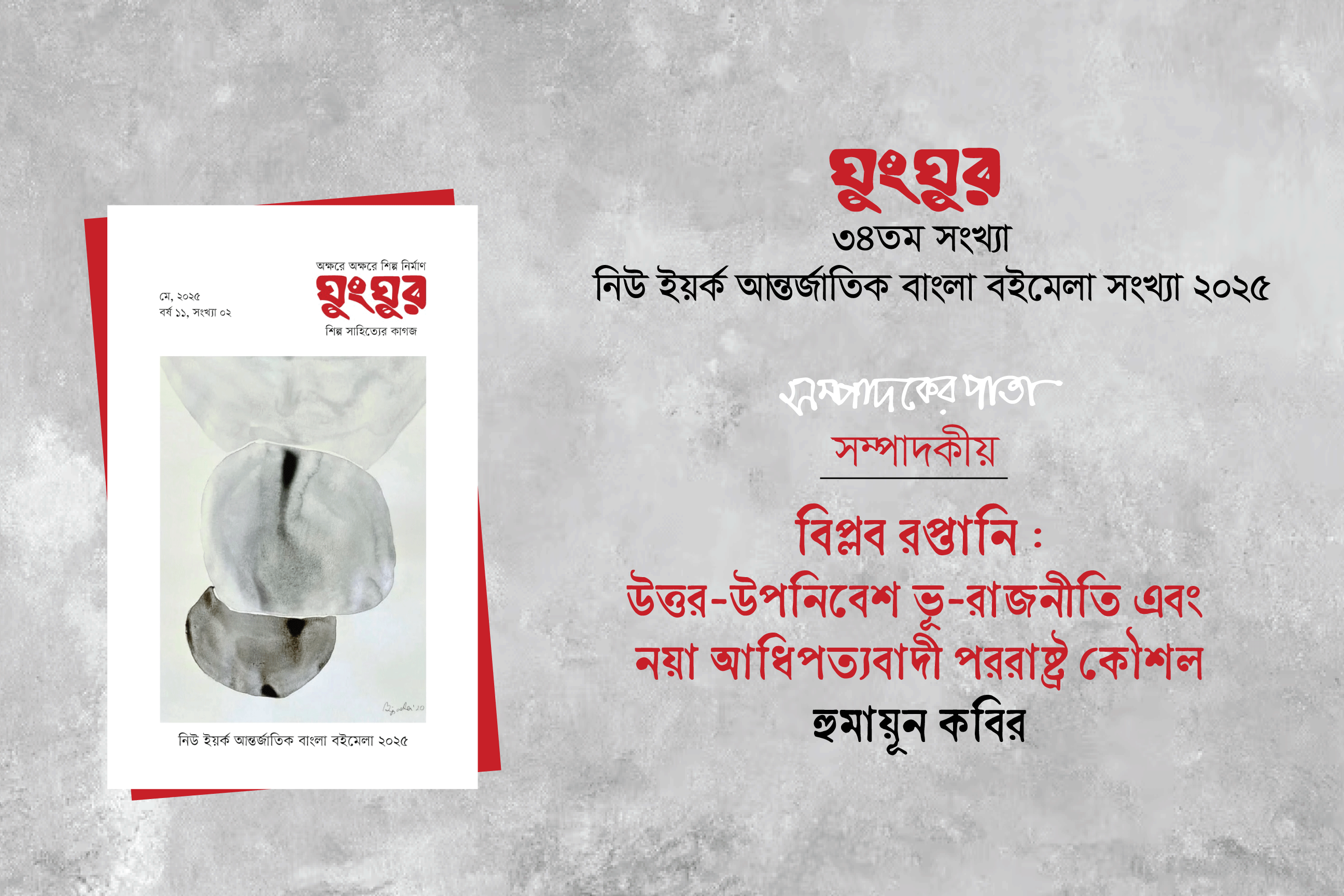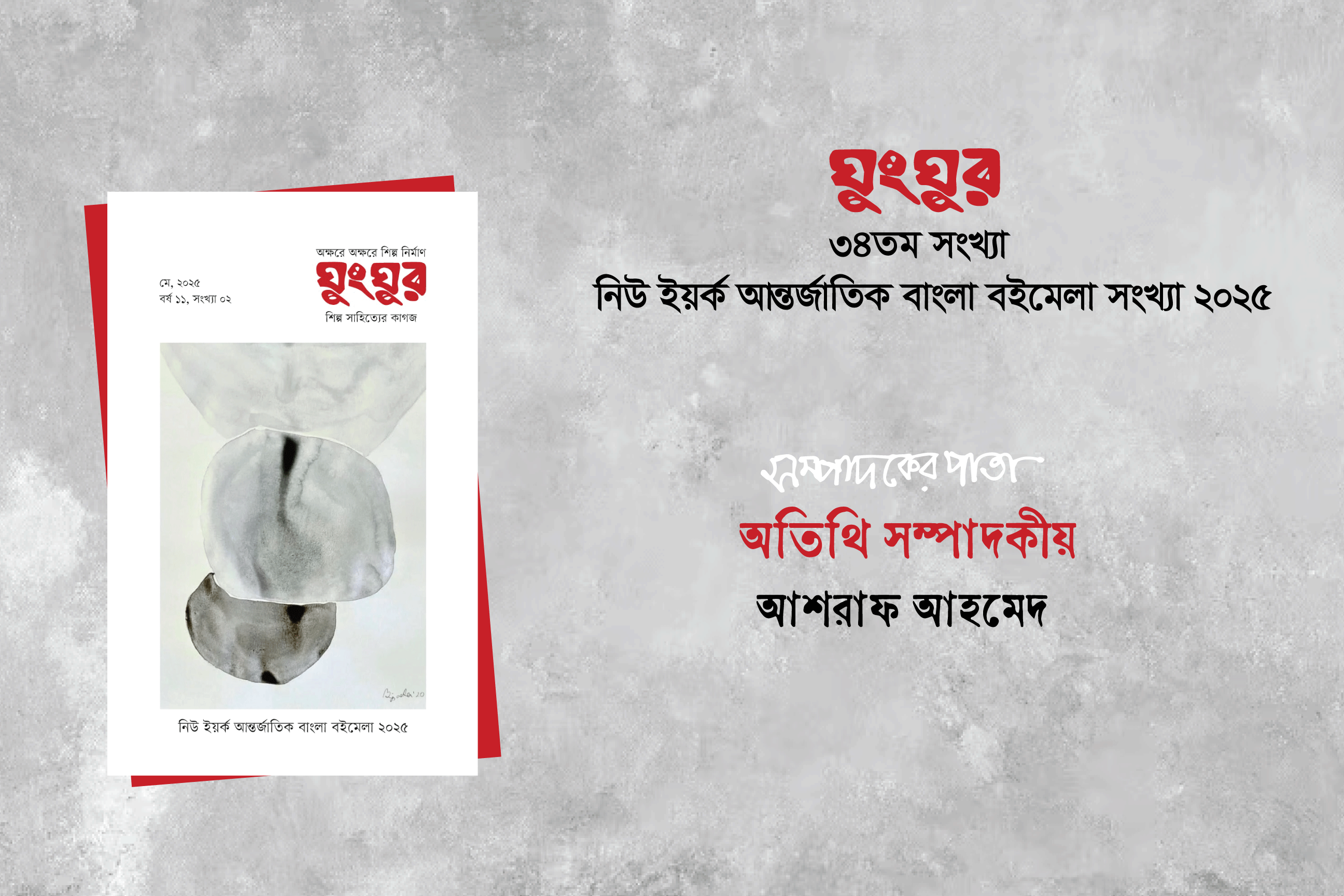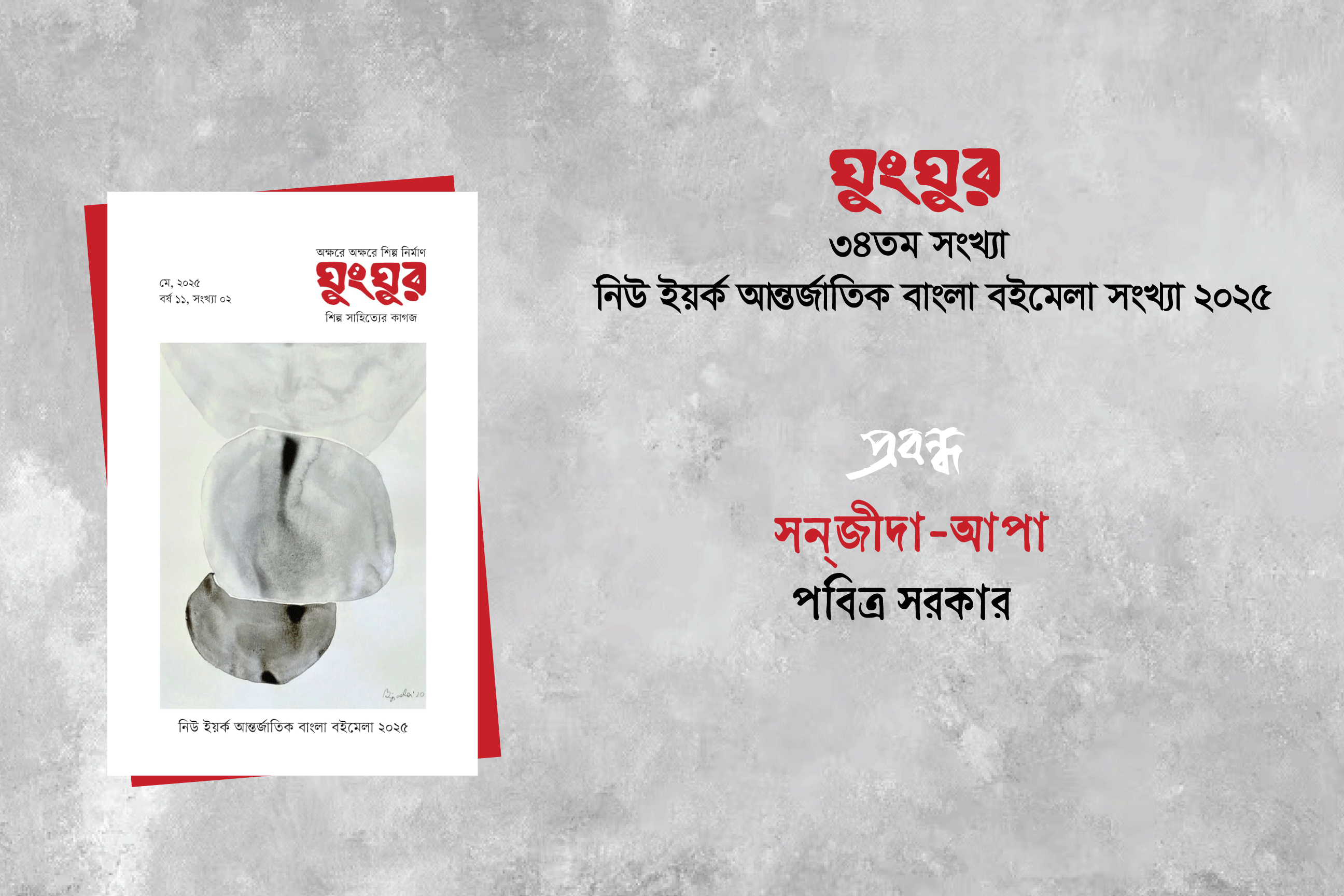সম্পর্কের সংস্কৃতি, সংস্কৃতির রাজনীতি
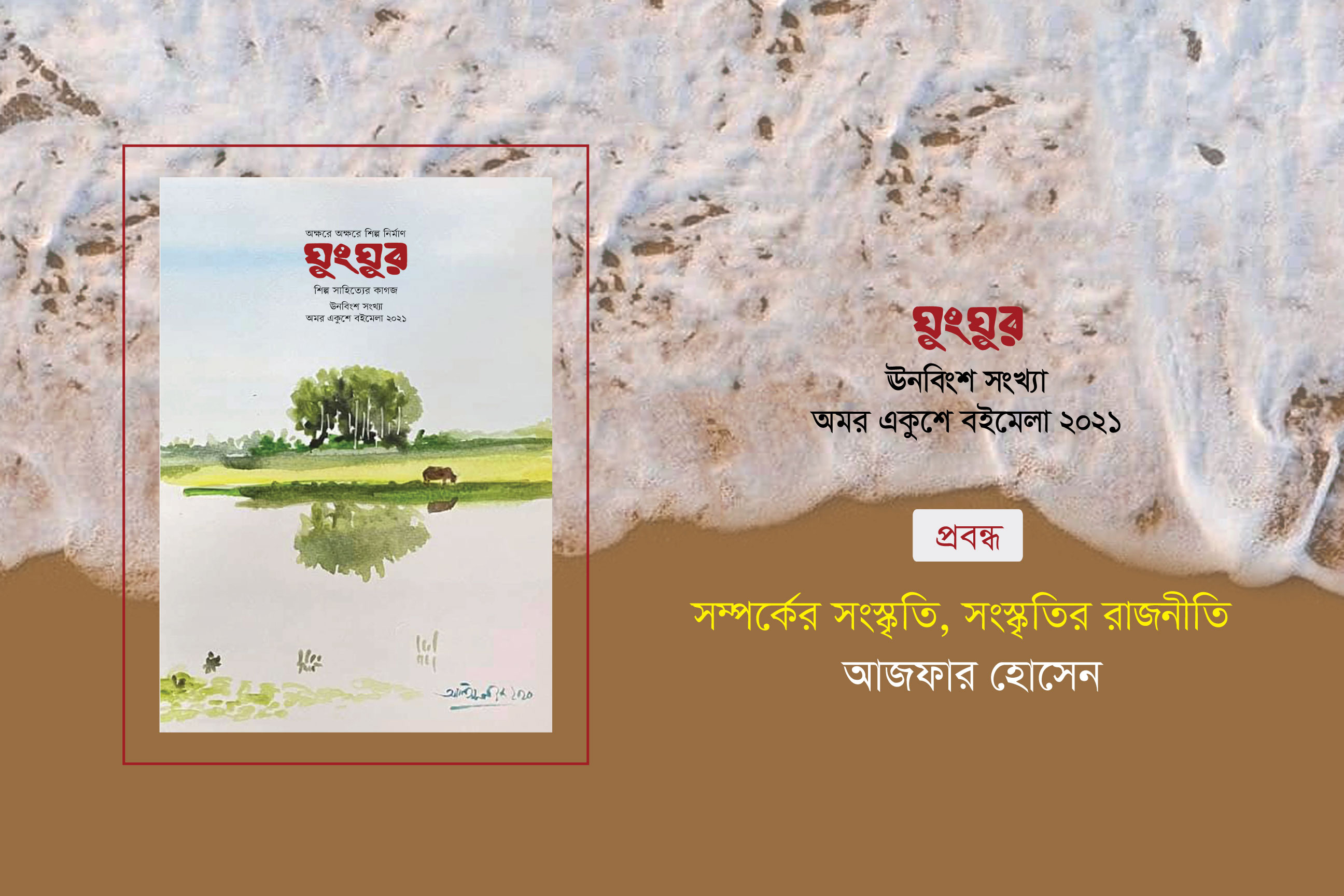
শ্রেণির মতো সংস্কৃতি প্রবলভাবে রাজনৈতিক। তবে ওই ঐতিহ্যের জের এখনো দারুণভাবেই টের পাওয়া যায়, যে ঐতিহ্য তার অঙ্গুলি নির্দেশেই সংস্কৃতির জমিনকে নির্দিষ্ট করে ফেলে, যে ঐতিহ্য নিজের সীমানা এঁকে তৈরি করে বিভিন্ন ধরনের উঁচু-নিচু বিভাজন, তৈরি করে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাও
সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এখনো বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একাংশ গদ্গদ হয়ে উনিশ শতকের ইংরেজ কবি ও সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড আওড়ান এভাবে : সেরা যা কিছু চিন্তা করা হয়েছে বা বলা হয়েছে, তাই সংস্কৃতি। কিন্তু কে কীভাবে ঠিক করে দেয় মানুষের চিন্তার বা বয়ানের শ্রেষ্ঠত্ব? তবে আর্নল্ডের ক্ষেত্রে বলা যাবে, শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা নেমেছেন তো বটেই, কিন্তু তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, ওই বিচারে ভূমিকা রেখেছে দীর্ঘ সময় ধরে গড়ে-ওঠা একটি সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিকে আমরা অনায়াসেই ইউরোপকেন্দ্রিক বলতে পারি।
এই সংস্কৃতি কমপক্ষে পাঁচশ বছরের বেশি সময় ধরে প্রথমত নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে বিভিন্নভাবে উদযাপন করেছে এবং শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি ও নিরিখও তৈরি করে উপনিবেশবাদের সুবাদেই দুনিয়ার অধিকাংশ জায়গায় তাদের বৈধতা জারি রাখার চেষ্টা করেছে। এমনকি মহান জর্মন কবি ও নাট্যকার গ্যেটে ‘বিশ্বসাহিত্য’-এর ধারণাকে সামনে এনে ওই বিশ্বের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন ইউরোপকেই। আর ইউরোপের অন্তর্গত করেছেন গ্রিসকে, যে গ্রিসকে গ্যেটে চূড়ান্ত দৃষ্টান্তে শিল্পসাহিত্য বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর শিষ্য একেরমানকে লেখা এক চিঠিতে গ্যেটে সরাসরি জানাচ্ছেন যে, ইউরোপের বাইরের পৃথিবীর সাহিত্যকে ‘শ্রেষ্ঠ’ ভাবার কোনো কারণ নাই, কেননা গ্রিস বা ইউরোপ তো তার শ্রেষ্ঠত্বকে ইতোমধ্যেই সর্বজনীন করে তুলেছে। গ্যেটে এখানে মোটেই একলা নন। গ্যেটের পরেও জ্ঞানভাষ্যিক অনুশীলনে ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বিভিন্নভাবেই জারি থেকেছে।
এই ইউরোপকেন্দ্রিক সংস্কৃতি নিজেই সংস্কৃতির সীমা-পরিসীমা নির্ধারণে এক ধরনের সাংস্কৃতিক পুলিশি চালু রেখেছে। এর ফলে সংস্কৃতিকে দেখা হয়েছে এমনভাবে যে, এমনকি এর নির্দিষ্ট স্বত্বাধিকারও তৈরি হয়েছে বটে। অর্থাৎ সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে এমন এক এলাকা যেখানে সকলের প্রবেশাধিকার নাই বা সমান নয়। এভাবেও বলা যায় : সকলেই নয়, কেউ কেউ সংস্কৃতিবান।
তাহলে সংস্কৃতিবান কারা? উত্তরে বলা হয় : সংস্কৃতিবান তাঁরাই যাঁরা ‘ক্লাসিকস্’-এর চর্চা করেন কিংবা যাঁরা বেটোফেন বা মৌৎসার্ট-এর সংগীতের সমঝদার কিংবা যাঁরা গড়গড় করে শেক্সপিয়ার আওড়াতে সক্ষম অথবা যাঁরা নিয়মিত আর্ট গ্যালারিতে ঘোরাঘুরি শেষে ঠোঁটের ওপরে শিল্প-সম্পর্কিত চোস্ত কিছু উচ্চারণ প্রস্তুত রাখেন। আমাদের দেশে আবার সংস্কৃতিবানদের এক ধরনের ‘জাতীয়তাবাদী’ রুপও তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরাই সংস্কৃতিবান যাঁরা ‘শুদ্ধ’ বাংলায় কথা বলেন, যাঁরা রবীন্দ্র-সংগীতে মজে থাকার ক্ষমতা রাখেন, যাঁরা বিমূর্ত কম্পোজিশনের মর্ম বোঝেন, যাঁরা উচ্চাঙ্গ সংগীতের সমঝদার, যাঁরা বাংলা ‘ক্লাসিকস্’-এর সঙ্গে পরিচিতও বটে। এঁদের কেউ কেউ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের গরিমায় আবার অনেককেই ‘আনকালচার্ড’ বলে গালিও দিয়ে থাকেন, পরোক্ষভাবে হলেও সংস্কৃতির ওই ইউরোপকেন্দ্রিক এবং অভিজাতবাদী ধারণাকে বৈধ করার তাগিদে।
এবারে আসি ‘ক্লাসিকস্’ প্রসঙ্গে। ইউরোপকেন্দ্রিক সংস্কৃতি নিজেই ওই ‘ক্লাসিকস্’-এর ধারণাকে শুধু তৈরিই করে নাই, তা দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে। লক্ষ্য না করে উপায় নাই যে, এই ‘ক্লাসিকস্’ কথাটায় ‘ক্লাস’ বা শ্রেণি কথাটাও লুকিয়ে থাকে। অর্থাৎ উঁচু-নিচু বিভাজনের বিষয়টা থাকেই। বলা দরকার, যেসব সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক উৎপাদনকে খোদ ইউরোপ ‘ক্লাসিকস্’ হিসাবে বিবেচনা করে এসেছে, আমি সেই সব কাজের গুরুত্বকে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে একপেশে অবস্থান নিতে মোটেই রাজি নই। আমি একথা কখনই বলতে রাজি নই যে, গ্রিক নাট্যকারদের কাজগুলো কিংবা বেটোফোনের কাজগুলো একেবারেই ক্ষতিকারক এবং আমাদের জন্য সেগুলো একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। তবে এইখানে আমি যা ধরার চেষ্টা করছি তা হলো ইউরোপশাসিত চিহ্নায়ন ও চরিত্রায়ন প্রক্রিয়ার সংস্কৃতি, যা প্রবলভাবে রাজনৈতিকও বটে। এই প্রক্রিয়ায় ‘ক্লাসিকস্’-এর ধারণাকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের উঁচু-নিচু বিভাজন তৈরি হয়েছে। এই সব বিভাজন আবার আদর্শিকভাবেই সম্পর্কিত থাকে আরও বিভাজনের সঙ্গে : আমরা/ তারা, সংস্কৃতিবান/ সংস্কৃতিহীন, সভ্য/ অসভ্য এবং এমনকি পশ্চিম/ পূর্ব। এছাড়া তো রয়েছেই ‘উঁচু’ সংস্কৃতি ও ‘নিচু’ সংস্কৃতির ধারণা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ‘উঁচু’ সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে গ্রিক নাট্যকার সফোক্লিস-এর নাটক ঈডিপাস; অন্যদিকে ‘নিচু’ সংস্কৃতির ভেতরে কোনোভাবে স্থান করে নেয় ক্যারিবীয় প্লান্টেশানে গাওয়া ক্রীতদাসের গান, যেখানে রক্তমাখা ধ্বনিসব সংগ্রামী পোড়-খাওয়া দেহ থেকেই উৎসারিত হয়।
বলা প্রয়োজন, ইতিহাসে পুঁজিবাদ ও উপনিবেশবাদ পরস্পর-সম্পর্কিত হয়ে সাংস্কৃতিকভাবেই বিভিন্ন ধরনের উঁচু-নিচু বিভাজনকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছে। অর্থাৎ এই বিভাজনগুলো মোটেই নিরীহ নয়; বরঞ্চ বিভিন্ন পরিসরে তারা আধিপত্যের দ্যোতক—যার রয়েছে একইসঙ্গে জ্ঞানভাষ্যিক ও বস্তুক তাৎপর্য। এই বিভাজনগুলোর কথা বলতে গেলে তাহলে অবশ্যই বলতে হবে শ্রেণি-বৈষম্য, লিঙ্গ-বৈষম্য, বর্ণ-বৈষম্য, জাতি-বৈষম্যসহ আরও বৈষম্যের কথা, যাদের উৎপাদনে ও পুনরুৎপাদনে এবং বৈধতা তৈরির ক্ষেত্রে সংস্কৃতির ভূমিকা থাকে।
ইতিহাসই তার চলমান থিয়েটারে সংঘটিত অসংখ্য ঘটনার ভেতর দিয়েই স্পষ্ট করেছে যে, ইউরোপকেন্দ্রিক সংস্কৃতি ইউরোপীয় উপনিবেশবাদকে পোক্ত ও প্রসারিত করার ক্ষেত্রে এমন এক মানসিকতা তৈরি করেছে, যা ওইসব বিভাজন ও বৈষম্যকে স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক, অনিবার্য এবং এমনকি চিরন্তন ধরে নেয়। এই মানসিকতা কেবল উপনিবেশবাদী শক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, তা উপনিবেশায়িতদের ক্ষেত্রেও খাটে। উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের ইতিহাসের ভেতর থেকেই আমরাও ওই মনকে, ওই মানসিকতাকে কোনভাবেই খোল-নলচে পাল্টে-দেয়া বিউপনিবেশায়নের লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে ধ্বংস করতে পারি নাই। পারি নাই বলেই অনেক এলাকার মধ্যে শিল্পসাহিত্যের বিবেচনার এলাকাতেও আমরা মুখস্থ বলতে থাকি এই ধরনের কথা : ‘শেক্সপিয়ার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার,’ ‘ইংরেজের সভ্যতা বাংলা সাহিত্যের উজ্জলতম অর্জনগুলোকে সম্ভব করেছে,’ ‘গ্রিক সভ্যতা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সভ্যতা,’ কিংবা ‘গ্যেটে মহত্তম কবি।’
গ্যেটে নিয়ে ছেড়ে-আসা প্রসঙ্গে তাহলে ফিরে আসা যাক। আমরা আসলেই গ্যেটেকে প্রশংসা করতে বাধ্য হই যখন দেখি তিনি ইউরোপের পরিপ্রেক্ষিতে ‘জাতীয় সাহিত্য’-এর সীমাবদ্ধতাকে স্পষ্ট করে ধরিয়ে দিচ্ছেন। আবার তিনি যখন ‘বিশ্বসাহিত্য’-এর উন্মেষকে সেই আঠারো শতকে আঁচ করে তাকে স্বাগত জানান, তখন গ্যেটের দূরদৃষ্টি আমাদের প্রশংসা কেড়ে নেয়। কিন্তু তারপরও গ্যেটে পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্যের ওপর স্থান করে দিতে চান ওই গ্রিক সাহিত্যকেই। তাঁর শিষ্য একারমানকে লেখা একটি চিঠিতে গ্যেটে এমনকি এও বলেন : যে স্থান বা মূল্য গ্রিক সাহিত্যকে দেয়া হয়েছে, সেই মূল্য চৈনিক সাহিত্য বা সার্বীয় সাহিত্যকে দেয়া যাবে না। অর্থাৎ গ্যেটে গ্রিসের শ্রেষ্ঠত্বকে আগেভাগেই ধরে নিয়েছেন; কিংবা তাকে স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক এবং এমনকি চিরন্তনও ধরে নিয়েছেন। এও যুক্ত করা দরকার, এই সময় চীনা সাহিত্যের সঙ্গে গ্যেটের পরিচয় একেবারেই প্রাথমিক ছিল আর সার্বীয় সাহিত্যের একটা ভগ্নাংশের মৌহূর্তিক ঝলকানি ছাড়া আর কিছুই উপস্থিত ছিল না গ্যেটের নিজস্ব পড়াশোনায়। আসলে ইউরোপের বাইরের সাহিত্য সম্পর্কে গ্যেটের ধারণা একেবারেই সীমিত ছিল, যদিও তিনি কালিদাসের শকুন্তলার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু শুধু শকুন্তলা দিয়ে তো আর পূর্বকে বা এমনকি ভারতকে বিবেচনা করা যায় না। কিন্তু তারপরও গ্যেটে কেবল (সাংস্কৃতিক) ক্ষমতার জোরেই তাঁর ধারণা এবং বিচার-বিবেচনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।
ইউরোপে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তুলনামূলক সাহিত্যের এলাকায় গ্যেটের গ্রিসকেন্দ্রিক বা ইউরোপকেন্দ্রিক ধারণার তুমুল প্রভাব ও পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করে চলেছি এখনো। আমরা জেনে এসেছি যে, জ্ঞানই ক্ষমতা। কিন্তু গ্যেটেদের কথা বিবেচনায় রাখলে এও অনায়াসেই বলা সম্ভব যে, ক্ষমতা হচ্ছে জ্ঞান (এই বিষয় নিয়ে আগের সংখ্যার অতিথি-সম্পাদকীয়তে বেশ কিছু কথা লিখেছি অবশ্য)। আর ক্ষমতাবলে জ্ঞান উৎপাদন করা এবং জ্ঞানকে জায়েজ করা সম্ভব হয়েছে বারবারই। এভাবেও দেখা যায় : জোর যার মুল্লুক তার, আর মুল্লুক যার, জ্ঞান তার। সাম্রাজ্যের বা উপনিবেশবাদের লজিক এভাবেই ইতিহাসে কাজ করেছে বারবার।
ওই লজিক থেকে মহান জর্মন দার্শনিক হেগেলও মুক্ত নন, যদিও আঠারো ও উনিশ শতকের এই অন্যতম ও প্রতিভাবান দার্শনিক এবং বিখ্যাত ইউরোপীয় আলোকায়ন প্রকল্পের এই দৃষ্টান্তমূলক প্রতিনিধি আমাদের ‘স্পিরিট’-এর সার্বিক মুক্তির পক্ষে তুমুল ওকালতি করেছেন। এই হেগেলেই লক্ষ্য করি গ্যেটের ইউরোপকেন্দ্রিকতার পুনরাবৃত্তি, যদিও গ্যেটের পরিসর ও পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন। যেখানে গ্যেটে বলেছেন বিশ্বসাহিত্যের কথা, সেখানে হেগেল বলেছেন বিশ্ব-ইতিহাসের কথা। হেগেল এই বিশ্ব-ইতিহাসের কথা বলেছেন তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বই দ্য ফিলসফি অফ হিস্ট্রি-তে। এখানে স্পষ্টত হেগেলের খায়েশ হচ্ছে বিশ্বের ইতিহাস রচনা করা। এবং সর্বজনীন ইতিহাস রচনা করা। কিন্তু কী করে বসলেন হেগেল? ওই বইয়ের ভূমিকায় হেগেল ঘোষণা দিলেন এই বলে যে, আফ্রিকার কোনো ইতিহাস নাই; বললেন : আফ্রিকা অনড়, স্থির, প্রাকৃতিক। এও বললেন যে, বিশ্বের ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি আফ্রিকাকে আর মোটেই উল্লেখ করবেন না। এই ভাবে আফ্রিকাকে ইতিহাসের বিশাল গোল্লা বানিয়ে হেগেল আবার এশিয়াকে হাঁটিহাঁটি-পা-পা শিশুর সঙ্গে তুলনা করলেন। অর্থাৎ যে বিশ্বের ইতিহাস লিখবেন বলে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করেছেন, সেই বিশ্বের অধিকাংশ জায়গা ও মানুষকে অগ্রাহ্য করে বা তুচ্ছ বিবেচনা করে তিনি বিশ্বকে দেখেছেন। কিন্তু সারা দুনিয়ার কেন্দ্রে তিনি তত্ত্বের ঢাকঢোল পিটিয়ে ইউরোপকে স্থাপন করলেন এই বলে যে, সভ্যতার আলোকপ্রাপ্তির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ওই ইউরোপই। হ্যাঁ, হেগেলের জন্য ইউরোপ ছাড়া গতি নাই, গন্তব্য নাই, কেন্দ্র নাই, আলো নাই, সভ্যতা নাই। এইভাবেই হেগেলের দ্য ফিলসফি অফ হিস্ট্রি ইউরোপকেন্দ্রিকতার তুমুল প্রতার্কিক বা জ্ঞানভাষ্যিক উৎসবে পরিণত হয়েছে।
আগেই যেমন বলা হয়েছে যে, গ্যেটে একলা নন, ঠিক তেমনি একই কথা বলা যাবে হেগেলের ক্ষেত্রেও। ম্যাথু আর্নল্ড-এর কথা তো তাদের আগেই বলেছি, যদিও তিনি বয়সে গ্যেটে ও হেগেলের চেয়ে ছোটো এবং যদিও তিনি ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডের মানুষ। এই ত্রয়ী আবার কেবল তিনজন চিন্তাবিদকেই নির্দেশ করেন না; তাঁরা একইসঙ্গে জ্ঞানের অনুশীলনের একটি বিশেষ সংস্কৃতিরও প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সংস্কৃতি নিজেই ‘সংস্কৃতি’র ধারণাকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আর এই ধারণা উপনিবেশবাদের ঔরসজাত এবং তার চালিকাশক্তিও বটে। ধারণাটা হচ্ছে এই যে, সংস্কৃতি কতগুলো নির্দিষ্ট অনুশীলনের নাম, যে অনুশীলনে সকলেই বা এমনকি পূর্ব ও পশ্চিম সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। এই ধারণাটাকে পুরা উনিশ শতকজুড়ে তো বটেই, বিশ শতকেও বিভিন্নভাবে টানা হয়েছে। অর্থাৎ সংস্কৃতির ইউরোপকেন্দ্রিক, অভিজাতবাদী, বিচ্ছিন্নতাকামী ও বিভাজনজ্ঞাপক ধারণাকে ব্যবহার করেই বলা হয়েছে যে, কালো মানুষেরা অসভ্য ও অসংস্কৃত। এবং বলা হয়েছে যে, আরব জগতের ‘মাথামোটা’ আদমিরা যুক্তির ভাষা বোঝে না, বোঝে শক্তির ভাষা। এবং এও বলা হয়েছে যে, এশিয়ার হিন্দুরা অলস ও ঘুমকাতুরে; স্বদেশীরা ফাঁকিবাজ এবং শ্রমবিমুখ।
আর এইসব ধারণা পুনরাবৃত্ত ও পুনরুৎপাদিত হয়েছে, যার অনুপুঙ্খসমৃদ্ধ খতিয়ান পাওয়া যাবে মার্কিন-ফিলিস্তিনী বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতি-সমালোচক এডওয়ার্ড সাঈদের কাজে। এইসব ধারণাকে চালু রেখে ইউরোপ তার ‘অপর’কে সৃষ্টি করেছে এমনভাবে যে, তাদেরকে বিশেষ ছাঁচে, আদলে, চিত্রকল্পে বারবারই উপস্থিত করা যায়। কিন্তু কাজটা কেবল এভাবেই শেষ হয় না। যদি ইউরোপের পক্ষে দেখানো ও বোঝানো সম্ভব হয় যে, ইউরোপের বাইরের মানুষেরা ‘অসভ্য’ ও ‘অসংস্কৃত,’ তাহলে তখন ওইসব মানুষকে ‘সভ্য,’ ‘শিক্ষিত,’ ও ‘সংস্কৃতিবান’ করার দায়িত্ব পালনের পথ ও সুযোগ খুঁজে পায় ইউরোপ নিজেই। তখন ইউরোপ বাইরে থেকেই তার ‘অপর’-এর ভূমিতে এবং মগজে ঢোকার সুযোগ পায়; তাদেরকে এমনকি সরাসরি শাসন করার অধিকার অর্জন করে। আর এই শাসনের ভেতর দিয়ে তো সম্ভব হয়েছে অন্যের জমি, সম্পদ, ভাষা, জ্ঞান ইত্যাদি লুটপাট করে ইউরোপকে সম্প্রসারিত, সমৃদ্ধ, বিত্তশালী করা। লড়াকু কালো তাত্ত্বিক ও বিপ্লবী ফ্রানৎস্ ফানো’র সেই বিখ্যাত কথাটা মনে আসে : “ইউরোপ আক্ষরিক অর্থেই তৃতীয় বিশ্বের সৃষ্টি।”
উপরের আলোচনাটা খেয়াল করলেই ধরা পড়ে উপনিবেশবাদ কীভাবে কাজ করে। শুধু তাই নয়, উপনিবেশবাদ কিছু সম্পর্ককে প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে নির্দেশও করে বটে। অর্থাৎ চট করেই চোখে পড়ে উপনিবেশবাদের সঙ্গে বর্ণবাদের সম্পর্কটাকে। কালো তাত্ত্বিক ডাব্লিউ ই বি ডুবয়েস এবং সি এল আর জেইমস তাদের বিভিন্ন কাজে বারবারই বলেছেন যে, উপনিবেশবাদের চরিত্র বুঝতে গেলে দেখে নিতে হয় কীভাবে উপনিবেশবাদ বর্ণবাদী হয় এবং কীভাবে বর্ণবাদও উপনিবেশবাদী হয়ে ওঠে। তাহলে কী এই বর্ণবাদ?
বর্ণবাদের সংজ্ঞার্থ একটি নয়, একাধিক। তবে একটা যুৎসই সংজ্ঞার্থের সাক্ষাৎ মেলে তিউনিশিয়ার ইহুদি তাত্ত্বিক আলবেয়ার মেমি’র রেইসিজম নামের বইয়ে। মেমি এই মর্মে বলেন যে, বর্ণবাদ হচ্ছে আধিপত্যবাদী বা আধিপত্যকামী ব্যবস্থা, যা চামড়ার রঙ ব্যবহার করার মাধ্যমে ভিন্নতাকে বৈধ রূপ দিয়ে উঁচু-নিচু বা শাসক-শাসিত সম্পর্ক সৃষ্টি করে থাকে। বর্ণবাদের উপনিবেশবাদী ইতিহাসই তো বলে দেয় কীভাবে সাদারা দুনিয়াজুড়ে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে, কালোদের ‘কালো’ বানিয়ে এবং এভাবে তাদেরকে আলাদা ও এমনকি ‘নিকৃষ্ট’ প্রমাণ করে। এখানে এও বলে নেয়া দরকার, মানুষকে কালো ও শাদা বলার রেওয়াজ পৃথিবীব্যাপী তৈরি করেছে বর্ণবাদী উপনিবেশবাদ বা উপনিবেশবাদী বর্ণবাদ নিজেই। আর যাকে আমরা এর মধ্যে ‘ইউরোপকেন্দ্রিকতা’ বলেছি, মতাদর্শিকভাবে তার সঙ্গে গভীর সম্পর্কে যুক্ত থাকে উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদ। এই কারণে যে কোনো পরিসরেই ইউরোপকেন্দ্রিকতার আলোচনা একইসঙ্গে উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদের আলোচনা দাবি করে।
অবশ্যই বলা যাবে যে, ইউরোপকেন্দ্রিকতা নিজেই বর্ণবাদী হয়ে ওঠে। হয়েছেও। আফ্রিকার ইতিহাস নিয়ে হেগেলের ইউরোপকেন্দ্রিক ধারণাকে আবারও স্মরণ করা যেতে পারে। চীনা ও সার্বীয় সাহিত্য নিয়ে গ্যেটের গ্রিসকেন্দ্রিক ধারণাটাও একটা কেজো উদাহরণ হিসাবে এখানে আরও একবার সামনে আনা যায়। আর ইউরোপকেন্দ্রিকতা, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদের সঙ্গে সম্পর্কে জড়াজড়ি করে থাকে প্রাচ্যবাদ নিজেই, যে ধারণার তুমুল তত্ত্বায়ন পাই এডওয়ার্ড সাঈদের বাঁক-নেয়া কাজ ওরিয়েন্টালিজম-এ (১৯৭৮)।
আর এই সাঈদের দোহাই পেড়েই—এবং ঐতিহাসিকভাবেও—বলা সম্ভব যে, প্রাচ্যবাদ নিজেই একই সঙ্গে ইউরোপকেন্দ্রিক, উপনিবেশবাদী ও বর্ণবাদী হয়েছে, যদিও সাঈদ তাঁর কাজে সবসময় এদের আন্তঃসম্পর্ক বা পারস্পরিক সম্পর্ককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন নাই। সম্পর্কের আরেক পরিসরের কথা না হয় বাদই দিলাম। এই পরিসরের নাম পুঁজিবাদ, যাকে সাঈদ রীতিমতো এড়িয়ে গেছেন (যদিও মাঝেমাঝে সাঈদের দায়সারা গোছের উচ্চারণে ‘পুঁজিবাদ’ কথাটা অবশ্যই পাওয়া যাবে।) আর পুরুষতন্ত্রের আলোচনা? একেবারেই অনুপস্থিত। সেগুলো জরুরি কিন্তু ভিন্ন প্রসঙ্গ। আমি এখন সেদিকে যাচ্ছি না। তবে প্রাচ্যবাদ নিয়ে দু-একটা কথা বলে নেয়া যাক।
প্রথমেই বলা দরকার, সাঈদের ওরিয়েন্টালিজম-এর চার দশকেরও বেশি সময় পরে, অর্থাৎ বর্তমান করোনাক্রান্ত বৈশ্বিক মুহূর্তেও, প্রাচ্যবাদের সমস্যা তার প্রাসঙ্গিকতা হারায় নাই মোটেই; বরঞ্চ তার প্রাসঙ্গিকতা নতুনভাবে দেখা দিচ্ছে এই অর্থে যে, বর্তমান সময়ে চীনকে ও প্রাচ্যকে ভাইরাসসহ সকল বালা-মসিবতের উৎস হিসাবে দেখার পশ্চিমা বর্ণবাদী প্রবণতা কমার পরিবর্তে বৃদ্ধিই পেয়েছে। কিন্তু আবারও প্রশ্নটা ওঠাতে হয় : আসলে কী এই প্রাচ্যবাদ? যদিও এই বর্গটার আদি শব্দাংশে ‘প্রাচ্য’ চিহ্নটা জ্বলজ্বল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে, সেখানে কিন্তু প্রাচ্য কেন্দ্রে অবস্থান করে না মোটেই; বরঞ্চ সেখানে কেন্দ্রে অবস্থান করে পশ্চিমই। প্রাচ্যবাদের একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার্থ এভাবে উপস্থিত করা যায় : প্রাচ্যবাদ হচ্ছে প্রাচ্যের উপস্থাপনার এক বিশেষ পশ্চিমা প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি, যা একইসঙ্গে বা আলাদাভাবে হতে পারে প্রাতিষ্ঠানিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক ও সত্তাতাত্ত্বিক। অর্থাৎ তৈরি-করা কিছু ছাঁচে, আদলে, চিত্রকল্পে পশ্চিম পূর্বকে বারবার হাজির করতে থাকে এমনভাবে যে, পূর্বকে চেনা-জানার জ্ঞানতাত্ত্বিক ও জ্ঞানভাষ্যিক ‘কোড’ বা সূত্র হয়ে দাঁড়ায় ওইসব আদল, ছাঁচ, বা চিত্রকল্প, যেগুলো আবার একইসঙ্গে অর্জন করে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ ও বৈধতা এবং এমনকি মতাদর্শিক আধিপত্য (বা ইতালীয় মার্কসবাদী আন্তোনিয়ো গ্রামসি যাকে ইতালীয় ভাষায় বলেছেন ‘এগেমোনিয়া’ বা ইংরেজিতে ‘হেজেমনি’।)
আমরা জানি যে, পশ্চিমা মুলুকেই উৎপাদিত ও পুনরুৎপাদিত বিভিন্ন বয়ানে, আখ্যানে, ভাষণে, উচ্চারণে, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ভাষ্যে পূর্বের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের ‘রহস্যময়,’ ‘লাস্যময়,’ ‘বর্বর,’ ‘কামার্ত,’ ‘অলস,’ ‘অবৈজ্ঞানিক,’ ‘অনৈতিহাসিক,’ ‘আদিম,’ ইত্যাদি বলে পশ্চিম ওই পূর্বেরই চরিত্রায়ন স্থির ও নির্দিষ্ট করেছে এমনভাবে যে, প্রাচ্যের বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ বাস্তবতাকে, প্রাচ্যের পরিবর্তনশীল ইতিহাসকে, এমনকি পূর্বের হাড়-মাংসের মানুষকেই অস্বীকার করা হয়েছে। অসংখ্য উদাহরণ জড়ো করে বিষয়গুলোকে পরিষ্কার করেছেন সাঈদ নিজেই তাঁর ওই ওরিয়েন্টালিজম বইটাতেই। সাঈদ এও দেখিয়েছেন যে, পূর্বকে নিয়ে পশ্চিমের জ্ঞানোৎপাদনের প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও রুপান্তরিত হয়েছে, অর্থাৎ প্রাচ্যবাদ নিজেই হয়ে উঠেছে একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক নিরিখ বা লেন্স এবং একটি বিশেষ মনোভঙ্গি, যা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন নাই পশ্চিমের মহারথীরাও—পশ্চিমের বড় বড় চিন্তাবিদ, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও শিল্পী। অবশ্যই এঁদের মধ্যে পড়েন গ্যেটে, হেগেল, আর্নল্ডসহ আরও অনেকেই, যদিও গ্যেটে ও হেগেল নিয়ে সাঈদের আলোচনা বেশি দূর এগোয় নাই।
২
তাহলে গ্যেটে প্রসঙ্গে আবারও সামান্য ফিরতে হয়।
গ্যেটের গীতিকবিতার একটি বিশেষ সংগ্রহ নিয়ে তথাকথিত উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকরা তেমন কোনো আলোচনা করেন নাই। গ্যেটের এই বিশেষ সংগ্রহের নাম ওয়েস্ট-ওস্টিলিকের দিওয়ান (ইংরেজিতে ‘ওয়েস্ট-ইস্টার্ন দিওয়ান’)। পারস্য সুফি কবি হাফিজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গ্যেটে ১৮১৪ থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে লিখে ফেলেন ১২ সর্গে ভাগ-করা আস্ত দিওয়ান। সন্দেহ নাই যে, ফার্সি কবিতা নিয়ে গ্যেটের আগ্রহ ছিল গভীর। এও বলা যাবে যে, হাফিজকে নিয়ে গ্যেটের এক ধরনের ঘোর ও অভিভবও কাজ করেছে, যেমন সেটি আরেক প্রসঙ্গে ও পরিসরে প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকার ও কবি কালিদাসকে নিয়েও কাজ করেছে বটে।
যাই হোক, গ্যেটে তাঁর হাফিজ-প্রভাবিত দিওয়ানে তাঁর মতো করেই আজকের লিবারেলদের গদগদ কায়দায় পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন কামনা করেছেন। তবে ওই দিওয়ানে গ্যেটে বিভিন্ন ধরনের কবিতাভঙ্গি ও কবিতা হাজির করেছেন বটে : সেখানে আছে প্রতীকি কবিতা, ইঙ্গিতময় গল্প-ভরা আখ্যান, ইতিহাসের আঁকিবুকিতে ভরা গীতিকবিতা, হাফিজকে নিয়ে পুরা আখ্যান, তৈমুরকে নিয়ে আরেকটি আখ্যান, এমনকি জোলেখা-ইউসুফকে নিয়ে কবিতা ইত্যাদি।
কিন্তু—হায়!—এই মহান কবি গ্যেটের দিওয়ানেও পূর্বকে দেখা হয়েছে এক দারুণ দুর্বোধ্য, রহস্যময় কিন্তু রোমাঞ্চ-জাগানিয়া জগৎ হিসাবে, যে জগৎ শেষ পর্যন্ত গ্যেটের দৃষ্টিতে স্থবির, বৈচিত্র্যহীন এবং এমনকি ইতিহাসবিহীনই হয়ে থাকে। আরও বলা দরকার, পূর্বকে প্রশংসা করতে গিয়েও অনেক পশ্চিমা লেখক পূর্বকে স্থির স্পেস হিসাবে দেখেছেন বা বিবেচনা করেছেন। প্রায়ই একই ধরনের পূর্বকে হাজির দেখি ফরাসি রাজনৈতিক-দার্শনিক মতেস্কুর বিখ্যাত পার্সিয়ান লেটারস (পারস্যের চিঠি)-এ। এই কাজটি ১৭২১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।
আরেকটি কাজের কথা এখানে না বললেই নয়; সেটি হচ্ছে মার্কিন কবি এডগার অ্যালেন পো’র একটা নাতিদীর্ঘ কবিতা, যার নাম ‘আল আরাফ’। ১৮২৯ সালে কবিতাটা প্রথম ছাপা হয়। কবিতায় পো কোরআন শরীফের ৭নং সুরাকে খানিকটা ব্যবহার করেছেন। ওই সুরার খানিকটা মধ্যস্ততায় এবং পো’র ভাষ্য মোতাবেক ‘আল আরাফ’ একটি বিশেষ স্থানকে নির্দেশ করে, যে স্থান ঝুলে থাকে বেহেশত ও দোজখের মাঝামাঝি, যেখানে বসবাস করে অর্ধেক পাপী অর্ধেক পুণ্যবানেরা, যারা বেহেশতে ও দোজখে—উভয় জায়গাতেই—যাওয়ার সম্ভাবনা ধারণ করে।
কবিতাটা আসলেই বেশ জমে ওঠে পো’র দুর্দান্ত কাব্যকৌশলের কারণেই। কিন্তু গোল বাধে তখনই যখন পো ওই কবিতার কিছু কিছু জায়গায় আরব জগৎ নিয়ে কথা বলা শুরু করেন। আর কথা বলেন এমনভাবে যে, মনে হয় ওই জগতে রয়েছে কেবল রহস্য আর রোমাঞ্চ, তার বেশি কিছু নয়।
আর আরব জগত নিয়ে পো’র ইঙ্গিতময় কাব্যিক বয়ান নিমেষেই মনে করিয়ে দেয় ইংরেজ আলোকচিত্রী ফ্রান্সেস ফ্রিথ (১৮২২-১৮৯৮)-এর মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক ফটোগ্রাফির কথা; এমনকি আরও মনে করিয়ে দেয় সেই ১৯২১ সালে তৈরি-করা এবং জর্জ মেলফোর্ড পরিচালিত বিখ্যাত ‘সাইলেন্ট মুভি’র কথা, যার শিরোনাম দ্য শেইখ। এই প্রসঙ্গে হিটলারের একটা প্রিয় সিনেমার নামও উল্লেখ করা যায়। এই সিনেমাটার শিরোনামেই আমাদের অঞ্চলের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। শিরোনামটা হচ্ছে দ্য লাইভস অফ এ বেঙ্গল ল্যান্সার। ১৯৩৫ সালে ছবিটা তৈরি করা হয়। আর ১৯৩০ সালে ফ্রান্সিস ইয়েটস-ব্রাউন (১৮৬৬-১৯৪৪) ওই একই শিরোনামে একটি আত্মজৈবনিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন।
বলা দরকার, এই ইয়েটস-ব্রাউন একসময় মেজর হিসাবে ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন এবং ভারতের মাটিতেই তিনি ভারতকে দেখার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তার আগ্রহের দুটো এলাকাকে অনায়াসেই চেনা যায়। একটি হচ্ছে মুসলমান এবং অপরটি যোগ ব্যায়াম। উপন্যাসটিতে ইয়েটস-ব্রাউনের সাক্ষাৎ সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতায় ভারতের চিত্রায়ন প্রাচ্যবাদী অভিক্ষেপকে মোটেই এড়াতে পারেনি। সেখানে ভারত হয়ে উঠেছে একপেশে আধ্যাত্মিকতার আবাসভূমি, তার বেশি কিছু নয়।
কিন্তু এই উপন্যাসের চেয়েও আরও বেশি প্রাচ্যবাদী হয়ে থাকে ওই সিনেমাটি। অবশ্য সিনেমাটা অনেকাংশেই মূল উপন্যাসের প্লট থেকে সরে এসেছে; ওখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে ভারতের দানা-বেঁধে-ওঠা স্বদেশীদের বিদ্রোহ দমনের বিষয়টা আর ওই বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর বীরত্বের কথা। অবশ্যই বলা যাবে যে, এই ছবিটির প্রতিটি মুহূর্তেই পুরুষতন্ত্র তার পেশি ফোলাতে থাকে। মোহাম্মাদ খান নামের একটা চরিত্র পাওয়া যাবে এই ছবিতে। কিন্তু ছবিটাতে সে যতোটা না বিদ্রোহী, তার চেয়ে বেশি বর্বর।
হ্যাঁ, এভাবে সাদা চামড়ার মানুষেরা অনায়াসেই ভারতীয় মুসলমানদের এবং অন্যান্য অ-সাদারও ‘বর্বরতা’র ছবি এঁকে ফেলে। আরেকটি বিশেষ কারণে ছবিটাকে তাৎপর্যপূর্ণ ঠেকে : সেটি হলো ঔপনিবেশিকতার পুরুষতান্ত্রিক চেহারা ও চরিত্র, যে বিষয়টি মোটেই বিবেচনায় আনেন নাই এডওয়ার্ড সাঈদ।
সাঈদের দেয়া অসংখ্য উদাহরণের বাইরেও আরও অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব কী করে প্রাচ্যবাদ হয়ে ওঠে একটি উপনিবেশবাদী-বর্ণবাদী-পুরুষতান্ত্রিক প্রকল্প, যা এখনো বিভিন্নভাবে জারি আছে বর্তমান দুনিয়ায়।
৩
উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদ এবং তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ ও চালিকাশক্তি হিসাবে ইউরোপকেন্দ্রিকতা ও প্রাচ্যবাদ, বা প্রাচ্যবাদী ইউরোপকেন্দ্রিকতা ও ইউরোপকেন্দ্রিক প্রাচ্যবাদ সকলেই বিভিন্ন ধরনের ছোট-বড় প্রতিরোধের মুখে পড়েছে ‘তৃতীয় বিশ্ব’-তেই। এই প্রতিরোধের কথা বলতে গেলে বলতে হয় এশিয়া ও আফ্রিকায় সংঘটিত বিভিন্ন বিউপনিবেশায়নের আন্দোলন বা জাতীয় মুক্তির লড়াইের কথা—যেগুলো মোটামুটিভাবে চল্লিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অবশ্যই এই সব প্রতিরোধ-লড়াই-আন্দোলন রাজনৈতিকভাবে খানিকটা সাফল্য অর্জন করেছে। এশিয়ায় ও আফ্রিকায় সেই কারণে স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে, অর্থাৎ ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের পতন ঘটেছে। কিন্তু ওইসব প্রতিরোধ-লড়াই-আন্দোলন রাজনৈতিকভাবে খানিকটা সফল হলেও সাংস্কৃতিকভাবে সেগুলো সফল হয় নাই মোটেই; কেননা এখনো ঘরের ভেতরেই আধিপত্যকামী পশ্চিমা ‘সভ্যতা’ ও সংস্কৃতির জয়গান শুনি—এখনো প্রশ্নাতীতভাবে আমাদের কাছে মহান ও মহৎ হয়ে থাকে গ্রিক ‘সভ্যতা’ কিংবা একজন গ্যেটে বা এমনকি একজন আর্নল্ডও (তবে আমি অবশ্যই এঁদের কাজের নান্দনিক গুরুত্বকে কখনো অস্বীকার করি না)।
সাম্প্রতিক সময়ের উপনিবেশবাদী সংস্কৃতিসহ বর্ণবাদ, প্রাচ্যবাদ ও ইউরোপকেন্দ্রিকতার কথা বলতে গেলে অবশ্যই বলতে হবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কথা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি আজ ইউরোপকেন্দ্রিকতাকেই ঢেলে সাজিয়েছে এমনভাবে যে, ওই ইউরোপকেন্দ্রিকতা রূপান্তরিত হয়েছে মার্কিনকেন্দ্রিকতায়। বলা দরকার যে, তৃতীয় বিশ্বে সংঘটিত বিভিন্ন বিউপনিবেশিকীকরণের আন্দোলনের সাংস্কৃতিক ব্যর্থতার সুযোগ নিয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিজেই। বিশ্বায়নের নামে (এই বিশ্বায়ন আসলেই মার্কিন পুঁজিবাদের সাম্প্রতিক স্তরের নামও বটে আর এই স্তরটা হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিজেই) এশিয়ায়, আফ্রিকায় ও লাতিন অ্যামেরিকায় মার্কিন কর্পোরেট সংস্কৃতি তার দারুণ আধিপত্য জারি রেখেছে। এখানে এও বলা দরকার, পুঁজি কেবল একা একা দুনিয়াজুড়ে উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়ায় না; তার সঙ্গে থাকে তার নিজস্ব অলঙ্কারশাস্ত্র, বয়ান, ভাষা ও ভাষ্য, মতাদর্শ, পাইক-পেয়াদা বা সৈন্য-সামন্ত। আর এগুলো একত্রে বিবেচনায় রাখলে বলতে হয় সংস্কৃতির কথাই, যে প্রসঙ্গে আবারও চলে আসে উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ ও প্রাচ্যবাদের কথাও।
তাহলে নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে বলা যাবে যে, মার্কিন উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ ও প্রাচ্যবাদের ইতিহাস নিদেনপক্ষে শুরু হয় সেই ১৭৭৬ সালে থেকেই। এমনকি উনিশ শতকের মানবতাবাদী মহারথীরাও প্রাচ্যবাদী ধ্যানধারণা ও কল্পনা থেকে মুক্ত নন। উদাহরণ হিসাবে বলা যাবে এমনকি ওয়াল্ট হুইটম্যানের মতো প্রগতিশীল কবির ‘প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া’ নামের কবিতাটার কথা (যা আমাদের নিমিষেই ই এম ফরস্টার-এর উপন্যাস এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া’র কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়)। এই কবিতায় হুইটম্যানের গণতান্ত্রিক মানবতাবাদ দুনিয়া সফর করতে গিয়ে প্রাচ্যবাদের খপ্পরেই পড়ে যায়; পৃথিবীটাকে ঠিকঠাক করার এক দারুণ আকাঙ্ক্ষা কবিতায় উচ্চারিত হতে থাকে এই ধারণা দিয়ে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঠিকই আছে, কেবল সমস্যা অন্য জায়গায়। এই কবিতায় ‘সাদা’ চোখে বা নিরিখে ভারত আবারও একমাত্রিকভাবে আধ্যাত্মিকতার আবাসভূমি হয়ে ওঠে। তবে হুইটম্যান (বা হোয়াইট ম্যান?) একলা নন। তাঁর কাছাকাছি আছেন মার্কিন কবি এডগার অ্যালেন পো, যাঁর কাজের কথা আগেই উল্লেখ করেছি।
কিন্তু মার্কিন প্রাচ্যবাদের দীর্ঘ ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্ব স্পষ্ট হয়ে থাকে ১১-সেপ্টেম্বর-পরবর্তী পৃথিবীতে। এই পর্বের সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির যোগাযোগ একেবারেই সরাসরি। মার্কিন প্রাচ্যবাদের এই সাম্প্রতিক পর্বে প্রধান (একমাত্র না হলেও) খলনায়ক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে “আরব জগত” (যার ভেতরে আফগানিস্তানকে ফেলার পশ্চিমা বা মার্কিন রেওয়াজ এখনো লক্ষ্য করা যায়)। সত্য, আরব, ইসলাম, মুসলিম ও দক্ষিণ এশিয়াকে গুলিয়ে ফেলে এদের সমার্থক করে তোলা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক বয়ানে ও ভাষ্যে যেমনি, হলিউডেও তেমনি। প্রাচ্যবাদী দৃষ্টিকোণটাও সক্রিয় থাকে তীব্রভাবেই : মুসলিম মানেই ‘টেরোরিস্ট’ আর আরব মানেই মুসলমান! বলা দরকার, এক হলিউডই কয়েকশ’ ফিল্ম তৈরি করেছে, যেসব ফিল্মে কোনো না কোনোভাবে প্রাচ্যবাদী ছাঁচে ও আদলে উপস্থিত করা হয়েছে আরবদের।
এখানে ফিল্ম নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ, তুলনামূলকভাবে পুরনো কিন্তু এখনো প্রাসঙ্গিক গবেষণামূলক বইয়ের কথা উল্লেখ করতে হচ্ছে। বইটির নাম রিল ব্যাড অ্যারাবস্। বইটি লিখেছেন ফিল্ম-ইতিহাসবিদ জ্যাক জি শাহীন। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০০১ সালে। লেখক বইটিতে হলিউড থেকে উৎপাদিত ৯০০টি ফিল্মের পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, হলিউড নিজেই আরবদের তৈরি করেছে মাথামোটা সন্ত্রাসী কিংবা ভয়ঙ্কর বা বিপজ্জনক হিসাবে। শাহীনের ফর্দ মোতাবেক কতগুলো হলিউডি ফিল্মের নাম বলে নেয়া যাক : রুলস্ অফ এনগেইজমেন্ট, দ্য ডেল্টা ফোর্স, ডেথ বিফোর ডিসঅনার্, টু লাইস্ ইত্যাদি।
উদাহরণ অবশ্যই বাড়ানো সম্ভব। তবে এর মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ আর প্রাচ্যবাদ গভীরভাবে পরস্পর-সম্পর্কিত। আর এদের পরস্পর-সম্পর্কিত বলয়েই আমাদের সাংস্কৃতিক অনুশীলনও অন্যভাবে ‘অপর’ তৈরি করতে থাকে; নারী অপর, চাকমা অপর, শ্রমিক অপর ইত্যাদি। অন্যদিকে মধ্যবিত্তের ‘আমরা’ আবার ‘পশ্চিমা’ সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণ করে বসে থাকি এবং তাদের স্থানিক সংস্করণও তৈরি করতে থাকি। বলিউডে মজে থাকি। হলিউডেও। আমাদের সাহিত্য-সমালোচনার অধিকাংশ জুড়েই তো থাকে ঔপনিবেশিক মনোগঠনজাত বিচার-বিবেচনা ( যেন নজরুলকে বায়রন ও শেলী’র মতো সাদা মহারথী-কবিদের সঙ্গে তুলনা করলেই নজরুল যেন জাতে ওঠে!) অন্যদিকে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার চেহারা ও চরিত্র অনেকাংশেই ঔপনিবেশিক, যেমন ঔপনিবেশিক চেহারা নিয়েই বহাল তবিয়তে আছে আমাদের মিলিটারি ব্যবস্থা ও পুলিশ ব্যবস্থা।
তাই বিউপনিবেশায়ন এখনো আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মতোই অসমাপ্ত প্রকল্প। প্রকৃতপক্ষে সাংস্কৃতিক বিউপনিবেশায়ন ছাড়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিও সম্ভব না। ইতিহাসের এই পর্বে যে গণতন্ত্র তার অ্যাজেন্ডায় বিউপনিবেশায়নকে অন্তর্ভুক্ত করে না, তা গণতন্ত্রই নয়। তবে উপনিবেশবাদবিরোধিতা বা বিউপনিবেশায়ন মানেই প্রশ্নহীন বর্জন বা বিচ্ছিন্নতা নয়। যা জরুরি তা হচ্ছে দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত থেকেই দুনিয়ার সঙ্গে প্রশ্নমূলক বোঝাপড়ার ভেতর দিয়েই গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সার্বিক মুক্তির লড়াই।
আজফার হোসেন, অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক, যুক্তরাষ্ট্র