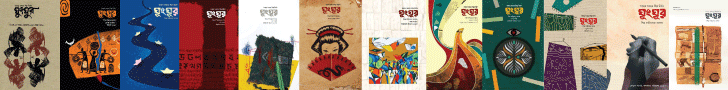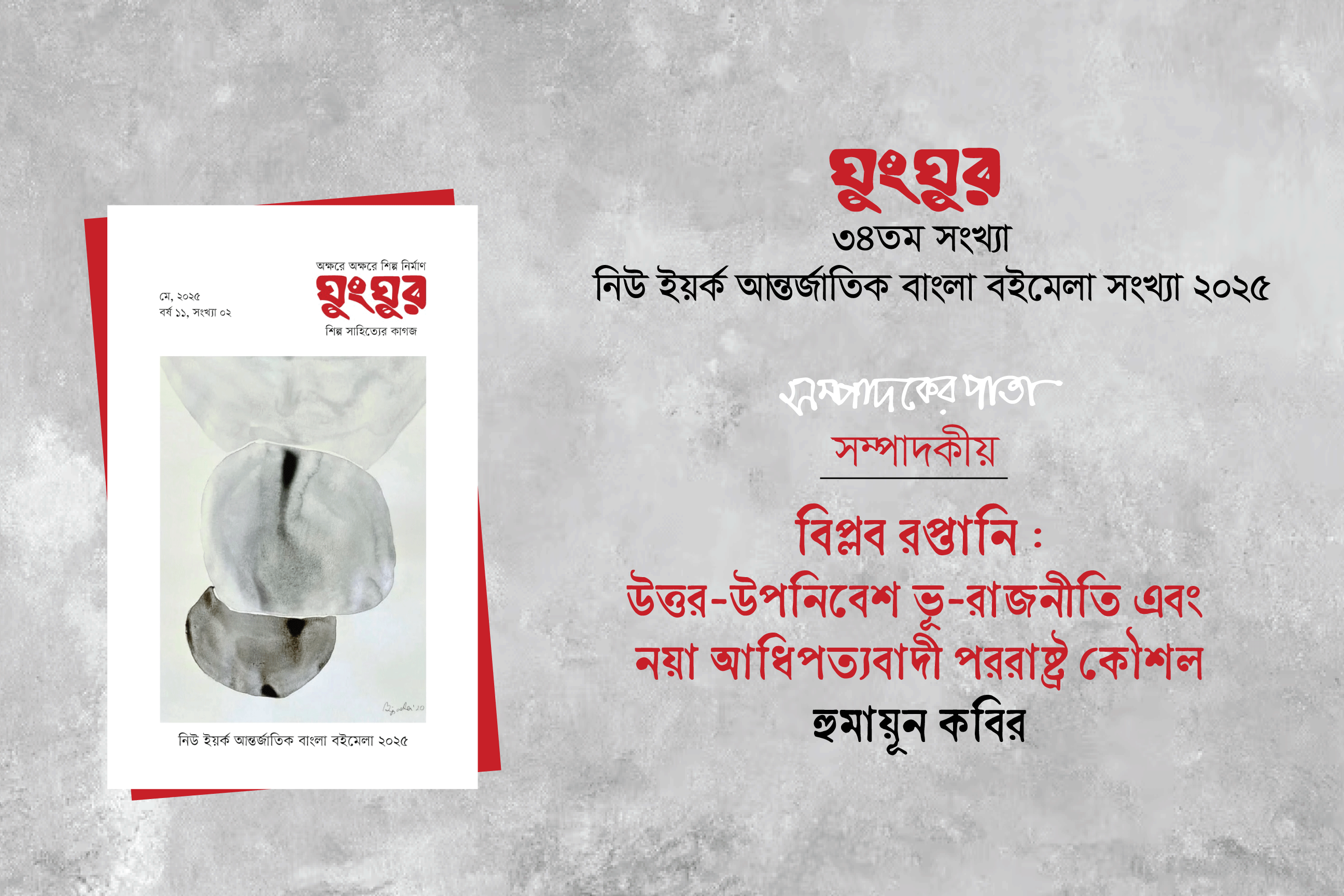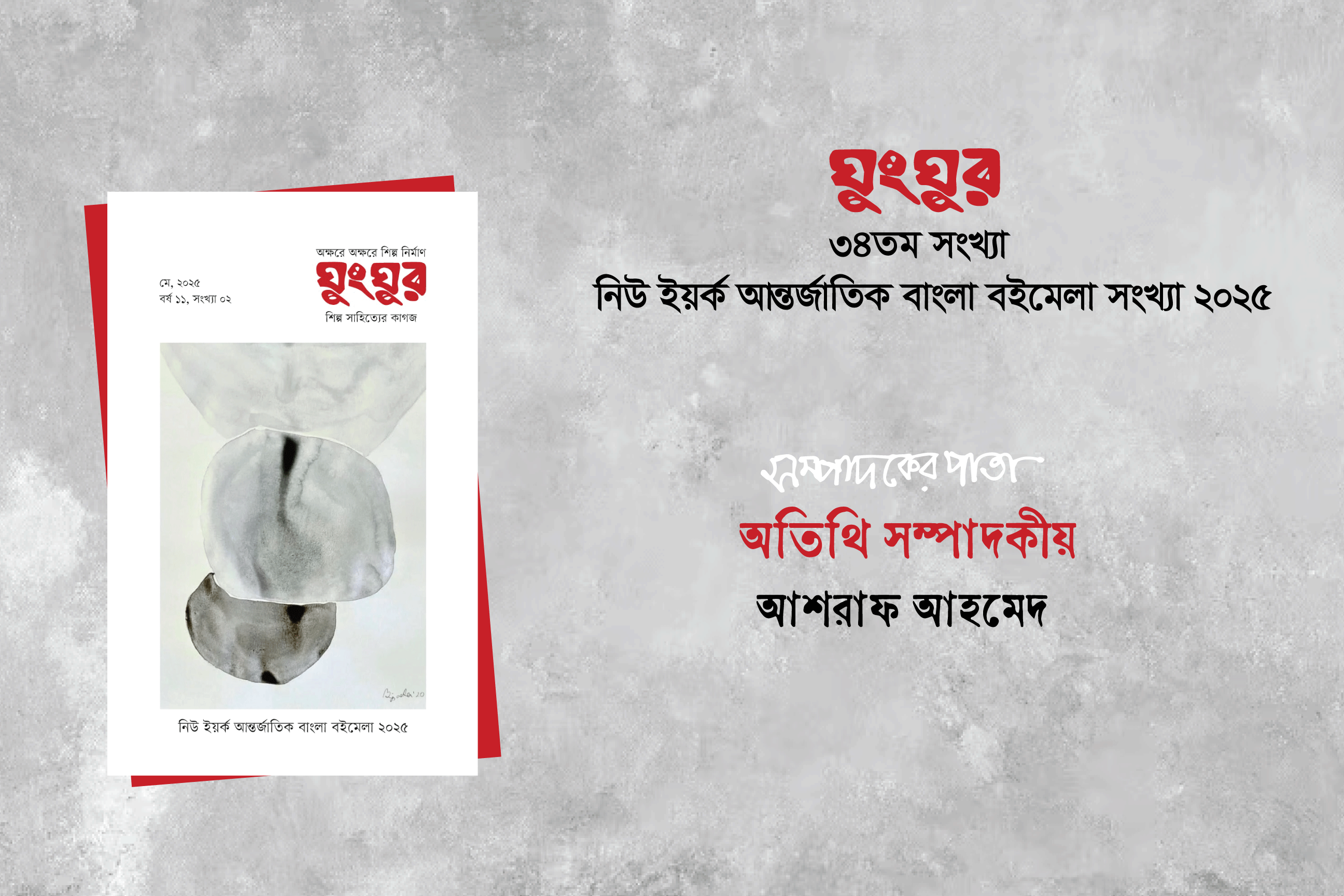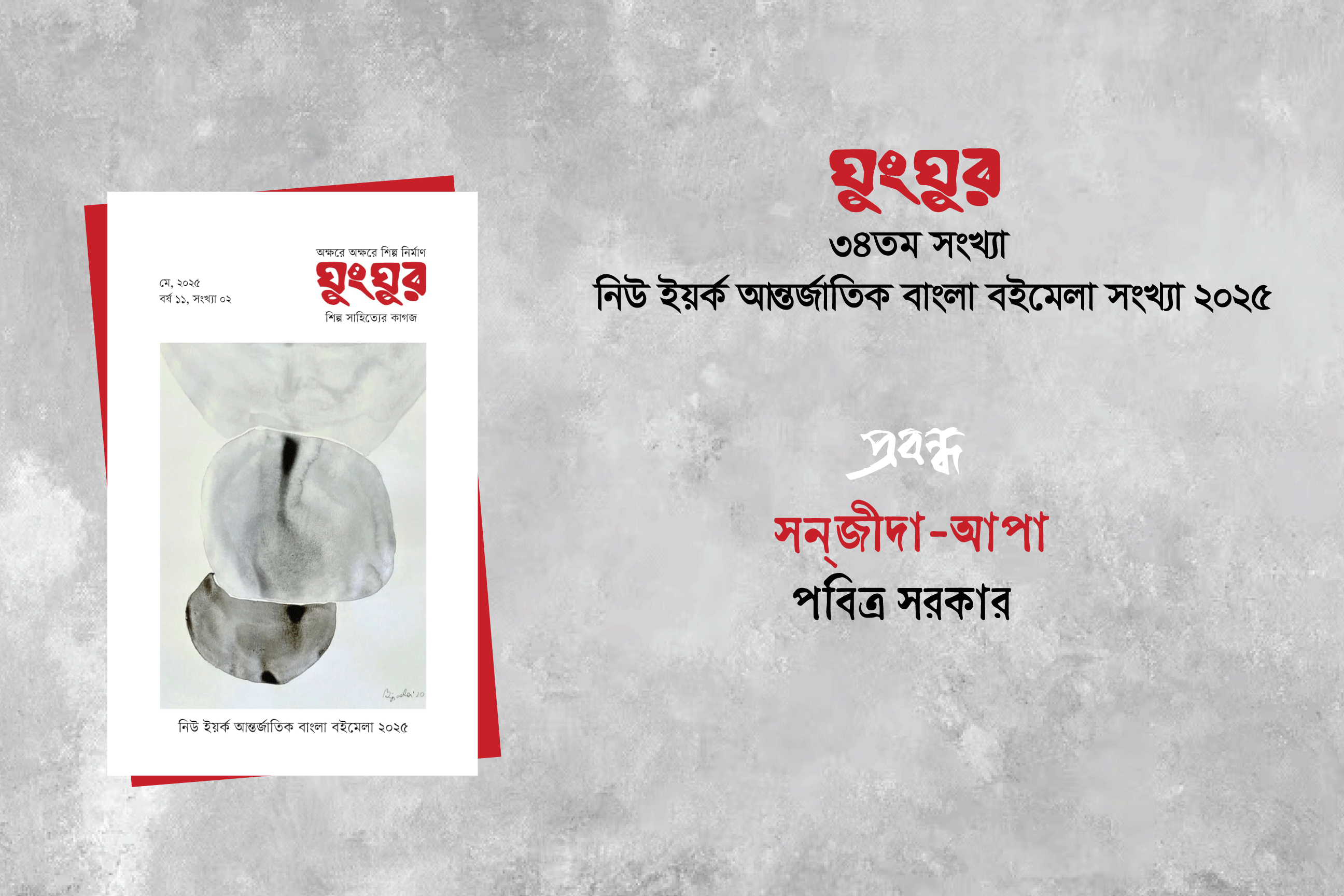অতিথি সম্পাদকের ভাষ্য

ঔপনিবেশিক জ্ঞান/ক্ষমতা, সাংস্কৃতিক সংগ্রাম ও সৃজনশীলতা
গোড়াতেই ঘুংঘুর-এর এই সংখ্যার সকল লেখককে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। একইসঙ্গে অভিনন্দন জানাই ঘুংঘুর-এর সম্পাদক হুমায়ূন কবিরকেও, যিনি পাঁচ বছর ধরে এই পত্রিকা নিয়মিত বের করার ভেতর দিয়ে তাঁর অঙ্গীকার, নিষ্ঠা আর উদীপ্ত কর্মশক্তিকে আমাদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক করে রেখেছেন। তাঁকে বিশেষভাবে ধন্যবাদও জানাই এই কারণে যে, তিনি আমাকে বর্তমান সংখ্যার অতিথি-সম্পাদক হিসাবে নিমন্ত্রণ করেছেন। আমি সনাতন অর্থে অভিজ্ঞতাবাদী নই; তবুও জীবনের বিভিন্ন সময়ে পত্রিকা-সম্পাদনার সুখকর ও তিক্ত উভয় ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে অনায়াসেই বলতে পারি, লেখক ও পাঠক ছাড়া সম্পাদনার কাজ যেমন অর্থহীন, ঠিক তেমনি সেই কাজের আনন্দ বোধ করি নিহিত থাকে এক ধরনের পরজীবিতায়, যেখানে ‘পর’কেই আপন ভাবা স্বাভাবিক ঠেকে। তাই এই সংখ্যার কবিসহ সকল লেখককে আপন ভেবেই বর্তমান বয়ানের উপসংহারে আমার তর্জমায় একটি ‘পর’দেশি কবিতা তাঁদেরকে উৎসর্গ করার সুযোগ নিয়েছি।
এও বলা দরকার, আমি এখানে সনাতন অর্থে কোনো সম্পাদকীয় লেখার চেষ্টা করছি না মোটেই। লেখকদের কাজ নিয়ে সম্পাদকের মন্তব্য বা মতামত শুরুতেই জুড়ে দেয়ার প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতিকে অনুসরণ করার পক্ষপাতী নই আমি, কেননা আমি মনে করি—এবং আশাও করি—যে, বর্তমান সংখ্যার প্রতিটি লেখা—প্রতিটি কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, আলোচনা—নিজেই তার নিজের মতো করে নিজের কথা জানান দেবে। তবে উষ্ণ আতিথেয়তায় আমাকে এখানে যে পরিমান পরিসর বরাদ্দ করা হয়েছে, তাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিষয়ে—এবং শিল্পসাহিত্য-সম্পর্কিত বিষয়েও—আমার কিছু ভাবনা, পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও এমনকি প্রস্তাবনা পেশ করার সুযোগ নিচ্ছি। তবে যুক্ত করা দরকার যে, বর্তমান বয়ানে হাজির-হওয়া আমার কোনো মতামতই ঘুংঘুর পত্রিকার সামগ্রিক মতামত বা অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে না, কেননা অন্যদের মতোই আমিও আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এখানে একজন লেখক হিসাবে হাজির হয়েছি।
২
সুরা পান আর শেকসপিয়র-পাঠ হাত ধরাধরি করে চলেছে এক সময়। এখনো চলে।
মনে পড়ে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ নামের বইয়ে উনিশ শতকের একদল বাঙালি তরুণের রঙ-মাখা সঙ-সাজা জীবনের একটা খণ্ডচিত্র হাজির করেছিলেন। তখন বাংলায় ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের পোয়াবারো। শিবনাথ শাস্ত্রীর বয়ান মোতাবেক ওইসব তরুণ সুরা পান করাকে এবং তার সঙ্গে শেকসপিয়র আউড়ানোকে দারুণ ব্যাপার মনে করতো। শেকসপিয়রের একেকটি লাইন উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যেন তারা একেকটি রাজ্য জয় করতো।
সুরা ও শেকসপিয়র যে একেবারে অন্তর্নিহিতভাবে প্রতিক্রিয়াশীল বা উপনিবেশবাদী, তা কিন্তু বোঝাতে চাচ্ছি না; কিন্তু কী করে ওই সুরা ও শেকসপিয়র আধিপত্যবাদী ক্ষমতা-সম্পর্কের ‘কনফিগারেশন’-এ কাজ করতে থাকে, সেটা দেখানো দরকার বলে আমি মনে করি। হ্যাঁ, সুরা ও শেকসপিয়র অবশ্যই তাদের কাছে কেবল অনুপ্রাসের বিষয় ছিল না; সেগুলো ছিল শ্রেণী-অবস্থান ও সামাজিক অবস্থান নিয়ে, রুচি ও আভিজাত্য নিয়ে, তাদের অহংকারের বিষয়। শুধু তাই নয়। সেগুলো ছিল বাংলাদেশের ‘নোংরা’ আমজনতার প্যাচপেচে শীর্ণ দেহের সাক্ষাৎ বিপরীত। আরেক স্পেসে, খানিকটা সুরা ও শেকসপিয়রের পথ ধরে, এক ধরনের আত্ম-সচেতন কিন্তু নকলবাগিশ ভঙ্গি তৈরি হচ্ছিল। প্রভাবিত হওয়া মানেই যে স্খলন বা বিচ্যুতি বা ‘জাত-যাওয়া’ ব্যাপার তা তো নয়; কিন্তু কোন্ প্রভাব কোন্ প্রসঙ্গে কি কাজ করে সেটা দেখা দরকার। তো, সেই নকলবাগিশ ভঙ্গিটা তৈরি হচ্ছিল খোদ সাহিত্যের এলাকায়। এই ভঙ্গির বিভিন্ন আলামত লক্ষ্য করা যায় সাহিত্যিক আধুনিকতাবাদেই।
শুধু পশ্চিমাই নয়, পশ্চিমাকেন্দ্রিক ও ইউরোপকেন্দ্রিক নন্দনতত্ত্বের রমরমা আধিপত্যকে স্বেচ্ছায় স্থানীয় মর্যাদা ও বৈধতা দেওয়ার রেওয়াজ শুরু হয়েছিল ওই ‘তিরিশি’ আধুনিকতাবাদের একটা বিশেষ ভার্সনের সুবাদেই; যেন এমনি একটা মন্ত্র কাজ করে যাচ্ছিল : কবিতার জন্য চাই বোদলেয়র ও ব্রথেল।
অবশ্যই আধুনিকতা মানে কেবল বোদলেয়র ও ব্রথেল নয়; কিন্তু তাদের সহাবস্থানের নান্দনিক উদযাপন কেবল খামখেয়ালিপনা বা নিছক নিরীক্ষার বিষয় ছিল না। বরঞ্চ এর তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফলকে এখনো আমরা লক্ষ্য করে চলেছি। এবং তার একটা তাৎক্ষণিক প্রভাবের কথা এভাবে বলা যায় : সেই সময় গ্রাম-ভরা ঢাকা বা কলকাতা শহর লন্ডন বা প্যারিসের মতো মেট্রোপলিটন মহানগরী না হলেও ওই ঢাকা বা কোলকাতার বাসিন্দা হয়েই একেবারে ভিনদেশি কায়দায় ‘মহানাগরিক’ হওয়ার খায়েশ কাজ করেছে। সোজা কথায় : দেহটা কলকাতায়, কিন্তু মানসিক নোঙ্গরটা একেবারেই প্যারিসে—আহ, ঝলমলে প্যারিস নগরী! আইফেল টাওয়ার, জমে-ওঠা আর্ট গ্যালারি, বোহেমিয়ান বোদলেয়র, কিংবা তর্কের ঝড়-তোলা, শিল্প-বয়ানে-ভরপুর, কফির গন্ধ-মৌ-মৌ-করা ক্যাফে, কিংবা নাগরিক জীবনের বিবমিষা-ভরা বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি দৃশ্যকল্প বা অনুষঙ্গ ঘুরঘুর করতে থাকে কবির মনের অলিগলিতে (বা রাজপথে)।
নান্দনিকতার অর্থও তৈরি হতে থাকে; যেমন নান্দনিকতা থাকে সেই দূরত্বে, যে দূরত্ব ভাব ও বস্তুর এবং মন ও দেহের মাঝখানে জোর করেই তৈরি করা হয়।
আর এই ‘ভাব/বস্তু’ কিংবা ‘মন/দেহ’-এর একটা বড় ‘স্প্লিট’ বা ফারাক বাংলা আধুনিকতাবাদী সাহিত্যের একটি বিশেষ পর্যায়কে চিহ্নিত করে রাখে। বিরাজমান উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে সংস্কৃতির বিভিন্ন কিসিমের যোগাযোগের বিষয়টি বিবেচনায় না রেখেই কলকাতা বা ঢাকায় বসে জোর করে নাগরিকতা ফলানোর ভেতর দিয়ে যে কাব্য-সংস্কৃতি এক সময় গড়ে উঠেছিল ‘তিরিশী’ আধুনিকতাবাদী কবি বুদ্ধদেব বসু ও সুধীন দত্তদের হাতে ধরেই, সেই কাব্য-সংস্কৃতি নিজেই উপনিবেশবাদের সঙ্গে আধুনিকতাবাদের সম্পর্কটাকে বারবার হাতেনাতে ধরিয়ে দেয় বটে। এখানে বিশেষ করে বুদ্ধদেব বসু নিয়ে দুয়েকটি কথা না বললেই নয়।
না, বুদ্ধদেব বসুর অবদানকে অস্বীকার করার কোনো জো নেই। সব্যসাচী লেখক হিসাবে তাঁর খ্যাতি এখনো অক্ষুন্ন। একাধিক মনে-রাখার মতো কবিতা তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন, যেমন তিনি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তকে দিয়েছেন মন-মাতানো পাঠযোগ্য গদ্য। আর কেই-বা অস্বীকার করবেন বুদ্ধদেব বসুর দুর্দান্ত সাহিত্যিক তৎপরতাকে? তাঁর সেই তৎপরতা দুর্দান্তই বটেই এবং তা মোটেই ফলাফলশূন্য নয়। এই কারণে মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক ‘রুচি’ গঠনে বুদ্ধদেবের কাজের একটা বড় ভূমিকা আছে : তিনি মধ্যবিত্তকে ইউরোপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেনও বটে। এখানে তাঁর বোদলেয়র-অনুবাদের প্রসঙ্গ সঙ্গত কারণেই চলে আসে, যেমন আসে তাঁর বোদলেয়র-পাঠের প্রসঙ্গও। কিন্তু কোন বোদলেয়র?
সত্যি কথা বলতে, জর্মন সংস্কৃতিতাত্ত্বিক ওয়াল্টার বেনজামিনের বিখ্যাত বোদলেয়র-পাঠের পাশে যখন বুদ্ধদেবের বোদলেয়র-পাঠকে রাখি, তখন সহজেই ধরা পড়ে বুদ্ধদেবীয় আধুনিকতাবাদের পশ্চিমা উপনিবেশবাদ-প্রভাবিত চেহারাটা। অবশ্যই বুদ্ধদেবের বোদলেয়র আর বেনজামিনের বোদলেয়র একই সঙ্গে না যাওয়ারই কথা। তাদের সঙ্গতিপূর্ণ যোগাযোগ আমি আশাও করি না। তবে তাদের পাঠের পার্থক্যটা তাৎপর্যপূর্ণ বটে। যেখানে বুদ্ধদেবের কাছে বোদলেয়র হয়ে ওঠেন বস্তুজগত-বিচ্ছিন্ন কিন্তু ইন্দ্রিয়-ধাক্কা-দেয়া চিত্রকল্পের কবি বা জমজমাট চৈহ্নিক অর্থনীতির ‘আধুনিক’ কবি, সেখানে বেনজামিনের রাজনৈতিক-অর্থনীতি-প্রভাবিত সাংস্কৃতিক-নান্দনিক বিবেচনায় বোদলেয়র হচ্ছেন দারুণভাবে জমে-ওঠা পুঁজিবাদের একজন গুরুত্বপূর্ণ লিরিক কবি, মেট্রোপলিসের কবি, যিনি ‘আধুনিকতা’ যে ‘শক-ওয়েভ’ তৈরি করেছিল, কবিতার স্পেসে তারই ভাষিক মধ্যস্ততা করে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সেই প্রবণতার উজ্জ্বলতম প্রতিনিধি।
কিন্তু এও জোরেশোরে বলা দরকার, বেনজামিনের বিবেচনায় বোদলেয়রের কবিতা সরাসরি উনিশ শতকের পণ্য-সংস্কৃতির একটি বিশেষ পর্যায়কে তুলে ধরে এবং এই কারণে ওই পণ্য-সংস্কৃতির আলোচনা ব্যাতিরেকে বোদলেয়রের কবিতার আলোচনা অপর্যাপ্ত থেকে যেতে বাধ্য। সেখানেই শেষ নয়। বেনজামিনের আলোচনায় ধরা পড়ে এই বিষয়টা যে, বোদলেয়রের কবিতা-পাঠের ভেতর দিয়েই দেখা সম্ভব কী করে ‘অ্যালেগরি’ ও পণ্য-রূপের মধ্যে এক ধরনের আত্মীয়তা তৈরি হয়। এটি আরেক প্রসঙ্গ। তবে বেনজামিনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তত্ত্বায়ন নিজেই বুদ্ধদেবের বোদলেয়রকে পশ্চিমা উপনিবেশবাদের সাংস্কৃতিক পণ্য হিসাবে চিহ্নায়িত করতে সাহায্য করে, যে পণ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী সাংস্কৃতিক উদযাপন আমরা লক্ষ্য করি বুদ্ধদেব বসুর কাজে। এর একটা ফল দাঁড়ালো এই যে, বুদ্ধদেব-প্রভাবিত সাহিত্যিক আধুনিকতাবাদ বিভিন্নভাবেই এক ধরনের নান্দনিক উপনিবেশবাদের পক্ষে কাজ করে চললো।
বুদ্ধদেব বসু ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আনা দরকার। ইউরোপীয় বিশ, তিরিশ ও চল্লিশের দশকের অনেক সাদা লেখকের কাজে বুদ্ধদেব ও সুধীন দত্তের তুমুল আগ্রহ ছিল বটে। ইউরোপীয় সাহিত্যে এঁদের জ্ঞান-গরিমা নিয়ে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের অনেকেই এখনো অহংকার করে থাকেন, যেমন ইংরেজি-জানা পণ্ডিতদের অনেকেই সেই কাজটা করেন। কিন্তু ওই দশকগুলোতে ‘মূলধারা’র সাদা আধুনিকতাবাদের বিপরীতে উপনিবেশবাদবিরোধী বিকল্প আধুনিকতাবাদের যে সংস্করণ তৈরি হচ্ছিল ওই পশ্চিমা মুলুকেই, তাতে বুদ্ধদেব বসু ও সুধীন দত্তের এবং তাদের অনুসারীদের কোনো আগ্রহ ছিল না বললেই চলে।
এখানে দুটো আন্দোলনের কথা অনায়াসেই উল্লেখ করা যায় : একটি হলো ‘হারলেম রেনেসাঁস’ আন্দোলন এবং অপরটি ‘নিগ্রিচিউড’ বা ‘নিগ্রোবাদ’ আন্দোলন। এই দুই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত লেখক ও সাংস্কৃতিক অ্যাকটিভিস্টদের কাজগুলো যে বুদ্ধদেব বসু ও সুধীন দত্তের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল তা বলা যাবে না। কিন্তু, না, একজন কালো কবি—আফ্রিকান অ্যামেরিকান কবি—ল্যাংস্টন হিউস বা আফ্রিকার কবি, সেনেগালের কবি, লিওপল্ড সেডার সেঙ্ঘর বুদ্ধদেব বসুদের টানে নাই মোটেই, কেননা তিরিশি আধুনিকতাবাদীদের রাজনীতিবিমুখতার রাজনীতির কারণে তাঁদের কাছে অগ্রাধিকার পেয়েছিলো ইউরোপীয় বা সাদা সাহিত্যিকরা। আর এই তিরিশি আধুনিকতাবাদ নিজেই নান্দনিকতার দোহাই পেড়ে বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা-সম্পর্কের জাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখে। এই জালে এখনো আমাদের ভাষা, বয়ান, পাঠ, সমালোচনা, তর্ক-বিতর্কের ধরন, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি আটকে থাকে। ঠিক এই কারণেই এখনো ওইসব অধ্যাপক আর ‘সংস্কৃতিসেবক’ ও ‘সৃজনশীল’ লেখকের ভুরু কুঁচকে যায় উপনিবেশবাদ কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে। তারা বলে ওঠেন, ‘উপনিবেশবাদ নিয়ে এত টানাটানি কেন?’
৩
উপনিবেশবাদ নিয়ে এত টানাটানি কেন?’ প্রশ্নটা একটা কথোপকথনের কথা মনে করিয়ে দেয়।
বছর কয়েক আগে গ্রীষ্মের এক রোদেলা বিকেলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির এক তরুণ শিক্ষকের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর কাজের ও আগ্রহের এলাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই চোখ তাঁর চিকচিক করে ওঠে। ‘হ্যাঁ, উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্য ও তত্ত্বেই আমার আগ্রহ,’ কথাটা বলেন ইংরেজির ওই শিক্ষক।
আমি বাংলায় কথা বলি, তিনি বলেন ইংরেজিতে।
এবার আমি জিজ্ঞাসা করি, ‘আপনি কি আপনার বিষয় নিয়ে কিছু লিখেছেন?’
‘অবশ্যই’।
‘বাংলায়’?
‘না। লিখেছি ইংরেজিতে। আসলে বাংলা আমার আসে না’।
দ্রুত উত্তর দেন ইংরেজির ওই শিক্ষক। তাঁর কণ্ঠস্বরে সামান্যতম কম্পন লক্ষ্য করি না। এবারে আমি বলি : ‘আপনি কি তাহলে ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় বা বিদেশে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটানোর কারণেই ইংরেজিকে প্রথম বা মাতৃভাষা হিসাবে বেছে নিয়েছেন?’ উত্তরে তিনি জানান : ‘হ্যাঁ, বিদেশে কিছু সময় কাটিয়েছি বটে। তবে বাংলাদেশে ইংরেজি মিডিয়ামে পড়ার কারণে বাংলা শেখার সুযোগ হয় নাই’।
অজুহাতটা লক্ষ্য করার মতো : ইংরেজি মিডিয়ামে পড়ার কারণে বাংলা শেখার সুযোগ হয় নাই! আহা, এদের জন্য সুযোগের বড়ই অভাব! যুক্ত করা দরকার যে, ইংরেজির এই শিক্ষক বাংলাদেশের প্রধান বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়াশোনা করেছেন এবং তিনি বাংলাদেশেই থাকেন। যতদুর জানি, সুরায় ও শেকসপিয়ারে তাঁর আগ্রহ থাকলেও তিনি ভাত-মাছই খেয়ে থাকেন। তারপরও তিনি বাংলা শেখার সুযোগ পান নাই! কথাটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। বরঞ্চ হয়তো বলা যাবে যে, তিনি বাংলা শেখার সুযোগ নেন নাই বা বাংলা শিখতে চান নাই। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে : কেন চান নাই? আমার প্রিয় বিপ্লবী চিন্তাবিদ এবং ইতালীয় মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও রাজনীতিক আন্তোনিয়ো গ্রামসি বলেছিলেন এভাবে যে, আমরা কোন বিষয়ের ওপর জোর দেই আর কোন বিষয়ের ওপর জোর দেই না, কিংবা আমরা কি চাই আর কি চাই না, সেগুলো রাজনৈতিকভাবে বা মতাদর্শিকভাবে মোটেই নিরীহ নয়; বরঞ্চ বিভিন্নভাবেই সেগুলো অর্থবহ হয়ে ওঠে।
বলা দরকার, ওপরের কথাগুলা আমি কোনো ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বলি নাই (বরঞ্চ বাংলাদেশে ওই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের আধিপত্যবাদী রাজনীতি নিয়ে আমার মেলা সমালোচনা আছে)। তবে আমি ইংরেজি ও বাংলার মধ্যে বিরাজমান অসম ক্ষমতা-সম্পর্কের বিষয়টা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতেই বোঝার চেষ্টা করছিলাম, যেমন ওই বাংলার সঙ্গে আবার সংখ্যালঘু জাতিসত্তার বিভিন্ন ভাষার অসম ক্ষমতা-সম্পর্ককেও বিবেচনায় রেখেছিলাম। কিন্তু ইংরেজির ওই শিক্ষক সংখ্যালঘু জাতিরও তো কেউ নন।
যাই হোক, আমাদের কথাবার্তার আরেকটি পর্যায়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্য-তত্ত্ব প্রসঙ্গে এডওয়ার্ড সাঈদের কথা চলে আসে। আবারও চিকচিক করে ওঠে ওই বাংলা-না-জানা ইংরেজির শিক্ষকের চোখ। তিনি বলেন, ‘এডওয়ার্ড সাঈদ আমার অত্যন্ত প্রিয় তাত্ত্বিক’।
‘অত্যন্ত প্রিয়’?
‘হ্যাঁ’।
আমাদের কথাবার্তা খানিকটা আগায়। প্রসঙ্গও পালটাতে থাকে। ইংরেজির ওই শিক্ষক আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন্ কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি পড়িয়েছি তা দারুণ আগ্রহ নিয়েই জানতে চাইলেন। হ্যাঁ, পেশাগত কারণে আমি নিজেই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজি পড়িয়েছি। এবং পড়াইও। বোধ হয়, ইংরেজির ওই শিক্ষক আমার সঙ্গে এক ধরনের পেশাগত ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু কি এক প্রসঙ্গে আমি ‘সাম্রাজ্যবাদ’ কথাটা উচ্চারণ করতেই তাঁর ভুরু কুঁচকে যায়।
তিনি প্রশ্ন করেন, ‘ইম্পিরিয়ালিজম? আপনি এখনো এই কথাটা ব্যবহার করেন?’
‘হ্যাঁ করি’। আমি সংক্ষেপেই উত্তরটা দেই।
‘ইম্পিরিয়ালিজম কথাটা তো বেশ পুরানা হয়ে গেছে’।
‘তাই? কতটা পুরানা’?
‘সোভিয়েত ইউনিয়নের লোকেরা একসময় ওই কথাটা ব্যবহার করত’।
‘আপনি কি এডওয়ার্ড সাঈদের ভক্ত?’
‘অবশ্যই। কথাটা আপনাকে আগেই বলেছি’।
‘কিন্তু জানেই তো যে, আপনার প্রিয় তাত্ত্বিক সাঈদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের নাম কালচার অ্যান্ড ইম্পিরিয়ালিজম । বইটা সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পরে অর্থাৎ ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে। আর বইটাতে সাঈদ কমপক্ষে শতাধিকবার ‘ইম্পিরায়ালিজম’ বর্গটা ব্যবহার করেছেন। খোদ শিরোনামেই তো বর্গটা আসন গেড়ে বসে সরাসরি আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে’।
থ’ মেরে যান ওই বাংলা-না-জানা, সাঈদ-ভক্ত, ইংরেজি-ফোটানো ফুটানি-মারা ইংরেজির শিক্ষক, যিনি এক প্রসঙ্গে আবার শেক্সপিয়রের তুমুল গুণকীর্তনও করেছিলেন। আমিও যে করি না তা নয়। তবে অবশ্যই শেকসপিয়র পুরানা নন, কিন্তু ‘ইম্পিরিয়ালিজম’ বর্গটা ‘পুরানা!’ কিন্তু এরাই বা কোনো কিছুকে পুরানা বলে নতুন কি দিচ্ছেন আমাদের? নতুন তো কিছু দিচ্ছেন না বটেই, বরঞ্চ পুরানা এবং বারবার ঘুরে-ফিরে-আসা ফকফকা বাস্তবতাকে অস্বীকার করার বা ধামাচাপা দেয়ার ভেতর দিয়েই ওই বাস্তবতার খপ্পরে শুধু আটকেই থাকছেন না, বরঞ্চ তার পক্ষেই কোনো না কোনোভাবে কাজ করে চলেছেন।
পুর্তোরিকান অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ ভিক্তর ভিয়ানুয়েভার সঙ্গে এক আলোচনার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে-আসা একটা উচ্চারণ মনে পড়ে : ‘উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের কথা শুনলেই যাদের ভুরু কুঁচকে যায় বা নান্দনিকতার বোধ হোঁচট খায়, তারা ওই উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের সংস্কৃতিতেই এত বেশি অভ্যস্ত যে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা শোনায় তারা রাজি নয়। বরঞ্চ এদের সহজেই শেকসপিয়রের ট্র্যাজেডি থেকে ‘টু বি অর নট টু বি’-মার্কা লাইন কিংবা বোদলেয়র থেকে একটা স্তবক কিংবা এলিয়টের ‘দ্য লাভ সং অফ জে অ্যালফ্রেড প্রুফ্রক’ থেকে মজার মজার লাইন শোনানো সম্ভব। এতে তাদের কাছ থেকে বাহবাও পাওয়া যায়’।
বলা দরকার, আমি মোটেই শেকসপিয়র বা বোদলেয়র বা এলিয়ট পড়ার বিরুদ্ধে নই। তবে সাম্রাজ্যবাদের যুগে আমরা তাদের কিভাবে পাঠ করছি, কিভাবে ব্যবহার করছি, বা তাদের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা কি ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করছি, সেগুলো নিয়ে জিজ্ঞাসা বর্তমান সময়ের তাগিদেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর হ্যাঁ, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস নিজেই পরিষ্কার করে সাক্ষ্য দেয় যে, তারা প্রশ্ন করাকে ভয় পায় কিংবা বরদাশত করে না, যে কারণে তিউনিশিয়ার ইহুদি তাত্ত্বিক আলবেয়র মেমি এক সময় ঠিক-ই বলেছিলেন, ‘উপনিবেশায়িত মন প্রশ্নহীন মন’। তাই প্রশ্ন তোলাকেও মেমি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাজ হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। আবার এও বুঝিয়েছিলেন, সব প্রশ্নই এক ধরনের নয় এবং এমনকি সব প্রশ্নই আবার প্রশ্নও নয়। প্রশ্নকে প্রশ্ন হয়ে উঠতে হয়। সেখানেও থাকে ক্ষমতার পক্ষে অবস্থান কিংবা তার বিপক্ষে লড়াই। কালো কবি অড্রে লর্ড একসময় বলেছিলেন, ‘লড়াইয়ের স্বার্থেই লড়াকু প্রশ্নও চাই’।
কিন্তু প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলেছেন এডওয়ার্ড সাঈদ নিজেই, যাঁর কথা আগেই বলেছি। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন সাম্রাজ্যবাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে, পূর্বকে নিয়ে ফাঁদা পশ্চিমা জ্ঞানভাষ্য নিয়ে। আধিপত্যবাদী পশ্চিমা ধ্যানধারণাকে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি তুলোধুনো করেছেন। অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে এবং জায়নবাদী প্রকল্পের অন্তর্গত ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাঈদ যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তা বলা যাবে, যদিও সাঈদের সীমাবদ্ধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায়, যেমন প্রশ্ন তোলা যায় তাঁর উদারনৈতিক মানবতাবাদকে নিয়ে কিংবা রাজনৈতিক অর্থনীতিতে তাঁর তুমুল অনাগ্রহকে নিয়ে। এই কারণে সাম্রাজ্যবিরোধিতার ক্ষেত্রে সাঈদ আমাদের একমাত্র মডেল নন।
কিন্তু কী কাজ করছেন আমাদের দেশের ওইসব সাঈদভক্ত, যারা এমনকি ‘সাম্রাজ্যবাদ’ শব্দটা উচ্চারণ করতে দ্বিধা করেন কিংবা ভয় পান কিংবা সেই উচ্চারণে নাখোশ হন? এদের কেউ কেউ আবার একইসঙ্গে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাসীনদের ভক্ত এবং ক্ষমতাবিরোধী বুদ্ধিজীবী এডওয়ার্ড সাঈদেরও ভক্ত! সাঈদের এইসব ভক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত ওইসব সাদা তরুণ-তরুণীর কথা মনে করিয়ে দেয়, যারা চে গুয়েভারা আর বব মার্লির ভক্ত। এদের টি-শার্টে কিংবা টুপিতে কিংবা বেল্টে কিংবা চাবির রিং-এ চে ও মার্লির ছবি দেখা যায়। একবার এক স্বঘোষিত চে-ভক্তকে প্রশ্ন করেছিলাম : ‘মানবজাতির বড় শত্রু : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—এই উক্তিটা কার?’ উক্তিটা করেছিলেন চে গুয়েভারা নিজেই, কিন্তু ওই চে-ভক্ত উত্তরে বলেছিলেন, ‘নিশ্চয়ই কোনো টেরোরিস্ট উক্তিটা করে থাকবে।‘ হায়রে চে-ভক্তি!
হ্যাঁ, চে ও মার্লি (এই উপনিবেশবাদবিরোধী কালো ক্যারিবীয় সঙ্গীতকার ও গায়কের কথাকে তার সুর থেকে বিচ্ছিন্ন করার দুনিয়াব্যাপী আয়োজন পুঁজিতন্ত্রের বিচ্ছিন্নবাদী লজিকের সঙ্গেই সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ) যেমন পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে, প্রায় তেমনি কারুর কারুর কাছে সাঈদ বা উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব হয়ে উঠেছে কাঙ্ক্ষিত পণ্য বা এমনকি—ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক পিয়ের বুরদো যাকে বলেছেন—‘প্রতীকী পুঁজি’। কোনো কোনো সাহিত্য বিভাগের কারিকুলাম হয়ে উঠেছে টি-শার্ট, যাতে শোভা পায় এডওয়ার্ড সাঈদের ছবি। হ্যাঁ, এডওয়ার্ড সাঈদ বা উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের মধ্যেও যতটুকু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনীতি বা উপাদান রয়েছে, তাকেও বেমালুম গায়েব করে দিয়েছে বাংলাদেশের বাংলা-না-জানা, ইংরেজি-ফোটানো সাঈদভক্তরা, যারা বুদ্ধদেবের বোদলেয়রকে সঙ্গে নেবে, বেনজামিনের বোদলেয়রকে নয়। এভাবেও বলা যাবে : বুদ্ধদেবের হাতে যেমন বোদলেয়রের তুমুল বিরাজনীতিকীকরণ ঘটেছে, প্রায় তেমনি ওইসব সাঈদভক্তের হাতেও সাঈদের তুমুল বিরাজনীতিকীকরণ ঘটে চলেছে। তাঁর বিরাজনীতিকীকরণের প্রক্রিয়াটা নিজেই সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিরই অন্তর্গত বটে।
৪
বিরাজনীতিকীকরণের প্রক্রিয়াটা ঐতিহাসিক ও সামাজিকভাবে উৎপাদিত ক্ষমতা-সম্পর্কের বলয়ের বাইরে অবস্থান করে না। তাহলে ক্ষমতা কিভাবে কাজ করে থাকে তাও দেখে নেয়া দরকার। ওই কথাটা আমরা বাংলাদেশেই ছেলেবেলা থেকে শিখে এসেছি : জ্ঞান হচ্ছে ক্ষমতা। হ্যাঁ, জ্ঞানের ক্ষমতা তো রয়েছেই। আর জ্ঞানের বিভিন্ন সংজ্ঞার্থও জারি আছে। ফরাসি সংস্কৃতিতাত্ত্বিক পল ভিরিলিও তাঁর দ্য ইনফর্মেশন বম (তথ্য বোমা) নামের বইয়ে জানিয়েছেন, পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়া এখন তথ্য-বিস্ফোরণের যুগে আটকে আছে, যেখানে তথ্যের অতিরিক্ত উৎপাদনের ভেতর দিয়েই তথ্যের বোমাবাজিও চলতে থাকে এমনি এক মাত্রায় যে, তথ্য দিয়ে ভূমিদখল ও মন-দখল করা যায় যেমনি, তেমনি তথ্য দিয়ে কাউকে খুন করাও সম্ভব বটে।
বর্তমান করোনাক্রান্ত বৈশ্বিক মহাদুর্যোগের এই অভূতপূর্ব মুহূর্তেও তথ্যদুর্যোগের বিষয়টা স্পষ্ট থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই করোনা নিয়ে ‘ইনফর্মেশন-ওভারলোড’-এর কারণে মৃত্যুর আগেই মৃত্যু ঘটেছে; অর্থাৎ, বিশেষ করে এপ্রিল ও মে মাসে, যুক্তরাষ্ট্রে করোনা নিয়ে বিভিন্ন ভীতিকর তথ্য-প্রবাহ এমনভাবে অব্যাহত ছিল যে, বেশ কিছু মধ্যবয়সী ও বৃদ্ধ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার আগেই ‘হার্ট ফেইলিউর’-এ মারা গেছেন। এই প্রসঙ্গে একদিকে যেমন আমরা তথ্য-সন্ত্রাসের কথা বলতে পারি, অন্যদিকে আমরা অবশ্যই এখনো তথ্য-উপনিবেশবাদ এবং মিডিয়া-সাম্রাজ্যবাদের কথা বলতে পারি, যার কেন্দ্রে সচরাচর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই অবস্থান করে এসেছে। বর্তমান দুনিয়ার করোনাজনিত সংকটকে কাজে লাগিয়ে সেই কেন্দ্রীয় অবস্থানকে আরও শক্ত ও পোক্ত করার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কাজ করে যাচ্ছে এবং যাবে তা অবশ্যই বলা যাবে, যদিও বেশ আগেই বর্তমান শতককে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘ডিক্লাইন’-এর শতক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন বিশ্বব্যবস্থা-তাত্ত্বিক ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইনসহ আরও বেশ কিছু রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ। যাই হোক, এই মার্কিনায়িত তথ্য-উপনিবেশবাদের যুগে অবশ্য জ্ঞান-আহরণ ও তথ্য-আহরণকে সমার্থক ভাবা হয়।
কিন্তু ‘জ্ঞানই ক্ষমতা’—এই কথা বলাটাই যথেষ্ট? এর উল্টো ব্যাপারটাও কি কাজ করে না? অর্থাৎ ক্ষমতাও কি জ্ঞান হয়ে ওঠে না? অথবা এভাবেও প্রশ্ন তোলা যায় : ক্ষমতা কি জ্ঞান উৎপাদন করে না বা জ্ঞানকে জ্ঞান হিসাবে বৈধতা দেয় না? উত্তরে ‘হ্যাঁ’ বলেন বিশ শতকের ফরাসি তাত্ত্বিক ও দার্শনিক মিশেল ফুকো, যিনি ‘ক্ষমতা/জ্ঞান’-সম্পর্কের তুমুল তত্ত্বায়নের জন্য প্রসিদ্ধ এবং এমনকি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উদযাপিত, যদিও ফুকোর ক্ষুদে ক্ষমতার গতিতত্ত্ব—চূড়ান্ত দৃষ্টান্তে অদ্বান্দ্বিক হওয়ার কারণেই—‘ক্ষুদ্র’-এর সঙ্গে ‘বৃহৎ’-এর পরস্পর-প্রভাববিস্তারী সম্পর্ককে ধারণ করতে সক্ষম হয় না বলেই ফুকোর তত্ত্ব দিয়ে ফলপ্রসূভাবে রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জটিল লব্ধিকে ব্যাখ্যা করা যায় না বললেই চলে। এটি আরেক প্রসঙ্গ। তবে ফুকোর ধারণা অনুসারে ক্ষমতাবলেও যে জ্ঞান-উৎপাদন সম্ভব, এই বিষয়টা আমাদের দেশের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিভাবে?
আমাদের দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা কিংবা বন্দুকের ক্ষমতা কিংবা প্রতীকী ক্ষমতাবলে মাঝেমাঝেই জং-ধরা আমলারা এবং এমনকি সামরিক আমলারাও বিভিন্ন বিষয়ে ‘বিশেষজ্ঞ’ হয়ে ওঠেন। সেটা তো দেখেছি বেশ সময় ধরে। বন্দুকের নলের জোরে একজন রাষ্ট্রপতির ‘কবি’ হয়ে ওঠার নজির আমাদের দেশেই আছে বৈকি। অর্থাৎ বন্দুকের নলও ‘কবি’র ক্ষমতা তৈরি করে এমনভাবে যে, সমাজে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত কবিরা ওই বন্দুকওয়ালা ‘কবি’কে ভয়ে বা লোভে বা স্বেচ্ছায় স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। এই ভাবে সাহিত্য-না-জানা আমলা কেবল ক্ষমতার জোরে হয়ে ওঠেন সাহিত্যের আসরের মধ্যমণি। কিংবা ওই একই কারণে একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ ব্যারিস্টার রাস্ত্রবিজ্ঞানীদের জ্ঞান বিতরণ করেন তাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি হিসাবেই। আমাদের দেশে এমন অনেক বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক, লেখক ও সাংবাদিক আছেন, যাঁরা ক্ষমতাকেই জ্ঞান মনে করেন। মনে করেন বলেই কার্তেসীয় জ্ঞানতত্ত্ব বা চার্বাকের দর্শনের ওপর কোনো সেমিনার অনুষ্ঠিত হলে সেখানে ওইসব বুদ্ধিজীবী সমাজের ক্ষমতাবানদের ডেকে এনে তাঁদের বক্তৃতা শোনেন, যদিও তাঁরা ফরাসি দার্শনিক দেকার্তের নামের বানানটা ঠিক লিখতে বা বলতে পারবেন কিনা তাতে সন্দেহ হয়। কিন্তু ওই ক্ষমতাবানরা ক্ষমতার জোরেই যা বলবেন তা জ্ঞান হিসাবে বিবেচিত হতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, তাদেরকে ‘জ্ঞানী’ বা ‘বিশেষজ্ঞ’ বানানোর জন্য উঠেপড়ে লেগে যায় শক্তিশালী গণমাধ্যমগুলো, যারা প্রতিনিয়ত জ্ঞানের সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্ক বিভিন্নভাবে দেখিয়ে দেয়।
হ্যাঁ, ক্ষমতা টাকার মতোই কথা বলে। আর যখন সে কথা বলে, নিজের কথাকে সে জ্ঞান হিসাবে জাহির করতে থাকে।
৫
ক্ষমতার প্রতি নতজানু থেকে, সব প্রশ্নকে বন্ধ ও বন্ধক রেখে, জীবন এবং চেতনার বিরাজনীতিকীকরণ ঘটিয়ে মানসিক পরাধীনতার যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে আজ, তা অবশ্যই গণতন্ত্রের সাক্ষাৎ শত্রু। আর, হ্যাঁ, এই সংস্কৃতি নির্মাণে একদিকে যেমন বিভিন্নভাবে (কিন্তু যান্ত্রিকভাবে নয়) ভূমিকা রেখেছে বিভিন্ন বস্তুক নিয়ামক, অন্যদিকে তেমনি ভুমিকা রেখেছে দীর্ঘ সময় ধরে গড়ে-ওঠা আমাদের ঔপনিবেশিক মনোগঠন, যা আবার ওই সংস্কৃতির দ্বারাই পাল্টা-প্রভাবিত। এই মনোগঠনেই ইউরোপীয় আধুনিকতাবাদ বা তথাকথিত ধ্রুপদী ইউরোপীয় সাহিত্য বা বিলিতি কায়দায় ইংরেজি বলা কিংবা এমনকি বাংলা-না-শেখার বিষয়টিও তুমুল বাহবা পায় আমাদের দেশেই। অবশ্যই বলা যাবে যে, আমাদের সময়ের একটি প্রধান সাংস্কৃতিক সমস্যা হচ্ছে আমাদের ঔপনিবেশিক মনোগঠন, যাকে আমাদের জাতীয় মুক্তিসহ সার্বিক মুক্তির স্বার্থেই ভেঙে ফেলা দরকার। কিন্তু তাকে তো আপনাআপনি ভেঙে ফেলা সম্ভব নয়। ভেঙে ফেলার জন্য দরকার লাগাতার উপনিবেশবাদবিরোধী সাংস্কৃতিক সংগ্রাম ও সৃজনশীলতা, দরকার উপনিবেশবাদবিরোধী শিক্ষাও, সেই শিক্ষা যা রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে পরস্পর-সম্পর্কিত করবে। দরকার সেই শিক্ষা, সেই সংগ্রাম আর সেই সৃজনশীলতা যেগুলো বিরাজমান নিপীড়ক প্রথা আর প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলবে, সর্বসাধারণের সার্বিক মুক্তির স্বার্থেই।
সবশেষে আমার অনুবাদে দক্ষিণ আফ্রিকার কালো কবি আলেক্সিস নিউন্দাইয়ের একটি কবিতা, যে কবিতা ওই ঔপনিবেশিক জ্ঞান/ক্ষমতা সম্পর্ককে আর আমাদের ঔপনিবেশিক মনোগঠনকেই ভেঙে ফেলার ডাক দেয়; আর এই কবিতাকে আমি বর্তমান সংখ্যার সকল কবি ও লেখককে উৎসর্গ করছি :
কামলা নকসুর উল্টো লিখন
শস্যের দানায় দানায় কামলা নক্সুর নোকতা-ভরা নোনতা ঘাম
শস্যের দানায় দানায় রক্ত ছলকে ওঠে দাউ দাউ পূর্ণিমায়
রক্তের টান জমিনের টান জবানেরে টান কামলার কামের টান
টান টান টান টান টান টান টান টান টান টান টান টান টান।
দারুণ টানে ফিরে আসে আমাদের বাক্য সব
আমাদের চিহ্নগুলো ডাক ছাড়ে রক্তাক্ত দিগন্তের তাণ্ডব শেষে
আমাদেরও টগবগ-করা মহাকাব্য আছে
আমাদেরও আছে বলকানো ইশতেহার
কালো মানুষের দেহের পরতে পরতে দমকে দমকে ওঠে
আমাদের নিঃশ্বাসে বিশ্বাসে রচিত আখ্যান সব।
আমাদেরও আখ্যান আছে
আমাদেরও নদী নক্ষত্র নয়শ মোহনার নয়শ আকাশ আছে
আমাদের দেহের ছন্দঃস্পন্দে ভাষার সীমান্ত-ভাঙা অঢেল জমিন আছে
আমাদের ইতিহাসে কামলা নকসুর নোকতা-ভরা ঘামে
শত শত কাব্য পংক্তির ভেতরে খুন ঝরে—টুপটাপ টুপটাপ
অথবা অঝোর ধারায় ধ্বনির দৃষ্টি-মাতানো বৃষ্টি—বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি
ভীষণ উল্লাসে ধেয়ে চলে আমাদের কাহিনী-কিসসা
তোমাদের উপনিবেশ ভেঙে ভেঙে ভেঙে ভেঙে ভেঙে
তোমাদের উপনিবেশ
কামলা নকসু
কামলা নকসু
কামলা নকসু
কামলা নকসু
কামলা নকসুর নোকতা-ভরা নোনতা ঘামে
লাঙলের ফলা কাব্য ফলায় জমিনের গতরে
গাঙে ওঠে ঢেউ চন্দ্রিমায় তড়পায় তড়পায়
সভ্যতার নামে বর্বরতার বেসামাল আস্ফালনে
আমাদের ইতিহাস জ্বলে দাউ দাউ দাউ দাউ
তারপরও আমরা উঠি
ভোরকে সামনে রেখে
কামলা নকসু
কামলা নকসু
কামলা নকসু
ওঠে
যাত্রা তার শুরু হয় মহাকাব্যের সর্গ থেকে সর্গে
সীমান্ত ধংস-করা মানুষের মানচিত্রহীন দুনিয়ায়।
আজফার হোসেন
ইন্টিগ্রেটিভ, রিলিজিয়াস অ্যান্ড ইন্টারকালচারাল স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট
গ্র্যান্ড ভ্যালি স্টেইট ইউনিভার্সিটি
মিশিগান, যুক্তরাষ্ট্র।