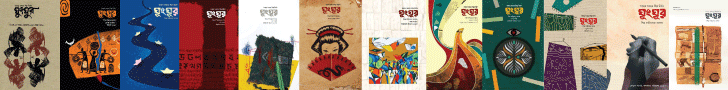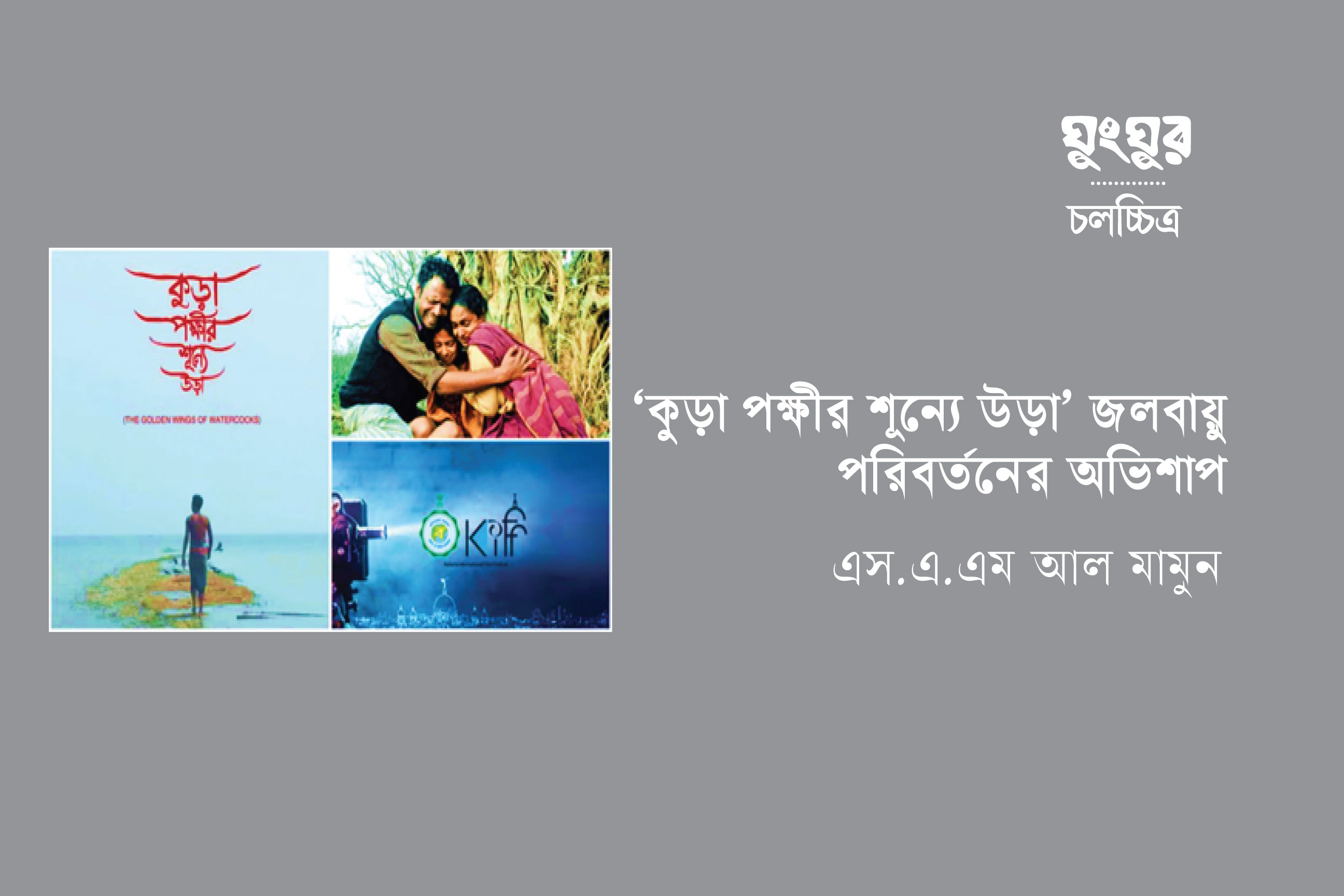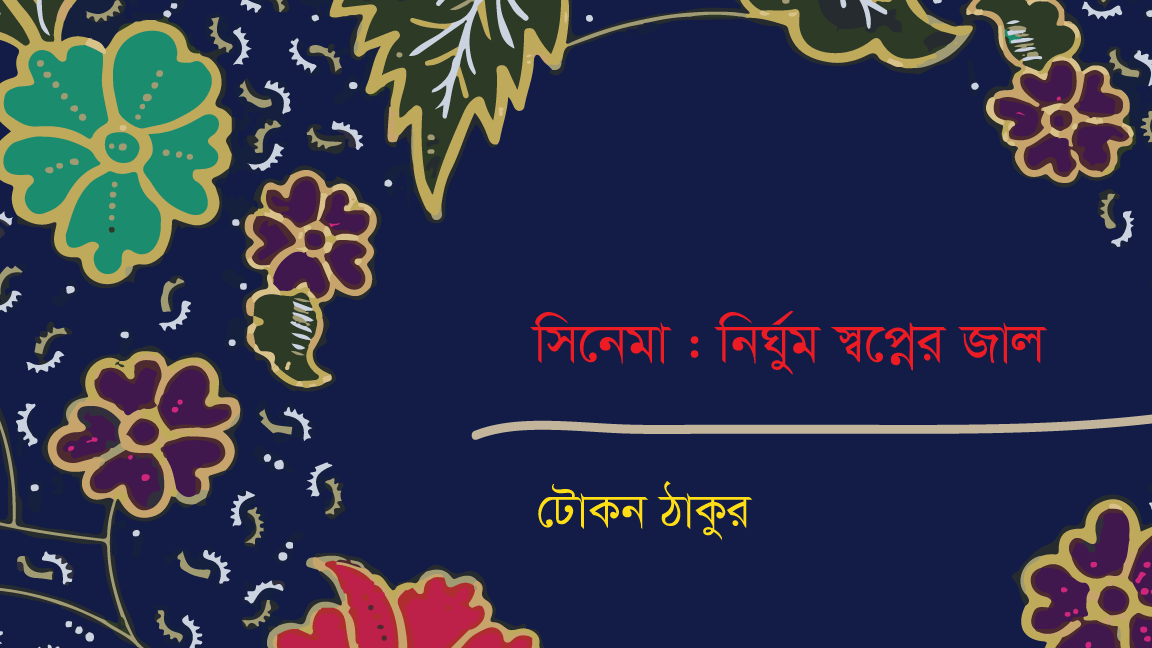রুস্তাভেলি রোড

তিব্লিসি শহরের রুস্তাভেলি রোডের যে বাড়িতে এসে উঠেছি, তার উলটোদিকে এক মস্ত বড় সেকেলে পোড়ো বাড়ি। ভূমি থেকে কয়েক ধাপের সিঁড়ি বেয়ে তবেই সদর দরজা। দরজার ক্ষয়ে যাওয়া পাল্লাদুটো বহু কষ্টে আঁকড়ে আছে ধুলোমাখা কাচ আর নীল রঙের প্রলেপ। পাল্লা দুটো হাট করে খোলা। যে কেউ চাইলেই ভেতরে ঢুকে যেতে পারে। ভেতরে অন্ধকার প্যাসেজ। ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে দেখি দোতলার মাথায় এক টুকরো চিলেকোঠা ঘর। সূর্যালোক আহরণের জন্যে ঘরটির এদিককার দেয়ালে আর জানালায় অসংখ্য চৌকোনা কাচের উপস্থিতি। তাদের মাঝে কয়েকটি এ ঘরকে বিদায় জানিয়ে ঝরে গেছে মেলা আগেই। সেই শূন্যতাকে অগ্রাহ্য করে জানালায় ঝুলছে মলিন জীর্ণ পর্দা। ফাঁকা পথ গলে ভেতরে যাওয়া হাওয়া ক্ষণে ক্ষণেই দুলিয়ে দেয় পর্দার ধূসর জমিনকে। ও ঘরে কি কেউ থাকে? বেশ কিছুক্ষণ ঠায় তাকিয়ে থেকেও কারুর উপস্থিতি আমি ধরতে পারি না।
সেই ভূতুড়ে বাড়ির দোতলার জানালার পানে তাকিয়ে থেকে বাড়িটিকে যখন প্রায় পরিত্যক্ত আখ্যা দিয়ে ফেলেছি, ঠিক সেই মুহূর্তে এক যুবতী সেই সদর দরজা ঠেলে এগিয়ে আসে। মেয়েটির পরনে আজানুলম্বিত স্কার্ট। ঊর্ধ্বাঙ্গে জ্যাকেট আর গলায় পেঁচিয়ে রাখা উলের মাফলার। এমন শীতল সমীরণে আবদ্ধ সকাল আর সকল কিছুকে জব্দ করতে পারলেও মেয়েটির মোজাবিহীন ফর্সা পা দুটিকে হয়তো জব্দ করতে পারেনি। আমাকে দেখে মেয়েটি ‘গামারজবা’ অর্থাৎ হ্যালো বলে দু-বাড়ির মাঝকার উঠোন পেরিয়ে মূল সড়কের পানে হেঁটে যায়।
সেই চিলেকোঠার ঘরের দিকে কৌতূহলমাখা দৃষ্টির সঞ্চালনকে ব্যাহত করে এবারে মেয়েটির গমনপথের দিকে তাকাই। দেখি, গ্যাসের লাইনকে আঁকড়ে ধরে লতিয়ে ওঠা আঙুর গাছের হলদেটে পাতার অরণ্য মেয়েটিকে নিমেষেই গ্রাস করে নেয়। সেই অরণ্যের মাঝে এখানে-ওখানে শুকিয়ে যাওয়া কালচে আঙুরের থোকা। অবহেলায় পড়ে থেকে তারা আজ বিশুষ্ক, রস নিঃশেষিত, বিগত যৌবনা। তাদের কেউ কেউ হয়তো এ শহরের গ্রীষ্মকালীন পাখিদের উদরে গেছে। কিন্তু শীতের আগমনে সেই পাখির দলগুলো নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ায় থোকায় ঝুলে থাকা বাকি ফলগুলোর অবস্থা যেন স্বর্গের অপেক্ষায় প্রহর গোনা জরাগ্রস্থ প্রবীণের ন্যায়। প্রাণবায়ু উদ্গত হবার অপেক্ষায় উন্মুখ। তেমন কিছু আঙুর অবশ্য জীবনদায়িনী বৃক্ষের সাথে বন্ধন ছিন্ন করে এর মাঝেই ঝরে পড়েছে নিচের ভূমিতে। পাশের পাইন গাছের ঝরে পড়া ফিকে হলদে-সবুজ পাতায় আকীর্ণ উঠোনটি তাই স্থানে স্থানেই কালচে।
নিজের গ্রেট কোটটিকে ভালো করে বোতামবন্দি করে আমিও এবারে সেই মেয়েটির ন্যায় উঠোন পেরোবার প্রস্তুতি নিই। এ বাড়ির ঠিক কোণের দিকে মুদি দোকান। গতকাল রাতে সেখান থেকেই রুটি কিনে আজ সকালের প্রাথমিক খিদে মিটিয়েছি। এ দোকানে কিন্তু শুধু রুটি নয়, ম্যাচবাতি থেকে শুরু করে ফুলকপি-মরিচ সবই মেলে। আহা, এমন একখানা দোকান যদি আমেরিকায় থাকত! ঘরে মরিচ-পেঁয়াজ শেষ হলেই দু বাড়ি দূরের এমন দোকানে ছুটে গিয়ে কিনে আনতাম। বাস্তবতা হল, খানিক নুন কিনতে হলেও আমাকে গাড়ি ছোটাতে হয় পাঁচ মাইল দূরের দোকানে। আমেরিকার প্রবল পুঁজিবাদী অসুরকূল এ ধরনের ক্ষুদ্র উদ্যোগকে বেশি দূরে এগোতে দেয় না; বহু আগেই গলা টিপে মেরে ফেলে। আমেরিকান জীবনে তাই সুপার মার্কেটই কেনাকাটার শেষ ঠিকানা।
আমি এই দোকানটির নাম দিয়েছি–বুড়ির দোকান। দিবারাত্র একজন বৃদ্ধা দোকান সামাল দেন। গোলগাল চেহারা। চোখে লেগে থাকে মুখের গড়নের সাথে মানাসই বৃত্তাকার ফ্রেমের চশমা। দোকানের দরজাটি ভেতরের দিকে খুলে রেখে ভারী জলের বোতলের চাপে ঠেক দিয়ে রাখা। সে কারণেই দোকানের ভেতরটি তেমন উষ্ণ নয়।
বৃদ্ধা শীতের ছোবল থেকে রক্ষে পাবার জন্যে কান আর মাথা পেঁচিয়ে রাখেন মলমলের মাফলারে। গত দুদিনে এটা-সেটা কিনতে বেশ কয়েকবার এখানে আসায় বৃদ্ধা আমার মুখ চিনে গেছেন। তাই একশ লারির নোটের ভাঙতি চাইবার জন্যে যখন দোকানে ঢুকি, তিনি সহাস্যে বলেন, ‘রোগর খার?’ মানে–কেমন আছ? আমি কিছুটা সংকোচপূর্ণ ভঙ্গিমায় ভাঙতি দেওয়া যাবে কিনা জানতে চাই। এই সংকোচের কারণ ঢাকাবাসের অভিজ্ঞতা।
ঢাকায় এমন সক্কাল বেলায় ভাঙতি চাইতে গেলে দোকানিরা বলে বসত ‘এহনো সহালের বউনি করি নাই, ভাঙতি দেওন যাইব না। অন্য দোহানে খোঁজ নেন।’ কিন্তু না, বৃদ্ধা কিন্তু আমাকে অন্য দোকানের পথ দেখিয়ে দিলেন না। ভাঙতিগুলো নেওয়ার পর তাই তাকে ‘মাদলোবা’ অর্থাৎ ধন্যবাদ না বলে পারি আমি?
বুড়ির দোকানের পর একটি ফুলের দোকান। নাম– লোনলি রোসেস। নামের সাথে বাস্তবতারও কী সাযুজ্য। গত দুদিন একটি খদ্দেরও এ দোকানের ভেতরে দেখিনি। দোকানের গোলাপগুলো তাই সতেজ রেণু নিয়েও বড্ড নিঃসঙ্গ। তবে এরপরের দোকানটি কিন্তু আবার তেমন প্রাণহীন নয়। ওটি একটি দর্জির দোকান। ভেতরে কাজ করছেন চার-পাঁচজন বৃদ্ধা। পথের দিকে মুখ করে সেলাই মেশিন নিয়ে বসেছেন। প্রত্যেকের নাকের ডগায় ঝুলছে কালো ফ্রেমের চশমা। তাঁদের ব্যবহৃত জলপাইবর্ণা সেলাই মেশিনগুলো হয়তো কয়েক দশকের পুরনো। কাচের দেয়ালের ফাঁক গলে আসা দৃশ্যের মাঝে আমি দেখতে পাই–কেউ হয়তো কোটের সেলাই কেটে ছোট করছেন, আবার কেউ বা বেঢপ আকৃতির বক্ষবন্ধনীর চারপাশে চালাচ্ছেন বাড়তি সুতো। দর্জির দোকানের উলটোদিকের ফুটপাথের রেলিঙে ঠেস দিয়ে এক জবুথবু বৃদ্ধা। ভেতরের দোকানের বৃদ্ধাদের মতো শীতের হাত থেকে রক্ষে পাবার উপায় তাঁর নেই। তাই সর্বাঙ্গ মুড়ে থাকা কালো চাদরটিই তাঁর ভরসা। ভিক্ষে চাইবার জন্যে কিন্তু তিনি এখানে বসেননি। হাতের প্লাস্টিক ব্যাগে কিছু কাঁচা-পাকা লেবু। এগুলো বিক্রি করবেন। তিনটি লেবু এক লারি। বাড়ি ফেরার সময়ে এঁকে দেখলে না হয় কিছু লেবু কিনে তাকে কিছুটা সাহায্য করা যেত। কিন্তু এখন লেবু নিয়ে পথ হাঁটব কী করে! সেই লেবুওয়ালি বৃদ্ধার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার সময় খেয়াল করি, রাস্তার উলটোদিকের বাড়িটির দোতলার জানালা খুলে গেল। এই বাড়িটি জীর্ণ। একসময়ে ওই দোতলার কাছটিতে ছিল বেশ কিছু নরমুখের রিলিফ। যত্নের অভাবে, বিত্তের অভাবে সেই রিলিফগুলোর কেউ হারিয়েছে নাক, কেউ হারিয়েছে মুখমণ্ডলের অর্ধাংশ। এ শহরের বনেদি পাড়াগুলোর অবস্থা এমনই। বাড়িগুলো পলেস্তরা খসা, বারান্দার লোহার রেলিঙে কোনও এক প্রাগৈতিহাসিক কালের পর আর রঙের প্রলেপ পড়েনি, জানালার কাঠগুলো খরা জর্জরিত মাঠের মতোই চৌচির। বোঝাই যায়, ষাট-সত্তরের দশকের জৌলুসধারী ভবনগুলো সোভিয়েত সময়ের পর আর নিজের লাবণ্য ধরে রাখতে পারেনি। ইদানীং অবশ্য কিছু আরব দেশের শেখ এসে কিনে নিচ্ছেন এমন সব অ্যানটিক বাড়ি। বেশ কিছু জায়গায় ইংরেজি আর আরবি হরফে লেখা দেখেছি–‘ফর সেল। গুড প্রাইস।’ মূলত ভিনদেশি ক্রেতাকে টার্গেট করে যে এই বিজ্ঞাপনগুলো, সে তো ওই হরফ দেখেই বোঝা যায়।
যাকগে, যে জানালার কথা বলছিলাম, সেখানে কেউ একজন গ্লাসে করে কিছু শস্যদানা এনে ছড়িয়ে দিলেন কার্নিশে। সেই দানার লোভে হাওয়া থেকে ভোজভাজির মতো উদয় হল এক ঝাঁক কবুতর। স্কুলের মাঠে সকালের প্যারেডে যেমন করে ছেলে-মেয়েরা লাইন বেঁধে দাঁড়ায়, এই কবুতরের দলও তেমনই লাইন করে কার্নিশে বসে শস্যদানা ঠুকরে খাওয়াতে মন দেয়।
কিছুটা দূর হাঁটার পরই আমাকে একটা আন্ডারপাস পেরোতে হয়। এ শহরের মানুষেরা দরিদ্র হলেও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আন্ডারপাস ফেলে তারা সড়কের মাঝ দিয়ে ফুস করে দৌড়ে রাস্তা পেরোয় না। আন্ডারপাসের সিঁড়ি দিয়ে নামলেই ডানদিকে একটি বেকারি। আর বাঁদিকে মেয়েদের লেগিংসের দোকান। আমাকে যেতে হবে ওই বাঁদিকেই। সেখানটায় সিঁড়ি বেয়ে আবারও রুস্তাভেলিতে উঠে পেয়ে যাই এক পুরনো বইয়ের দোকানদারকে। ইনি প্রতিদিনই আন্ডারপাসের দেওয়ালে বই বিছিয়ে সন্ধে অব্ধি বেচাবিক্রি চালান।
উলটোদিকেই প্রাইমারি স্কুল। তাই তার ক্রেতাকূলে শিশুদের সংখ্যাই হয়তো বেশি। বইয়ের স্তূপে থাকা অসংখ্য শিশুতোষ বই দেখেই সেটা আন্দাজ করা যায়। মূলত রুশ আর জর্জিয়ান ভাষায় এসব বইগুলো। ইংরেজি আছে দু-একটি। আমি একটু দাঁড়িয়ে তেমন একখানা বই খোঁজায় মন দিলাম। যে বইটি পেলাম, তার নাম ম্যাক্সিম।
দেড় লারি দিয়ে বইটি কিনে দেয়ালে হেলান দিয়ে পড়া শুরু করে দিলাম সেখানেই। একেবারেই ছোট শিশুদের বই। দশ বারো পাতার। লেখার চেয়ে অলংকরণ বেশি। আর সেই অলংকরণের লোভেই তো বইটি হাতে নিলাম। বইয়ের গল্পটি এমন–
১৭ সালের বিপ্লবের পর শ্বেতরক্ষী বাহিনীর সাথে যখন বলশেভিক লাল বাহিনীর নানা স্থানে যুদ্ধ হচ্ছে, সে রকম সময়েই লালবাহিনীর একটি দল এসে পৌঁছল কিরঘিজ এক গ্রামে। গ্রামের জোতদারের বাড়িতে কাজ করে একটি অনাথ ছেলে। তারা শুনল ছেলেটিকে জোতদার কিনে এনেছেন, অর্থাৎ সে একপ্রকার ক্রীতদাস। কিরঘিজ সমাজে সে সময়ে এটি কোনও বিরল ঘটনা ছিল না। এদিকে ছেলেটি লাল বাহিনীর ডেরায় এসে নানা কাজে সাহায্য করে। বাহিনীর কাজে যে তার প্রবল আগ্রহ, সেটি সে বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু তার নাম কী?
বাহিনীর কমান্ডার যখন তাকে নাম জিজ্ঞেস করে, ছেলেটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তার তো কোনও নাম নেই! কোনও মানুষের যে নাম থাকতে পারে, এই ব্যাপারটিই যেন তার বোধগম্যতার বাইরে। পরিশেষে কমান্ডার নিজেই ছেলেটির একটি নাম দিলেন–ম্যাক্সিম। শুধু নামই দিলেন না, ছেলেটিকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে লালবাহিনীর সদস্য বানিয়ে ছুটে গেলেন পরের যুদ্ধক্ষেত্রে।
এই ছিল ম্যাক্সিমের কাহিনি। বলাই বাহুল্য, গল্পের মাঝ দিয়ে খানিকটা হলেও বলশেভিক বাহিনীর মাহাত্ম্য শিশুমনে লেপন করাই ছিল এমন গল্পের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। বইটি পড়া শেষ হবার পর যখন গুটিয়ে কোটের পকেটে রাখছি, তখন সেই দোকানদার ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, ‘আর দুদিন পরে আসুন। আমি আরও কিছু ইংরেজি বই আপনার জন্যে আনিয়ে রাখব।’
তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আবারও রুস্তাভেলির পথে নামি।