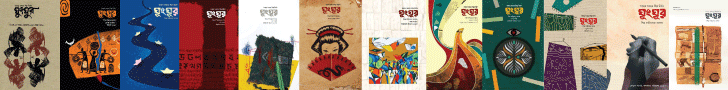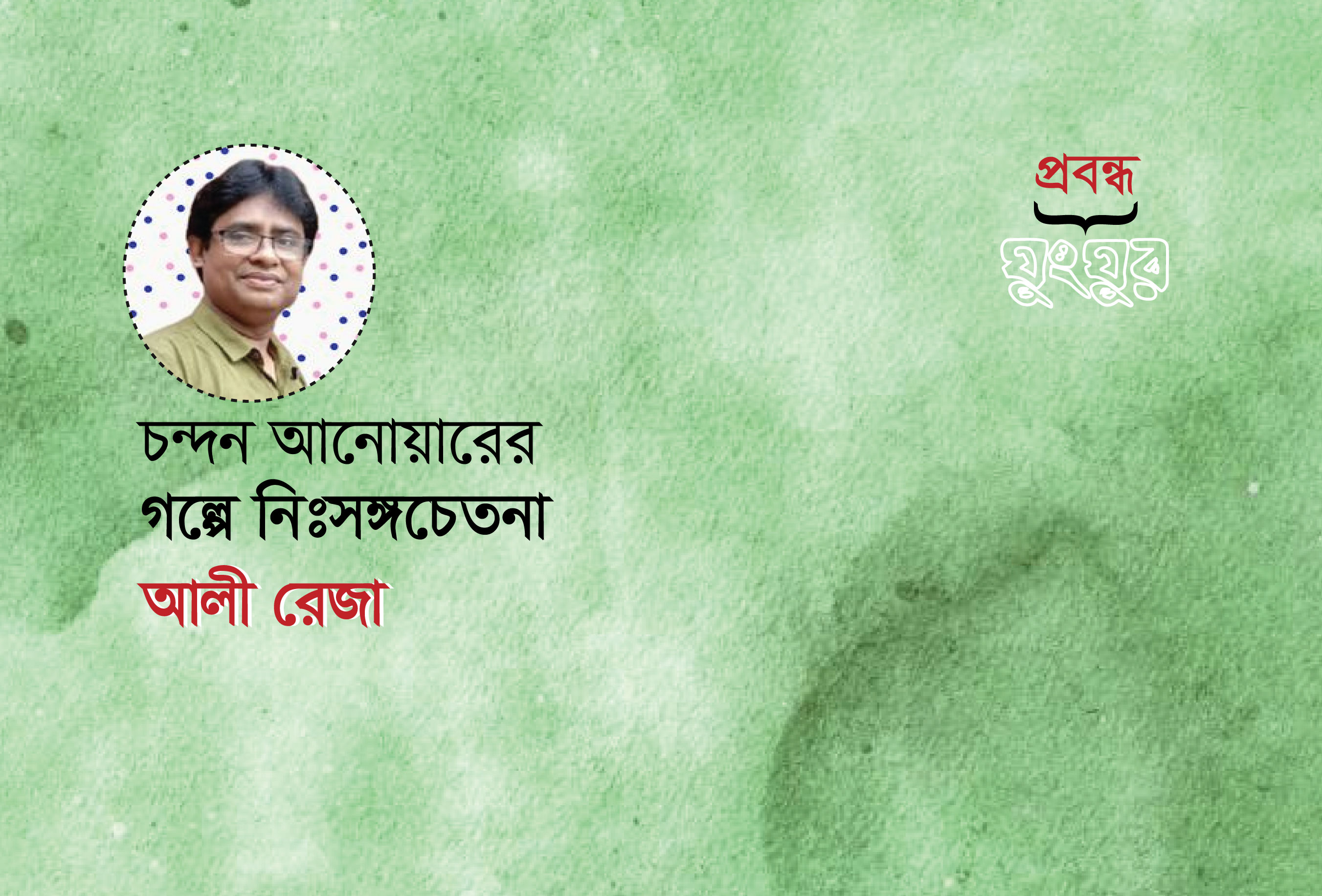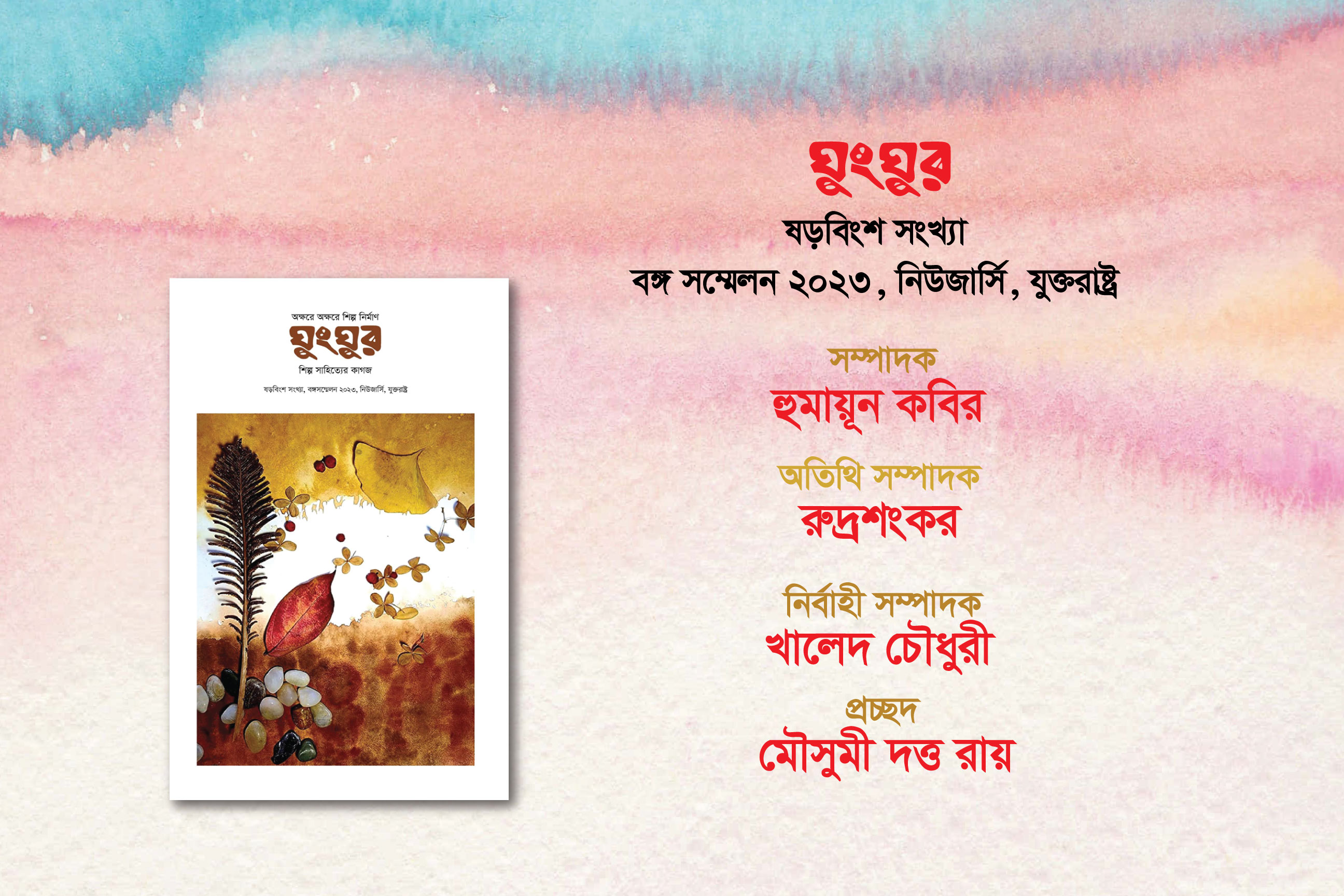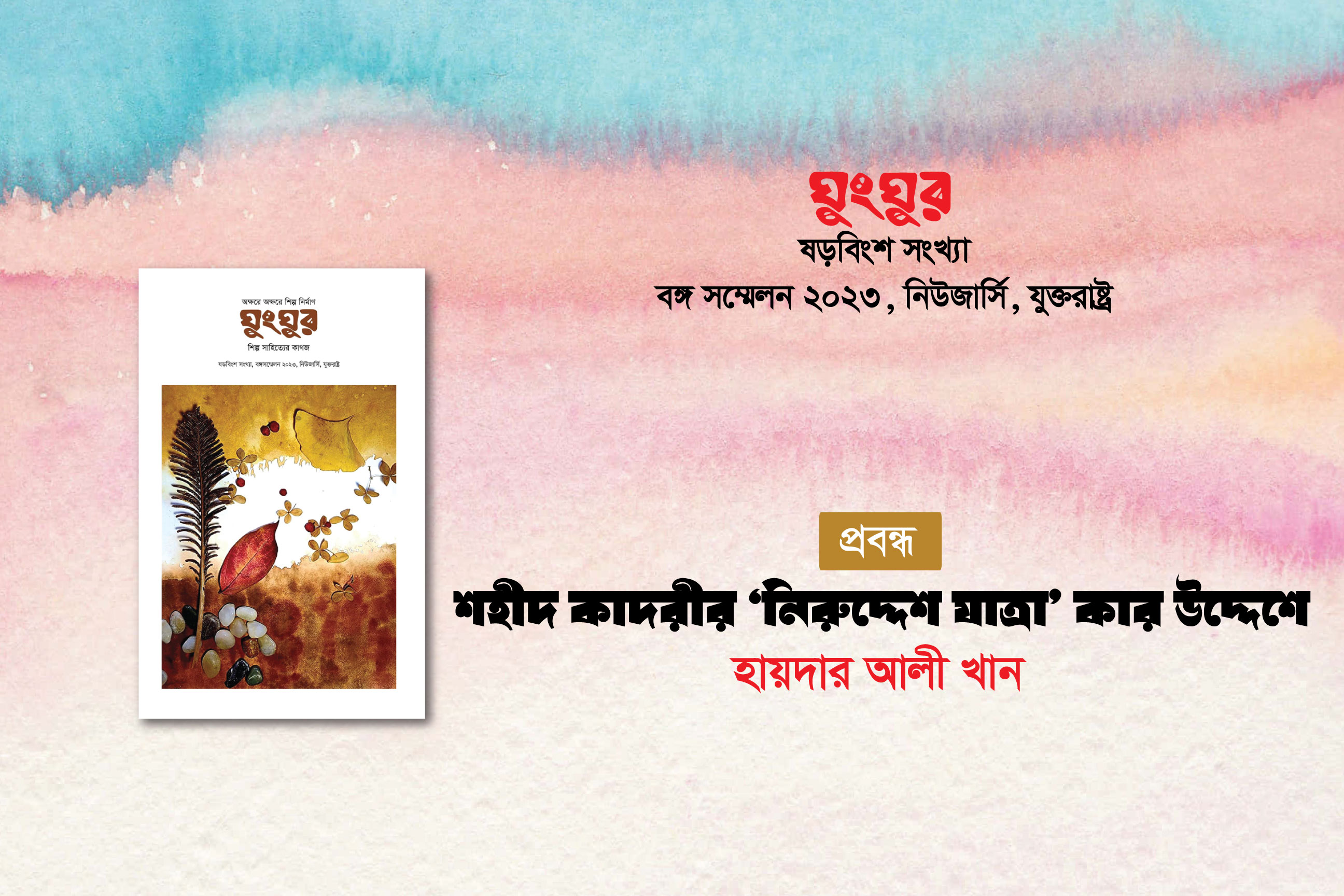উজানবাঁশির উজানকথা

বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে এত এত মিথ ছড়িয়ে আছে যে, কখনো কখনো মনে হয় গোটা দেশটাই একটা মিথের কূপ। মিথের সঙ্গে এখানকার মানুষের বসবাস। তারা মিথ সৃষ্টি করে, মিথ যাপন করেন, মিথে আনন্দ লাভ করে, মিথে শাসিতও হয়। মিথকে আমি কথাসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে করি। বাংলায় যত মিথ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, প্রত্যেকটি দিয়ে একেকটি উপন্যাস রচনা সম্ভব, গল্প রচনা সম্ভব। আমাদের ঔপন্যাসিকরা যে তাঁদের উপন্যাসে মিথের ব্যবহার করেননি, তা নয়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামায় দেখি মিথের সফল ব্যবহার। কাৎলাহার বিলের ধারে ঘন জঙ্গল সাফ করে বাঘের ঘাড়ে জোয়াল চাপিয়ে আবাদ শুরু করার দিনের এক বিকেলবেলায় মজনু শাহর অগুনতি ফকিরের সঙ্গে মহাস্থানগড়ের দিকে যাওয়ার সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেপাই সর্দার টেলারের গুলিতে মারা পড়ে মুনশি বয়তুল্লাহ শাহ। কাৎলাহার বিলের দুই ধারের গিরিরডাঙা ও নিজগিরির ডাঙার মানুষ সবাই জানে, বিলের উত্তরে পাকুড়গাছে আসন নিয়ে রাতভর বিল শাসন করে মুনশি।
এই যে বাঘের ঘাড়ে জোয়াল চাপিয়ে আবাদ শুরু করা, এটা মিথ। মুনশি বয়তুল্লাহ যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেপাই সর্দারে গুলিতে মারা পড়েছিলেন, এটা বাস্তব; ঐতিহাসিক সত্য। আবার কাৎলাহার বিলের উত্তরে পাকুড়গাছে আসন নিয়ে যে তিনি বিল শাসন করেন, এটা মিথ। অর্থাৎ একই জনপদে মিথ ও বাস্তবতা পাশাপাশি বসবাস করছে। এই মিথকে মানুষ পুরোপুরি বিশ্বাস করে না, এবার পুরোপুরি অবিশ্বাসও করে না। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী স্থানে মিথের বসবাস। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর কৌশলী হাতে মিথ ও বাস্তবতার মিশেলে এক অসাধারণ শিল্প সৃষ্টি করেছেন, যার নাম খোয়াবনামা।
আমি প্রচুর ভ্রমণ করি। সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়ি। যেখানেই ঘুরতে যাই কোনো না কোনো মিথের সঙ্গে পরিচিত হই। যেন আমি সেসব মিথের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যই এখানে এসেছি। যেন মিথেরা আমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যই এতকাল অপেক্ষা করছিল। একবার বাংলাদেশের দক্ষিণের দ্বীপ চর কুকুরি মুকরি ভ্রমণে গেলাম। ওই দ্বীপে ইসলামি শরিয়তের কঠোর অনুশাসন বিদ্যমান। কিন্তু শরিয়তকে চাপিয়ে এক মিথ বিরাজ করছে সেখানে। কালাপীর নামক এক অদৃশ্য সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে চরের অধিকাংশ মানুষ। চর কুকরি মুকরির মানুষদের সুখে-দুঃখে থাকেন কালাপীর। তার ভয়ে এই চরে কেউ চুরি-ডাকাতি করার সাহস পায় না। যদি কেউ খারাপ কাজ করে, সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজের প্রতিফল পেতে শুরু করে। কালাপীর তাকে শাস্তি দেন। তার শাস্তির ভয়ে এই চরের কেউ কারও সঙ্গে ঝগড়া-ফ্যাসাদ করে না। কোনো অপরাধ সংঘটিত হয় না। স্বাধীনতার পর এই চরে একটা খুনের ঘটনাও ঘটেনি। শালিস-দরবারও হয় না খুব একটা। একটা পুলিশ ফাঁড়ি আছে, কিন্তু গ্রেপ্তারের মতো কোনো আসামি খুঁজে পায় না পুলিশ। পরবর্তীকালে এই মিথ নিয়ে ‘কালাপীর’ নামে একটি গল্প লিখি, যা আমার বানিশান্তার মেয়ে গল্পগ্রন্থে রয়েছে।
এমনই একটি মিথের কথা জানতাম বহু বছর আগ থেকে। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এক এলাকায় (এলাকাটির নাম উহ্য থাকুক) এমনই এক মানুষ ছিলেন, শৈশবে যাকে বাঘে গিলে ফেলেছিল, চল্লিশ বছর যিনি বাঘের পেটে ছিলেন, চল্লিশ বছর পর বাঘ যাকে উগরে দিয়েছিল। আমার শৈশবে মানুষটিকে দেখেছিও। সবসময় নেংটা থাকতেন। তীব্র শীতেও কিছু গায়ে দিতেন না। সবাই তার নাম দেয় বাঘামামা। সবাই তাকে পীর সাব্যস্ত করে। তার অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কথা ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। মৃত্যুর পর তার সমাধিক্ষেত্রে মাজার ওঠে। প্রতি বছর ওরস হয়। শত শত মানুষ জমায়েত হয়। হিন্দু-মুসলমান সবাই। প্রসাদ হিসেবে খিঁচুড়ি-মাংস খায়।
বাঘামামার চল্লিশ বছর বাঘের পেটে থাকার মিথটি জানি, কিন্তু এটা নিয়ে কখনো সিরিয়াসলি ভাবিনি। কখনো মনেই আসেনি এটা নিয়ে কোনো গল্প-উপন্যাস রচিত হতে পারে। ২০১৭ সালের কোনো একদিন, যখন আমি মায়ামুকুট উপন্যাসটি লিখছি, হঠাৎ মনে পড়ে গেল বাঘামামার মিথটি। মনে হলো এই মিথ নিয়ে তো একটি উপন্যাস হতে পারে! কী আশ্চর্য গল্প! চল্লিশ বছর কিনা একটা মানুষ বাঘের পেটে ছিল! খুবই উত্তেজনা অনুভব করলাম। কিন্তু উপন্যাস লেখার মতো পর্যাপ্ত রসদ তো আমার কাছে নেই। আছে শুধু এই কটি লাইন—চল্লিশ বছর বাঘামামা বাঘের পেটে ছিল, চল্লিশ বছর পর বাঘ তাকে উগরে দিল। ব্যস, এটুকুই। আর কিচ্ছু না।
ভাবতে থাকি। মাথার ভেতর আখ্যানটা সাজাতে থাকি। প্রধান চরিত্রের নাম রাখি আবু তোয়াব। পটভূমি ভারতের পাহাড় থেকে নেমে আসা খরস্রোতা নদী নীলাক্ষি বিধৌত সীমান্তবর্তী এক জনপদ। সেই জনপদের অস্তিত্ব কি বাস্তবে আছে? আছে। কিন্তু তার বাস্তব নামটি না রেখে এক কাল্পনিক নাম রাখি। আশপাশের গ্রামগুলোর নামও পাল্টে দিই। সব নদী, খাল, বিল, হাটবাজারের নামও। নীলাক্ষি নদীরও অস্তিত্ব আছে, তবে তা অন্য নামে। কিন্তু একটি চরিত্র দিয়ে তো উপন্যাস হবে না, সৃষ্টি করতে হবে আরো চরিত্র। আমি চরিত্রগুলো সাজাতে থাকি। কার কী ভূমিকা তা ভাবতে থাকি। আখ্যানের পর আখ্যান যুক্ত করতে থাকি। কিন্তু শুধু মাথায় রাখলে তো হবে না। যেকোনো সময় ভুলে যাব। তাই একটা ডায়েরিতে টুকে রাখতে থাকি।
মায়ামুকুট লেখা শেষ হলো। উজানবাঁশি লেখা শুরু করব ভাবছি। আমি তো সাধারণত হাতে লিখি, তারপর কম্পিউটারে কম্পোজ করি। এর একটা সুবিধা হচ্ছে কম্পোজ করতে করতে প্রথম দফার এডিট হয়ে যায়। তারপর প্রিন্ট নিয়ে দ্বিতীয় দফা এডিট করি। কিন্তু উজানবাঁশি শুরু করতে পারছি না। প্রায় প্রতিদিনই কাগজ-কলম নিয়ে বসি, কিন্তু কীভাবে শুরু করব বুঝে উঠতে পারছি না। এ সমস্যাটা সম্ভবত প্রত্যেক ঔপন্যাসিকেরই হয়। উপন্যাসের শুরুটাই আসল। একবার শুরু হয়ে গেলে আর থামে না, তরতর করে এগোতে থাকে।
২০১৮ সালের ৫ ডিসেম্বর। খাতা-কলম নিয়ে বসলাম। পৌষের এক কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরের বর্ণনা দিয়ে শুরু করলাম লেখা। সেই ভোরে এক নেংটা মানুষকে দেখা যায় নয়নচরের মাঝখানে নিঃসঙ্গ প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকা এক তেঁতুলগাছের তলায়। মানুষটি কোথা থেকে এলো, কোন পথে এলো, কারও চোখে পড়েনি। যেন সাপের মতো মাটি ফুঁড়ে উঠেছে, কিংবা শকুনের মতো আকাশ থেকে নেমেছে। কুয়াশা কিছুটা হালকা হওয়ার পর দূর থেকে তাকে মহাদেবের মতো মনে হচ্ছিল। মহাদেবের যে চার ঠ্যাং, আর মানুষটির যে দুই পা—আলাদা করে কেউ খেয়াল করেনি। কিংবা মহাদেব নয়, ভালুক মনে হচ্ছিল। কিংবা ভালুকও নয়, হনুমান। কিন্তু যখন সূর্যের লাজ ভাঙে, যখন দেখা দেয় নয়নচরের পুবের বেড়িবাঁধে বিএসএফের ওয়াচ টাওয়ার, নেংটা মানুষটিকে তখন ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন সন্ন্যাসীর মতো মনে হচ্ছিল। কিংবা সন্ন্যাসী নয়, উজানগাঁর গোয়ালাবাড়ি মন্দিরের মা মাতঙ্গীর মতো মনে হচ্ছিল। চতুর্ভুজা। চার হাতে খড়গ, অসুরের ছিন্ন মুণ্ডা, বর ও অভয়মুদ্রা, গলায় নরমুণ্ডের মালা, ডান পা মহাদেবের বুকে।
ক্রমে দিগন্ত আরও ফর্সা হয়। মানুষটিও। এবার ধন্দ কাটে সবার। না, মহাদেব নয়, ভালুক বা হনুমান নয়, সন্ন্যাসী বা মাতঙ্গীও নয়, লম্বা চুল আর দাড়িগোঁফধারী অদ্ভুত এক নেংটা মানুষ। সবাই ভাবে, মানুষটি হয়তো ভবঘুরে। শীত এলে এমন ভবঘুরে প্রায়ই দেখা যায়। কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়, কেউ খেয়ালে রাখে না। নেংটা মানুষটিকে মৌসুমি ভবঘুরে ভেবে কেউ আর মাথা ঘামায় না।
ব্যস, শুরু হয়ে গেল। এবার আর চিন্তা নেই। চেষ্টা করি প্রতিদিন একটু একটু করে লিখতে। কিন্তু প্রতিদিন কি আর লেখা হয়? কোনো কোনো দিন শুধুই ভাবি, লিখি না। কোনো কোনোদিন লেখার চেষ্টা করি, কিন্তু লেখা হয় না। আবার কোনো কোনো দিন এক টানে লিখে ফেলছি পাঁচশো বা এক হাজার বা দুই হাজার শব্দ। এভাবে একটু একটু করে লিখতে লিখতে কেটে গেল ২০১৯ সাল। কিন্তু উপন্যাস শেষ হচ্ছে না। আখ্যান দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। শেষ করতে পারছি না। যখনই ভাবি এখানে শেষ করে দেব, তখনই মনে হয়, না, এখানে শেষ করলে হবে না, অপূর্ণ থেকে যাবে; আরও একটি পর্ব লেখা দরকার।
২০২০ এর মার্চে এসে দেখি পাণ্ডুলিপির শব্দসংখ্যায় দাঁড়িয়েছে প্রায় এক লাখ ৩২ হাজার। মার্চের শেষে দেশে শুরু হয়ে গেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের লকডাউন। অফিস বন্ধ, আড্ডা বন্ধ। আমার অখণ্ড অবসরতা। এই অবসরটাকে কাজে লাগাতে চাইলাম। পাণ্ডুলিপিটির প্রিন্ট নিলাম। শুরু করলাম এডিট। প্রথম এডিটে বাদ পড়ল প্রায় ২৭ হাজার শব্দ। প্রথম দফায় এডিট শেষ করে আবার প্রিন্ট নিলাম। এবারও কিছু বাদ পড়ল এবং যোগ হলো। সেপ্টেম্বরের ১৬ তারিখে যখন পাণ্ডুলিপির সম্পূর্ণ সম্পাদনা শেষ করি, তখন দেখি, এবার শব্দ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় এক লাখ ১১ হাজার।
এডিট করতে করতে রীতিমতো বিরক্তি ধরে গেছে। বড় ক্লান্ত। পাণ্ডুলিপিতে আর হাত দিতে ইচ্ছে করছে না। বুঝলাম, এই পাণ্ডুলিপি এডিট করার মতো আর কিছু নেই। অন্তত আমার পক্ষ থেকে আর কিছু এডিট করার নেই। এডিট সম্ভব কোনো দক্ষ এডিটরের পক্ষে। প্রত্যেক উপন্যাস লেখার সময় আমি এমনটাই করি। এডিট করতে করতে যখন স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হয়ে যায়, যখন বিরক্তি চলে আসে, তখন বুঝি পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ হয়েছে, আর সংযোজন-বিয়োজন করার কিছু নেই। উজানবাঁশির ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। পাণ্ডুলিপিটি পাঠিয়ে দিলাম প্রকাশক কামরুল হাসান শায়ককে।
এই উপন্যাসের নামকরণ নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতার শেষ নেই। অবশ্য প্রত্যেক উপন্যাসের নামকরণ নিয়েই আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়। বইয়ের নামকরণ আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। বইয়ের নামকরণে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করি। কারণ লেখক কতটা সৃজনশীল, তা প্রতিভাত হয় তার বইয়ের নামকরণের মধ্য দিয়ে। দুর্বল লেখকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামকরণেও দুর্বলতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। কখনো কখনো শক্তিমান লেখকরাও নামকরণে সৃজনশীলতা দেখাতে ব্যর্থ হন। অনেকে আবার নাম নকলও করে থাকেন। আবার কখনো নামের সঙ্গে কাকতালীয়ভাবে নাম মিলে যায়। কাকতালীয়ভাবে মিলে গেলে লেখককে দোষ দেওয়া চলে না। কিন্তু লেখক যখন জানেন তার লেখা বইটির যে নাম তিনি দিয়েছেন সেই নামে পৃথিবীর অন্য লেখকের বই রয়েছে, সেক্ষেত্রে নামটি ব্যবহার না করাই উত্তম মনে করি। লেখক যদি তার পূর্বজ লেখকের দ্বারা নামকরণের অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে উচিত বইয়ের ভূমিকায় স্পষ্টভাবে অনুপ্রাণিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে দেওয়া।
বইয়ের নামকরণ প্রসঙ্গে আর্থার শোপেনহাওয়ারের কথাটি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। তিনি বলেছেন, ‘গ্রন্থের নামকরণের বিশেষ সাবধান হওয়া কর্তব্য। কারণ, চিঠির ঠিকানার মতোই ওই নামের দ্বারা তাকে পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। নাম যদি খুব দীর্ঘ হয়, বা অর্থহীন হয়, কিংবা দ্ব্যর্থপূর্ণ হয়, তবে তেমন নাম ভালো নয়; যদি তা মিথ্যা বা ভিন্নার্থবোধক হয়, তবে তো কথাই নেই—তেমন গ্রন্থ ভুল ঠিকানাযুক্ত চিঠির দশা প্রাপ্ত হয়। আর যদি চুরি করা নাম হয়, অর্থাৎ অপর কোনো বইয়ের নাম হয়, তবে তার মতো মন্দ আর কিছু হতে পারে না। কারণ, প্রথমত, তা একরূপ সাহিত্যিক চৌর-কর্ম। দ্বিতীয়ত, তার দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে, ওই লেখকের লেশমাত্র মৌলিকতা নেই।’
উজানবাঁশি প্রথম যখন লিখতে শুরু করি তখন তার কোনো নাম ছিল না, নাম ছাড়াই লিখছিলাম। নাম নিয়ে খুব ভাবছিলাম। একেকটা নাম ঠিক করি, আবার বাতিল করি। আবার ভাবি। গল্পকার মোজাফ্ফর হোসেনকে বলি। তিনি বাতিল করে দেন। কোনো নামই তার পছন্দ হয় না। একটা সময় হাল ছেড়ে দিই। কিছুদিন পর একটা নতুন নাম রাখলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, এটাই হবে উপন্যাসের নাম। মোজাফফর শুনেই বললেন, ‘এটাও হলো না। আপনার বিষয়ের সঙ্গে যাচ্ছে না।’ পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্সের প্রকাশক কামরুল হাসান শায়ক ভাইও বললেন, ‘নামটি যুৎসই মনে হচ্ছে না। আরও ভাবেন।’ ভাবার বদলে আমি আবারও হাল ছেড়ে দিলাম। হঠাৎ একদিন মাথায় উঁকি দিল একটি নাম—উজানবাঁশি। নামটা বিষয় সম্পৃক্ত মনে হলো। এই নামই রাখব সিদ্ধান্ত নিলাম। মোজাফ্ফর বললেন, ‘এই নাম হতে পারে। আগের গুলোর চেয়ে এটি অনেক ভালো।’ একদিন কথাসাহিত্যিক হামীম কামরুল হকের সঙ্গে দেখা। দুজন বাংলা একাডেমির বাসে করে যাচ্ছিলাম। তাঁকে বললাম নামটি। তিনি শুনেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। বললেন, ‘আর কোনো কথা নেই, এটাই ফাইনাল, অসাধারণ নাম। এর কোনো তুলনা হয় না।’ দুই লেখক-বন্ধুর স্বীকৃতি পেয়ে আনন্দিত হলাম এবং এ নামই চূড়ান্ত করলাম।
শুরুতে যে মিথের কথা বললাম, তাতে যে কারো মনে হতে পারে, উজানবাঁশি সম্ভবত মিথ কেন্দ্রিক উপন্যাস। মোটেই তা নয়। উজানবাঁশিতে মিথ ব্যবহার হয়েছে ঠিক ততটুকু, যতটুকু ডিমান্ড করেছে আখ্যান। প্রধান চরিত্র বাঘামামার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে আরও অনেক চরিত্র। যেমন উজানগাঁর ভূস্বামী অনাদি দত্ত, দেখতে যিনি অবিকল রবীন্দ্রনাথ, যিনি রবীন্দ্রনাথের মতোই আলখাল্লা পরেন, রবীন্দ্রনাথের মতোই তার মাথার চুল, মুখের দাঁড়িগোঁফ। যেমন মাওলানা আবদুল কয়েদ, যিনি উজানগাঁয়ের সর্বজন মান্য ব্যক্তিত্ব। তিনি বাঘামামাকে নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, মানুষ কি চল্লিশ বছর বাঘের পেটে থাকতে পারে? একদিন মাটি খুঁড়তে গিয়ে কায়েদ মাওলানা আবিষ্কার করেন এক প্রাচীন শিলালিপি। সেই শিলালিপির লিপিকে ঘিরে মোড় নেয় আখ্যান। শরিয়ত পন্থা থেকে মারেফত বা আধ্যাত্মবাদের দিকে ধাবিত হন কায়েদ মাওলানা। তার পুত্র মোহন রেজা, যার গায়ে ভেসে বেড়ায় বুনো কলমির ঘ্রাণ, ঘুমে-জাগরণে যে শুনতে পায় হট্টিটি পাখির ডাক, প্রাচীন শিলালিপির বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে শুরু করে জ্ঞান অন্বেষণ। আরও আছে শেক আহমদ ওরফে শেকা। ভরা পূর্ণিমা রাতে মানুষ, পশুপাখি আর কীটপতঙ্গরা জেগে থাকে শেকার বাঁশির সুরে। ময়ূরমুখো নৌকায় চড়ে নীলাক্ষির ঘাটে ঘাটে গল্পের আসর জমিয়ে তোলেন রহস্যপুরুষ মোখেরাজ খান। দত্তপরিবার দেশান্তরি হওয়ার পর নিশিমহলে শুরু হয় সাপের বসতি। সেই কবে নিখোঁজ হওয়া অনাদি দত্ত আলখাল্লা পরে ঘুরে বেড়ান পথে-প্রান্তরে, দেখা দেন মানুষের স্বপ্নে। যৌথ বাহিনীর অভিযানের মুখে সুড়ঙ্গ পথ ধরে কি বায়ুবেলুনে চড়ে পালিয়ে যান স্বৈরশাসক কুতুব বকশি ওরফে দাদাসাব। আছে আরও অনেক চরিত্র। প্রত্যেক চরিত্রকে পূর্ণ অবয়বে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছি। বাস্তবতা ও কুহকের মিশেলে মূলত বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সমাজ ও রাজনীতি, রক্ষণশীলতা ও উদারপন্থা, জ্ঞান ও নির্জ্ঞান এবং বহুমাত্রিক সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব নিয়ে রচিত উপন্যাস উজানবাঁশি।
একজন ঔপন্যাসিক অনেক উপন্যাস লেখেন। সবই কি তার পছন্দসই হয়ে ওঠে? শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে? না, কোনো কোনোটি তার অধিক পছন্দের হয়। তিনি মনে করেন, এই উপন্যাসে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তা ঠিকঠাক বলতে পেরেছেন। মাঝেমধ্যে কোনো কোনো পাঠক আমার কাছে জানতে চান তিনি আমার কোন উপন্যাসটি পড়বেন। তখন দ্বিধায় পড়ে যাই। কোনটির কথা বলব? রাজনটী, না বেগানা? হীরকডানা, না কালকেউটের সুখ? শেষ জাহাজের আদমেরা, না মায়ামুকুট? উজানবাঁশি লেখার পর মনে হচ্ছে, এখন যদি কেউ আমাকে এমন প্রশ্ন করেন, আমি তাঁকে দ্বিধাহীন উত্তর দেব, উজানবাঁশি পড়ে দেখতে পারেন। কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে, এ যাবৎ যে কটি উপন্যাস লিখেছি সেগুলোর মধ্যে উজানবাঁশি শ্রেষ্ঠ। এ উপন্যাসে আমি যা বলতে চেয়েছি, ঠিকঠাক বলতে পেরেছি। যে বার্তাটা দিতে চেয়েছি, ঠিকঠাক দিতে পেরেছি। শিল্পের যে নির্মাণটা করতে চেয়েছি, ঠিকঠাকভাবে করতে পেরেছি। যদি কেউ আমার একটিমাত্র উপন্যাস পড়তে চান, তবে উজানবাঁশিই পড়বেন।
এবং অপেক্ষায় আছি, এই উপন্যাসে যা আমি বলতে চেয়েছি কোন পাঠক আমার মূল বক্তব্যটা ঠিকঠাক ধরতে পারেন। কারণ উজানবাঁশিতে আমি অপেক্ষকৃত কৌশলী। মূল সত্যকে ঢেকে দিয়েছি অসংখ্য মিথ্যায়। মূল কাহিনিকে ভেঙে দিয়েছি অসংখ্য উপকাহিনি দিয়ে। অনেকটা মুক্তার মতো। মুক্তোটি বের করতে হলে প্রথমে সমুদ্রে যেতে হবে। তারপর ঝিনুক ধরতে হবে। ঝিনুকের খোলসটি ছড়াতে হবে। নাড়িভুঁড়ি কেটে তারপর মুক্তোদানাটি বের করে আনতে হবে। কিংবা সেই ফুলের মতো, যার অসংখ্য পাপড়ি। কুঁড়িটিকে পেতে হলে একটি একটি করে পাপড়ি ছিঁড়তে হবে। তারপর হদিস পাওয়া যাবে কুঁড়ির এবং কুঁড়িতে অবস্থিত মধুর।
জানি, উজানবাঁশি নিয়ে আমার এই যে তৃপ্তি, তা ক্ষণস্থায়ী। হয়তো অল্প কিছুদিন থাকবে। একটা সময় এই তৃপ্তি উবে যাবে। উজানবাঁশিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো নতুন কোনো উপন্যাসের বিষয় হয়তো পেয়ে যাব। হয়তো সেই উপন্যাস ছাড়িয়ে যাবে উজানবাঁশিকে। যদিও আমি নিশ্চিত না। আসলে ঔপন্যাসিক তার সৃষ্টির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেন না। তিনি বিস্তর লেখেন। কোনটি কালের বিচারে টিকে যাবে আর কোনটি প্রত্যাখ্যাত হবে, তা তার পক্ষে বলা মুশকিল। তবু অপেক্ষায় আছি, উজানবাঁশিকে পাঠক গ্রহণ করবেন। হতেও তো পারে, যে কালের কাছে আমি অঞ্জলি পেতেছি সেই কাল আমাকে নিরাশ করবে না।
স্বকৃত নোমান, কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক, বাংলাদেশ